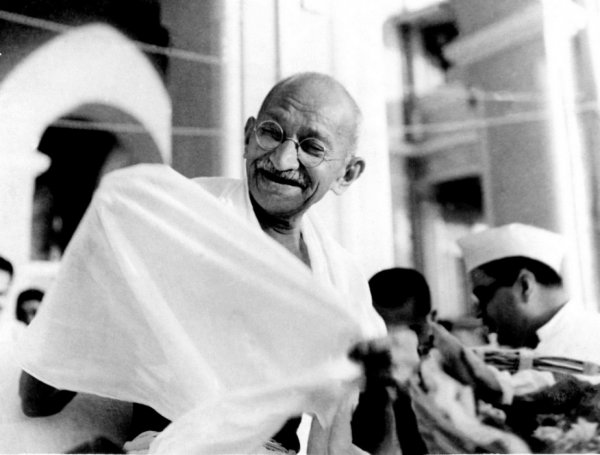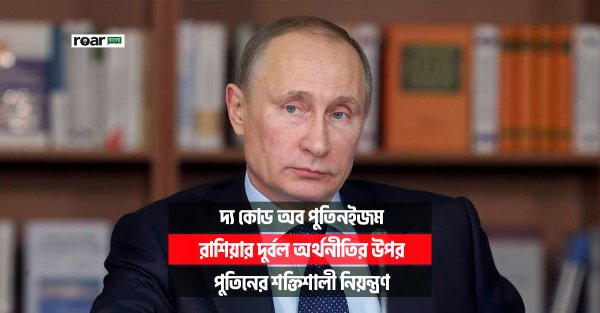.jpg?w=1200)
জান-মালের নিরাপত্তার জন্য মানুষের সীমানা প্রাচীর গড়ার ইতিহাস বেশ দীর্ঘ। চীনের মহাপ্রাচীর থেকে জার্মানির বার্লিন প্রাচীর— যুগে যুগে এমন বহু উদ্যোগ দেখা গেছে। সাম্প্রতিক সময়ের দিকে চোখ বোলানো যাক। গ্রাম, নগর, শহর ভরে যাচ্ছে প্রাচীরে প্রাচীরে। আধুনিক বিশ্বের সকল অরাজকতাকে সামাল দিতে সকলের কাছে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হলো প্রাচীর। নিরাপত্তার প্রশ্নে প্রাচীর নামের এই পাথেয়টির তুলনা বোধ হয় আর কিছুর সঙ্গেই চলে না। আবার নিরাপত্তার সব উপকরণ থাকলেও, বাড়ির চারদিক ঘিরে প্রাচীর থাকা চাই-ই চাই। এখন প্রশ্ন হলো, প্রাচীর কি আদৌ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে? না-কি সকলের অগোচরে উল্টো বিপদ বাড়িয়ে দেয়?
২০১৯ সালে টেডএক্সে দেওয়া এক বক্তব্যে সোশাল ডিজাইনার (Social Designer) আলেকজান্দ্রা আউই বলেন, “প্রাচীর শুধু নিরাপত্তার অনুভূতি দেয়, যা প্রকৃত নিরাপত্তা থেকে আলাদা।” ‘দ্য ইনট্যানজিবল ইফেকটস অফ ওয়ালস’ শীর্ষক সেই বক্তৃতার পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ তুলে ধরা হচ্ছে রোর বাংলার পাঠকদের জন্য।

মানবজাতি প্রাচীর গড়তে ভালোবাসে। আপনি কি কখনো এটা লক্ষ্য করেছেন? আমরা প্রতিটি বিষয়ের জন্য প্রাচীর গড়ে তুলি, যেমন: আশ্রয়ের জন্য, সুরক্ষার জন্য, গোপনীয়তার জন্য। বিগত ৭০ বছরে, দেশে দেশে প্রাচীরের সংখ্যা হয়ে গেছে দ্বিগুণ। বর্তমানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির থেকেও বেশি প্রাচীর রয়েছে, যা সংখ্যায় স্নায়ুযুদ্ধের সময়কালের থেকেও বেশি।
বার্লিন প্রাচীরের পতন এবং জার্মানির বেড়ে ওঠা; আমার কাছে সবসময় একটি নতুন বিশ্বের সূচনার মতো ছিল। সেখানে কোনো প্রতিবন্ধক ছিল না। কিন্তু ৯/১১ এর হামলার পর থেকে প্রকল্পের সংখ্যা বেড়েছে। বর্তমানে তা বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে গেছে। নতুন করে অন্তত ৩০টি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে, কিংবা নির্মাণ করা হয়েছে। প্রাচীর ও বেড়া সবসময় অন্য গোষ্ঠী থেকে, অপরাধ থেকে, অবৈধ ব্যবসা থেকে নিরাপত্তা পাবার জন্য তৈরি করা হয়। কিন্তু এগুলো স্রেফ নিরাপত্তার অনুভূতি দেয়, যা প্রকৃত নিরাপত্তা থেকে আলাদা। এগুলো আমাদের নিরাপদ বোধ করাতে পারলেও, নিজে থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারে না।
নিরাপত্তার দেওয়ার বদলে এগুলো ভিন্ন কিছু করে— আমাদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে। পক্ষ-বিপক্ষ তৈরি করে। শত্রুপক্ষ তৈরি করে। বাস্তবিক প্রাচীর আমাদের মস্তিষ্কে আরেকটি প্রাচীর গড়ে তোলে, সেটা হলো মনস্তাত্ত্বিক প্রাচীর। মনস্তাত্ত্বিক প্রাচীর আমাদের ধীরে-ধীরে দৃষ্টিহীন করে তোলে। অন্য পাশের লোকেদের সঙ্গে আমাদের যে মিল আছে, তা বুঝতে দেয় না।
এছাড়াও, মনস্তাত্ত্বিক প্রাচীর এতটাই শক্তিশালী হয় যে, তা বাস্তবিক প্রাচীর নির্মাণ, সংরক্ষণ বা শক্তিশালীকরণে আমাদেরকে আরো উৎসাহিত করে। বাস্তবিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রাচীর ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত, এবং সবসময় একে অন্যের সাথে আবির্ভূত হয়। বাস্তবিক প্রাচীর মনস্তাত্ত্বিক প্রাচীরকে শক্তিশালী করে, এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রাচীর বাস্তবিক প্রাচীরকে— এভাবেই ধ্রুব চক্রটি চলে; কখনও একটি অংশ পড়ে গেলে চক্রটি ব্যাহত হয়।
বার্লিন প্রাচীরের কথাই ধরা যাক। প্রাচীরটি যখন গড়ে তোলা হয় তখন কে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছে, তা বলা মুশকিল। কারণ তখন এর আশেপাশে বসবাসকারী জনসাধারণ এক হিসাবে চিহ্নিত হতো। সেখানে পক্ষ-বিপক্ষ বলে কিছু ছিল না। সেখানে অন্য কেউ বলে কিছু ছিল না। কিন্তু বিচ্ছেদকালীন, উভয় পাশ আলাদাভাবে বিকশিত হয়েছিল, এবং লোকেরা নিজেদের জন্য পৃথক পরিচয় তৈরি করেছিল। ফলে, সেখানে হঠাৎ করেই পক্ষ-বিপক্ষ তৈরি হয়ে গিয়েছিল।
বস্তুত, সেখানে একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রাচীর গড়ে উঠেছিল। ১৯৮৯ সালে যখন বার্লিন প্রাচীরের পতন হয়, তখনও লোকের মাথায় মনস্তাত্ত্বিক প্রাচীরটি রয়ে যায়। পূর্বাঞ্চলীয় জার্মানদেরকে তাদের নিজেদের দেশে পুনঃএকত্রিত হতে হয়েছে। তবে তাদের অনেকে আজও মনে করেন, তারা কখনোই পুরোপুরি এক হতে পারেনি। প্রাচীরের রয়ে যাওয়া প্রভাব এখনও পরিলক্ষিত হয়।

২০০৫ সালে বার্লিনের ফ্রেই ইউনিভার্সিটির এক গবেষণায় দেখা গেছে, পুনরায় একত্রীকরণের ১৫ বছর পরেও জার্মানরা বিশ্বাস করত যে, প্রাচীরের এক প্রান্ত আর অপর প্রান্তের মধ্যে বিস্তর তফাৎ। গবেষণায় আরো দেখা গেছে, রাজনৈতিক মতবাদ ও এর মধ্যকার পার্থক্যের মধ্যে একটি যোগসূত্র রয়েছে; যিনি যত বেশি জার্মান পুনরেকত্রীকরণের বিপক্ষে ছিলেন, তিনি তত বেশি অনুমান করেছিলেন যে— শহরগুলোর মধ্যকার তফাৎ বিস্তর। আদতে, মনস্তাত্ত্বিক প্রাচীর শহরের এক প্রান্তকে অপর প্রান্ত থেকে দূরে রেখেছে; এবং প্রাচীরটি যতটা উঁচু ও শক্তিশালী, তার কাছে পৌঁছানো ততটা দুষ্কর।
প্রাচীরের প্রভাব আজও আছে কি-না, তা আমি দেখতে চেয়েছিলাম। সেজন্য বার্লিন প্রাচীর না দেখে বেড়ে উঠেছে এমন একদল তরুণ জার্মানদের উপর আমি পুনরায় গবেষণা করার সিদ্ধান্ত নেই। ফলাফলে দেখা যায়, এই প্রজন্ম, আমার প্রজন্ম, পূর্ব-পশ্চিমের অধিকাংশই ভূগোলে কাঁচা।
তবে আমাদের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে, বিষয়টিকে ইতিবাচক হিসাবে দেখা যেতে পারে, তাই না? আমাদের বাস্তবিক প্রাচীর দেখার অভিজ্ঞতা হয়নি। আদতে বাস্তবিক প্রাচীর আমাদের মাঝে মনস্তাত্ত্বিক প্রাচীর গড়ে তুলতে সক্ষম হয়নি। তাই এটাকে আমি গুরুতর সংকেত হিসাবে দেখতে পারি যে, বিভাজিত জার্মানির ভবিষ্যত হয়তো মনস্তাত্ত্বিক প্রাচীরবিহীন হবে।
তবে আমি মনে করি, আমাদের বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হবে। একটি প্রাচীর বিলোপ পেতে পারে। কিন্তু ইতোমধ্যে, আরও এক বিলিয়ন গড়ে উঠেছে। উদাহরণ হিসাবে বলতে পারি, বর্তমান পৃথিবীজুড়ে ফটকবেষ্টিত কমিউনিটি গড়ে ওঠার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। (ফটকবেষ্টিত কমিউনিটি হচ্ছে আবাসিক এলাকার আধুনিক সংস্করণ, যেখানে সর্বক্ষণিক নজরদারি ও কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকে।)
একভাবে, ফটকবেষ্টিত কমিউনিটিকে রাষ্ট্রের অনুকরণ করতে দেখা যায়। এর কারণ উভয়ই নাগরিকদেরকে অন্যান্য নাগরিকদের থেকে সুরক্ষিত রাখতে চারদিকে সীমানা প্রাচীর ও বেষ্টনী গড়ে তোলে। তবে ফটকবেষ্টিত কমিউনিটির বেলায় তা হয় ক্ষুদ্র পরিসরে। আর দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো— ফটকবেষ্টিত কমিউনিটিতে এটা সকলের ইচ্ছাতে হয়। তবে বেষ্টনীর ভিতরে ও বাইরে বসবাসকারী মানুষের উপর উভয়ের শারীরিক ও মানসিক প্রভাব অভিন্ন। এগুলো শহর, পাড়া, খেলার মাঠও বিভক্ত করে।

গত বছর বসন্তের কথা। আমি ব্রাসেলসের দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি প্রকল্পে কাজ করেছি। ঘটনাটি সেখানকার। উভয় বিদ্যালয় প্রবেশদ্বার ও প্রাঙ্গণ ভাগ করে নিয়েছে। উভয় বিদ্যালয়ে ডাচ ভাষায় পড়ানো হয়। কিন্তু এর একটিতে প্রধানত বেলজিয়ামের বাচ্চারা এবং অপরটিতে অভিবাসী বাচ্চারা পড়ে। প্রাচীর ও বেড়া বিদ্যালয় দুটিকে বিভক্ত করেছে।
বিদ্যালয় প্রাঙ্গণকে বিভক্তকারী বেড়াটি বাচ্চাদের মাঝে মিথষ্ক্রিয়ার কোনো সুযোগ দেয়নি, বরং তাদেরকে বিভাজিত করেছে। আমি যখন কাজ শুরু করলাম, তখন সেখানকার বাচ্চাদেরকে তাদের অন্য পাশের বন্ধুদের সঙ্গে বেড়ায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে দেখে কিছুটা ব্যথিত হলাম (বেড়ার উপর দাঁড়িয়ে আছে এমন এক বাচ্চার ছবি দেখিয়ে)। আরও ভয়াবহ বিষয় হলো— এদের অধিকাংশ বাচ্চাই কখনো অন্য পাশে বন্ধু বানানোর সুযোগ পাবে না।
বিদ্যালয় এমন একটি জায়গা যেখানে বাচ্চারা একসঙ্গে শিক্ষকের কাছ থেকে শেখে। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, একে অপরের কাছ থেকে শেখা। সেখানে বৈচিত্র্য যত বেশি থাকবে, সবাই তত শিখতে পারবে। বস্তুত, বিদ্যালয় মানব জীবনের একমাত্র সময় হতে পারে, যেখানে সামাজিক ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব। তবে বাচ্চাদেরকে তাদের বিকাশকালে বিভাজিত করলে, তা তাদের একত্রীকরণকে অসম্ভব না করলেও অত্যন্ত কঠিন করে তুলবে।
তখনও ব্রাসেলসে এক আমিই ছিলাম যে বেড়াটিকে সমস্যা হিসাবে দেখছিলাম। বেশিরভাগ অভিভাবক, শিক্ষক ও শিশুরা কাঠামোটির দিকে নজর দিচ্ছিল না। অন্তত তারা এটা নিয়ে প্রশ্ন করা বন্ধ করে দিয়েছে। তাদের জন্য এটা যা ছিল, তা-ই। কেউ একে কখনো অন্যভাবে দেখেনি। বরং, সকলে এর পক্ষে। আমি একবার একটি ছেলেকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে অন্য পক্ষের সঙ্গে খেলতে চায় কি-না, এবং সে বলল, “না”। আমি তাকে আবার জিজ্ঞেস করলাম, বেড়া না থাকলে সে তাদের সাথে খেলবে কি-না? প্রতিউত্তরে সে বলল, “সম্ভবত”। কিন্তু সে আবার সঙ্গে সঙ্গেই বলল, বেড়া থাকা উচিত, কারণ অন্যপক্ষ খারাপ; তারা কখনোই বল ফিরিয়ে দেয় না।
ব্যাপারটি হাস্যকর। কারণ, আমি উভয় পাশের বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম, এবং সবাই আমাকে বলেছিল যে অন্যপক্ষ খারাপ; এর কারণ তারা কখনোই বল ফিরিয়ে দেয় না। উভয় পাশের বাচ্চারা একে অপরকে অপছন্দ করত। এ নিয়ে তাদের মাঝে নিয়মিত কথা-কাটাকাটি হতো; যা সকলের কাছে বেড়া থাকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করার প্রধান কারণ। তাদের ভাবত, এটা বাচ্চাদের একে অপরের থেকে সুরক্ষিত রাখে। অন্তত তাদের খেলনা রক্ষা করে এবং বিশৃঙ্খলা রোধ করে। মাঝেমধ্যেই বাচ্চারা তাদের বল ফিরে পেতে বেড়ার নিচ দিয়ে হামাগুড়ি দিত; এটা থামাতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেখানে ধাতব প্লেট দিয়ে দিয়েছে। এরপর থেকে তারা বেড়া ডিঙানো শুরু করে।

আমি জানি না ব্রাসেলসে আগে কোনটি এসেছে; মনস্তাত্ত্বিক প্রাচীর— যা এতটাই শক্তিশালী হয়েছে যে তা তাদের দিয়ে বাস্তবিক প্রাচীর তৈরি করিয়েছে, নাকি বাস্তবিক প্রাচীর— যা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণেও সামাজিক ব্যবধানকে আরো জোরালো করেছে। কিন্তু আমি যখন সেখানে কাজ শুরু করি তখন আমি পরিস্থিতি কিছুটা পরিবর্তন করতে চেয়েছিলাম। তাদের মধ্যে কতটা মিল রয়েছে, তা উভয় পক্ষকে দেখাতে চেয়েছিলাম।
বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, এটা করা খুব কঠিন নয়। কারণ, বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের একটিতে ডাচ এবং অপরটিতে ফরাসি, তুর্কি ও আরবি ভাষায় কথা বলা হলেও, খেলার সময় তাদের সকলেই একটি সর্বজনীন ভাষায় কথা বলে। দেখা গেল, তাদের মধ্যে অনুমিত পার্থক্যের চেয়ে খেলার ইচ্ছা প্রবল ছিল। তাই আমি বিভিন্ন খেলার আয়োজন করলাম (টেনিস, ব্যাডমিন্টন ইত্যাদি), যা বেড়াটিকে প্রতিবন্ধকতার পরিবর্তে একটি ইন্টারফেসে পরিণত করেছিল। এটা দেখতে সাধারণ মাঠের মতো লাগছিল।
এক সময় বাচ্চারা একসাথে ড্রয়িং করা শুরু করল, নিজেদের মধ্যে পেন্সিল বিনিময় এবং ফোনে কথা বলতে লাগল। বিশেষত, ফোনে কথা বলার ব্যাপারটি সত্যিই দারুণ ছিল। কারণ, বাচ্চারা ডিভাইসটির মাধ্যমে অন্য পাশের কথা শুনতে পারত; যা তাদের এতটাই বিস্মিত করেছিল যে তারা আর কথা না বলে পারেনি।
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বাবা-মা তাদের সন্তানের দৈনন্দিন জীবন ও পরিবেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাই আমি জানতাম, পরিবর্তন আনতে চাইলে যে করেই হোক আমাকে তাদেরও দেখাতে হবে যে, অন্য পাশের বাচ্চাদের সাথে তাদের বাচ্চাদের কতটা মিল রয়েছে। তবে পিতা-মাতার ক্ষেত্রে, এটা করা অনেক কঠিন। কারণ, তাদের অধিকাংশই ভিন্ন ভাষায় কথা বলে, ভিন্ন বেতনে বিভিন্ন চাকরি করে, ভিন্ন সমাজিক বলয়ে বাস করে, ভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী, ভিন্ন সংস্কৃতি চর্চা করে এবং ভিন্ন মূল্যবোধের অধিকারী। তাহলে আমি কীভাবে দেখাতে পারি যে, তাদের মধ্যে কতটা মিল রয়েছে?
আমি নিজে থেকে তাদের না বুঝানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। তবে আমি চাচ্ছিলাম তাদের সন্তানেরাই এই কাজটি করুক। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি ছবি প্রদর্শনীর আয়োজন করলাম; ছবিগুলোতে দেখা যাচ্ছিল, প্রাচীর থাকা সত্ত্বেও বাচ্চারা একসাথে খেলছে। প্রদর্শনী শেষে এ সম্পর্কে তাদের চিন্তা, চেতনা ও আকাঙ্ক্ষার কথা বড় কাঠের বাক্সে লিখতে বললাম। আর বাক্সের গায়ে লিখে দিলাম “তুমি কী ভাব?”
অনেকে তার উপর “হ্যাঁ” লিখেছিল। আমি কখনোই আমার মতামত কিংবা এমন কোনো কিছুর কথা উল্লেখ করিনি যা সকলের অনুসরণ করা উচিত, তাহলে তারা কোন প্রশ্নের উত্তরে ‘হ্যাঁ’ লিখেছিল? আমি তাদের জিজ্ঞেস করেছিলাম, আর তারা বলেছিল, বেড়ার প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ, আমরা অন্য পক্ষের সঙ্গে খেলতে চাই।
কখনো প্রস্তাবিতই হয়নি— এমন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য ছবিগুলো যথেষ্ট ছিল। তারা এবার পরিস্থিতির অযৌক্তিকতা বুঝেছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল যে, বেড়াটি কতটা অপ্রয়োজনীয়। আমাকে আর তাদের জোর করে বুঝাতে হয় নি। প্রদর্শনীটি দুই পক্ষকে একবারের জন্য হলেও তাদের মাঝের সাদৃশ্যতা দেখিয়েছে। সেদিন সেখানে পক্ষ-বিপক্ষ বলে কিছু ছিল না। অন্য কেউ বলে কিছু ছিল না। অবশেষে, মনস্তাত্ত্বিক প্রাচীরটি ক্ষয় হতে শুরু করেছিল।

আমি ‘ক্ষয়প্রাপ্ত’ শব্দটি ব্যবহার করছি। এর কারণ, মনস্তাত্ত্বিক প্রাচীর ভাঙা খুব সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কাজটি বাস্তবিক প্রাচীর ভাঙার থেকেও অনেক কঠিন। এর জন্য আমাদের নিজেদের মতামত ও বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে। এমনকি নিজেদের ভুলও স্বীকার করতে হতে পারে। ব্রাসেলসে যা ঘটেছিল তা ছিল একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, এমন একটি পদক্ষেপ যা জার্মানিতে কয়েক প্রজন্ম বয়ে নিয়ে এসেছে।
ব্রাসেলস ও জার্মানির মতো বিশ্বেজুড়ে এমন অনেক উদাহরণ আছে, যা থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি। অথচ যে প্রাচীর মূল সমস্যার সমাধান করতে পারে না, তাকেই আমরা সমস্যার সমাধান হিসাবে দেখি। কিছু করতে পারলে, এটা শুধু সমস্যার উপসর্গ কমাতে পারে।
তাই আমি চাই, এরপরে আপনারা যখন প্রাচীর গড়ার পরিকল্পনা করবেন, কিংবা প্রাচীর গড়তে চায় এমন কাউকে সমর্থন করবেন, আপনারা আজ এর প্রভাব সম্পর্কে যা কিছু জেনেছেন, তা স্মরণ করবেন। কারণ, মামুলি প্রাচীর খুব একটা সুরক্ষা দিবে না। উল্টো, যারা ভৌগোলিক ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও নিজেদের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ ভাগাভাগি করে নিতে চায়, তাদের প্রভাবিত করবে। তাদের জন্য আপনি একটি নয়, দুটি প্রাচীর গড়ছেন— যার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে তাদের কয়েক দশক ও কয়েক প্রজন্ম লেগে যাবে।



.jpg?w=600)