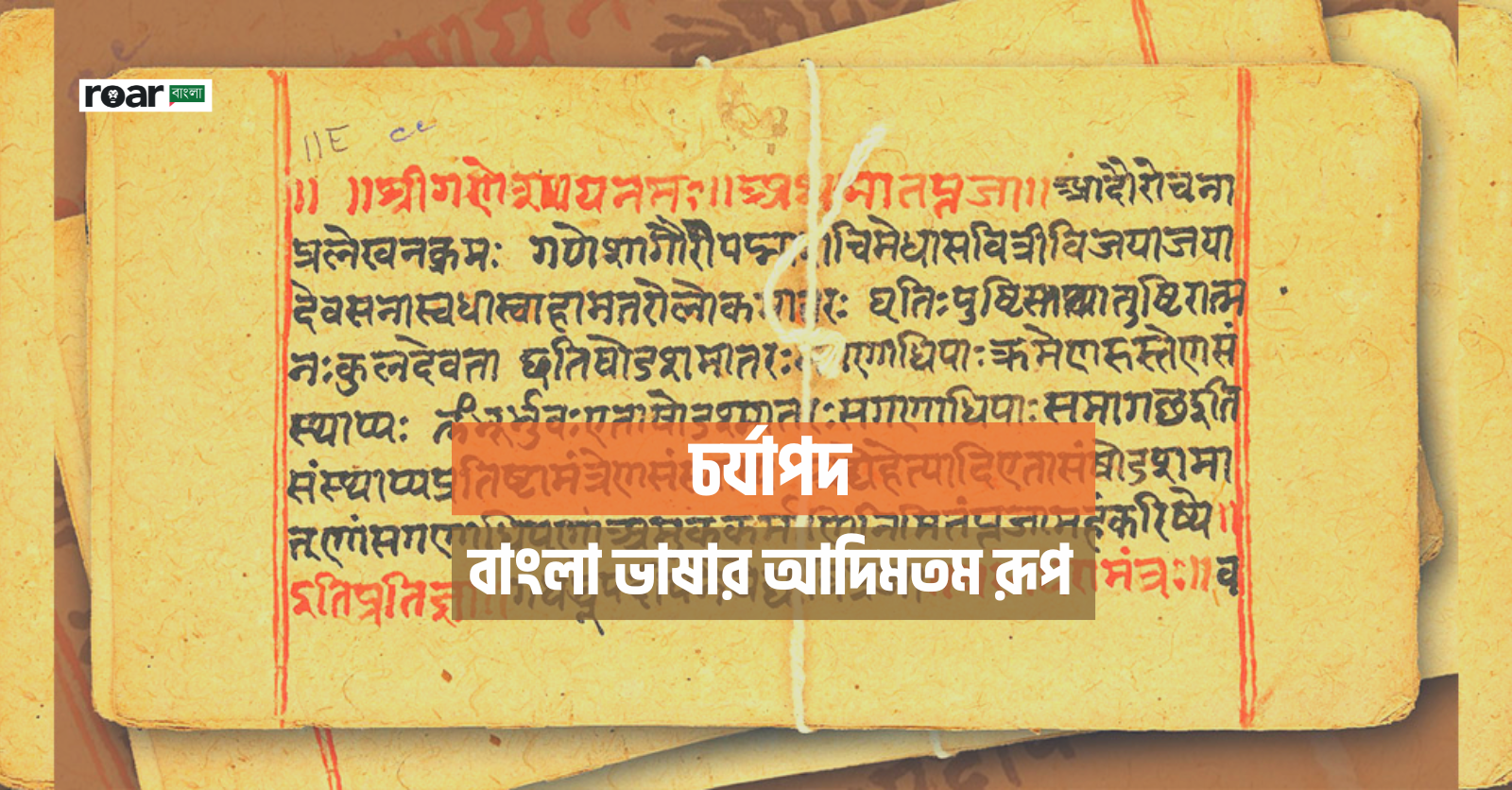
আজ কথা হবে বাংলা সাহিত্যের একেবারে গোড়ার দিকটা নিয়ে। বঙ্কিম, শরত কিংবা কালীপ্রসন্ন নন, কাহ্নপা আর লুইপাদের সাহিত্যের কথা বলছি। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম কাব্য তথা সাহিত্য নিদর্শন হলো এই চর্যাপদ। বাংলা ভাষার উৎস ধরা হয় যে ভাষাকে, অর্থাৎ ‘নব্য ভারতীয় আর্যভাষা’, তারও প্রাচীনতর নিদর্শন চর্যাপদ।
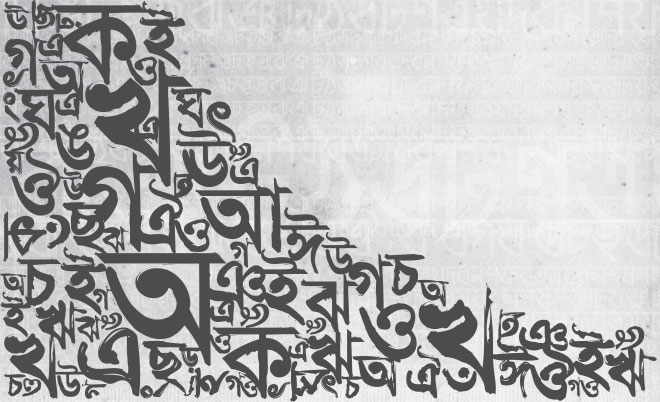
এই বাংলারই আদিমতম রূপ চর্যাপদ; Source: The daily star
সান্ধ্যভাষায় রচিত খ্রিস্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে রচিত এই গীতিপদাবলীর রচয়িতারা ছিলেন সহজিয়া বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ। চর্যাপদ রচনার পেছনে তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিলো বৌদ্ধধর্মের গূঢ় অর্থ সাংকেতিক রূপের আশ্রয়ে ব্যাখ্যা করা। চর্যাপদ থেকে পরবর্তী সময়ে বাংলা সাধনসঙ্গীতের সূচনা হয়। তাই ধরেই নেওয়া যায়, চর্যাপদ ছিল একটি নির্দিষ্ট ধর্মগোষ্ঠী দ্বারা রচিত এবং একটি ধর্মগ্রন্থজাতীয় রচনা। তারপরও একে আমাদের সাহিত্যের ‘গোড়ার দিক বলার মূল কারণ হলো এর ভাষা। এর ভাষার সঙ্গে আমাদের আজকের বাংলা ভাষার অদ্ভুত এক সাযুজ্য পাওয়া যায়। ধর্মের ব্যাখ্যার পাশাপাশিও চর্যাপদে ফুটে উঠেছে সেই নির্দিষ্ট সময়ের সামাজিক ও প্রাকৃতিক চিত্রাবলী। তাই এর সাহিত্যগুণ এতগুলো বছর পরও তার আবেদন হারায়নি পাঠক কিংবা গবেষক সমাজের কাছে।
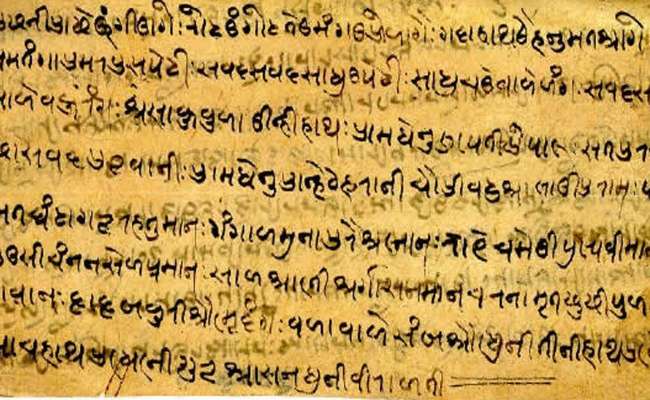
আলো-আঁধারি ভাষা; Source: dailyo.in
মজার ব্যাপার হলো, আবিষ্কারের পর সবাই চর্যাপদ নিয়ে একপ্রকার টানাটানিই শুরু করেছেন! টানাটানিটা মূলত এর ভাষা নিয়ে। অসমিয়ারা দাবি করে এর ভাষা অসমিয়া, মৈথিলিরা বলে মৈথিলি, উড়িয়ারাও দাবি জানায় এর ভাষা উড়িয়া! সকলের দাবিকে সমন্বিতভাবে মিলিয়ে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এর নাম দিয়েছেন বঙ্গ-কামরূপী বা প্রত্ন-বাংলা-আসামি-উড়িয়া-মৈথিলি ভাষা। ভাষাবৈজ্ঞানিকদের বহু তর্ক-বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে তারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, চর্যাপদ বাংলারই আদিমতম রূপ নিয়ে রচিত। এই যোগসূত্র স্থাপনে ভূমিকা রেখেছেন ভাষাবিদ ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
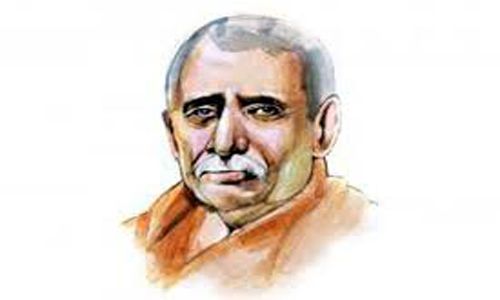
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী; Source: sokalerkhobor24.com
চর্যাপদের ভাষা অস্পষ্ট এবং প্রায় দুর্বোধ্য রীতিতে গঠিত, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাই এই ভাষার নাম দিয়েছেন ‘সান্ধ্য কিংবা সন্ধ্যা ভাষা’। তার মতে,
“সহজিয়া ধর্মের সকল বই-ই সন্ধ্যা ভাষায় লেখা। সন্ধায় ভাষার মানে আলো আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বোঝা যায়,খানিকটা বোঝা যায় না। অর্থাৎ এই সকল উঁচু অঙ্গের ধর্মকথার ভিতরে একটা অন্য ভাবের কথাও আছে। সেটা খুলিয়া ব্যাখ্যা করিবার নয়। যাহারা সাধন ভজন করেন, তাঁহারাই সে কথা বুঝিবেন, আমাদের বুঝিয়া কাজ নাই”।
তিব্বতি ভাষায় সন্ধ্যা ভাষার অর্থ ‘প্রহেলিকাচ্ছলে উক্ত দুরূহ তত্ত্বের ব্যাখ্যা। ম্যাক্সমুলার সন্ধ্যার অর্থ করেছেন ‘প্রচ্ছন্ন উক্তি (Hidden saying)’। চর্যাপদের ছন্দ নির্ণয় করা হয়েছে মাত্রাবৃত্ত।
চর্যাপদ নিয়ে যারা মাথা খাটিয়েছেন, করেছেন ভাষাতত্ত্বের নানান গবেষণা, তাদের মধ্যে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, পরেশচন্দ্র মজুমদার ও ডক্টর রামেশ্বরের নাম উল্লেখযোগ্য। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবারে রয়েল লাইব্রেরি থেকে মোট সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ আবিষ্কার করেন। এর মধ্যে ২৪, ২৫ ও ৪৮ নং পদ পাওয়া যায়নি। সুতরাং এর মোট পদসংখ্যা ৫০। চর্যাপদ, নামান্তরে কখনো কখনো ‘চর্যাচর্যবিনিশ্চয়’ বা ‘চর্যাগীতিকোষ’ এর রচয়িতার নাম ও সংখ্যাও এর বিষয় এবং ভাষার মতোই আলো আঁধারে খেলা করে। চর্যাপদের কবির সংখ্যা ২৩, মতান্তরে ২৪ (কারণ অনেকেই বলেন যে দারিকপা আর দাড়িম্বপা দুজন ব্যক্তি)। কবিদের মধ্যে মীনপা, কুক্করীপা, ঢেণ্ডনপা, সানুপা, চৌরঙ্গীপা, শবরীপা, লুইপা, বিরূপা, ডোম্বীপা, তেলিপা, পরোপা, দারিম্পা, ভুসুকুপা, কাহ্নপা- এদের নাম জানা যায়। এদের মধ্যে প্রাচীনতম কবি লুইপা না সরহপা, এ নিয়েও রয়েছে তর্ক। সবচেয়ে বেশি পদ রচনা করেছেন কাহ্নপা।

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়; Source: anandabazar.com
নেপালের তিব্বতাঞ্চলে এখনও এই ধারার সঙ্গীত টিকে আছে ‘বজ্রা’ নামে। চর্যাপদ বাংলার প্রাচীনতম রূপ, কিন্তু তা পাওয়া গেল নেপালে। এমনকি নেপালে আজো তার সুর বেজে চলেছে। কেন? কারণ সাম্রাজ্যবাদের প্রকোপ। একাদশ শতকের শেষের দিকে পাল সাম্রাজ্যের ইতি ঘটে সেন রাজাদের হাতে। পালরা ছিলেন বৌদ্ধধর্মের মহাযান রূপের অনুসারী এবং সেনরা হিন্দু। তাই সেনদের আগমনের ফলে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বাংলায় অবস্থান আর নিরাপদ রইলো না। সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনে বেশিরভাগ সময় কোপটা ধর্মের উপর দিয়েই পড়ে, খুব স্বাভাবিকভাবেই বৌদ্ধ বিত্তবান লোকেরা দেশান্তরিত হয়। আর বাকিরা হয় প্রাণ হারায়, আর নয়তো ধর্মান্তরিত হয়ে রাজধর্ম গ্রহণ করে হিন্দু হয়। আমজনতার ক্ষেত্রে ধর্মান্তরের এই চক্র পরবর্তীতে মুসলিম শাসনামলেও চালু থাকে। দেশান্তরিত বৌদ্ধদের অধিকাংশই গিয়েছিল নেপাল ও ভুটানে। এবং বলাই বাহুল্য, তাদের সাথে তাদের সংস্কৃতিও স্থানান্তরিত হয়েছিল। সেখানকার ভাষার সাথে যুক্ত হয় চর্যার ভাষা। আবার চর্যার ভাষায় যুক্ত হলো স্থানীয় ভাষা। ভাষার এই অদলবদলে বাংলা ভাষার আদিম রূপের একখানা তিব্বতি সংস্করণ বেরোল, যার টীকাকারের নাম মুনিদত্ত। সেই তিব্বতি সংস্করণ থেকেই চর্যাপদের আবিষ্কার হয়েছে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দ্বারা।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ; Source: natunbarta.com
“আপনা মাংসে হরিণা বৈরী” এই কথাটি আমাদের খুবই পরিচিত। কারো কোনো ভালো দিকই যখন তার জন্য খারাপ বা ক্ষতিকর কিছু বয়ে নিয়ে আসে, তখন আমরা এই কথাটি ব্যবহার করে থাকি। এই অতি পরিচিত উক্তিটিও এসেছে কবি ভুসুকুপার একটি পদ থেকে। চর্যাকবিরা কল্পনার চাইতে যে বাস্তবকে অনেক বেশি আশ্রয় দিয়েছেন তাদের রচনায়, তার প্রমাণ হচ্ছে প্রায় প্রতিটি পদেই প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের সরব উপস্থিতি। মানবশরীরকে বৃক্ষের সাথে তুলনা দিয়ে বলা হয়েছে ‘কায়াতরু’, যার পাঁচটি ডাল। এই পাঁচটি ডাল দ্বারা বোঝানো হয়েছে পঞ্চেন্দ্রিয়কে।
সমাজচিত্র
তখনকার দিনে ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া প্রভাব বজায় থাকতো সমাজে। ডোম, সবর প্রভৃতি নিম্নবর্গের লোকেদের বাসস্থান ছিল নগরের বাইরে, পর্বতগাত্রে বা টিলায়। উচ্চশ্রেণির লোকেদের সাথেও তাদের সম্পর্ক ছিল, তবে সেটি প্রভুত্বের সম্পর্কের বাইরে কিছু নয়। ডোম্বিরা অনেকক্ষেত্রেই অভিজাত শ্রেণির মনোহরণের চেষ্টা করতো। বর্ণের দিক দিয়ে বা জাতিতে যাদের নিচু ধরা হতো, তাদের জীবনযাত্রার মান ও ধরনও ছিল অনেক অশ্রদ্ধেয়। চর্যাপদে বর্ণিত হয়েছে এই নিম্নশ্রেণির কথন। সাধারণ মানুষের কথা বলতে গিয়েই হয়তো চর্যাকবিরা রাজকীয় সংস্কৃতের বদলে বেছে নিয়েছেন সেই মুখে বলা ভাষাকে, যে ভাষায় কথা বলতো সে যুগের ডোম-তাঁতী-মুচিরা। তাদের প্রাত্যহিক কর্মতালিকায় ছিলো জুয়াখেলা, শিকার করা, মাছ ধরা, নৌকা বাওয়া, চাঙ্গারি বোনা, বনে বনে আহার্য গ্রহণ করা, মদ্যপান ইত্যাদি।

সহজিয়া বৌদ্ধরা রচেছেন এই চর্যা; Source: naztanu.wordpress.com
২৬ নং চর্যায় বাঙালি তাঁতীদের শিল্পচাতুর্যের কথা পাওয়া যায়। ডোম জাতির নারীদের তাঁত বুনন ও তুলোধুনার কথা বর্ণিত হয়েছে একাধিক চর্যাপদে। ২১ নং চর্যায় আমরা পাই ইঁদুরের উপদ্রবে কৃষি বিপর্যস্ত হওয়ার কথা। এছাড়া ৪৫ নং চর্যায় কুঠারের সাহায্যে গাছ কাটার কথা বলা হয়েছে। তৎকালীন সমাজের অসঙ্গতি, অসম শাসনব্যবস্থা, দুঃখবোধ অনুভব করে সিদ্ধাচার্যগণ সহজিয়া সাধনায় সমতার ক্ষেত্রে মানবতাকে আহ্বান জানিয়েছেন।
জীবিকা নির্বাহ বা কর্মতালিকার পাশাপাশি তৎকালীন সমাজের শিল্প-সংস্কৃতির কথাও উঠে এসেছে চর্যাপদে। ১০ নং চর্যায় বর্ণন হয়েছে নটবৃত্তির কথা। বিনোদনের পাশাপাশি জীবিকা নির্বাহের অন্যতম উপায় হিসেবে তাদের নৃত্য-গীতের কলাকৌশল ছিল বিচিত্রমুখী। ১৭ নং চর্যায় জানা গেছে অভিনয়কলার কথাও।
এক গৃহবধূর অভিসারের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে কুক্করীপা রচিত ২ নং চর্যায়,
“দিবসহি বহুড়ী কাউহি ডর ভাই।
রাতি ভইলে কামরু জাই”
অর্থাৎ, যে বধূটি দিনের বেলায় কাকের ভয়ে ভীতু হবার ভান করে, রাতের বেলায় সকলের অগোচরে সেই কামরূপ চলে যায়।
তখনকার দরিদ্রের অনাহারের ক্রন্দন চর্যায় ব্যক্ত হয়েছে এভাবে,
“টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাড়ীতে ভাত নাহি নিতি আবেসী।।
বেঙ্গ সংসার বডহিল জাঅ।
দুহিল দুধু কি বেন্টে ষামায়।।”
এর অর্থ করা হয়েছে,
টিলায় আমার ঘর, প্রতিবেশী নেই। হাঁড়িতে ভাত নেই, নিত্যই ক্ষুধিত (অতিথি)। (অথচ আমার) ব্যাঙের সংসার বেড়েই চলেছে (ব্যাঙের যেমন অসংখ্য ব্যাঙাচি বা সন্তান, তেমনি আমার সন্তানের সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান)। দোয়ানো দুধ আবার বাঁটে ঢুকে যাচ্ছে। যে খাদ্য প্রায় প্রস্তুত, তা-ও নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছে।
চর্যাকবিরা আনন্দের নয়, বেদনার সুরেই রচেছেন এ সাহিত্য। তারা নিয়মিত জীবনের দুঃখ-কষ্ট-অভাব-বৈষম্য দেখে সইতে না পেরে চর্যা রচনা করেছেন।
তথ্যসূত্র:
১। চর্যাপদ- বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন; সংগ্রহ: হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অনুবাদ: অতীন্দ্র মজুমদার; সম্পাদনা: আনিসুর রহমান
২। লাল নীল দীপাবলি; লেখক: হুমায়ুন আজাদ, আগামী প্রকাশনী
ফিচার ইমেজ- sealang.net







