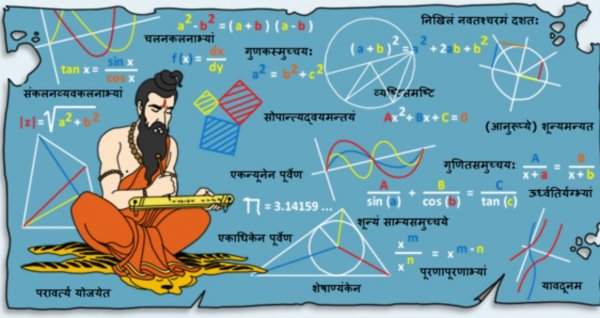১৯৬৫ সালের ৯ আগস্ট যখন মালয়েশিয়ার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হলো, তখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র সিঙ্গাপুরের বন্ধু ছিল হাতেগোনা অল্প কিছু। তারচেয়েও কম ছিল তাদের প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ। তাহলে সেই সিঙ্গাপুরই কীভাবে শূন্য থেকে শিখরে পৌঁছে গেল, বনে গেল বৈশ্বিক অর্থনীতির অন্যতম প্রাণকেন্দ্র? দেশটির প্রথম প্রধানমন্ত্রী লি কুয়ান ইউ’র মতে কৌশলটি ছিল খুবই সহজ, “উন্নয়ন সাধন করা আমাদের দেশে বিদ্যমান একমাত্র প্রাকৃতিক সম্পদের: আমাদের জনগণের।”
অর্থাৎ আমাদের বাংলাদেশে যে মুখস্ত বুলিটি প্রায়ই আওড়ানো হয়ে থাকে যে, “জনসংখ্যাকে রূপান্তরিত করতে হবে জনশক্তিতে”, সিঙ্গাপুর তাদের উন্নয়নের জন্য ঠিক সেই প্রকল্পটিই হাতে নিয়েছিল। এখন প্রশ্ন হলো, কীভাবে তারা তাদের জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করেছিল? উত্তরটিও খুব সহজ: তারা তাদের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতিতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বারোপ করেছিল। কারণ বাস্তবিকই তাদের বিশ্বাস ছিল যে শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড, এবং সদ্য যাত্রা শুরু করা একটি জাতির মাথা তুলে দাঁড়ানোর জন্য শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।
শিক্ষাব্যবস্থাকে উন্নত করার প্রচেষ্টায় সিঙ্গাপুর ঠিক কতটুকু সফল, তা যাচাইয়ের জন্য আমরা তাকাতে পারি ওইসিডি’র প্রোগ্রাম ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট অ্যাসেসমেন্ট (পিসা)-র প্রকাশিত ত্রিবার্ষিক ফলাফলগুলোর দিকে, যেখানে ধারাবাহিকভাবেই সেরাদের তালিকায় অবস্থান করছে সিঙ্গাপুর (২০১২ সালে দ্বিতীয়, ২০১৫ সালে প্রথম, ২০১৮ সালে দ্বিতীয়)।

জানিয়ে রাখা ভালো, পিসা হলো বিশ্বের উচ্চ ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোর শিক্ষাব্যবস্থাকে পরিমাপের জন্য গৃহীত একটি পরীক্ষা, যেখানে অংশ নিয়ে থাকে ১৫ বছর বয়সী শিক্ষার্থীরা। যেমন- ২০১৮ সালে সর্বশেষ গৃহীত পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ৭৯টি দেশ ও অঞ্চলের ১৫ বছর বয়সী মোট ৬ লক্ষ শিক্ষার্থী, যারা সেসব দেশ ও অঞ্চলের মোট ৩ কোটি ২০ লক্ষ ১৫ বছর বয়সী শিক্ষার্থীর প্রতিনিধিত্ব করে। কম্পিউটারের মাধ্যমে দুই ঘণ্টায় গৃহীত এই পরীক্ষার মূল বিষয় তিনটি: গণিত, পঠন দক্ষতা ও বিজ্ঞান। এই তিনটি বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের পারফরম্যান্সের উপর ভিত্তি করেই নির্ধারিত হয় যে কোন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা কতটুকু এগিয়েছে, কিংবা পিছিয়েছে, এবং বৈশ্বিক আঙিনায় তাদের অবস্থানই বা ঠিক কোথায়।
এই পরীক্ষা থেকেই উঠে এসেছে যে, সিঙ্গাপুরের ১৫ বছর বয়সী শিক্ষার্থীরা আমেরিকার সমবয়সী শিক্ষার্থীদের চেয়ে গণিতে প্রায় তিন বছর এগিয়ে। শুধু তা-ই নয়, সিঙ্গাপুরের একজন গড়পড়তা শিক্ষার্থী অন্যান্য অধিকাংশ প্রথম বিশ্বের অধীনস্থ দেশগুলোর শিক্ষার্থীদের চেয়ে ইংরেজি পাঠে ১০ মাস, এবং গণিতে ২০ মাস এগিয়ে রয়েছে।
ট্রেন্ডস ইন ইন্টারন্যাশনাল ম্যাথম্যাটিকস অ্যান্ড সায়েন্স স্টাডিজ (টিআইএমএস)-এর গবেষণায় উঠে এসেছে যে অন্যান্য আন্তর্জাতিক পরীক্ষাগুলোতেও গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে সিঙ্গাপুরের শিক্ষার্থীরা শীর্ষস্থান লাভ করে। তাছাড়া সিঙ্গাপুরের অপেক্ষাকৃত কমবয়সী শিক্ষার্থীরাও বিভিন্ন পরীক্ষায় একই রকম ভালো করে, এবং দেশটির বিভিন্ন স্কুল থেকে বেরোনো গ্র্যাজুয়েটরা এখন ছড়িয়ে রয়েছে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে।
এসব কারণেই সিঙ্গাপুরের শিক্ষাব্যবস্থা এখন বিবেচিত হচ্ছে গোটা বিশ্বের মধ্যে সেরা হিসেবে। চমকপ্রদ বিষয় হলো, মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)-র আকারে আমাদের বাংলাদেশ এই মুহূর্তে সিঙ্গাপুরের থেকে এগিয়ে। কিন্তু বিবেচ্য যদি হয় শিক্ষার মান, সেখানে সিঙ্গাপুরের ধারেকা-ছেও নেই বাংলাদেশ। পিসার এই পরীক্ষায় এখনো অংশগ্রহণ করতে পারেনি বাংলাদেশ। তাই পিসার র্যাংকিং অনুযায়ী বাংলাদেশ ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে তুলনা করা অসম্ভব। আমরা বাংলাদেশ ও সিঙ্গাপুরের শিক্ষাব্যবস্থার তুলনার্থে ধার করতে পারি ২০১৯ সালের লিগেটাম প্রসপারিটি ইনডেক্সের ফলাফলকে। সেখানে সামগ্রিকভাবে ১৬তম অবস্থানে থাকলেও, শিক্ষায় সিঙ্গাপুর যথারীতি প্রথম। অন্যদিকে সামগ্রিকভাবে ১২৭তম অবস্থানে থাকা বাংলাদেশ শিক্ষায় ১২২তম।
সুতরাং, দ্য ইকোনমিস্ট-এর বলা “এই দ্বীপরাষ্ট্র অনেক কিছুই শেখাতে পারে বিশ্বকে” উক্তি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরাও বলতে পারি, সিঙ্গাপুরের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে অনেক কিছুই শেখার আছে বাংলাদেশেরও।

সিঙ্গাপুরের থেকে সবচেয়ে বড় শিক্ষণীয় বিষয় হলো, শিক্ষাখাতে ব্যয়। যদি শিক্ষাকেই জাতির মেরুদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়, সেটির প্রতিফলনও অবশ্যই থাকবে জাতীয় বাজেটে। সিঙ্গাপুরের ক্ষেত্রে সেই প্রতিফলন বরাবরই থাকে। প্রতি বছর মোট জাতীয় বাজেটের ২০ শতাংশের মতো তারা ব্যয় করে থাকে শিক্ষাখাতে। কিন্তু আমরা যদি বাংলাদেশের দিকে তাকাই, সেখানকার চিত্র হতাশাজনক।
বাংলাদেশ সরকার ইউনেস্কো ও ডাকার সম্মেলনে শিক্ষাখাতে জিডিপির ৭ শতাংশ ও ৬ শতাংশ এবং মোট বাজেটের ২০ শতাংশ ব্যয় করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে তা ১০ থেকে ১২ শতাংশেই ঘুরপাক খাচ্ছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ছিল মোট বাজেটের ১২.৬ শতাংশ। আর দশ বছর পর ২০১৯-২০ অর্থবছরে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে বরাদ্দ মোট বাজেটের ১৫.১৯ শতাংশ। অর্থাৎ ১০ বছরে কিছুটা হলেও উন্নতি অবশ্যই পরিলক্ষিত হচ্ছে। তবে যদি শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাত থেকে প্রযুক্তিকে বাদ দিয়ে শুধু শিক্ষার কথা বিবেচনা করা হয়, তাহলে কিন্তু বরাদ্দের পরিমাণ কমে আসবে ১১.৬৮ শতাংশে, যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরের চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশি (০.২৭ শতাংশ) হলেও, এক দশক আগের অর্থবছরের চেয়ে প্রায় ১ শতাংশ কম।
সিঙ্গাপুরের শিক্ষাব্যবস্থার একটি বিশেষ দিকের সাথে অবশ্য উন্নত বিশ্বের অনেক দেশের শিক্ষাব্যবস্থার একটি বড় বিভেদ রয়েছে। তারা চিরাচরিত শিক্ষাপ্রদান নীতিতে বিশ্বাসী, যেখানে একটি শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকই হবেন সর্বেসর্বা, তিনিই শিক্ষার্থীদের সরাসরি পাঠদান করবেন। অনেক প্রগতিশীল রাষ্ট্র এমন শিক্ষাপ্রদান পদ্ধতিকে সেকেলে বলে মনে করে। তাদের মতে, শিক্ষাব্যবস্থা হবে এমন যেখানে শিক্ষার্থীদেরকে নিজে নিজেই সবকিছু শেখার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হবে।
অবশ্য অনেক আন্তর্জাতিক গবেষণায় উঠে এসেছে যে, সিঙ্গাপুরের সরাসরি শিক্ষাপ্রদান পদ্ধতি আসলে ততটা খারাপ নয়, যতটা মনে করা হয়। বরং এর সুফলও যথেষ্ট। ২০১৫ সালে পিসার একটি নতুন ধরনের পরীক্ষার ফলাফলেও তেমনটিই দেখা গেছে। সে বছর অংশগ্রহণকারীদের সহযোগিতামূলক সমস্যা সমাধান করতে দেয়া হয়েছিল, এবং সেখানেও সিঙ্গাপুরের শিক্ষার্থীরাই প্রথম হয়েছিল, এমনকি পঠন দক্ষতা ও বিজ্ঞানে আগের থেকে তুলনামূলক বেশি নম্বরও পেয়েছিল। এ থেকেই প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল যে সিঙ্গাপুরের বিদ্যমান শিক্ষাপ্রদান পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত দক্ষতায় কোনো ধরনের প্রভাব ফেলছে না, আবার তারা দলীয় কাজেও নিজেদের সেরাটাই দিচ্ছে।
এটুকু পড়ে অনেকেই মনে করতে পারেন, তাহলে অন্তত শিক্ষাপ্রদান পদ্ধতির দিক থেকে তো আমাদের বাংলাদেশ সঠিক পথেই আছে, কারণ এখানে সিঙ্গাপুরের শিক্ষাপ্রদান নীতিকেই অনুসরণ করা হয়। তেমনটি মনে করার কোনো কারণ নেই। কারণ সিঙ্গাপুরের শিক্ষানীতি প্রণেতারা নিজেরাও মনে করছেন, পরিসংখ্যানের দিক থেকে সবকিছু ঠিকঠাক থাকলেও, তাদের পক্ষে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে আরো উন্নত করে তোলা সম্ভব, যাতে শিক্ষার্থীদের উদ্বেগ কমে, এবং সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

এ লক্ষ্যে সিঙ্গাপুরের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাব্যবস্থাকে পরীক্ষামুক্ত করা হয়েছে। ২০১৯ সাল থেকে প্রাথমিক স্তরের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য মার্কিং ও গ্রেডিংয়ের বদলে আলোচনা, হোমওয়ার্ক ও কুইজ নিয়ে আসা হয়েছে। অর্থাৎ এই দুই বছর শিক্ষার্থীরা কোনো রকম পরীক্ষার চাপ ছাড়াই, হাসি-আনন্দে শিক্ষালাভ করতে পারছে। এছাড়া সামগ্রিকভাবেও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের অন্যান্য শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য পরীক্ষাকে অপেক্ষাকৃত কম প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক করা হয়েছে। যেমন- কেউ ভগ্নাংশে নম্বর পেলে, ডেসিমালের স্থলে তাকে নিকটতম পূর্ণসংখ্যার নম্বরটি দেয়া হয়। অনেকের কাছেই এটিকে খুব একটা তাৎপর্যপূর্ণ না-ও মনে হতে পারে। কিন্তু এর ফলে আগে যেমন .১ নম্বরের এদিক-ওদিক হওয়াও শিক্ষার্থীদের কাছে অনেক বড় ব্যাপার ছিল, এবং পরীক্ষার সাফল্যকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হতো, সে ধরনের মানসিকতা নিশ্চিহ্ন হবে।
এবার কিন্তু বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার সাথে সিঙ্গাপুরের শিক্ষাব্যবস্থার একটি দৃশ্যমান পার্থক্যের সন্ধান ঠিকই মিলল। তবে এই পার্থক্যের চেয়েও বড় বিষয় হলো, একদম জরুরি অবস্থা জারি না হলেও, এবং বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থা যথেষ্ট ফলদায়ক (এবং বিশ্বসেরা) হওয়া সত্ত্বেও, সিঙ্গাপুরের শিক্ষা মন্ত্রণালয় যেভাবে তাদের শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার করেছে। বাংলাদেশে কি এ ধরনের মানসিকতা দেখা যায়? বরং এ দেশে কি পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হলেও, এবং নানাভাবে তা প্রমাণিত হয়ে গেলেও, শীর্ষমহল থেকে সেটিকে অস্বীকারের চেষ্টা চালানো হয় না? তাছাড়া আমাদের দেশে কি পাবলিক পরীক্ষার ফল, আরো নির্দিষ্ট করে বললে জিপিএ-৫ প্রাপ্তের সংখ্যাকেই শিক্ষাব্যবস্থায় উন্নতির সূচক হিসেবে ধরা হয় না?
সুতরাং পার্থক্যটা আসলে নীতি-নির্ধারক ও সিদ্ধান্ত-প্রণেতাদের মানসিকতায়। সিঙ্গাপুরের শিক্ষা মন্ত্রণালয় যেখানে জরুরি অবস্থা জারি না হলেও শিক্ষাব্যবস্থার ক্রমোন্নতির লক্ষ্যে নিজে থেকেই চেষ্টা করে যাচ্ছে, সেখানে বাংলাদেশের শীর্ষ মহলে দেখা যায় উন্নাসিকতা, দেখেও না দেখা কিংবা বাস্তবতাকে অগ্রাহ্য করার প্রবণতা।
এবার গোটা বিষয়টির আরো একটু গভীরে প্রবেশ করা যাক। সিঙ্গাপুরে যেকোনো জরুরি অবস্থা জারি না হলেও, এবং প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা ফলদায়ক হওয়া সত্ত্বেও, শিক্ষাব্যবস্থায় এমন বড় একটি পরিবর্তন আনা হলো- তা কি নিছকই খেয়ালের বশে? মোটেই না। দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাবে, তারপর তারা পরিবর্তন আনবে, এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিতেও তারা বিশ্বাসী নয়। তারা প্রচুর পরিমাণ বিনিয়োগ করে শিক্ষার উপর গবেষণায়, এবং প্রতিনিয়ত পরীক্ষানিরীক্ষা করে দেখে যে নতুন কোনো ধারণার বাস্তবায়ন করা যায় কি না, তাতে বর্তমানের চেয়েও বেশি সুফল পাওয়া যায় কি না। বড় ধরনের সংস্কারের বিষয়গুলো তো রয়েছেই, এমনকি তারা পাঠ্যপুস্তক রচনা, পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, পরীক্ষার সময়সূচি নির্ধারণ ইত্যাদিও করে থাকে গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে, যাতে প্রতিনিয়তই তারা সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে, শিক্ষাব্যবস্থার সর্বোচ্চ শিক্ষার্থীবান্ধবতা যাতে নিশ্চিত হয়।
আমাদের বাংলাদেশে কি শিক্ষা নিয়ে এ ধরনের কোনো সুদূরপ্রসারী গবেষণা হয়? একেবারে হয় না বললে ভুল হবে, কারণ বাংলাদেশে বর্তমানে অনেক প্রতিষ্ঠানই শিক্ষা নিয়ে গবেষণার প্রয়াস চালাচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস), গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ ব্র্যাক, প্ল্যান বাংলাদেশ, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম), বিআইডিএস, ঢাকা আহছানিয়া মিশন, গণসাক্ষরতা অভিযান, শিক্ষা সংবাদ (চ্যানেল আই’র নিয়মিত শিক্ষা নিয়ে গবেষণা সংবাদ) ইত্যাদি।

তবে সবচেয়ে ফলপ্রসূ কাজ করছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট। সেখানে থিসিস ওয়ার্কের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম চলছে। শিক্ষা নিয়ে গবেষণা করাই শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের মুখ্য উদ্দেশ্য। শিক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষার ভিত্তি, নন-ফরমাল এডুকেশন, শিক্ষা প্রশাসন, শিক্ষাক্রম, জেন্ডার এডুকেশন, শিক্ষা গবেষণা, শিক্ষা মনোবিজ্ঞান, কম্পিউটার, বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে পাঠদানের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাবিষয়ক বিশেষজ্ঞ হিসেবে গড়ে তোলে তারা।
কিন্তু এতসবের পরও কেন বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় খুব বৈপ্লবিক কোনো পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না? কেন এসব গবেষণার সুফল এখনো সেভাবে সাধারণ জনগণের চোখে দৃশ্যমান হচ্ছে না? কারণ এ ধরনের বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার পর্যবেক্ষণ ও ফলাফল মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে যেমন আন্তরিকতা প্রয়োজন, সেটি এখনো অনুপস্থিত। এছাড়া শিক্ষা নিয়ে গবেষণার ফলাফল সরাসরি শিক্ষাব্যবস্থায় সংযোজিত না হওয়ার আরেকটি বড় কারণ শিক্ষা গবেষণার জাতীয় নীতিমালা প্রণীত না হওয়া। যেদিন এমন একটি কার্যকর নীতিমালা প্রণীত হবে, সেদিন দেশি প্রেক্ষাপটে পরিচালিত গবেষণার ভিত্তিতেই শিক্ষাব্যবস্থায় নানা পরিবর্তন আনা যাবে, অন্ধের মতো অনুসরণ করার প্রয়োজন পড়বে না বিদেশী শিক্ষাপ্রদান পদ্ধতির- যার মধ্যে অনেকগুলো হয়তো আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে একেবারেই উপযুক্ত নয়।
সিঙ্গাপুরের শিক্ষাব্যবস্থার আরেকটি শিক্ষণীয় দিক হলো পাঠ্যক্রম প্রণয়ন। তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে শিক্ষার্থীদের জন্য সংক্ষিপ্ত কিন্তু গভীরতর পাঠ্যক্রম প্রণয়নের, বিশেষত গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে। এর কারণ, তারা চায় একটি শ্রেণীর হাতেগোনা কয়েকজন সব পড়া শিখতে পারবে, আর বাকিরা পিছিয়ে থাকবে এবং সেই পশ্চাদপদ অবস্থায়ই পরের শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবে- এমন পরিস্থিতি যেন সৃষ্টি না হয়।
এই বিষয়টি আমাদের দেশেও খুবই জরুরি। কারণ একদম নিম্নমানের শিক্ষার্থীদের কথা যদি বাদও দিই, মধ্যম মানের শিক্ষার্থীদেরও পাঠ্যক্রমের অসামাঞ্জস্যতা ও ভারসাম্যহীনতার জন্য প্রচণ্ড পরিমাণে ভুগতে হয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রমে অনেক অধ্যায় ও অনেক বিষয়কে সংযুক্ত করা হয় বলে, খুব কম শিক্ষার্থীর পক্ষেই সম্ভব হয় ওই সকল বিষয়কে পুরোপুরি বুঝে ও আয়ত্ত্বে এনে পরের শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়া।
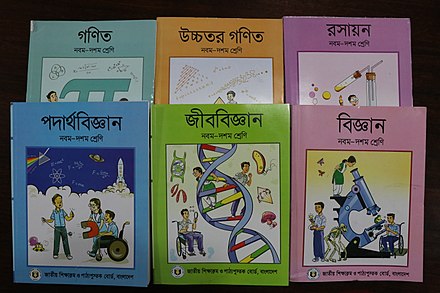
অষ্টম শ্রেণীতে হয়তো একটি শিক্ষার্থী দায়সারাভাবে বিজ্ঞানের কিছু বিষয় সম্পর্কে ধারণা পেল, এবং পরীক্ষায় ভালো ফল করল। সে মনে করল ঐ বিষয়ে সে সব জেনে ফেলেছে। বাস্তবে কিন্তু তা সত্য নয়। ওই বিষয়ে তার ভিত মজবুত হয়নি, তাই নবম-দশম শ্রেণীতে কিংবা কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে উঠে যখন তাকে ওই বিষয়কেই আরো বিস্তারিতভাবে শিখতে হবে, পূর্বজ্ঞান ভাসাভাসা হওয়ায় সে পড়বে বিপাকে। অথচ সিঙ্গাপুরের মতো যদি আমাদের দেশের পাঠ্যক্রমও এমন হতো যে প্রাথমিক স্তর থেকেই পাঠ্যক্রম হবে সংক্ষিপ্ত কিন্তু বিদ্যমান বিষয়গুলোতে পরিপূর্ণ ও গভীরতম জ্ঞান লাভের সুযোগ থাকবে, তা লম্বা দৌড়ে সাহায্য করত সকল শিক্ষার্থীকেই।
সিঙ্গাপুরের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে শিক্ষণীয় সর্বশেষ কিন্তু সবচেয়ে জরুরি দিকটি হলো, উন্নতমানের শিক্ষক গড়ে তোলা। শিক্ষার্থীরা ততটুকুই ভালো হবে, যতটুকু ভালো হবেন তাদের শিক্ষকেরা। তাই শিক্ষকেরা যাতে সম্ভাব্য শ্রেষ্ঠতম গুণসম্পন্ন হন, তা নিশ্চিত করার কোনো বিকল্প নেই। সিঙ্গাপুর সরকার এই বিষয়টি খুব ভালোভাবেই বোঝে। তাই এমনকি সর্বোচ্চ পর্যায়ের শিক্ষকদের জন্যও তারা প্রতিবছর অন্তত ১০০ ঘণ্টার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে, যাতে ওই শিক্ষকরাও শিক্ষাপ্রদানের একদম হালনাগাদ কৌশলগুলো সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারেন। এছাড়া সিঙ্গাপুরে শিক্ষকদেরকে খুব মোটা অঙ্কের সম্মানীও দেয়া হয়, যাতে তাদের সংসারে কোনো টানাপোড়েন না চলে, শ্রেণীকক্ষে নিজেদের সবটুকু ঢেলে দেয়ার ক্ষেত্রে তাদের যেন বিন্দুমাত্র মানসিক বিক্ষেপণেরও সম্মুখীন হতে না হয়।
ওইসিডির হিসাব অনুযায়ী একটি আদর্শ শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যা হওয়া উচিত ২৪। তবে সিঙ্গাপুরের শ্রেণীকক্ষে ৩৬ জন পর্যন্ত শিক্ষার্থীও একসাথে পাঠগ্রহণ করে। অপেক্ষাকৃত বড় শ্রেণীকক্ষ রাখার কারণ তারা মনে করে: ছোট শ্রেণীকক্ষে মধ্যমমানের শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষাপ্রদানের চেয়ে, অপেক্ষাকৃত বড় শ্রেণীকক্ষে শ্রেষ্ঠতম শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষাপ্রদান শ্রেয়। উন্নত বিশ্বের কাছে এটি একটি বড় শিক্ষা হতে পারে, তবে আমাদের কাছে কিন্তু ৩৬ সংখ্যাটিও খুব একটা বড় মনে হচ্ছে না। কারণ আমাদের দেশের অনেক শ্রেণীকক্ষে এর দ্বিগুণ বা তার বেশি শিক্ষার্থীও একসাথে বসে শিক্ষাগ্রহণ করে থাকে!

আপাতত শ্রেণীকক্ষের আকৃতির বিষয়টি না হয় বাদই দিই। কিন্তু সর্বোচ্চ প্রশিক্ষণ ও উচ্চ বেতনের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠতম শিক্ষক সৃষ্টির যে দৃষ্টান্ত সিঙ্গাপুর স্থাপন করে চলেছে, সেটি কিন্তু অবশ্যই শিক্ষণীয়। আমাদের দেশে এখনো শিক্ষকতা অর্থনৈতিকভাবে খুব একটা লাভজনক পেশা নয়। বর্তমানে দেশের প্রাথমিক স্তরের স্কুলগুলোতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ১১তম গ্রেডে, প্রশিক্ষণবিহীন প্রধান শিক্ষক ১২তম গ্রেডে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষক ১৪তম গ্রেডে এবং প্রশিক্ষণবিহীন সহকারী শিক্ষক ১৫তম গ্রেডে বেতন পাচ্ছেন।
প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের বেতন শুরুই হচ্ছে যেখানে ১১তম গ্রেড থেকে, সেখানে বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাকে এদেশে কতটা হেলাফেলা করা হয়। শিক্ষাই যদি জাতির মেরুদণ্ড হয়; এবং সেই মেরুদণ্ডের প্রাথমিক ভিত্তিটা যদি শিশুদেরকে একদম শৈশবে, প্রাথমিক স্কুলে থাকতেই প্রদান করা হয়, তাহলে সেই প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের বেতনে কেন এমন বৈষম্য করা হবে? আর যদি এমন বৈষম্য করা হয়, তাহলে কেনই বা দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষিতরা অন্যান্য লাভজনক পেশা ছেড়ে শিক্ষকতাকে বেছে নেবেন? স্বাভাবিকভাবেই যাদের বড় ও বেশি লাভজনক কোনো কর্মসংস্থান হয় না, কিংবা যারা সর্বোচ্চ পর্যায়ের শিক্ষিত নন, তারাই আসেন প্রাথমিক স্তরে শিক্ষকতা করতে। এমন শিক্ষকদের যতই প্রশিক্ষিত করা হোক, তাদের পক্ষে কি কোমলমতি শিশুদের সর্বোচ্চ মানের শিক্ষাদান করা সম্ভব? আর যদি সম্ভব না হয়, তাহলে কি দেশের শিক্ষাব্যবস্থার একদম গোড়ায়ই গলদ থেকে যাচ্ছে না?
বিশ্বের চমৎকার, জানা-অজানা সব বিষয় নিয়ে আমাদের সাথে লিখতে আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন এই লিঙ্কে: https://roar.media/contribute/
সিঙ্গাপুর সম্পর্কে আরও জানতে পড়তে পারেন এই বইগুলোঃ