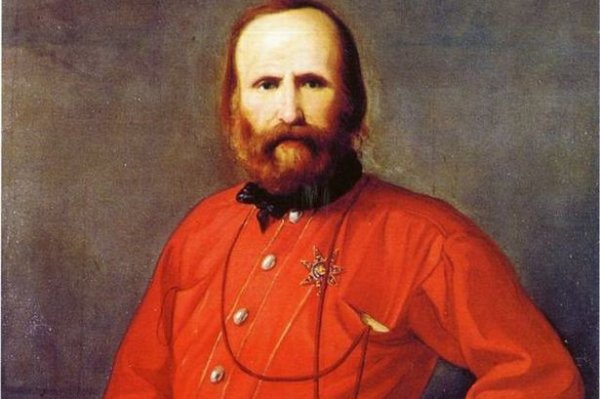প্রাচীন মিশর নিয়ে আমাদের জানার আগ্রহের কোনো কমতি নেই। মমি, পিরামিড, ফারাও, হায়ারোগ্লিফ ইত্যাদি নানা বিষয়ের জন্য দেশটির প্রাচীন ইতিহাস বরাবরই আমাদের চুম্বকের মতো টানে। এজন্য সেই প্রাচীন মিশরেরই অজানা কিছু বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আজকের এ লেখায়।
যাতায়াতের মাধ্যম
রাজবংশীয় শাসনামল শেষের দিকে আসার আগ পর্যন্ত মিশরীয়রা যাতায়াতের জন্য উট তেমন একটা নিয়মিতভাবে ব্যবহার করতো না। বরং এ কাজে তখন গাধাই ছিলো তাদের কাছে অধিক পছন্দনীয়। আর নৌপথে যাতায়াতের জন্য নৌকা তো ছিলোই।

Source: historyextra.com
মিশরের বুক চিরে বয়ে যাওয়া নীল নদ একদিকে যেমন তাদের যাতায়াতের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ছিলো, অন্যদিকে তা তাদের নর্দমা হিসেবেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতো। বাড়িঘর সহ অন্যান্য নানা স্থাপনা খালের মাধ্যমে নীল নদের সাথে যুক্ত ছিলো। বড় বড় কাঠের বজরায় করে খাদ্যশস্য ও পাথরখন্ড পারাপার করা হতো। অন্যদিকে প্যাপিরাসের হালকা নৌকায় করে পার হতো মানুষজন।
সবাইকে মমি করা হতো না
মিশরের নাম শুনলে হাতে গোণা যে দু-তিনটি জিনিসের নাম সবার আগে মাথায় টোকা মারে, মমি তার মাঝে একটি। তবে মমি বানানোর কাজটি একইসাথে বেশ সময়সাপেক্ষ ও পরিশ্রমের ছিলো বলে সমাজের উচ্চবিত্তরাই মূলত মৃতদেহ সৎকারের এ পথ বেছে নিতো। নিম্ন ও মধ্যবিত্ত জনতা তাদের মৃতদেহের শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে পেত মরুভূমিতে খোঁড়া কোনো গর্ত।

মমি; Source: ancient-origins.net
এখন তাহলে প্রশ্ন হলো, উচ্চবিত্তরা কেন মমি করতে গেলো? আসলে তারা বিশ্বাস করতো যে, মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন লাভ করা সম্ভব কেবলমাত্র যদি মৃতদেহটি শনাক্ত করার মতো অবস্থায় থাকে। এ কাজটি মরুভূমিতে মৃতদেহ কবর দেয়ার মাধ্যমেও করা যেত। কেননা সেখানকার উত্তপ্ত বালু মৃতদেহ থেকে আর্দ্রতা শোষণ করে সেটি সংরক্ষণের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা করে দিতে পারতো। কিন্তু ধনী ব্যক্তিবর্গ চাইতেন যে, তাদের দেহটি যেন কফিনে ভরে কবরে রাখা হয়। এতে সেটি সরাসরি উত্তপ্ত মাটির সংস্পর্শে না থাকায় পচা শুরু করতো।
তাই সাধারণ জনতার থেকে আলাদা উপায় বেছে নিয়ে মৃতদেহকে শনাক্ত করার মতো অবস্থায় রাখার জন্যই মমিকরণের উদ্ভব ঘটেছিলো।
জীবিত ও মৃতদের একসাথে খাওয়াদাওয়া!
মমিদের জন্য সমাধিস্তম্ভটি তাদের চিরন্তন আবাসস্থল হিসেবেই বানানো হতো। সেখানে ব্যক্তিটির পাশাপাশি তার আত্মা, যাকে তারা ‘কা’ বলে ডাকতো, থাকতো বলে বিশ্বাস করতো প্রাচীন মিশরীয়রা। মৃতব্যক্তির পরিবারের সদস্য, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং যাজকেরা মাঝেমাঝেই বিভিন্ন দ্রব্যাদি তার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতো, যা ‘কা’-এর কাজে লাগতো। অন্য্যদিকে মমিটি সুরক্ষিত স্থানে রাখা হতো যেন কেউ সেটির কোনো ক্ষতি সাধন করতে না পারে।

মৃতদের জন্য উৎসর্গ করা খাবার; Source: DeAgostini/Getty-Images
সমাধিস্তম্ভগুলোতে প্রায়সময়ই বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় উৎসর্গ করা হতো। তারা বিশ্বাস করতো যে, সেই খাবারগুলো মৃতের আত্মা আধ্যাত্মিকভাবে খেয়ে নিয়েছে। এজন্য এরপর জীবিতরাই সেই খাবারগুলো খেয়ে নিতো! ‘উপত্যকার খাদ্যোৎসব’ নামে তারা বাৎসরিক একটি ভোজ-অনুষ্ঠানের আয়োজন করতো যেখানে মৃতদের সাথে জীবিতদের পুনরায় সাক্ষাত হয় বলেই বিশ্বাস করতো মিশরীয়রা। সেই সময়টায় রাতের আধার নেমে আসলে তারা সমাধিস্তম্ভেই রাতটা কাটিয়ে দিতো। মশাল জ্বেলে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণের মাধ্যমেই মৃতের সাথে পুনর্মিলনকে স্মরণীয় করে রাখতো তারা।
নারী-পুরুষের সমঅধিকার

প্রাচীন মিশরীয় নারী; Source: bogglingfacts.com
একই সামাজিক মর্যাদার অধিকারী নারী ও পুরুষকে আইনের দৃষ্টিতে একইভাবে দেখা হতো প্রাচীন মিশরে। অর্থাৎ নারীরাও সেখানে আয়-উপার্জন করা, কেনাবেচা করা কিংবা সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতে পারতো। ইচ্ছে হলে তারা কোনো পুরুষের অভিভাবকত্ব ছাড়াই স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে পারতো। বিধবা হলে কিংবা স্বামীর সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলে একজন মা একাই তার সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে পারতেন। আইনের কাছে কোনো বিষয়ে বিচার চাইতে যেমন তাদের কোনো বাঁধা ছিলো না, তেমনি কোনো বিষয়ে দোষী সাব্যস্ত হলে তাদের বিন্দুমাত্র ছাড় দেয়া হতো না। স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রী-ই তার ব্যবসাবাণিজ্য দেখাশোনা করতে পারতেন।
স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিবাহ পরবর্তী দায়িত্ব বন্টন অবশ্য এখনকার মতোই ছিলো। ঘরের যাবতীয় কাজকারবার সামলানোর দায়িত্ব যেমন স্ত্রীর হাতে থাকতো, তেমনি স্বামীর কাজ ছিলো জীবিকার্জনের ব্যবস্থা করে সংসারটিকে চালানো।
হায়ারোগ্লিফের প্রচলন ছিলো খুব কম
মিশরের সাথে হায়ারোগ্লিফ একেবারে অবিচ্ছেদ্য অংশরুপে জড়িয়ে আছে। সেখানকার প্রাচীন সংস্কৃতির যে সুন্দর খোদাই করা ছোট ছোট ছবি বার্তারুপে আমরা দেখতে পাই, সেগুলোকেই হায়ারোগ্লিফ বলে। তবে এগুলো করতে অনেক সময় লাগতো বিধায় খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ও বার্তার জন্যই এ পদ্ধতি অবলম্বন করা হতো। বিভিন্ন সমাধস্তম্ভ, মন্দিরের দেয়াল ও রাজকীয় নানা অর্জনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করে রাখতেই হায়ারোগ্লিফ ব্যবহার করা হতো।

হায়ারোগ্লিফ; Source: looklex.com
তবে দৈনন্দিন কাজের জন্য তারা ব্যবহার করতো আরেক ধরনের লিখন পদ্ধতি, যাকে বলা হতো হায়ারেটিক। এটি ছিলো হায়ারোগ্লিফেরই সরলীকৃত সংস্করণ। রাজবংশীয় শাসনামলের শেষের দিকে তারা হায়ারেটিক ছেড়ে ঝুঁকে পড়েছিলো ডেমোটিকের দিকে, যা কিনা হায়ারেটিকেরও সরলীকৃত রুপ।
সকল ফারাও পিরামিড বানাতেন না
পুরাতন সাম্রাজ্য (২৬৮৬-২১২৫ খ্রি.পূ.) ও মধ্যবর্তী সাম্রাজ্য (২০৫৫-২৬৫০ খ্রি.পূ.)-এর প্রায় সকল ফারাওই পিরামিড বানিয়েছিলেন। এগুলো বানানো হতো দেশটির উত্তরাঞ্চলীয় মরুভূমিতে। কিন্তু নতুন সাম্রাজ্যকালীন সময়ে (১৫৫০ খ্রি.পূ.) পিরামিড বানানোর এ প্রচলন বিলুপ্তির পথে যাত্রা শুরু করে।
তখন রাজারা তাদের মৃত্যু উপলক্ষ্যে দুটো সম্পূর্ণ পৃথক স্মৃতিস্তম্ভ বানানোর চল শুরু করেন। মিশরের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর থেবসে নীল নদের দক্ষিণ তীরে ‘রাজাদের উপত্যকা’য় পাথর কেটে বানানো হতো রাজাদের জন্য গোপন সমাধিস্তম্ভ। অন্যদিকে জনবসতি ও মরুভূমির মাঝামাঝি এলাকায় স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে বানানো হতো আরেকটি মন্দির যা থাকতো জনতার মূল আকর্ষণ।
নতুন সাম্রাজ্যের পতনের পরবর্তীকালীন সময়ের রাজাদেরকে মিশরের উত্তরাঞ্চলে কবর দেয়া হতো। তাদের অনেকের কবর আজও অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে।
গ্রেট পিরামিড ক্রীতদাসরা বানায় নি
ইতিহাসবিদ হেরোডোটাস বিশ্বাস করতেন যে, আনুমানিক ১,০০,০০০ ক্রীতদাসের রাত-দিনের অমানুষিক পরিশ্রমের ফসল হিসেবে গড়ে উঠেছিলো গ্রেট পিরামিড। তার সেই কল্পনা পরবর্তীকালে নানা সিনেমার মাধ্যমে আরো জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু সত্যি কথা হলো, এ ধারণাটি ভুল।

Source: Traveling-Canucks
অতীতের নানা পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন সম্পর্কে গবেষণা করে ইতিহাসবিদেরা জানিয়েছেন যে, আনুমানিক ৫,০০০ নিয়মিত বেতনভুক্ত শ্রমিক কাজ করেছিলো গ্রেট পিরামিড বানানোর জন্য। এদের পাশাপাশি কাজ করতো আরো প্রায় ২০,০০০ অনিয়মিত শ্রমিক। এই শ্রমিকেরা সবাই ছিলো মুক্ত মানুষ অর্থাৎ ক্রীতদাস না। ৩-৪ মাসের শিফটে তারা পিরামিডের ওখানে কাজ করতো।
পিরামিডের কাছেই অস্থায়ী বাড়িতে বাস করতো সেসব শ্রমিক। মজুরি হিসেবে তারা পেত খাদ্য, পানীয় ও চিকিৎসা সেবা। কর্মরত অবস্থায় মৃত শ্রমিকদের শেষ ঠিকানা হতো নিকটবর্তী কবরস্থানে।
প্রাচীন মিশরীয়রা পছন্দ করতো বোর্ডের খেলা

Source: Gianni Dagli Orti/Corbis
কর্মব্যস্ত দিনের শেষে নানা ধরনের খেলাধুলার মাধ্যমে নিজেদের অবসর বিনোদনের ব্যাপারটা সেরে নিতো তৎকালীন মিশরীয়রা। তাদের পছন্দের তালিকার শীর্ষে ছিলো বিভিন্ন ধরনের বোর্ডের খেলা। ‘মেহেন’, ‘কুকুর ও শেয়াল’ ইত্যাদি বোর্ড খেলার কথা জানা যায়। তাদের সবচেয়ে জনপ্রিয় বোর্ড খেলার নাম ছিলো সেনেত। আনুমানিক ৩,৫০০ বছর আগের সেই খেলাটিতে বড় ধরনের বোর্ড ব্যবহৃত হতো যাতে ৩০টি ঘর কাটা ছিলো। ছক্কার গুটি আল দিয়ে কিংবা কাঠির সাহায্যে গুটি চালা হতো।
ফারাওরা ছিলেন বেশ স্থূলকায়
মিশরের আগেকার দিনগুলোর বিভিন্ন ছবি দেখলে মনে হয় ফারাওরা ছিলেন সুস্থ ও কৃশকায়। কিন্তু বাস্তবতা ছিলো একেবারেই উল্টো। তৎকালীন রাজপরিবারের সদস্যদের খাদ্যতালিকায় ছিলো বিয়ার, ওয়াইন, রুটি ও মধুর প্রাচুর্য। বিভিন্ন মমির দেহ গবেষণা করে বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন যে, তাদের অনেকেই বিভিন্ন অসুখে ভুগছিলেন। অতিরিক্ত স্থূলকায় দেহের পাশাপাশি ডায়াবেটিসও বাসা বেঁধেছিলো সেসব ফারাওয়ের শরীরে। উদাহরণস্বরুপ খ্রিষ্টপূর্ব পনের শতকের বিখ্যাত রাণী হাতশেপ্সুতের কথা বলা যায়। ইতিহাসবিদদের মতে তিনি একদিকে যেমন স্থূলকায় ছিলেন, তেমনি তার মাথার চুলও অসুস্থতাজনিত কারণে পড়ে যাচ্ছিলো।
মিশরীয়দের পশুপ্রেম

Source: The Art Archive/Corbis
বিভিন্ন পশুপাখিকে প্রাচীন মিশরের অধিবাসীরা দেবতার প্রতিমূর্তি বলে মনে করতো। এজন্য যেসব সভ্যতা পশুদেরকে গৃহপালিত প্রাণী হিসেবে গ্রহণ করেছিলো, মিশরীয়রা ছিলো তাদের মাঝে প্রথম দিককার। তারা বিড়াল খুব পছন্দ করতো যা ছিলো তাদের দেবী বাস্টেটের সাথে সম্পর্কিত। এর পাশাপাশি বাজপাখি, আইবিস পাখি, বেবুন, সিংহ, কুকুরও তারা পালতো। বাড়িতে তাদের কদর ছিলো সবসময়ই। এমনকি অনেক সময় মালিকের মৃত্যুর পর তার পোষা প্রাণীটিকেও মমি করে মালিকের সাথে দিয়ে দেয়া হতো।
নারী ও পুরুষের রুপচর্চা

Source: The Art Archive/Corbis
মিশরীয় নারী ও পুরুষ উভয়েই রুপচর্চা করতো। তারা মনে করতো যে, এগুলো তাদেরকে দেবতা হোরাস ও রা-এর প্রতিরক্ষা দেয়। ম্যালাকাইট ও গ্যালেনা আকরিক চূর্ণ করে তারা কোহ্ল নামে একধরনের প্রসাধনী দ্রব্য বানাতো। এরপর সেগুলো কাঠ, হাড় ও হাতির দাঁত দিয়ে বানানো বিভিন্ন জিনিসের সাহায্যে চোখের চারপাশে প্রয়োগ করতো তারা। মহিলারা তাদের গালে লাল রঙ দিয়ে মাখাতো এবং হাত ও হাতের আঙুল সাজাতে ব্যবহার করতো মেহেদি।
বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ তেল ও দারুচিনি থেকে প্রস্তুত সুগন্ধিদ্রব্য ব্যবহার করতো মিশরীয়রা। তারা ভাবতো যে, এসব প্রসাধন সামগ্রীর রোগ দূরীকরণ ক্ষমতা আছে। আর তাদের এ ধারণাকে একেবারে উড়িয়েও দেয়া যায় না। কারণ গবেষকেরা দেখেছেন যে, সীসা ভিত্তিক একপ্রকার প্রসাধনী দ্রব্য নীল নদের তীরের অধিবাসীরা ব্যবহার করতো যা তাদেরকে চোখের নানাবিধ রোখ থেকে রক্ষা করতো।