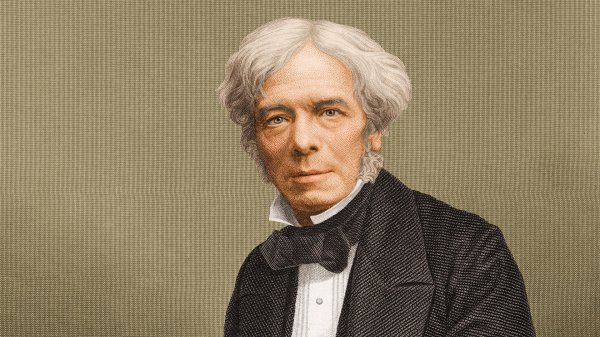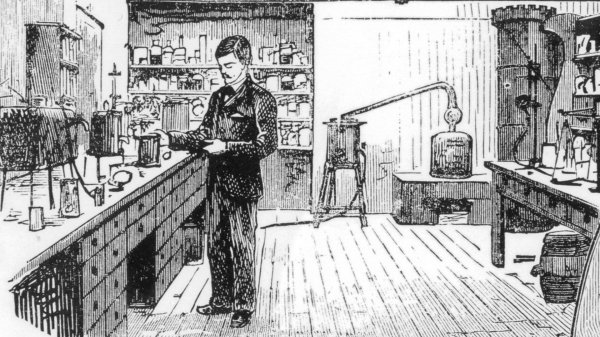রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের শাসনামল তখন। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বিদেশ সফরে পাঠানো হবে কন্ঠশিল্পীদের। শিল্পকলার ডিজি, বিশিষ্টজন মুস্তাফা মনোয়ার রাষ্ট্রপতির নিকট একজন বাউলশিল্পীর নাম সুপারিশ করলেন। কিন্তু চৌকষ জেনারেল তো আর নাম শুনেই যাকে তাকে যেতে দেবেন না। সারাজীবন কঠোর নিয়ম ও নজরদারীতে অভ্যস্ত জেনারেল ও রাষ্ট্রপতি এরশাদ মুস্তাফা মনোয়ারের উদ্দেশ্যে পুলিশি জেরার মতো প্রশ্ন ছুঁড়ে জানতে চাইলেন, সে কেমন বাউল, আর দেখতেই বা সে কেমন?’
অচেনা সেই বাউল শিল্পীটির ওপর গভীরভাবে আস্থা সম্পন্ন মুস্তাফা মনোয়ার প্রেসিডেন্টের দুশ্চিন্তা মুক্ত করতে নির্লিপ্ত গলায় জবাব দিলেন, আমি যাকে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছি তার গান শুনেই আমি তাকে নির্বাচন করেছি। রাষ্ট্রপতিকে দুস্থ এই বাউল শিল্পীটির অবস্থা সম্পর্কে অবগত করতে তিনি আরো বললেন, সে গরীব মানুষ, চির কাঙাল। কাব্যিক মনের প্রেসিডেন্ট তখন উত্তরে বললেন, সে তো মহিলা মানুষ। মহিলা মানুষ আবার কাঙাল হয় কীভাবে? আজ থেকে তার নাম কাঙালিনী।
আর এভাবেই বুড়ি হইলাম তোর কারণে, কোন বা পথে নিতাইগঞ্জে যাই খ্যাত বাউল সম্রাজ্ঞী, অসংখ্য মাটি ঘেঁষা ও শেকড়ের গন্ধমাখা গানের ফেরিওয়ালা, কালজয়ী লোকসঙ্গীত রচয়িতা, সুরকার ও শিল্পী সুফিয়া খাতুন সেদিন থেকে হয়ে গেলেন কাঙালিনী সুফিয়া।

ফরিদপুর জেলার রামদিয়া গ্রামের সবচেয়ে গরীব ঘরে জন্ম নেয়া কাঙালিনী বেড়ে উঠেছেন চন্দনা নদীর সাথে শখ্যতা করে। আর সেজন্যই হয়তো নদীর সাথে তার জীবনের চিত্রনাট্যেও রয়েছে বেশ মিল। বাঁকে বাঁকে ভাঙা গড়ার খেলা খেলতে খেলতে বয়ে চলা নদীর মতোই নানা বৈচিত্র্যে বিচিত্র কাঙালিনীর সারাটা জীবন। পিতার গৃহে কাঙালিনীর নাম ছিল অনিতা হালদার। তিন ভাইবোনের মধ্যে সবার ছোট অনিতাকে বাবা-মা আদর করে বুচি বলে ডাকতেন।
বাবা খোকন হালদার পেশায় জেলে হওয়ার সুবাদে নদীর সাথে অনিতার মেলামেশা শৈশবেই। নৌকায় চড়ে নদীর বুকে ভেসে ভেসে জীবিকা নির্বাহ করা বাবা ও ভাইয়ের সাথে অনিতাও যেতেন তাদের ছোট্ট সহযোগী হিসেবে। বাবার জালে রুপালী ইলিশের ঝলকানি দেখে অনিতা আনন্দিত হতেন, জালে বড় কোনো মাছের অস্তিত্ব আবিষ্কার করে হাততালি দিয়ে উঠতেন ছোট্ট অনিতা।
সংগীতের দীক্ষায় উচ্চশিক্ষিত হলেও কাঙালিনী তথা অনিতা হালদারের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বলতে বলা যায় মাত্র একমাসের স্কুল জীবন। তবে এর পেছনে ছোট্ট একটি গল্পও রয়েছে। অ, আ পড়ার সময় একবার এক বেরসিক শিক্ষক অনিতাকে এমন মারই মেরেছিলেন যে, মারের চোটে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন অনিতা। এরপর থেকে আর ওমুখো হননি তিনি। কেননা তার মা তার আদরের মেয়ের সাথে শিক্ষকের এমন ব্যবহার একটুও মেনে নিতে পারেননি। আর তাই মেয়ের স্কুলে যাওয়াই বন্ধ করে দেন তিনি।

এভাবে শিশু শ্রেণীতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা অনিতার এক নিরবচ্ছিন্ন খেলাধুলাময় শৈশব কাটানোর কথা থাকলেও তা আর হয়ে উঠেনি। কেননা স্কুলের অনুশাসন থেকে মুক্তি পেলেও এবার তাকে বন্দী হতে হলো সংসার নামক আরেক অনুশাসনের কাঠামোয়। শৈশব পেরোতে না পেরোতেই তাঁকে বসতে হয়েছিল বিয়ের পিঁড়িতে।
সেদিন কাঙালিনী তথা অনিতার বাড়িতে বাজেনি কোনো বিয়ের সানাই, গরীবের বিয়ে বাড়ির মতো রঙিন কাগজও কাটা হয়নি তাদের বাড়িতে। বরং বিয়ের সাজে সেজেছিলো ঐ গাঁয়েরই অন্য একটি বাড়ি। কেননা বিয়ে তো সেদিন অনিতার ছিল না, বিয়ে ছিল বিয়ের সাজে সাজা পাশের বাড়ির মেয়েটির। কিন্তু বিয়ে করতে এসে বরের অভিভাবকদের ভালো লেগে গেল ৭-৮ বছর বয়সী অনিতাকে। সেই সূত্রেই যশোর জেলা থেকে ফরিদপুরের রামদিয়াতে বিয়ে করতে আসা সুধীর হালদারকে বিয়ে করতে হলো বাবা-মায়ের পছন্দের অনিতাকে।

পুতুল খেলার বয়সে বিয়ের পিঁড়িতে বসলেও স্বামী-সংসার কী তার অর্থ তখন বুঝে উঠতে পারেননি অনিতা। স্বামীকে দেখে মুচকি হেসে কাছে গিয়ে দুটো কথা বলবেন কী, উল্টো ঘোমটা দিতেন তিনি, কখনো বা ভয় পেয়ে দৌড়ে পালাতেন। কিন্তু একটা সময় পর অনিতা যখন বুঝলেন জগৎ সংসারে এই মানুষটিই এখন তার সবচেয়ে আপন, এই মানুষটির সাথেই স্রষ্টা তাকে বেঁধেছেন জন্মান্তরের এক অদৃশ্য সুতোয়।
তখন তিনি স্বামীর কাছাকাছি এলেন। কিন্তু কাছে গিয়ে বুঝলেন অগ্নি স্বাক্ষী রেখে আনুষ্ঠানিক বন্ধন তৈরি হলেও এখানে আত্মার কোনো বন্ধন নেই। তাই এখানে জন্মান্তরের বন্ধনও সম্ভব না। আর এর প্রমাণ তো হাড়ে হাড়েই পাচ্ছিলেন তিনি। স্ত্রীর প্রতি ভালবাসাহীন এবং পরনারীতে আসক্ত সুধীর অমানুষিক নির্যাতন চালাতেন কাঙালিনীর ওপর। এসব দেখে যেখানে ভালবাসা নেই সেখানে আর মিছে মায়ার বন্ধনের আশায় বসে থাকেননি কাঙালিনী। ফিরে এলেন রামদিয়াতে বাবা বিমল হালদারের ঘরে। কিন্তু একা না, সাথে নিয়ে এলেন স্বামীর ঔরসজাত ভ্রুণ। মেয়ে সন্তান জন্মানোর পর স্বামীর থেকে তালাকপ্রাপ্তা কাঙালিনী এবার যেন সমাজ সংসারকেই তালাক দিয়ে দিলেন।

মেয়েকে মায়ের কাছে রেখে তিনি চলে গেলেন সোনাপুর মাঝবাড়ির আশ্রমে, শিষ্যত্ব নিলেন গুরু গৌর মোহন্তের। গৌর মোহন্তর নিকটই সংগীত শিক্ষার হাতেখড়ি কাঙালিনীর। গৌর মোহন্তের নিকট দীক্ষা নিয়ে কাঙালিনী হয়ে গেলেন বোষ্টমী। বাড়ি বাড়ি ঘুরে গান গেয়ে ভিক্ষা করাই তখন তার কাজ। তবে গৌর মোহন্তের হাত ধরে সংগীতে কাঙালিনীর হাতেখড়ি হলেও একে পূর্ণতা দান করেন তার আরেক গুরু দেবেন খ্যাপা।
দেবেন খ্যাপার সাথে কাঙালিনীর পরিচয় গৌর মোহন্তর আশ্রমেই। একদিন গুরু গৌরর আদেশেই দেবেনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে অনিতা হালদার হয়ে যান অনিতা খ্যাপী। এবার যেন তিনি এসে পড়লেন সংগীতের আসল পাঠশালায়। এই দেবেন খ্যাপাই তার হাতে তুলে দেন একতারা যা আজও আছে তার জন্মান্তরের বান্ধব হয়ে। চলার পথে তার সাথে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ মানুষগুলো তাকে ছেড়ে গেলেও তাকে ছেড়ে যায়নি এই একতারা।
দেবেন খ্যাপার থেকে সাধন ভজন শিখে অনিতা খ্যাপী যখন সন্ন্যাস জীবন শুরু করেছেন তখন এ জনপদে বেজে উঠেছে যুদ্ধের ডামাডোল। মাটি ও মায়ের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে এ জনপদ বুক ফুলিয়ে লড়াই করছে শত্রুবাহিনীর সাথে। শত্রুবাহিনীর নিষ্ঠুর আক্রমণে এ জনপদ তখন ক্ষত-বিক্ষত। আকাশ ভারী স্বজন হারার আর্তনাদে, বাতাসে বারুদের ঘ্রাণ। বিপন্ন মানুষগুলো নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ছুটছে ভারতের উদ্দেশ্যে।
অনিতা ও দেবেন খ্যাপাও সেই দলে ভীড়ে যান, লাশের মিছিল ডিঙিয়ে, নদী-জঙ্গল পাড়ি দিয়ে সীমান্তের ওপাড়ে চলে যান তারা। এতদিন ধরে জীবিকা নির্বাহ ও ফকিরের উদ্দেশ্যে গান গাইলেও ওপারে গিয়ে নন্দী গ্রামে আশ্রয় নেয়া কাঙালিনীর গান গাওয়ার উদ্দেশ্যটা ছিল একেবারে ভিন্ন। অনিতা খ্যাপী এবার ট্রাকে ট্রাকে, মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরে ঘুরে গান মাটির জন্য, অধিকার আদায়ের জন্য গাইতে থাকেন। মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর, লাল ঘোলা, ভবনখোলা ও রানাঘাট ক্যাম্পে গান গেয়ে প্রশিক্ষণরত মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের উজ্জীবিত করতে থাকেন তিনি।

এই সময় বৈচিত্র্যময় জীবনের অধিকারী কাঙালিনী কিংবা অনিতার জীবনে আসে আরেক বৈচিত্র্য। যুদ্ধ মানুষের জীবন ও ঘর কেড়ে নিলেও অনিতা এই যুদ্ধেই পান নতুন জীবনের সন্ধান, পান নতুন ঘরের খোঁজ। ক্যাম্পে ক্যাম্পে গান করে বেড়ানোর সময় অনিতার সাথে ভাব জমে ওঠে এক মুক্তিযোদ্ধার। নাম মান্দার ফকির। অস্ত্র হাতে, দু’চোখে শত্রু নিধনের বারুদ জ্বলা মান্দার ফকিরের বুকের বাঁপাশে দ্রোহের নিচে নীরবে বাস করছিল ভালবাসা। সেই ভালবাসাই কাঙালিনীকে দেয় এক নতুন পরিপূর্ণতা।
যুদ্ধশেষে ওপার থেকে বীর মান্দার ফকির ঘরে ফেরেন প্রেয়সী অনিতা খ্যাপির হাত ধরে। বীর মান্দার অনিতার ভালবাসায় এতটাই বুঁদ ছিলেন যে তিনি মান্দার ফকির নাম বদলে হয়ে যান মান্দার খ্যাপা। এই পরিচয়ে যুদ্ধ পরবর্তী তিন বছর অনিতা খ্যাপী আর মান্দার খ্যাপা রাজবাড়ী, সিরাজগঞ্জসহ বিভিন্ন স্থানে পালাগান করে বেড়ান।
তিনবছর পর দ্বিতীয়বারের মতো ঘোর বাঁধেন অনিতা। তবে এবারের ঘর বাধার গল্পটা তার ভিন্ন ছিল। সেবার ঘর বেঁধেছিলেন তিনি বাবা-মা’র ইচ্ছায়। আর এবার ঘর বাঁধলেন তিনি ভালবাসার টানে। তাদের ভালবাসার এতটাই শক্তি ছিল যে, এর কাছে হেরে গেল কাঙালিনীর ধর্মের শৃঙ্খল। এমনকি মান্দারে মজে নিজের পিতৃপ্রদত্ত নামও পাল্টে ফেললেন তিনি। মান্দার ফকিরের হাত ধরে ফরিদপুর কোর্টে গিয়ে মান্দারকে বিয়ে করেন অনিতা। আর নাম বদলে ফেলে হয়ে যান সুফিয়া।
মান্দারের মনে টান ছিল সুফিয়ার জন্য। ভালবেসে সুফিয়াকে পাগলী বলে ডাকতেন তিনি। এভাবে সুখে-শান্তিতে দিন কাটছিল তাদের। এদিকে চার বছরে পা রাখে মান্দার ও সুফিয়ার সংসার জীবন, তখন একদিন ফরিদপুর রামদিয়া থেকে খবর এলো সুফিয়ার মা আর বেঁচে নেই। খবরটি শুনে কেঁদে ওঠে সুফিয়ার ভেতর বাস করা মাতৃমন। কেননা তার মায়ের কাছেই তো থাকতো তার একমাত্র মেয়ে পুষ্প। তার মা পৃথিবীতে নেই মানে পুষ্পকে এখন দেখবে কে? এ কথা ভেবেই সুফিয়া পুষ্পকে নিয়ে আসেন মান্দারের সংসারে। মেয়েকে নিয়ে মান্দারের বাড়িতে ভালই কাটছিল দিন। কিন্তু যার গান ছড়িয়ে যাবে সারা বিশ্বে, যিনি হবেন সারা দেশবাসীর কাঙালিনী, তার কি আর শুধু মান্দারের সুফিয়া হয়ে থাকলে চলে?

সৃষ্টিকর্তা কখন, কাকে, কীভাবে, কোথায় স্থানান্তরিত করেন সেটা তার লীলা, যা আমাদের বোঝা দায়। একদিন হঠাৎ মান্দারের সাথে প্রচন্ড ঝগড়া বাঁধে সুফিয়ার। স্বামীর সাথে রাগ করে দেশান্তরী হওয়ায় অভ্যস্ত সুফিয়া এবার মান্দারের ঘর ছেড়ে একাই চলে আসেন ঢাকায়। ঢাকা এসে মহাখালীর আমতলী বস্তিতে ঘর নিয়ে থাকা শুরু করেন তিনি। শত শত মানুষ ভাগ্য বদলাতে ঢাকা আসে।
কারো বদলায়, আবার কারো বদলায় না। কিন্তু ঢাকাই যেন এবার রাগ করে স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে আসা সুফিয়ার ভাগ্য গড়ার দায়িত্বটা নেয়। ঢাকায় এসে হাইকোর্ট মাজারে গান গাওয়া শুরু করেন কাঙালিনী। এখানেই তার সাথে পরিচয় ঘটে আব্দুর রহমান বয়াতি, মাতাল কবি রাজ্জাক দেওয়ান, পাগলা বাচ্চু, সুরুজ দেওয়ানসহ আরো অনেক কিংবদন্তী বাউল সম্রাটদের সাথে। এই হাইকোর্টের মাজারকে কাঙালিনীর জীবনে সৌভাগ্যের তীর্থক্ষেত্র বলা চলে। কেননা এখান গান করতে করতেই তার বেতার ও টেলিভিশনে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়।
একদিন মাজারে গান শুনতে আসা বেতারের পরিচালক ফজলে খোদার ভালো লেগে যায় কাঙালিনীর গান। তিনিই তাকে ডাকেন বেতারে। আর এভাবেই বেতারে গান গাওয়া শুরু হয় তার। এরপর মাজার সূত্রেই পরিচয় হওয়া বিটিভির ডিজির মাধ্যমে অডিশন দেন তিনি শিল্পী সমাজের সকলের স্বপ্নের মাঝে গচ্ছিত রাখা একটি শব্দ বাংলাদেশ টেলিভিশনে। অডিশন দিয়েই টিকে যান তিনি। এরপর আর পেছনে তাকাতে হয়নি তাকে।
রেডিওতে, টিভিতে, শিল্পকলাসহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে গান গাইতে গাইতে কাঙালিনী হয়ে উঠতে থাকেন এ দেশের বাউল অঙ্গনের একজন শক্তিশালী প্রতিনিধি। এ সময় তার গানগুলো অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। মানুষের মুখে মুখে ঘুরতে থাকে গানগুলো। কাঙালিনীর গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গানগুলো হলো বুড়ি হইলাম তোর কারণে, কোন বা পথে নিতাইগঞ্জে যাই, আমার ভাটি গাঙের নাইয়া, নারীর কাছে কেউ যায় না ইত্যাদি।

১৯৯০ সালে কাঙালিনীর বৈচিত্র্যময় জীবনে আরো একটি গল্প ভীড় করে, যে গল্পের কথা না বললে এই গল্পটাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। হাইকোর্টের মাজারে তখন মাঝে মাঝে আগমন ঘটতো শরীয়তপুরের নাওডুবির বিখ্যাত বাউল আব্দুল হালিম বয়াতির। কাঙালিনী ছিলেন হালিম বয়াতির গানের একজন অনুরাগী। মাজারে তিনি হালিম বয়াতির গানও পরিবেশন করতেন। এই হালিম বয়াতির উপদেশক্রমেই তিনি ঝুঁকে পড়েন বাউল সম্রাট লালন সাঁইজি গানে।
আজীবন সংগীতের জন্য নিবেদিতা কাঙালিনী সুফিয়া লালন আহরণের জন্য এতটাই উদগ্রীব হয়ে ওঠেন যে, তিনি মেয়ে পুষ্পকে নিয়ে ঢাকা ছেড়ে চলে যান সুদূর কুষ্টিয়া লালনের দেশে। সেখানে ১০০ টাকায় ঘর ভাড়া করে থাকতেন। আর নিত্য যাতায়াত করতেন সাঁইজির আখড়ায়। লালন ফকিরের আখড়ায় তার সখ্যতা হয় বাউল সেকমের সাথে। একপর্যায়ে কোর্টে বিয়ে করেন তারা। কিন্তু এই বিয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি বেশিদিন।

শিল্পকলায় গান করার সময় শিল্পকলার তৎকালীন ডিজি মুস্তাফা মনোয়ার কাঙালিনীর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য নাম। কেননা মুস্তফা মনোয়ারই তাকে এরশাদ সরকারের সময় সরকারি সফরে বিদেশ পাঠানোর ব্যবস্থা করে দেন। আর এরশাদের মাধ্যমেই যে তার নাম হয় কাঙালিনী সে গল্প তো সবারই জানা। উল্লেখ্য, এর আগেও তিনি তার কন্ঠের জাদু ছড়াতে বিদেশ সফর করেছেন কয়েকবার।
সব মিলিয়ে তিনি বেশ কয়েকবার সংগীত পরিবেশনের উদ্দেশ্যে দেশের বাইরে গিয়েছেন। কখনো চীন, কখনো লন্ডন, হংকং, থাইল্যান্ড, কোরিয়া এবং ১৯৯৭ সালে গান শোনাতে যুক্তরাষ্ট্রে যান কাঙালিনী। রেডিও টিভি চলচ্চিত্র প্রতিটি অঙ্গনেই কাঙালিনীর ছিল সফল বিচরণ। ছটকু আহমেদের চলচ্চিত্রে কন্ঠ দেয়ার মাধ্যমে চলচ্চিত্রেও অভিষেক হয় কাঙালিনীর। এরপর আরো অনেক সিনেমায় গান পরিবেশন করেছেন তিনি।
কাঙালিনীর গাওয়া গান, কাঙালিনীর লেখা গান আজ দেশে বিদেশে রাজত্ব করে যাচ্ছে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে। তিনিও দাপিয়ে বেড়িয়েছেন, পেয়েছেন ভক্তদের ভালবাসা, কুড়িয়েছেন সুনাম। সঙ্গীতে তিনি এ পর্যন্ত প্রায় ৩০টি জাতীয় ও ১০টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছেন। কিন্তু একটি জিনিসই পাওয়া হয়নি তার এ জীবনে। অথচ সেই জিনিসটিই বেশি প্রয়োজন ছিল তার। আর তা হলো টাকা বা পারিশ্রমিক।

প্রবাসী বাঙালীদের শেকড়ের গান শোনাতে বহুবার বিদেশ গেলেও তাকে দেয়া হয়েছে নামে মাত্র কিছু অর্থ। এভাবে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ঠকতে হয়েছে তাকে। কোথাও তিনি পাননি তার ন্যায্য পাওনা। অথচ তাকে নিয়ে ব্যবসা করে লাভবান হয়েছেন অনেকেই। তারা দূরের কেউ নয়। তারা শিল্পী সমাজেরই সংশ্লিষ্ট কিছু অর্থলোভী। তাদের কেউ কেউ এখন গুণীজন হিসেবেও সম্মানিত।
এদিকে কাঙালিনী ও তার পরিবারকে কাটাতে হচ্ছে চির কাঙাল হয়ে। মেয়ে পুষ্পকে বিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু মাদকাসক্ত জামাইয়ের ঘরে সুখ জোটেনি পুষ্পর। ঠাঁই নিতে হয়েছে সেই কাঙালের ঘরেই। পুষ্পর তিন মেয়ে। তারাও আছেন কাঙালিনীর সাথেই। পুষ্প ও তার সন্তান সন্ততি সব মিলিয়ে ৬/৭ সদস্যের একটি পরিবারকে দেখতে হয় কাঙালিনীর। তাই আজও তাকে আশি ঊর্ধ্ব বয়সেও পর দিন আহার জুটবে কিভাবে সেই ভাবনায় অস্থির থাকতে হয়।

কখনো কখনো একপেট আধপেট খেয়েও দিন কাটাতে হয়। মাস শেষে পান প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বরাদ্দকৃত ভাতা দশ হাজার টাকা ভাতা আর বছর শেষে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে ৩২ হাজার টাকার শিল্পী ভাতা। কিন্তু দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির এই বাজারে মাসিক দশ হাজার টাকায় কি আর এত বড় পরিবারের দিন যায়? আর তাই তো রোগকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও শরীরে বাসা বাঁধতে দিতে হয় তাকে। কেননা যেখানে খাবারই জোটে না ঔষধ তো সেখানে বিলাসিতা ছাড়া কিছু নয়।
সম্প্রতি এই শিল্পী ভীষণভাবে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত অসুস্থতায় দিন কাটাচ্ছেন। হাসপাতালেও ছিলেন বেশ কিছু দিন। কিন্তু অর্থাভাবে চিকিৎসা সুবিধা তাদের নিকট সোনার হরিণই ছিল, শেষমেশ প্রধানমন্ত্রীর মধ্যস্থতায় রাজধানীর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতালে চিকিৎসা সুবিধা পান তিনি। তাকে নিয়ে অর্থ উপার্জন শেষে সবাই চলে গেলেও তার দুঃসময়ে যতটুকু পাশে থাকার বাংলাদেশ সরকারই থেকেছে। বর্তমানে এই শিল্পী বাস করছেন সাভারের জামসিং এলাকায়। এখানে তিন শতাংশ জমির ওপর একটি টিনশেড ঘরে কাঙালিনী মেয়ে পুষ্প ও নাতনিদের নিয়ে থাকছেন।

একদিন হয়তো এভাবেই অনাদরে চলে যাবেন বাংলা গানের এই কিংবদন্তী শিল্পী। সেদিন তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে আসা মানুষের মিছিলে অশ্রুশিক্ত শুভানুধ্যায়ীদের অভাব হবে না। সেখানে হয়তো তারাও থাকবেন যারা কাঙালিনীকে ঠকিয়েছেন, তাকে ন্যায্য পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত করেছেন। সেদিন কাঙালিনীর চির কাঙাল জীবনের জন্য নিজেদের দায়ী করে একটুও কি অপরাধবোধে ভুগবেন না তারা? একটুও কি অনুশোচনা হবে না তাদের?
হয়তো হবে, হয়তো হবে না। তবে এটা বলা যায় যে, কাঙালিনীকে কাঙাল করে রাখা মানুষগুলো তাদের জীবন অবসানের পরপরই হারিয়ে যাবেন কিন্তু কাঙালিনী রয়ে যাবেন এই বাংলায় পৃথিবীর সমান আয়ু নিয়ে। কোনোদিন যদি দুই মুসাফির গল্পটি বাস্তবে চিত্রায়িত হয়, তবে সেখানে লালন ফকিরের মতো কাঙালিনীই রাজত্ব করবেন, তাকে ঠকিয়ে খাওয়া মানুষেরা নয়।