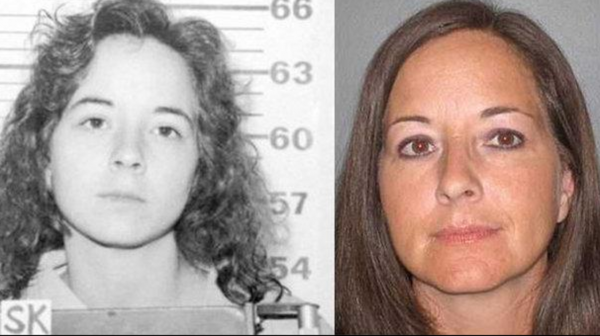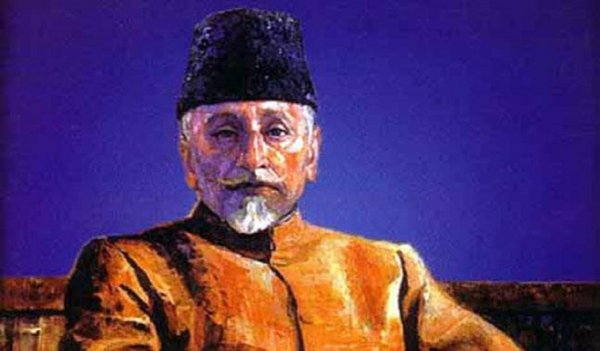মানবসেবার জন্য দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বব্যাপী স্থাপন করে গেছেন মানবতার অপূর্ব দৃষ্টান্ত, ইতিহাসের পাতায় এমন মানুষের সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। ইতিহাসের পাতায় জ্বলজ্বলে এই নামগুলোই আমাদের বাঁচার অনুপ্রেরণা দেয়, তাদের আমরা মনে রাখি যুগ যুগ ধরে।
কিন্তু সবাই পাদপ্রদীপের আলোটুকু পান না। কিছু মহান মানুষ আছেন, যারা লোকচক্ষুর আড়ালেই রয়ে যান সবসময়। হয়তো ইতিহাসের পাতায় উঠে আসার কোনো চিন্তা থেকে তারা উপকার করেন না। তবুও সন্ধানী মানুষের জালে তাদের কীর্তি ঠিকই উঠে আসে।
তেমনই একজন মেরি সিকোল। কৃষ্ণাঙ্গ বলে হয়েছিলেন বর্ণবাদের শিকার। কিন্তু এসব তাকে যুদ্ধাহত সৈনিকদের শুশ্রূষা থেকে বিরত রাখতে পারেনি। অনেকেই ঘৃণায় নাক সিঁটকালেও ক্রিমিয়ার যুদ্ধে অংশ নেওয়া হাজার-হাজার সৈনিক জানে, মেরি সিকোল স্বর্গ থেকে পাঠানো কোনো দেবদূত!
কখনো দেশ-বিদেশ ঘুরে বেরিয়েছেন অসুস্থ মানুষকে সুস্থ করে তুলতে, খুঁজে বেরিয়েছেন নতুন সব পথ্য। আবার কখনো তাকে দেখা যেতো যুদ্ধের ময়দানে, আহত সৈনিকদের ক্যাম্পে ফিরিয়ে আনছেন। মাথার উপর দিয়ে কেবল গুলি ছুটছে, আর মেরি সিকোল ছুটছেন শুশ্রূষা দিতে!
ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের সঙ্গে একই যুদ্ধের ময়দানে থেকেও ইতিহাস থেকে হারিয়ে যাওয়া এক নার্সকে নিয়েই আজকের লেখাটি।
পেছনের গল্প
মেরি সিকোলের জন্ম ১৮০৫ সালে জ্যামাইকার কিংস্টনে। তার বাবা ছিলেন একজন স্কটিশ যোদ্ধা, আর মা জ্যামাইকান একজন নার্স। আফ্রিকায় দাসপ্রথা তখনও বিলুপ্ত হয়নি, কিন্তু মেরির পরিবার দাস ছিলো না। উল্টো তারাই দাস রাখার মতো যোগ্য ছিল, জমিজমাও কিনতে পারতো। কিন্তু তাদের ভোটাধিকার কিংবা বহু রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা ছিল না।

ছোটোবেলা থেকেই মেরি সিকোল মায়ের সঙ্গে থাকার কারণে বহু ওষুধ সম্পর্কে জেনেছেন। কিংস্টনে ব্রিটিশদের ক্যাম্পগুলোতে অফিসারেরা মেরির মাকে ডেকে নিয়ে যেতেন আহত সৈনিকদের সেবা-শুশ্রূষার জন্য। তার কাজের দক্ষতার জন্য ব্রিটিশ ক্যাম্পগুলোতে তার নামডাক হয়ে পড়ে।
ওদিকে বাবার কাছ থেকে যুদ্ধের ময়দানের শ্বাসরুদ্ধকর সময়গুলোর গল্প শুনে বড় হতে থাকে মেরি। বাবার বলা গল্পে আহত সৈনিকদের আর্তচিৎকার তার মানসপটে ভেসে উঠতো। বাবা-মা দু’জনের গল্পকে একত্র করে ছোট্ট মেরি সিদ্ধান্ত নেয়, সে-ও একদিন যুদ্ধের ময়দানে দৌড়োবে। তবে অস্ত্র নিয়ে নয়, বরং আহত সৈনিকদের খোঁজ করবে তার দু’চোখ। কে শত্রু, কে মিত্র- এসবের ধার ধারবে না সে! তারপর ক্যাম্পে ফিরিয়ে এনে তাদের সুস্থ করে তুলবে।
১২ বছর বয়স থেকেই মেরি সিকোল মায়ের সঙ্গে আহত সৈনিক ও অফিসারদের সেবা করতে শুরু করেন। মায়ের নিপুণ হাতের কাজ সে গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখতো। ক্যাম্প জুড়ে আহত সৈনিকদের চিৎকারে পরিবেশটা গুমোট হয়ে যেতো।
হাইতি, কিউবাসহ ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ ঘুরে বেড়ানোর পর মেরি সিকোলের সুযোগ এলো ইংল্যান্ড যাওয়ার, তখন তার বয়স সবে ১৮। স্থানীয় লতাপাতার ওষুধের সঙ্গে পরিচিত হয়েই তার জীবন কেটে যেতো, কিন্তু ইউরোপের ছোঁয়া পেয়ে মেরি হয়ে উঠলো আরো উদার।
চিকিৎসার এতসব পদ্ধতি আর উপাদান দেখে মেরি সিকোল অভিভূত হয়ে পড়লো। নিজের জ্ঞানের পরিধি বাড়ানোর সাথে-সাথে ইউরোপের ঔষধি গাছগাছালিরও খোঁজ নেয় সে।
১৮৩৬ সালে মেরি বিয়ে করেন এডউইন হোরাতিও সিকোল নামক একজন মেরিন অফিসারকে। কিন্তু তার স্বামী প্রায়ই সি-সিকনেস বা সমুদ্রযাত্রাজনিত অবসাদে ভুগতো। বিয়ের আট বছরের মাথায় এডউইন মারা যাওয়ার পর মেরি আর কখনও বিয়ে করেননি।
স্বামীর মৃত্যুর পরপরই মেরির মা-ও মারা যায়। এরপর মেরি সিকোল পুরোপুরি মানবসেবার দিকে নজর দেন। কিংস্টনে ফিরে আসার পর মেরি মেডিসিন নিয়ে আবারও কাজ করা শুরু করেন। কিছুদিনের ভেতর মেরি সিকোলের নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।
তার কাজ ছিল মূলত স্থানীয় গাছপালা থেকে সংগৃহীত ওষুধের মাধ্যমে আহত সৈনিকদের সেবা দেওয়া। তার বানানো এসব ওষুধ খুবই কার্যকরী ছিলো। সৈনিকদের সেবাদানের পাশাপাশি মেরি কলেরা, টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া এবং গুটিবসন্তেরও চিকিৎসা করেন।

১৮৫০ সালে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে বহু মানুষ মৃত্যুবরণ করে। এরপরও মেরি সিকোল নিজের বানানো ওষুধ ব্যবহার করে বহু মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচান।
সে বছরই মেরি পানামায় তার ভাইয়ের কাছে পাড়ি জমান। সেখানে নিজের তৈরী একটি মেডিসিনের দোকান তৈরি করে সেগুলো স্থানীয়দের কাছে বিক্রি করেন। এক সন্ধ্যায় তার ভাই বন্ধুর সঙ্গে মদ্যপান করে বাড়ি ফেরে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই আকস্মিকভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সে। মেরি তাকে বাঁচানোর শত চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন।
এদিকে শহরবাসী সেই বন্ধুর উপর চড়াও হয় এবং দোষারোপ করতে থাকে তাকে। কিন্তু মেরি তাদের শান্ত করেন, কারণ তার কাছে এটি বিষক্রিয়া মনে হয়নি। এটি অন্যকিছু, যা তার শরীর জানান দিচ্ছিলো! অবশেষে মেরি সিকোল বুঝতে পারেন, তার ভাই কলেরায় ভুগেই মারা গেছে!
এরপর থেকেই কলেরা শহরময় ছড়িয়ে পড়ে। বাতাসের বেগে শহরময় কলেরা ছড়িয়ে পড়ায়, অল্প সময়েই বহু মানুষ প্রাণ হারায়। কিন্তু সেই সময়ে পানামায় কোনো চিকিৎসকও ছিল না, যিনি কিনা কলেরার চিকিৎসা করতে পারেন।
অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে দায়িত্ব নিজের কাঁধেই তুলে নেন মেরি। তার স্থানীয় চিকিৎসা পদ্ধতিই একমাত্র অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী অনেকটা একা হাতে অনেক মানুষকে বাঁচাতে সক্ষম হন মেরি।
বহু মানুষ ছিল, যারা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী নয়। তাদেরকে মেরি নিজ খরচেই চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করে তোলেন। সবার কাছে মেরি তাই হয়ে ওঠেন ‘ওয়ান ওম্যান আর্মি‘।
কলেরার প্রকোপ কমার পর মেরি সিকোল কিউবা হয়ে নিজ শহর কিংস্টনে ফিরে আসেন। ঠিক সেই সময়ে বলকান অঞ্চলে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠে। সৈনিকরা জ্যামাইকা ছাড়তে শুরু করে যুদ্ধে যোগ দিতে। এসব দেখে মেরিও নিজের নিয়তি ঠিক করে নেন।
ক্রিমিয়ার যুদ্ধের নায়িকা
১৮৫৩ সালে রাশিয়া এবং অটোমান সাম্রাজ্যের মাঝে যুদ্ধ বেঁধে যায়। পরের বছর, অর্থাৎ ১৮৫৪ সালে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড অটোমানদের সঙ্গে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যোগ দেয়। হাজার-হাজার সৈন্য কৃষ্ণসাগর এবং ক্রিমিয়ান উপদ্বীপে ভিড় করে। কিন্তু দেখা গেল, যুদ্ধের এক বছরের মাথায় প্রচুর ইংরেজ সৈনিক মারা যাচ্ছে। যাদের বেশিরভাগই কলেরায় আক্রান্ত হয়েছিল।
সৈনিকদের ভেতর কলেরার প্রকোপ বেড়ে যাওয়ায় ইংরেজ সরকার নার্স নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেয়। সবার মতো মেরি সিকোলও আবেদন করেন। কিন্তু সেই সময় তিনি ইংল্যান্ডে থাকার পরও শুধুমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ বলে তাকে সেখানে যেতে দেওয়া হলো না!
কিন্তু মেরি দমে যাওয়ার পাত্রী নন মোটেই। নিজের সকল সঞ্চয় কাজে লাগিয়ে মেরি ক্রিমিয়ার উদ্দেশে সাগর পাড়ি দিলেন আহত সৈনিকদের সেবা দিতে!

এখানে এসে মেরি স্থানীয় হাসপাতালগুলোতে আহত সৈনিকদের শুশ্রূষা দিতে শুরু করলেন। কেউ তাকে তেমন পাত্তা দিচ্ছিল না, এমনকি কাজ শেষে মেরিকে জাহাজের একটি ছোট কুঠুরিতে ঘুমোতে হতো।
কিন্তু চোরেদের উৎপাতে অসহ্য হয়ে মেরি সিকোল নিজেই একটি দোকান খুলে বসলেন, নাম দিলেন ‘ব্রিটিশ হোটেল’। এখানে সৈনিকদের জন্য খাওয়া-দাওয়াসহ চিকিৎসার সবরকম ব্যবস্থা রাখা হয়।
অন্যান্য জ্যামাইকান নার্সদের সমর্থনে তার ছোট হাসপাতালটি সবার মাঝে জনপ্রিয়তা পেতে থাকে। আহত সৈনিকরা এখানে আসতে থাকলো বিশ্রাম আর চিকিৎসার জন্য। মেরি নিজেও যুদ্ধের ময়দানে ছুটে যেতো কোনো আহত সৈনিককে সেবা দেওয়ার জন্য।
চারদিকে কেবল গোলাগুলি আর মৃত্যুর মিছিল। কখন কার গায়ে গুলি লেগে মারা যাচ্ছে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই! ঠিক এমন এক পরিস্থিতিতে মেরি সিকোল নির্বিকারভাবে কোনোরকম নিরাপত্তা ছাড়াই যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে যেতেন।
কে কোন দেশের সৈন্য, এটা দেখার মতো মানসিকতা তার ছিল না। বরং যেখানেই কাতরাতে থাকা কোনো সৈন্যকে দেখতে পেতেন, সেখানেই তার সেবা করতেন কিংবা নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিতেন।

তার সাহসিকতা আর সেবার নিদর্শন ইতোমধ্যে সব সৈন্য শিবিরে পৌঁছে গেছে। তাই সামরিক ডাক্তাররাও সময়ে-অসময়ে তাকে ডেকে পাঠাতে লাগলেন। এখন এই শিবিরে তো একটু পর আরেক সৈন্য শিবিরে।
যুদ্ধের মাঠে সবার শত্রু সবার চেনা, কিন্তু যারা মেরির সেবা পেয়েছে, তাদের কাছে মেরির পরিচয় ‘মাতা মেরি’ হিসেবে! না সে কারও বন্ধু না শত্রু; তার একটাই চিন্তা, আহতদের শুশ্রূষা দিতে হবে।
১৮৫৫ সালে রাশিয়া শান্তিচুক্তির জন্য আগ্রহী হয়ে উঠে। এতে করে বছরব্যাপী চলা এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসান ঘটে। ৩০ মার্চ, ১৮৫৬ সালে সব পক্ষ শান্তিচুক্তির ব্যাপারে একমত হয়। ইতিহাসে এটি ‘প্যারিস শান্তি চুক্তি‘ নামে পরিচিত।
শান্তিচুক্তির পর এতদিনের ক্রিমিয়ান উপদ্বীপ হঠাৎ করেই নীরব হয়ে পড়ে! প্রতি মুহূর্তের আতঙ্ক, গোলাগুলি আর আহত সৈনিকদের আর্তচিৎকার থেমে গিয়ে সেখানে ভর করে কবরের নীরবতা। একে-একে সবাই বাড়ি ফিরছিল। কিন্তু মেরির মাঝে কোনো তাড়া নেই যেনো। সে তখনও শুশ্রূষা দিয়ে যাচ্ছে। একসময় সবাই বাড়ি ফিরলে ক্লান্ত মেরিও ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন।
বাড়ি ফেরা
ইংল্যান্ডে ফেরার পর মেরির কাছে সহায়-সম্পত্তি বলতে কিছুই ছিল না। ক্রিমিয়ান যুদ্ধে তার সব সম্পদ ব্যয় হয়ে গিয়েছিল। এভাবে মেরি অনাহারে দিন কাটাতে শুরু করেন। কিছুদিন পর মেরি সিকোল নিজের বায়োগ্রাফি লিখেন ‘দ্য ওয়ান্ডারফুল এডভেঞ্চারস অভ মিসেস সিকোল ইন মেনি ল্যান্ডস’ নামে।
মেরির দুর্দশার কথা জানতে পেরে ক্রিমিয়ান যুদ্ধে তার সেবা পাওয়া সৈনিকরা মেরির জন্য ফান্ড কালেকশনে নেমে পড়ে। কিন্তু তাদের এই উদ্যোগ খুব একটা সফলতা পায়নি। মানুষ একজন কৃষ্ণাঙ্গ নারীর জন্য নিজের পকেটের টাকা ঢালতে রাজি হয়নি!
একেবারে কপর্দকহীন অবস্থায় মেরি সিকোল নিজ জন্মভূমি জ্যামাইকার কিংস্টনে ফিরে যান। এখানে এসে মেরিকে হতাশ হতে হয়নি। জ্যামাইকার মানুষ তাদের রত্নকে ঠিকই চিনে নিয়েছিল। অবশেষে মানুষের ভালোবাসা নিয়েই মেরি আবার লন্ডনে ফিরে আসেন। এখানে ১৮৮১ সালে মেরি সিকোল মৃত্যুবরণ করেন।

মেরির মৃত্যুর পর তার সব কীর্তি ঢাকা পড়ে যায়। এমনকি ব্রিটিশ মিডিয়া মেরি সিকোলকে ক্রিমিয়ান যুদ্ধের ময়দানের এক সামান্য ক্যান্টিন মালিক হিসেবে অভিহিত করে! অবশেষে তার মৃত্যুর শত বছর পর ২০০৪ সালে ব্রিটিশ সরকার ক্রিমিয়ান যুদ্ধে অবদান রাখার জন্য মেরি সিকোলকে সর্ব্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মাননায় ভূষিত করে।
কিছুদিনের মাথায় ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের মতোই ব্রিটিশ পাঠ্যপুস্তকগুলোতে মেরি সিকোলের অবদান তুলে ধরা হয়। মেরি সিকোলের নামে দ্য মন্টফোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা কেন্দ্র খোলা হয় এবং বহু হাসপাতালে তার নামে ওয়ার্ডের নামকরণ করা হয়।
এভাবেই মৃত্যুর শত বছর পর হলেও মেরি সিকোল নিজের প্রাপ্য সম্মানটুকু পেয়েছেন। জীবদ্দশায় যে নারী মানুষের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন, তিনিই কিনা বর্ণবাদের শিকার হয়ে সবার আড়ালে চলে গেলেন।
হয়তো মেরি সিকোল বুকভরা কষ্ট নিয়েই চোখ বন্ধ করেছিলেন শেষবারের মতো, কিন্তু দেরিতে হলেও তিনি যে সম্মান পেলেন, এটাই হয়তো মানবসেবার কাণ্ডারীদের আরেকবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার শক্তি যোগাবে।

.jpg?w=600)