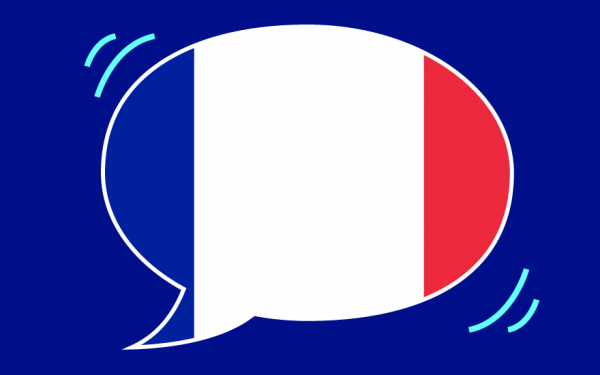পুরুষতন্ত্র কী? এ ব্যাপারে আমাদের সমাজে অনেকের ধারণাই অসম্পূর্ণ, ভাসা-ভাসা। তাই যখনই কোনো আলোচনায় পুরুষতন্ত্র শব্দটির আগমন ঘটে, অনেকে না-বুঝেই সেটির বিরোধিতা করে। অনেকে আবার পুরুষতন্ত্রকে ভুলভাবেও ব্যাখ্যা করে, যার ফলে গোটা আলোচনাই ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়।
তাই পুরুষতন্ত্র বলতে আসলে কী বোঝায়, এবং কেন পুরুষতন্ত্রের ধারণাটির সঙ্গে পরিচিত হওয়া আবশ্যক, তা আমাদের সকলেরই জানা প্রয়োজন। এবং এক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়ক হতে পারে কমলা ভাসিনের ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত ‘হোয়াট ইজ প্যাট্রিয়ার্কি?’
প্রশ্নোত্তর বা কথোপকথনের ভঙ্গিতে রচিত এই বইটি পুরুষতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের ভ্রান্ত ধারণাগুলো দূর করে, এ ব্যাপারে একটি বাস্তবসম্মত উপলব্ধি অর্জনে সাহায্য করবে। তাহলে চলুন, কমলা ভাসিনের রচনার আলোকে জানা যাক পুরুষতন্ত্রের আদ্যোপান্ত।

পুরুষতন্ত্র বলতে আমরা কী বুঝি?
পুরুষতন্ত্র শব্দটি এসেছে মূলত ইংরেজি ‘প্যাট্রিয়ার্কি’ (patriarchy) হতে, বাংলায় যার আক্ষরিক অর্থ পিতৃতন্ত্র বা পিতার শাসন। উৎপত্তিগতভাবে এই শব্দটি ব্যবহৃত হতো এক বিশেষ ধরনের ‘পুরুষ-অধীনস্থ পরিবার’ নির্দেশে, অর্থাৎ নারী, কমবয়সী পুরুষ, শিশু, দাস, গৃহকর্মী সকলকে অন্তর্ভুক্ত যে বিশাল পরিবার পরিচালিত হতো একজন আধিপত্যশীল পুরুষের অধীনে। কিন্তু এখন এটি বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে পুরুষের আধিপত্যকে নির্দেশ করতে; সেই শক্তি সম্পর্ককে বোঝাতে, যার দরুণ পুরুষ আধিপত্য বিস্তার করে নারীর উপর। তাছাড়া পুরুষতন্ত্রের মাধ্যমে সেই বিশেষ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যও নিরূপণ করা হয়, যেখানে বেশ কিছু উপায়ে নারীকে অধস্তন করে রাখা হয়।
আমরা (নারীরা) যে সামাজিক বা অর্থনৈতিক শ্রেণিরই প্রতিনিধিত্ব করি না কেন, প্রাত্যহিক জীবনে আমাদের সবাইকেই কিছু অধীনস্থতার সম্মুখীন হতে হয়, এবং সেগুলো আসে বিভিন্ন রূপে: বৈষম্য, অসম্মান, অপমান, নিয়ন্ত্রণ, শোষণ, নিপীড়ন, সহিংসতা ইত্যাদি। এগুলো ঘটে থাকে পরিবারের মধ্যে, কর্মস্থলে, সমাজে। ঘটনাগুলো বিস্তারিতভাবে হয়তো আলাদা, কিন্তু তাদের মূলভাব সবসময়ই এক ও অভিন্ন।
পুরুষতন্ত্র আসলে কীভাবে নিজেকে প্রকাশ করে? আমাদের নিজেদের জীবনে আমরা একে কীভাবে চিনতে পারব?
যারা এমনকি সূক্ষ্ম বৈষম্য, পক্ষপাত বা অস্বীকৃতিরও শিকার হয়েছে, তারা সকলেই এটি জানে এবং অনুভব করতে পারে। তবে হয়তো তারা জানে না এর নাম কী। যখনই কোনো ওয়ার্কশপে নারীরা তাদের অভিজ্ঞতার কথা বলে, তারা আসলে ব্যক্তিগতভাবে সম্মুখীন হওয়া নানা ধরনের পুরুষতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের কথাই বলে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে আমি কী বলতে চাইছি তা ভালোভাবে বোঝা যাবে। এদের প্রতিটিই কোনো নির্দিষ্ট ধরনের বৈষম্য এবং পুরুষতন্ত্রের কোনো দিক চিত্রায়িত করে।
- “আমি শুনেছি আমি যখন জন্মালাম, তখন আমার পরিবার খুশি ছিল না। তারা একটি পুত্রসন্তান চেয়েছিল।” (পুত্রসন্তান-প্রাধান্য)
- “আমার ভাইয়েরা খাবার চাইতে পারত, তারা হাত বাড়াতে পারত এবং নিজেদের ইচ্ছামতো খাবার নিতে পারত। কিন্তু আমাদেরকে বলা হতো খাবারের জন্য অপেক্ষা করতে। সবার খাওয়া হয়ে গেলে যা অবশিষ্ট থাকত, তা-ই খেতে বাধ্য হতাম আমরা বোনেরা এবং আমাদের মা।” (খাদ্য বিতরণে মেয়েদের প্রতি বৈষম্য)
- “আমাকে ঘরের কাজে মাকে সাহায্য করতে হয়, আমার ভাইদেরকে হয় না।” (নারী ও কমবয়সী মেয়েদের উপর গৃহস্থালি কাজের বোঝা)
- “স্কুলে যাওয়া আমার জন্য ছিল সংগ্রামের সমতুল্য। আমার বাবা ভাবত আমাদের মেয়েদের জন্য পড়াশোনা করা জরুরি নয়।” (মেয়েদেরকে শিক্ষার সুযোগ হতে বঞ্চিত করা)
- “আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে বা খেলতে বাইরে যেতে পারতাম না।”
- “আমার ভাইয়েরা যখন-খুশি বাসায় ফিরতে পারে, কিন্তু আমাকে অন্ধকার হওয়ার আগেই ফিরে আসতে হয়।” (মেয়েদের পরিসরের সীমাবদ্ধতা ও পরাধীনতা)
- “বাবা প্রায়ই আমার মাকে মারত।” (স্ত্রী-প্রহার)
- “আমার ভাইয়েরা আমার বাবার চেয়েও খারাপ। তারা আমাকে কোনো ছেলের সঙ্গেই কথা বলতে দেয় না।” (নারী ও মেয়েদের উপর পুরুষের নিয়ন্ত্রণ)
- “আমি যেহেতু আমার বসের চাহিদা মেটাতে চাইনি, তাই আমাকে চাকরি থেকে ছাঁটাই করে দেয়া হয়েছে।” (কর্মস্থলে নারীদের হেনস্থা)
- “বাবার সম্পত্তিতে আমার কোনো ভাগ নেই। স্বামীর সম্পত্তিও আমার নিজের নয়। আসলে আমার এমন কোনো ঘরই নেই যাকে আমি আমার নিজের বলে দাবি করতে পারি।” (নারীদের উত্তরাধিকার কিংবা সম্পত্তি অধিকারের অভাব)
- “যখনই আমার স্বামী চায়, তার কাছে আমাকে আমার শরীর বিলিয়ে দিতে হয়। আমার ‘না’ বলার উপায় নেই। আমি যৌনতাকে ভয় পাই। এটা উপভোগ করতে পারি না।” (নারীর শরীর ও যৌনতার উপর পুরুষের নিয়ন্ত্রণ)
- “আমি চেয়েছিলাম আমার স্বামী যেন পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতি ব্যবহার করে। কিন্তু সে রাজি হয়নি। সে আমাকে অস্ত্রোপচার করার অনুমতিও দেয়নি।” (নারীদের প্রজনন স্বাস্থ্যের নিয়ন্ত্রণ ও অধিকার না থাকা)
এই খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতাগুলো বিক্ষিপ্ত মনে হতে পারে, কিন্তু যখন আমরা এগুলোকে পরপর সাজাই, তখন একটি প্যাটার্ন তৈরি হতে শুরু করে, এবং আমরা অনুধাবন করতে পারি যে আমাদের প্রত্যেককেই কোনো না কোনো ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়। এ ধরনের পরাধীনতা, নিয়ন্ত্রণহীনতার অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা আমাদের আত্মসম্মান, আত্মবিশ্বাসকে ধ্বংস করে দেয়, এবং আমাদের স্বপ্নগুলোকেও সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ করে দেয়। যখনই আমরা কোনো সাহসী কাজ করি, আমাদের উপর নিন্দার বৃষ্টি শুরু হয়, আমাদেরকে বলা হয় ‘অনারীসুলভ’। যখনই আমরা নিজেদের জন্য নির্ধারিত পরিসর ও ভূমিকার বাইরে পা রাখি, আমাদেরকে বলা হয় নির্লজ্জ।
আমাদের পরিবার, সামাজিক সম্পর্ক, ধর্ম, আইন, স্কুল-কলেজ, পাঠ্যপুস্তক, গণমাধ্যম, কলকারখানা, অফিস-আদালত, সর্বত্রই বিদ্যমান ওসব নিয়ম ও চর্চা, যেগুলো আমাদেরকে পুরুষের চেয়ে হীন করে তোলে, আমাদের উপর অন্যের নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে দেয়।
আমরা যখন পরস্পরের অভিজ্ঞতার কথা শুনি, তখন আমরা বুঝতে পারি যে এই অধীনস্থতা মাত্র গুটিকতক অভাগা নারীর নিয়তি নয়, কিংবা এগুলো অল্প কয়েকজন ‘পাশবিক’ পুরুষের কারণেও হয় না, যারা নারীদেরকে শোষণ ও নিপীড়ন করে। আমরা বুঝতে শুরু করি যে আমরা দাঁড়িয়ে আছি একটি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, যে ব্যবস্থা হলো পুরুষের আধিপত্য ও শ্রেষ্ঠত্বের, পুরুষের নিয়ন্ত্রণের, যেখানে নারীর অবস্থান সর্বদাই নিচে।
পুরুষতন্ত্র পরিভাষাকে কি আমরা আমাদের চারপাশে সবসময় যে পুরুষের আধিপত্য দেখতে পাই সেগুলোর সামষ্টিক নির্দেশক বলতে পারি?
হ্যাঁ, তা পারেন। তবে এটি একটি পরিভাষার চেয়েও অনেক বেশি কিছু। নারীবাদীরা একে একটি ধারণা হিসেবে ব্যবহার করে, এবং অন্য সব ধারণার মতোই, এটাও আমাদের বাস্তবতাকে অনুধাবন করার একটি সহায়ক যন্ত্র। নানা মানুষ একে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে।
জুলিয়েট মিচেল বলে একজন নারীবাদী মনস্তত্ত্ববিদ পুরুষতন্ত্র শব্দটি ব্যবহার করেছেন সেই সম্পর্ক-ব্যবস্থাকে নির্দেশ করতে, যেখানে পুরুষরা নারীদেরকে বিনিময় করে; এবং সেই প্রতীকী ক্ষমতাকেও, যা পিতারা এই ব্যবস্থার অধীনে চর্চা করে থাকে। তার মতে, এই ক্ষমতাই দায়ী নারীদের ‘হীনম্মন্য’ মনস্তত্ত্বের পেছনে। এদিকে সিলভিয়া ওয়ালবি তার ‘থিওরাইজিং প্যাট্রিয়ার্কি’ বইতে একে বলেছেন সামাজিক কাঠামো ও অনুশীলনের একটি ব্যবস্থা, যেখানে পুরুষরা নারীদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে, তাদেরকে শোষণ ও নিপীড়ন করে। যে কথা আমিও আগে বলেছি, সিলভিয়া ওয়ালবি আমাদেরকে তা মনে করিয়ে দেন যে, পুরুষতন্ত্রকে একটি ব্যবস্থা হিসেবে অনুধাবন করা গুরুত্বপূর্ণ, কেননা তাহলে আমরা প্রত্যাখ্যান করতে পারি বায়োলজিক্যাল ডিটারমিনিজম বা জৈব নির্ধারণবাদকে (যার মূল কথা হলো এই যে, নারী ও পুরুষ প্রাকৃতিকভাবেই ভিন্ন তাদের জৈবিক বা দৈহিক কারণে, এবং সে কারণেই তাদেরকে সমাজে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা প্রদান করা হয়)। পাশাপাশি পুরুষতন্ত্রকে ব্যবস্থা হিসেবে অনুধাবনের ফলে আমরা সেই ধারণাকেও প্রত্যাখ্যান করতে পারি, যা দাবি করে প্রতিটি পুরুষ ব্যক্তিবিশেষই সবসময় আধিপত্যশীল অবস্থায় থাকবে, এবং প্রত্যেক নারীই থাকবে অধীনস্থ পর্যায়ে।
এই ব্যবস্থার সঙ্গেই যুক্ত রয়েছে সেই আদর্শ, যা বলে থাকে পুরুষরা নারীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, এবং সে-কারণে নারীকে সবসময়ই পুরুষের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকতে হবে, এবং নারী হলো পুরুষের সম্পত্তি। উদাহরণস্বরূপ, কিছু দক্ষিণ এশীয় ভাষায় ব্যবহৃত হয় স্বামী, পতি, মালিক প্রভৃতি শব্দ– যাদের প্রত্যেকেরই আক্ষরিক অর্থ হলো ‘প্রভু’ বা ‘মালিক’।
পুরুষতন্ত্র কি সর্বত্রই একই রকম?
না, সবসময় তা নয়। একই সমাজেরই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিতে এর প্রকৃতি হতে পারে ভিন্ন ভিন্ন। একই রকম ভিন্নতা লক্ষণীয় ইতিহাসের বিভিন্ন সমাজ কিংবা সময়কালে। তবে সামগ্রিক মূলনীতি সবসময় একই থাকে, অর্থাৎ, ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ থাকবে পুরুষদের হাতে। তবে সেই নিয়ন্ত্রণের ধরন কেমন হবে, সেক্ষেত্রে ভিন্নতা থাকতে পারে। যেমন ধরুন, আজকের দিনে পুরুষতান্ত্রিক অভিজ্ঞতা যেমন, আমাদের নানি-দাদিদের আমলে তা ছিল না। আবার উপজাতীয় নারী এবং উঁচু বর্ণের হিন্দুদের ক্ষেত্রে তা এক নয়। যুক্তরাষ্ট্রের নারী এবং ভারতের নারীদের বেলায়ও তা আলাদা। বস্তুত, প্রতিটি সামাজিক ব্যবস্থা বা ঐতিহাসিক সময়কালই তার নিজস্ব বৈচিত্র্য প্রদান করে, যা নির্ধারণ করে দেয় পুরুষতন্ত্রের স্বরূপ, এবং কীভাবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুশীলনগুলোর মাঝে পার্থক্য তৈরি হবে। এই পার্থক্যগুলো শনাক্ত করতে পারা জরুরি, যাতে করে আমরা আমাদের অবস্থাকে আরো ভালোভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি, একই সঙ্গে এই অবস্থা মোকাবিলায় সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশল কী হতে পারে তা-ও খুঁজে বের করতে পারি।

পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুরুষরা কোন জিনিসগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে?
প্রধানত নারীদের জীবনের নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলো পুরুষতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে থাকে।
১. নারীদের উৎপাদন বা শ্রম শক্তি
পুরুষরা নারীদের উৎপাদন ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে ঘরের বিনামূল্যের কাজ কিংবা বাইরের উপার্জনশীল কাজ, দুই জায়গাতেই। ঘরে নারীরা কোনো পারিশ্রমিক ছাড়াই তাদের সন্তান, স্বামী এবং পরিবারের সকল সদস্যকে সারা জীবনভর সেবা দিয়ে থাকে। সিলভিয়া ওয়ালবির বলা ‘উৎপাদনের পুরুষতান্ত্রিক ধারা’ মোতাবেক, নারীদের শ্রমের সুফল ভোগ করে তাদের স্বামী এবং পরিবারের অন্য সকলেই। ওয়ালবির মতে, গৃহবধূরা হলো উৎপাদক শ্রেণি, এবং স্বামীরা হলো দখলদার শ্রেণি। তাই তো গৃহবধূদের কোমর-ভাঙা, নিরন্তর, পুনরাবৃত্তিমূলক খাটুনিকে কাজ বলেই গণ্য করা হয় না, বরং মনে করা হয় গৃহবধূরা সবসময়ই তাদের স্বামীদের উপর নির্ভরশীল।
পুরুষরা নারীদের ঘরের বাইরের শ্রমকেও নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তারা হয় নারীদেরকে তাদের শ্রম বিক্রি করতে বাধ্য করে, নয়তো নারীদেরকে ঘরের বাইরে কাজ করতে বাধা প্রদান করে। এমনও অনেক সময় হয় যে নারীরা যা উপার্জন করে তা পুরুষরা জোর করে কেড়ে নেয়, কিংবা তারাই ঠিক করে দেয় নারীরা কখন কতটুকু কাজ করবে। এরপর আবার নারীদেরকে ভালো বেতনের চাকরি থেকেও বঞ্চিত করা হয়। তাদেরকে বাধ্য করা হয় তাদের শ্রমকে খুবই স্বল্প মজুরিতে বিক্রি করতে। কখনো কখনো তাদেরকে ঘরে বসে কাজ করতেও বাধ্য করা হয় ‘গৃহভিত্তিক উৎপাদন’ এর বুলি আউড়ে, যা কিনা সবচেয়ে শোষণমূলক ব্যবস্থা।
এই যে নারীদের শ্রমের উপর নিয়ন্ত্রণ ও শোষণ, এর অর্থ হলো পুরুষরা পুরুষতন্ত্র হতে বস্তুগত সুবিধা ভোগ করে। তারা নারীদের অধস্তনতার সুযোগ নিয়ে তাদের অর্থনৈতিক প্রাপ্তি ছিনিয়ে নেয়। অন্য কথায় বলতে গেলে, পুরুষতন্ত্রের একটি বস্তুগত ভিত্তি রয়েছে।
২. নারীদের প্রজনন
পুরুষরা নারীদের প্রজনন ক্ষমতাকেও নিয়ন্ত্রণ করে। অনেক সমাজে নারীদের স্বাধীনতা নেই সিদ্ধান্ত নেয়ার যে তারা কয়টি সন্তান নিতে চায়, কখন নিতে চায়, গর্ভনিরোধক ব্যবহার করতে চায় কি না, গর্ভপাত করতে চায় কি না ইত্যাদি। পুরুষের ব্যক্তিকেন্দ্রিক নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও, পুরুষের আধিপত্যশীল প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন চার্চ বা রাষ্ট্রও (অথবা ধর্ম ও রাজনীতি) নিয়ম বেঁধে দেয় নারীর প্রজনন ক্ষমতার ব্যাপারে। একে বলে প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত নিয়ন্ত্রণ। উদাহরণস্বরূপ, ক্যাথলিক চার্চের পুরুষ ধর্মীয় যাজকরা ঠিক করে দেন যে নারী ও পুরুষরা জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারবে কি না, কোন কোন পদ্ধতি ব্যবহারের অনুমতি পাবে, নারীরা গর্ভপাত করতে পারবে কি না, এবং আরো অনেক কিছু। গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে নারীদের এই যে প্রতিনিয়ত কী, কে, কীভাবে এবং আদৌ জাতীয় প্রশ্নের জালে আবদ্ধ থাকতে হয়, তা মূলত বিশ্বের সকল দেশেই দৃশ্যমান। এবং এ থেকেই বোঝা যায় যে এই নিয়ন্ত্রণ কতখানি শক্তিশালী, এবং পুরুষরা এই নিয়ন্ত্রণের লাগাম ছেড়ে দিতে কতটা নারাজ।
আধুনিক সময়ে, পুরুষতান্ত্রিক রাষ্ট্র নারীদের প্রজনন ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্পের মাধ্যমে। রাষ্ট্র ঠিক করে দেয় দেশের সন্তোষজনক জনসংখ্যার আকার, এবং সে অনুযায়ী নারীদের উৎসাহিত বা অনুৎসাহিত করে সন্তান জন্মদানে। যেমন ভারতে চালু রয়েছে একটি আগ্রাসী জন্ম নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প, যা চেষ্টা করে যাচ্ছে দেশটির গড় পরিবারের আকার নির্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ রাখার। আবার মালয়েশিয়ায় নারীদের প্রতি আহবান জানানো হচ্ছে কয়েকটি সন্তান নেয়ার, যেন দেশে উৎপাদিত শিল্পদ্রব্যের জন্য একটি মোটামুটি বড় ঘরোয়া বাজার সৃষ্টি করা যায়। এদিকে ইউরোপে, যেখানে সন্তান জন্মহার খুবই কম, সেখানে নারীদেরকে বিভিন্ন ইনসেনটিভের প্রলোভন দেখানো হয় যেন তারা বেশি বেশি সন্তান নেয়। সেখানে তাদের লম্বা সময়ের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটি দেয়া হয়, এবং ওই ছুটির সময়ে পুরো বেতনই দেয়া হয়। এছাড়াও রয়েছে খণ্ডকালীন চাকরির সুবিধা, চাইল্ডকেয়ার সুবিধা ইত্যাদি। কোনো কোনো দেশ আবার ‘পুরুষের মাতৃত্বকালীন ছুটি’ তথা ‘পিতৃত্বকালীন ছুটি’ও দিয়ে থাকে।
রাষ্ট্রের আদর্শ ও নীতিমালা শ্রম অর্থনীতির চাহিদার উপর ভিত্তি করেও বদলাতে থাকে। যেমন ধরুন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানিতে যখন প্রচুর শ্রম শক্তির প্রয়োজন পড়ে দেশটিকে পুনর্গঠন করতে, তখন নারীদেরকে আহবান জানানো হয় চাকরি করতে এবং জাতি গঠনে ভূমিকা রাখতে। বিপরীত চিত্র দেখা যায় ব্রিটেনে। যুদ্ধের সময় অনেক নারী সক্রিয়ভাবে সম্মুখভাগে কাজ করে গেলেও, একবার যখন ব্রিটেন যুদ্ধে জিতে গেল, তখন সেসব নারীদেরকে বলা হলো ঘরে ফিরে যেতে, কেননা পুরুষরাই যথেষ্ট, শান্তিপূর্ণ সময়ের কাজ সামলাতে। ১৯৫০-র দশকে যুক্তরাষ্ট্রে বিখ্যাত ‘বেবি বুম’-ও (১৯৪৬ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে জন্মহার ঊর্ধ্বমুখী থাকে) ঘটে একই কারণে, এবং এ ফলাফল থেকে প্রতিফলিত হয় মাতৃত্বের আদর্শকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রচারণাও।
মাতৃত্বের আদর্শই কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে নারীদের অবস্থার কট্টরপন্থী নারীবাদী (রেডিক্যাল ফেমিনিস্ট) বিশ্লেষণে। তাদের মতে, নারীরা পরাধীন মূলত এ কারণে যে তাদের, এবং শুধুই তাদের উপর, মাতৃত্ব ও সন্তান প্রতিপালনের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। প্রয়োজনীয় গর্ভনিরোধ-বিষয়ক তথ্যাবলি সম্পর্কে অবহিত না করেই কমবয়সী নারীদের উপর মাতৃত্বকে চাপিয়ে দেয়া হয়। তাছাড়া গর্ভনিরোধক প্রাপ্তিও নারীদের জন্য সহজ ও সুবিধাজনক ব্যাপার নয়। যেসব গর্ভনিরোধকের নাগাল তারা পায়, সেগুলোও হয়ে থাকে অনেক দামি, অবিশ্বস্ত অথবা ক্ষতিকর। তাছাড়া পুরুষতন্ত্র গর্ভপাতের সুযোগও কমিয়ে দেয়, এমনকি অনেক সময় সেটাকে অস্বীকৃতিও জানায়। কিন্তু একইসঙ্গে পুরুষতন্ত্র নারীর উপর তীব্র ও অবিরাম চাপ প্রয়োগ করে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হতে।
আরেকটি ব্যাপার হলো, পুরুষতন্ত্র নারীদেরকে শুধু মা হতেই বাধ্য করে না, সেই মাতৃত্বের স্বরূপ কেমন হবে তা-ও নির্ধারণ করে দেয়। মাতৃত্বের এই আদর্শ বিবেচিত হয় নারী নিপীড়নের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে, কেননা এটি পুরুষালি ও মেয়েলি চারিত্রিক ধরন সৃষ্টি করে, যা পুরুষতন্ত্রকে চিরস্থায়ী করে তোলে। এছাড়াও এর ফলে ব্যক্তিগত ও গণপর্যায়ে বিভাজন মজবুত হয়, নারীদের গতিশীলতা ও বিকাশ আটকে যায়, এবং পুরুষদের আধিপত্যের পুনরুৎপাদন ঘটে।
৩. নারীদের যৌনতার উপর নিয়ন্ত্রণ
নারীদের পরাধীনতার ক্ষেত্রে এটি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। যখনই পুরুষদের প্রয়োজন বা আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়, তখনই নারীরা তাদেরকে যৌন পরিষেবা দিতে বাধ্য হয়। প্রতিটি সমাজেই একটি পূর্ণাঙ্গ নৈতিক ও আইনি শাসন জারি থাকে বৈবাহিক সম্পর্কের বাইরে নারীদের যৌনতার বহিঃপ্রকাশকে বাধা দিতে। অথচ পুরুষদের বেলায় এই সমাজই যেন অনেকটা চোখ বন্ধ করে রাখে। মুদ্রার অপর পিঠে, পুরুষরা তাদের স্ত্রী, কন্যা কিংবা অন্যান্য নারীর উপরও জোর করতে পারে তাদের পতিতাবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে, অর্থাৎ অর্থের বিনিময়ে তাদের যৌনতাকে বিক্রি করতে। ধর্ষণ এবং ধর্ষণের হুমকি হলো আরেকটি পদ্ধতি নারীদের যৌনতার উপর আধিপত্য বিস্তার করার, এর সঙ্গে তাদের ‘ইজ্জত’ ও ‘সম্মান’-এর প্রশ্ন জুড়ে দেয়ার। নারীদের যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, আচরণ ও গতিশীলতাকে খুবই সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করা হয়; পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় নিয়মকানুনের উপর ভিত্তি করে।

একটি কট্টরপন্থী নারীবাদী বিশ্লেষণ দাবি করে যে পুরুষতন্ত্রের অধীন নারীরা কেবল মা-ই নয়, তারা যৌনদাসীও বটে। এবং পুরুষতান্ত্রিক আদর্শ সাধারণ নারীর মাতৃত্বের চেয়ে তার যৌন সত্তাকেই এগিয়ে রাখে। মাতৃত্বের আংশিক ব্যতিক্রমকে বাদ দিলে, পুরুষালি সংস্কৃতি মোটা দাগে নারীকে পুরুষের সুখের নিমিত্তে ব্যবহার্য যৌন বস্তু হিসেবেই সংজ্ঞায়িত করে। এর ফলে, ধর্ষণের অস্তিত্ব সকল সমাজেই বিদ্যমান না-ও হতে পারে, কিন্তু তবু এটি পুরুষতন্ত্রকে নির্ধারণকারী একটি অনুষঙ্গ। এটি ধর্ষণকে দেখে একটি কার্যকরী রাজনৈতিক যন্ত্র হিসেবে। ধর্ষণ হলো নিপীড়নের একটি রাজনৈতিক ধারা, যা ক্ষমতাবান শ্রেণির সদস্যরা ক্ষমতাহীন শ্রেণির সদস্যদের উপর অনুশীলন করে থাকে। কট্টরপন্থী নারীবাদীরা পুরুষতন্ত্রের অধীনে নারীর যৌনতার নিয়ন্ত্রণের উদাহরণ হিসেবে আরো মনোযোগ দেয় প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত পতিতাবৃত্তি, পর্নোগ্রাফি, এবং জোরপূর্বক বিষমকামিতার উপর।
৪. নারীদের গতিশীলতা
নারীদের যৌনতা, উৎপাদন ও প্রজননকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, পুরুষদের প্রয়োজন হয় নারীদের গতিশীলতাও নিয়ন্ত্রণ করার। নারীদের উপর নির্দিষ্ট পোশাক চাপিয়ে দেয়া, তাদেরকে ঘরের বাইরে যেতে বাধা দেয়া, তাদের ব্যক্তিগত ও প্রকাশ্য জীবনকে কঠোরভাবে বিচ্ছিন্ন করে রাখা, অন্য সেক্সের (প্রাকৃতিক লিঙ্গ) মানুষের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় বাধা দেয়াসহ আরো অনেক কিছুই নারীদের গতিশীলতা ও মুক্তিকে নিয়ন্ত্রণের স্বতন্ত্র উপায়। স্বতন্ত্র এ কারণে যে, এগুলো একদমই জেন্ডার-নির্দিষ্ট। পুরুষদের কখনোই এ ধরনের বিধিনিষেধের সম্মুখীন হতে হয় না।
৫. সম্পত্তি এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক খাত
অধিকাংশ সম্পত্তি এবং অন্যান্য উৎপাদনশীল খাতই পুরুষদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, এবং তারা এই নিয়ন্ত্রণ এক পুরুষ হতে আরেক পুরুষে হস্তান্তর করে। সাধারণত তা হয়ে থাকে বাবা থেকে পুত্রের কাছে। এমনকি যেসব জায়গায় নারীদের অধিকার রয়েছে আইনীভাবে এসব সম্পদের মালিক হওয়ার, সেখানেও নানাভাবে তাদেরকে বঞ্চিত করার চেষ্টা চলতে থাকে। প্রথাগত নিয়মের দোহাই, আবেগিক চাপ, সামাজিক নিষেধাজ্ঞার হুমকি, এবং কখনো কখনো, সরাসরি সহিংসতার মাধ্যমেও, তাদেরকে নিজেদের প্রাপ্য হতে বঞ্চিত করা হয়। আবার কিছু ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত আইনের ফলে তারা অধিকার লাভ তো করেই না, বরং যেটুকু অধিকার ছিল তা-ও হারায়। অর্থাৎ, সকল ক্ষেত্রেই, নারীরা সুবিধাবঞ্চিত। এ বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়ে ওঠে জাতিসংঘের পরিসংখ্যান থেকে: “নারীরা বিশ্বব্যাপী মোট কর্মঘণ্টার ৬০ শতাংশেরও বেশি সময় কাজ করে থাকে, কিন্তু বিনিময়ে তারা পায় বিশ্বের মোট উপার্জনের ১০ শতাংশ, এবং অধিকার লাভ করে বিশ্বের মোট সম্পদের ১ শতাংশ।” (সাম্প্রতিক উপাত্ত নয়)
আপনি একটু আগে বলেছেন সকল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানই প্রধানত পুরুষদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই ব্যাপারটি কি আরেকটু বিশদে বলবেন?
সমাজে বিদ্যমান প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি বিশ্লেষণ থেকে দেখা গেছে, তাদের সকলের প্রকৃতিই পুরুষতান্ত্রিক। পরিবার, ধর্ম, গণমাধ্যম, আইন ইত্যাদি হলো একটি পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও কাঠামোর মূল স্তম্ভ। এই ব্যবস্থার শেকড় এতটাই গভীরে প্রোথিত ও সুসংহত যে, তা পুরুষতন্ত্রকে একদম অপরাজেয় করে তোলে। তাছাড়া এর ফলে পুরুষতন্ত্রকে খুব স্বাভাবিক ব্যাপারও মনে হয়। চলুন, পুরুষতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রত্যেকটির ব্যাপারে আলাদাভাবে আলোচনা করি।
১. পরিবার
পরিবার হলো সমাজের মৌলিক একক, এবং এ প্রতিষ্ঠানটিই সম্ভবত সবচেয়ে পুরুষতান্ত্রিক। একজন পুরুষ বিবেচিত হয় পরিবারের মাথা হিসেবে; পরিবারের মধ্যে নারীদের যৌনতা, শ্রম বা উৎপাদন, প্রজনন ও গতিশীলতাকে সে নিয়ন্ত্রণ করে। এখানে একটি ক্রমিক শ্রেণিবিন্যাস রয়েছে, যা নির্দেশ করে যে পুরুষরা শ্রেষ্ঠ ও আধিপত্যশীল, এবং নারীরা হীনতর ও অধস্তন। তাছাড়া পরিবার খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সামাজিকীকরণের মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মকে পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধে দীক্ষিত করতে। পরিবার থেকেই আমরা অর্জন করে থাকি শ্রেণিবিভাজন, অধীনস্থতা, বৈষম্যের প্রাথমিক শিক্ষা। ছেলেরা শেখে কীভাবে নিজেদেরকে জাহির করতে হবে, কর্তৃত্ব ফলাতে হবে। মেয়েরা শেখে নতিস্বীকার করতে, অসমতাকে স্বাভাবিক ধরে নিতে। যদিও পরিবারভেদে পুরুষালি নিয়ন্ত্রণের বিস্তার ও প্রকৃতিতে তফাৎ পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু কোনো পরিবারেই এটি সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত থাকে না।
গের্ডা লার্নারের মতে, সমাজে শ্রেণিবিভাজন ব্যবস্থা সৃষ্টি ও সেগুলোকে সুসঙ্ঘবদ্ধ রাখতে পরিবার অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তিনি লিখেছেন, “পরিবার নিছকই রাষ্ট্রীয় বিন্যাসের প্রতিবিম্ব নয় এবং শিশুদেরকে সেই বিন্যাস অনুসরণ করতে শেখায় না। এটি নিজেও সেই বিন্যাসকে তৈরি করে, এবং ক্রমাগত সেটির শক্তিবৃদ্ধি করে।”
২. ধর্ম
অধিকাংশ আধুনিক ধর্মই পুরুষতান্ত্রিক, এবং তারা পুরুষের কর্তৃত্বকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে। তারা পুরুষতান্ত্রিক শ্রেণিবিন্যাসকে এমনভাবে উপস্থাপন করে যেন সেটি অতিপ্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত ধর্মের বিবর্তনের পূর্বে ক্ষমতার যে নারী-নীতি বিদ্যমান ছিল, ক্রমশ সেটি দুর্বল হয়ে পড়েছে। দেবীদের জায়গা দখল করেছে দেবতারা। সবগুলো প্রধান ধর্মেরই সৃষ্টি, ব্যাখ্যা ও নিয়ন্ত্রণ ঘটেছে উচ্চ শ্রেণি এবং উঁচু বর্ণের পুরুষদের হাত ধরে। তারাই নৈতিকতা, মূল্যবোধ, আচরণ এমনকি আইনকে সংজ্ঞায়িত করেছে; নারী-পুরুষের দায়িত্ব-কর্তব্য এবং অধিকার ভাগ করে দিয়েছে; নির্ধারণ করে দিয়েছে নারী-পুরুষের মধ্যকার সম্পর্কের স্বরূপ। তারা রাষ্ট্রীয় নীতিমালাকে প্রভাবিত করেছে, এবং এখনো অধিকাংশ সমাজেই সেই প্রভাব অক্ষুণ্ণ রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় তাদের ক্ষমতা ও উপস্থিতি অপরিসীম। উদাহরণস্বরূপ, ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হলেও, এখানে একজন ব্যক্তির বৈধ পরিচয় সংযুক্ত যেসব বিষয়ের সঙ্গে, যেমন বিয়ে, বিচ্ছেদ বা উত্তরাধিকার, সেগুলো নির্ধারিত হয় তার নিজস্ব ধর্মমতে।
বর্তমানে যথেষ্ট বিশ্লেষণ রয়েছে, যেগুলো থেকে দেখা যায় প্রায় সকল ধর্মই নারীদেরকে হীন, অপবিত্র ও পাপী হিসেবে বিবেচনা করে। প্রায় সকল ধর্মেই নারী-পুরুষের নৈতিকতা ও আচরণের দ্বৈত মানদণ্ড সৃষ্টি করা হয়েছে, এবং ধর্মীয় আইন প্রায় সময়ই ‘পথভ্রষ্ট’ নারীদের উপর সংঘটিত সহিংসতাকে বৈধতা দান করে। ধর্মীয় বিধান ও মৌলিক মতবাদই নারী-পুরুষদের বিষমকামী সম্পর্ককে অনুমোদন দেয়।
৩. আইনি ব্যবস্থা
অধিকাংশ দেশের আইনি ব্যবস্থাই পুরুষতান্ত্রিক ও বুর্জোয়া, অর্থাৎ সেগুলো পুরুষ ও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতাবান শ্রেণির পক্ষপাতিত্ব করে। পরিবার, বিয়ে ও উত্তরাধিকার বিষয়ক আইনগুলো খুব ঘনিষ্ঠভাবে সম্পদের উপর পুরুষতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে জড়িত। দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিটি আইনি ব্যবস্থাই পুরুষকে বিবেচনা করে পরিবারের প্রধান, শিশুদের প্রাকৃতিক অভিভাবক এবং সম্পদের প্রাথমিক উত্তরাধিকারী হিসেবে। আইনশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, বিচারপতি ও উকিলরা প্রায় সকলেই পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে, এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমেই বিদ্যমান আইনসমূহের ব্যাখ্যা করে।
৪. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ
পুরুষতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অধীনে, পুরুষরা অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে, অধিকাংশ সম্পদের মালিক হয়, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সরাসরি অংশ নেয়, এবং বিভিন্ন উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডের মূল্য নির্ধারণ করে। ফলে নারীদের করা অধিকাংশ উৎপাদনশীল কাজই স্বীকৃতি পায় না, এবং সেজন্য তারা পারিশ্রমিক থেকেও বঞ্চিত হয়। মারিয়া মাইস নারীদের কাজকে আখ্যায়িত করেছেন ‘ছায়াকর্ম’ (শ্যাডো ওয়ার্ক) হিসেবে, কেননা এসব কাজের ফলে সৃষ্ট উদ্বৃত্তকে সম্পূর্ণ নাকচ করে দেয়া হয়। নারীদের গৃহকর্মেরও কোনো মূল্যায়নই হয় না। তার উপর, সন্তানদের গর্ভে ধারণ, তাদেরকে জন্মদান ও তাদের লালন-পালনে নারীদের ভূমিকা ও শ্রম শক্তি কোনো অর্থনৈতিক অবদান হিসেবেও বিবেচিত হয় না।

৫. রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ
সমাজের সকল পর্যায়ে, হোক তা গ্রাম পঞ্চায়েত কিংবা জাতীয় সংসদ, সকল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানেই দেখা যায় পুরুষদের প্রাধান্য ও আধিপত্য। রাজনৈতিক দল কিংবা সংস্থাগুলোকে মুষ্টিমেয় নারীর উপস্থিতি দেখা যায়, যারা কোনো দেশের ভাগ্য নির্ধারণে অবদান রাখে। যখন নারীরা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পদে আসীন হয় (সিরিমাভো বন্দরনায়েকে, ইন্দিরা গান্ধী, বেনজীর ভুট্টো, খালেদা জিয়া), অন্তত প্রাথমিকভাবে তারা সেই পদাধিকার লাভ করে কোনো শক্তিশালী পুরুষ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ায়, এবং তারা পুরুষদের সৃষ্টি করা কাঠামো ও নীতিমালা অনুসরণ করেই কাজ করে। গোটা বিশ্বের মধ্যে এই অঞ্চল থেকেই সবচেয়ে বেশিসংখ্যক নারী রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া সত্ত্বেও, দক্ষিণ এশিয়ার সংসদে নারীদের উপস্থিতি কখনোই দশ শতাংশের উপরে ওঠেনি। (সাম্প্রতিক তথ্য ও উদাহরণ নয়)
৬. গণমাধ্যম
গণমাধ্যম হলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র, যেগুলো সমাজের উঁচু শ্রেণির, উঁচু বর্ণের পুরুষদের দখলে থাকে, এবং এর মাধ্যমে তারা শ্রেণি ও জেন্ডার বিষয়ক নিজস্ব মতবাদ প্রচার করে। চলচ্চিত্র, টেলিভিশন থেকে শুরু করে ম্যাগাজিন, সংবাদপত্র, রেডিও, সর্বত্রই নারীদের উপস্থাপন গৎবাঁধা ও বিকৃত। এসব জায়গায় পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব ও নারীদের হীনতার কথা বারবার বলা হয়; নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতার উপস্থিতিও অবাধ ও প্রচুর; বিশেষত চলচ্চিত্রে। অন্যান্য খাতের মতো, গণমাধ্যমেও নারীদের পেশাগত প্রতিনিধিত্ব খুব কম। তাছাড়া সংবাদের কাভারেজ, বিজ্ঞাপন এবং সামগ্রিক বার্তা এখনো অনেক বেশি সেক্সিস্ট (সেক্সের উপর ভিত্তি করে পক্ষপাতদুষ্টতা, বৈষম্য ও গৎবাঁধা দৃষ্টিভঙ্গি)।
৭. জ্ঞান ব্যবস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ
যখন থেকে শিক্ষা একটি প্রথাগত ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে, পুরুষরাই নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছে জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র তথা দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, আইন, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান ইত্যাদিকে। জ্ঞান সৃষ্টিতে পুরুষদের এরূপ আধিপত্য নারীদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে, তাদের দক্ষতা ও আকাঙ্ক্ষাকে, তাৎপর্যহীন ও অকিঞ্চিৎকর করে তুলেছে।
অনেক সংস্কৃতিতেই নারীদেরকে পদ্ধতিগতভাবে ধর্মগ্রন্থ পাঠের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হতো। এমনকি বর্তমান সময়েও, নারীদেরকে ধর্মীয় ও আইনি লিপির নিজস্ব ব্যাখ্যা সৃষ্টির সুযোগ খুব কমই দেয়া হয়। গের্ডা লার্নার বলেছেন:
“আমরা দেখেছি পুরুষরা কীভাবে নারী ক্ষমতার প্রধান প্রতীকগুলোকে প্রথমে নিজেরা ছিনিয়ে নিয়েছে, এবং পরবর্তীতে সেগুলোর রূপ পরিবর্তন করেছে। যেমন তারা রূপান্তর ঘটিয়েছে মাতৃ দেবী ও উর্বরতার দেবীর ক্ষমতাকে। আমরা দেখেছি পুরুষরা কীভাবে তাদের নিজেদের প্রজনন ক্ষমতার বিপরীতার্থক উপমার উপর ভিত্তি করে ধর্মতত্ত্ব সৃষ্টি করেছে, এবং সেখানে নারীদের অস্তিত্বকে নবরূপ দিয়েছে খুবই সংকীর্ণ ও যৌন-নির্ভরশীলভাবে। তাই শেষমেশ আমরা দেখেছি, কীভাবে জেন্ডার বিষয়ক উপমাগুলো পুরুষকে প্রচলিত রীতির ভেতর, এবং নারীকে প্রচলিত রীতির বাইরে হিসেবে চিত্রায়ণ করতে শুরু করেছে; পুরুষকে দেখিয়েছে পূর্ণাঙ্গ ও শক্তিশালী রূপে, এবং নারীকে দেখিয়েছে অসম্পূর্ণ, বিকলাঙ্গ ও পরাধীন রূপে। এ ধরনের প্রতীকী নির্মাণকে কাজে লাগিয়ে পুরুষরা বিশ্বকে তাদের নিজেদের মতো করে ব্যাখ্যা করেছে, এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর এমন উত্তর সাজিয়েছে যেন তারাই থাকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে।”
কয়েকজন নারীবাদীর মতে, পুরুষতান্ত্রিক চিন্তা ও জ্ঞানকে চিহ্নিত করা যায় বিভাজন, স্বাতন্ত্র্য, বিরোধিতা ও দ্বৈততার মাধ্যমে। তাদের মতে, পুরুষতন্ত্র বস্তুর চেয়ে মনকে, অন্যের চেয়ে নিজেকে, আবেগের চেয়ে যুক্তিকে, জিজ্ঞাস্যের চেয়ে জিজ্ঞাসাকারীকে বেশি গুরুত্ব দেয়। পুরুষতান্ত্রিক জ্ঞান ব্যবস্থায়ও দেখা যায় বিশেষীকরণের উপর গুরুত্বারোপ করতে, সামগ্রিক চিত্রের চেয়ে খণ্ডিত চিত্রকে বেশি প্রাধান্য দিতে।
পুরুষ নিয়ন্ত্রিত জ্ঞান ও শিক্ষা পুরুষতান্ত্রিক আদর্শকে সৃষ্টি করেছে এবং সেগুলোকে টিকিয়েও রাখছে। সিলভিয়া ওয়ালবির মতে, এই জ্ঞান ও শিক্ষা আরো তৈরি করেছে ‘মানসিকতার জেন্ডার-পৃথকীকৃত নানা রূপ’। পুরুষ ও নারীর আচরণ, চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষায় পার্থক্য দেখা যায় এ কারণে যে, তাদেরকে পুরুষালি ও মেয়েলি মানসিকতার পৃথক দীক্ষা দেয়া হয়েছে।
কোনো কোনো নারীবাদী কি বিশ্বাস করে না যে অনেক সমাজে নারীদের বিরুদ্ধে প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত সহিংসতা রয়েছে?
হ্যাঁ, তারা এটি বিশ্বাস করে, এবং তাদের মতে, নানা ধরনের সহিংসতাকে ব্যবহার করা হয় নারীদেরকে নিয়ন্ত্রিত ও আয়ত্তাধীন রাখতে। পুরুষ কর্তৃক এ ধরনের সহিংসতাকে অনেক ক্ষেত্রে বৈধ ও আইনসঙ্গতও মনে করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, নারীদের প্রতি সহিংসতা এতটাই বিস্তৃত যে, সিলভিয়া ওয়ালবি পুরুষালি সহিংসতাকে অভিহিত করেছেন একটি কাঠামো হিসেবে। তিনি লিখেছেন,
“আপাতদৃষ্টিতে ব্যক্তিবাদী ও বিচিত্র রূপ থাকা সত্ত্বেও, পুরুষালি সহিংসতা একধরনের কাঠামো তৈরি করে। এটি একধরনের আচরণে পরিণত হয়, যে আচরণ নারীদের সঙ্গে পুরুষরা নিয়মিতই করে থাকে। হাতেগোনা কিছু ব্যতিক্রম বাদে নারীদের প্রতি এ ধরনের সহিংস আচরণে রাষ্ট্রও হস্তক্ষেপ বা বাধা প্রদান করতে চায় না, যার ফলে পুরুষদের এই সহিংসতা পদ্ধতিগতভাবে ক্ষমাযোগ্য, বৈধ ব্যাপার হয়ে ওঠে।”
নারীদের প্রতি সহিংসতাই ছিল অন্যতম প্রথম ইস্যু, যেটি নিয়ে আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলনে আলোচনা ও বিশ্লেষণ শুরু হয়। নারীবাদী শিক্ষায় এই সহিংসতাকে নানা ধরনের তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হয়েছে। ওইসব তত্ত্বগুলোর সকলেই অন্তত একটি বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছে, সেটি হলো: এই সহিংসতা পদ্ধতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত।
মেরি ডেলি বলেন, পুরুষতন্ত্রের শাসকরা (ক্ষমতাবান পুরুষরা) স্বয়ং জীবনের বিরুদ্ধেই এক যুদ্ধ ঘোষণা করে।
“পুরুষতন্ত্রের রাষ্ট্র হলো যুদ্ধের রাষ্ট্র, যেখানে যুদ্ধ থেকে পরিত্রাণের এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির সময়গুলোকে ‘শান্তি’ নামক শ্রুতিমধুর অভিধা প্রদান করা হয়।”
ডেলির মতে, ভারতের সতীদাহ প্রথা, চীনের পদবন্ধন প্রথা, আফ্রিকার কমবয়সি মেয়েদের যৌনাঙ্গচ্ছেদ, ‘রেনেসাঁ’ যুগের ইউরোপে ডাইনি নিধন, আমেরিকান গাইনোকলজি ও সাইকোথেরাপির অন্তরালে গাইনোসাইড (নারী হত্যা) ইত্যাদি সবই হলো নারীর প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ ও সহিংসতার দৃষ্টান্ত, যা বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতিতে প্রচলিত রয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ায় নারীদের প্রতি সহিংসতা নিয়ে ব্যাপকভাবে লেখালেখি হয়েছে, আলোচনা হয়েছে, এবং চেষ্টা চালানো হয়েছে সহিংসতা এবং নারীদেরকে অর্থনৈতিকভাবে নিপীড়ন, সহিংসতা এবং যৌনতা, সহিংসতা এবং বর্ণ ও শ্রেণি প্রভৃতির মধ্যকার সম্পর্ক খোঁজার। ১৯৮৮ সালে ভারতে একটি স্বায়ত্তশাসিত নারী সংস্থার (নারী মুক্তি সংঘর্ষ সম্মেলন) সভা আয়োজিত হয়, যেখানে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তগুলো পাশ হয়:
“নারীরা নির্দিষ্ট ধরনের সহিংসতার সম্মুখীন হয়: ধর্ষণ এবং অন্যান্য ধরনের শারীরিক নিপীড়ন, কন্যাভ্রূণ হত্যা, ডাইনি নিধন, সতীদাহ, যৌতুকের জন্য খুন, স্ত্রী প্রহার। এ ধরনের সহিংসতা এবং নারীদের মাঝে জন্মানো অবিরাম অনিশ্চয়তার বোধ তাদেরকে ঘরে চার দেয়ালের মাঝে বন্দি করে থাকে, অর্থনৈতিকভাবে শোষণ করে এবং সামাজিকভাবে অবদমিত রাখে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীদের সহিংসতার সঙ্গে এই চলমান সংগ্রামে, আমরা রাষ্ট্রকে দিতে চাই অন্যতম উৎসের স্বীকৃতি। রাষ্ট্র থেকেই এসব সহিংসতার উৎপত্তি ঘটে এবং তারা পরিবারে, কর্মস্থলে, এলাকায় পুরুষ কর্তৃক নারীর উপর সহিংসতার পেছনে থাকে। এসব কারণে একটি গণ নারী আন্দোলনের উচিত ঘরে-বাইরে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দিকে ফোকাস করা।”
আমরা কি এ কথা বলতে পারি যে সব ধরনের প্রতিষ্ঠানে পুরুষের নিয়ন্ত্রণ পুরুষদেরকে সরাসরি উপকৃত করে?
সাধারণভাবে বলতে গেলে, আমরা পারি। পুরুষরা কেবলই বৃহত্তর সুবিধা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে উপকৃত হয় না, বরং তারা অর্থনৈতিকভাবে ও বস্তুগতভাবেও উপকৃত হয়। যেমনটি আগেই বলেছি, পুরুষতন্ত্রের রয়েছে বস্তুগত ভিত্তি। সিলভিয়া ওয়ালবিও এটিই বোঝাতে চান, যখন তিনি বলেন যে নারীরা উৎপাদক শ্রেণি এবং পুরুষরা দখলদার শ্রেণি। হাইডি হার্টম্যান নামের একজন নারীবাদী স্কলার পুরুষতন্ত্রের সঙ্গে পুঁজিবাদের গভীর যোগসূত্র খুঁজে পান। তিনি বলেন,
“যে মূলগত ভিত্তির উপর পুরুষতন্ত্র প্রধানভাবে নির্ভর করে সেটি হলো নারীদের শ্রম শক্তির উপর পুরুষদের নিয়ন্ত্রণ। পুরুষরা এই নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখে নারীদেরকে কিছু প্রয়োজনীয় উৎপাদনশীল সংস্থান (পুঁজিবাদী সমাজে যা হতে পারে এমন কোনো চাকরি যেখানে জীবনধারণের জন্য উপযুক্ত বেতন দেয়া হয়) থেকে দূরে সরিয়ে রেখে, এবং নারীদের যৌনতাকে সীমাবদ্ধ রেখে। একগামী বিষমকামী বিয়ে হলো তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক ও কার্যকর ধারা, যা পুরুষকে এই দুই ক্ষেত্রকেই নিয়ন্ত্রণের সুযোগ করে দেয়। নারীদের সংস্থান ও যৌনতার রাশ ধরে রাখার মাধ্যমে, পুরুষরা নারীদের শ্রম শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, এবং নারীদেরকে বাধ্য করতে পারে পুরুষদেরকে ব্যক্তিগত ও যৌন পরিষেবা প্রদান করতে, এবং সন্তান প্রতিপালন করতে। নারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত পরিষেবার বদৌলতে পুরুষরা দৈনন্দিন অনেক অপ্রীতিকর বা নিরানন্দ কাজই নিজ হাতে করার কষ্ট থেকে বেঁচে যায়; এবং এগুলো পারিবারিক কাঠামোর ভেতরে-বাইরে দুই জায়গাতেই হয়ে থাকে। এজন্যই, পুরুষতন্ত্রের বস্তুগত ভিত্তি কেবল সন্তান প্রতিপালনেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সব ধরনের সামাজিক কাঠামোতেই বিদ্যমান, যা পুরুষদেরকে সুযোগ করে দেয় নারীদের শ্রম শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে।”
পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নারীরা কি সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতাহীন?
সাধারণভাবে, একটি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতাই থাকে পুরুষদের হাতে। তবে এর মানে এই নয় যে পুরুষতন্ত্রের অধীনে নারীরা একদমই ক্ষমতাহীন, অথবা তাদের কোনো অধিকার, প্রভাব বা সংস্থান নেই। বস্তুত, কোনো অসম ব্যবস্থাই পুরোপুরি শোষিতের অংশগ্রহণ ছাড়া অব্যাহত থাকতে পারে না। আর তাই শোষিতরাও এই ব্যবস্থা থেকে কিছু কিছু সুবিধা ঠিকই লাভ করে। একই কথা পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও সত্য। অনেক নারীও ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেছে রানী কিংবা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার মাধ্যমে। তারা মাঝেমধ্যে ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, ছোট-বড় নানা ধরনের ফায়দাও লুটেছে। কিন্তু তাতে এই ব্যাপারটি মিথ্যে হয়ে যায় না যে এই ব্যবস্থাটি চলছে পুরুষদের কর্তৃত্বে- নারীদেরকে নিছকই অল্প কিছু জায়গা দেয়া হয়েছে। একটি সমান্তরাল উদাহরণ হিসেবে বলা যায় পুঁজিবাদী সমাজের কথা, যেখানে শ্রমিকরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তারা মাঝেমধ্যে ব্যবস্থাপনা পর্যায়েও অংশগ্রহণ করে। কিন্তু তার মানে এই না যে ওই শ্রমিকদের হাতেই ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।
এ ব্যাপারে গের্ডা লার্নার বলেছেন :
“পুরুষরা ও নারীরা বাস করে একটি মঞ্চের উপর, যেখানে তারা নিজেদের জন্য নির্ধারিত ভূমিকায় অভিনয় করে চলে, এবং উভয় ভূমিকাই সমান গুরুত্বপূর্ণ। দুই শ্রেণির পারফরমার ছাড়া নাটকটি চলতে পারে না। ওই দুই শ্রেণির কেউই সামগ্রিকভাবে কারো চেয়ে বেশি ‘অবদান’ রাখে না। কেউই তুচ্ছ বা অদরকারী নয়। কিন্তু মঞ্চটিকে তৈরি করেছে, রঙ করেছে, সাজিয়েছে পুরুষরা। নাটকটি রচনাও করেছে পুরুষরা। পরিচালনাও করছে পুরুষরা। প্রতিটি ঘটনার অর্থ ব্যাখ্যাও করছে পুরুষরা। এই পুরুষরাই নিজেদেরকে দিয়েছে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক, বীরত্বপূর্ণ চরিত্রগুলো, এবং নারীদেরকে রেখে দিয়েছে পার্শ্বচরিত্রের ভূমিকায়।”
অন্যভাবে বলতে গেলে, এটি সমস্যা নয় যে নারীরা কে বা তারা কী করে। সমস্যাটি হলো এই যে নারীরা কীভাবে মূল্যায়িত হয়, এবং সেই মূল্যায়নের অধিকার রয়েছে কাদের কাছে। এমনটি নয় যে পুরুষতন্ত্রের ফলে নারীরা পূর্ণাঙ্গভাবে ক্ষমতা বা সম্মান হতে বাদ পড়েছে – সমস্যা কাঠামোতে, এবং সেই কাঠামো নির্ধারণ করেছে পুরুষরা।
কিন্তু নারীরাও তো পুরুষদের শাসনকে সমর্থন করে। তাদের সহযোগিতা ছাড়া পুরুষতন্ত্র টিকে থাকতে পারত না। তাহলে নারীরা কেন পুরুষতন্ত্রকে সমর্থন করে?
এর পেছনে বেশ কিছু জটিল কারণ রয়েছে, যার মধ্যে কয়েকটি আমাদের পরিচিত। উদাহরণস্বরূপ, আমরা জানি যে স্থানীয় সৈন্য, পুলিশ, সরকারি কর্মচারী ছাড়া, মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্রিটিশ শাসকের পক্ষে বিশাল বিশাল দেশ বা মহাদেশ শাসন করা সম্ভব ছিল না। দাসদের নীরব সহযোগিতা ছাড়া দাস ব্যবস্থা এত লম্বা সময় ধরে চলত না। একই কথা প্রযোজ্য নারীদের ক্ষেত্রেও। তারাও এই ব্যবস্থার অংশ, তারাও এই ব্যবস্থার মূল্যবোধকে নিজেদের অন্তঃকরণে ঠাঁই দিয়েছে, এবং তারাও পুরুষতান্ত্রিক আদর্শ থেকে মুক্ত নয়। এবং যেমনটি আমরা আগেই বলেছি, নিঃসন্দেহে নারীদের মধ্যে কেউ কেউ এই ব্যবস্থা থেকে সুবিধাও লাভ করে। বেশ কিছু জটিল সম্পর্কের দরুণ নারীরা পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি তাদের সহযোগিতা বা অংশগ্রহণকে সক্রিয় রাখে।

গের্ডা লার্নারের মতে,
“এই সহযোগিতাকে নিশ্চিত করা হয়েছে বেশ কিছু বিষয়ের মাধ্যমে: জেন্ডার দীক্ষা; পর্যাপ্ত শিক্ষার অভাব; নারীদের নিজেদের ইতিহাসকে অস্বীকৃতি; নারীদের মাঝে বিভাজন, যৌন কর্মকাণ্ডের উপর ভিত্তি করে কাউকে ‘সম্মানিত’ আর কাউকে ‘পথভ্রষ্ট’ আখ্যা প্রদানের মাধ্যমে; নারীদের সংযম কিংবা সরাসরি জোরজবরদস্তি; অর্থনৈতিক সংস্থান ও রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের ক্ষেত্রে বৈষম্য; এবং কাউকে কাউকে শ্রেণি সুবিধা প্রদান করে, যার ফলে নারীদের পুরুষতন্ত্রকে আখ্যায়িত করা যায় পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্য হিসেবে।
“যতক্ষণ পর্যন্ত নারীরা পুরুষদের ‘নিরাপত্তা’র অধীনে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারাও পুরুষদের শ্রেণি সুবিধা সমানভাবে ভোগ করে। নারীদের জন্য (নিচু বর্ণের নারী ব্যতীত) পুরুষদের সঙ্গে ‘পারস্পরিক চুক্তি’র ব্যাপারটি এমন যে : নারীরা পুরুষদের নিকট তাদের যৌন, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অধীনস্থতা স্বীকার করবে, বিনিময়ে তারা পুরুষদের কাছ থেকে পাবে সেই শ্রেণি ক্ষমতা, যাকে কাজে লাগিয়ে তারা তাদের শ্রেণি অপেক্ষা নিচু শ্রেণির নারী-পুরুষ উভয়কে শোষণ ও নিপীড়ন করতে পারবে।”
নিজেদের সুবিধাপ্রাপ্তির উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য, নারীরা ক্রমাগত তাদের দর-কষাকষি ক্ষমতার সঙ্গে রফা করতে থাকে, এবং অনেকক্ষেত্রে তা করে থাকে অন্য নারীদের ক্ষতিসাধনের মাধ্যমে। তবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো সামগ্রিক ব্যবস্থার দিকে তাকে এর পেছনের কারণগুলোকে বিশ্লেষণ করা। এ কথা সত্য যে নারীরা অনেক সময়ই পুত্রসন্তানের প্রতি অধিক যত্ন নেয়, কন্যাসন্তানদের শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে, তাদের স্বাধীনতা হরণ করে, ছেলের বউদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে, এবং আরো কত কী! এই সব বিষয়কেই বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন পরিবার ও সমাজে পুরুষদের ও নারীদের ক্ষমতা ও অবস্থানের প্রেক্ষাপট বিচারের মাধ্যমে। একজন গ্রামীণ নারী বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছিলেন এভাবে,
“আমাদের পরিবারে পুরুষরা হলো সূর্যের মতো, তাদের নিজস্ব আলো আছে (নিজস্ব সংস্থান, উপার্জন, গতিশীলতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা ইত্যাদি)। কিন্তু নারীরা হলো উপগ্রহের মতো, তাদের নিজস্ব কোনো আলো নেই। তারা কেবল তখনই আলোকিত হয়, যখন সূর্যের আলো তাদেরকে স্পর্শ করে। তাই নারীদের সবসময়ই নিজেদের মধ্যে লড়াই চালিয়ে যেতে হয় যেন তারা সূর্যের আলোর বড় ভাগটা পায়। কেননা এই আলো ছাড়া যে তাদের জীবন বলতে কিছু নেই।”
সব পুরুষই কি পুরুষতন্ত্র থেকে সুবিধা ভোগ করে?
উত্তরটি হ্যাঁ এবং না। হ্যাঁ এ কারণে যে, পুরুষরা চাক বা না-চাক, তারা পুরুষ হিসেবে কিছু নির্দিষ্ট সুবিধা ঠিকই লাভ করে। এমনকি শ্রমিক শ্রেণির পুরুষরা, যারা বুর্জোয়া পুরুষদের বিপরীতে ক্ষমতাহীন, তারাও তাদের নিজেদের শ্রেণির নারীদের উপর ক্ষমতা জাহির করতে পারে। দক্ষিণ এশিয়ায়, সকল পুরুষেরই রয়েছে অপেক্ষাকৃত অধিক গতিশীলতা, সংস্থান। এমনকি পুরুষ হিসেবে তারা খাদ্য ও স্বাস্থ্যের মতো প্রাথমিক বিষয়গুলোতেও বেশি সুযোগ পেয়ে থাকে। অন্যভাবে বলতে গেলে, যেমনটি আগেও বলেছি, সামাজিক, ধর্মীয়, আইনি ও সাংস্কৃতিক চর্চাসমূহ পুরুষ হিসেবে তাদেরকে কিছু বাড়তি সুবিধা দেয়। এবং সেই সঙ্গে, ব্যবহারিকভাবে তারা সকল ক্ষেত্রেই বেশি অধিকার লাভ করে থাকে।
কিন্তু আরেকভাবে চিন্তা করলে, পুরুষতন্ত্রের কারণে পুরুষরাও অনেক ক্ষেত্রে সুবিধাবঞ্চিত। নারীদের মতো তাদেরকেও কিছু গৎবাঁধা ধারণার দিকে ঠেলে দেয়া হয়। তাদের উপর কিছু নির্দিষ্ট ভূমিকা চাপিয়ে দেয়া হয়। তাদেরকে স্বেচ্ছায়ই হোক বা অনিচ্ছায়, নির্দিষ্ট ভঙ্গিতে আচরণ করতে হয়। তাদের উপরও দায় রয়েছে সামাজিক বিধিনিষেধ মেনে চলার, এবং সেসব বিধিনিষেধের ফলে তারা অনেক কিছুই করতে বাধ্য হয়। যেসব পুরুষ নরম স্বভাবের এবং আগ্রাসী নয়, তাদেরকে নানাভাবে হেনস্থা ও উপহাসের শিকার হতে হয়। যারা তাদের স্ত্রীদেরকে সমান চোখে দেখে, তাদেরকে বলা হয় ‘স্ত্রৈণ’। আমি এমন একজন পুরুষকে চিনি, যাকে সারাজীবন অপমানিত হতে হয়েছে শুধু এই কারণে যে, সে কত্থক নৃত্যশিল্পী হওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল, এবং সে সেলাই বা এ ধরনের মেয়েলি কাজ করতে ভালোবাসত, যেগুলো ‘প্রকৃত’ পুরুষদের সঙ্গে যায় না।
পুরুষদেরকেও তাদের সত্যিকারের পছন্দ-অপছন্দ থেকে বঞ্চিত করা হয়। তাদের সামনেও সুযোগ নেই মূলধারা থেকে বেরিয়ে আসার, অর্থ ও নিরাপত্তা দাতার ভূমিকা ছেড়ে দেয়ার। যখনই কোনো তরুণ বা শিক্ষিত পুরুষ বলে যে সে বাইরে কাজ করতে যায় না, ঘরে থেকে সংসার সামলায়, তখনই সবাই তার দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকায়, ভ্রুকুটি করে। তাকে বলা হয়, “এসব কাজ তো নারীদের জন্য, পুরুষদের জন্য নয়।”
তবে এসব বিমানবিকীকরণকে (ডিহিউম্যানাইজেশন) কোনোভাবেই নারীদের পরাধীনতার সঙ্গে তুলনা বা একই সমতুল্য মনে করা যায় না। এর পেছনে প্রধান দুটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, সমগ্র পুরুষজাতিকেই এসব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয় না; এবং দ্বিতীয়ত, তাদেরকে ব্যাপকভাবে বৈষম্য বা পঙ্গুত্বের শিকার হতে হয় না।