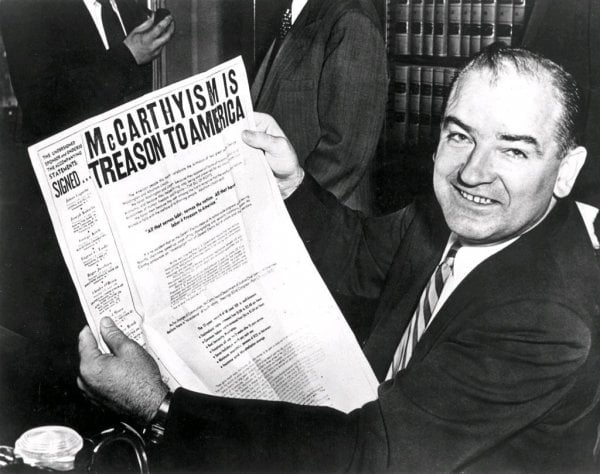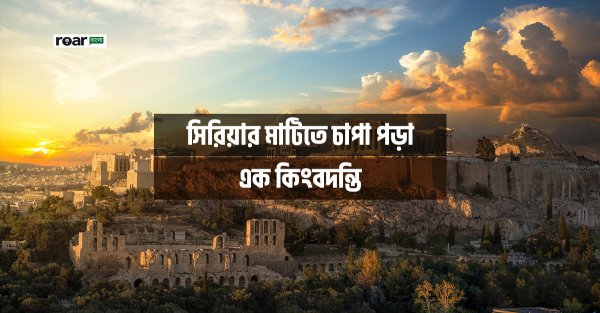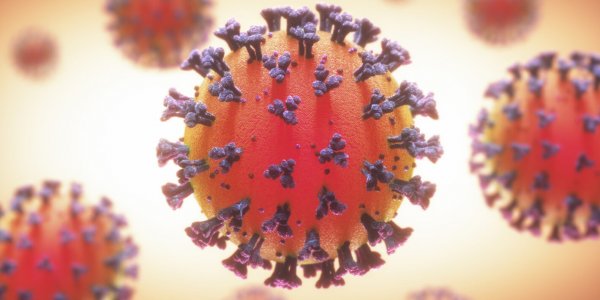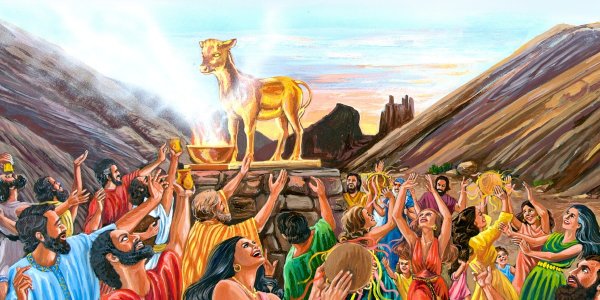প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মিত্রশক্তির সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ছয়টি রাষ্ট্রকে ‘মুখ্য মিত্রশক্তি’ (Principal Allied Powers) হিসেবে অভিহিত করা হতো। এই রাষ্ট্রগুলো ছিল ব্রিটেন, রাশিয়া, ফ্রান্স, জাপান, ইতালি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মহাযুদ্ধে ব্রিটেনের অংশগ্রহণ সম্পর্কে বিগত পর্বে আলোচনা করা হয়েছে। রাশিয়া, ফ্রান্স এবং জাপানের উক্ত মহাযুদ্ধে অংশগ্রহণ এই পর্বের আলোচ্য বিষয়বস্তু।
রাশিয়া
‘রুশ সাম্রাজ্য’ (রুশ: Российская Империя, ‘রোসিস্কায়া ইম্পেরিয়া’) ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মিত্রশক্তির অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। সেসময় ব্রিটেনের পর রাশিয়া ছিল বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র এবং ‘ইউরোপের স্টিমরোলার’ নামে পরিচিত রুশ সেনাবাহিনী ছিল বিশ্বের বৃহত্তম সেনাবাহিনী। অবশ্য পশ্চিম ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যগুলোর মতো রুশ সাম্রাজ্য বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত ছিল না এবং একমাত্র রুশ মধ্য এশিয়া ব্যতীত রুশ রাষ্ট্রের অন্য কোনো অংশকে ঠিক ‘উপনিবেশ’ হিসেবে চিহ্নিত করা যেত না। উল্লেখ্য, রুশ মধ্য এশিয়া ব্রিটিশ ভারতের মতো দুই ভাগে বিভক্ত ছিল– সরাসরি রুশ শাসনাধীন অঞ্চল এবং রুশ আশ্রিত রাষ্ট্র বুখারা ও খোরেজম। কিন্তু পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো যেরকম ব্যাপকভাবে উপনিবেশগুলো থেকে আগত লক্ষ লক্ষ সৈন্যকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহার করেছিল, রুশরা সেরকম কিছু করেনি। উল্টো রাশিয়া মধ্য এশীয়দের সেনাবাহিনীতে যোগদানের বাধ্যবাধকতা থেকে ছাড় প্রদান করেছিল।
বলকান অঞ্চলে বিদ্যমান রুশ প্রভাব বজায় রাখা ও এতদঞ্চলে রুশ সাম্রাজ্যের পরিধি সম্প্রসারিত করার আকাঙ্ক্ষা এবং বলকান ও পশ্চিম এশিয়ায় জার্মানি ও অস্ট্রিয়া–হাঙ্গেরির সঙ্গে রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক, সামরিক ও ভূকৌশলগত প্রতিযোগিতা ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার অংশগ্রহণের প্রধান কারণ। অবশ্য এগুলো এই মহাযুদ্ধে রাশিয়ার অংশগ্রহণের একমাত্র কারণ ছিল না এবং এর পশ্চাতে আরো নানাবিধ কারণ দায়ী ছিল, কিন্তু উল্লিখিত কারণগুলোই ছিল প্রণিধানযোগ্য। উল্লেখ্য, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী বছরগুলোতে রাশিয়া ‘রুশ–ফরাসি মৈত্রী’ (১৮৯৪) এবং ‘ইঙ্গ–রুশ কনভেনশন’ (১৯০৭) সম্পাদনের মধ্য দিয়ে যথাক্রমে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সঙ্গে মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। তদুপরি, বলকান অঞ্চলের দক্ষিণ স্লাভিক রাষ্ট্র সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রোর সঙ্গে রাশিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল।

রাশিয়ার প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রবেশের আনুষ্ঠানিক কারণ ছিল সার্বিয়ার বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়া–হাঙ্গেরির আগ্রাসন এবং এই আগ্রাসনে জার্মানির সমর্থন প্রদান। রাশিয়া ও সার্বিয়ার মধ্যে কোনো আনুষ্ঠানিক মৈত্রীচুক্তি সম্পাদিত হয়নি, কিন্তু সার্বদের সঙ্গে রুশদের জাতিগত, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও আদর্শিক সাদৃশ্য এবং নিজস্ব ভূরাজনৈতিক স্বার্থের কারণে সার্বিয়ার নিরাপত্তা নিশ্চিত করাকে রাশিয়া নিজেদের দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করত। এজন্য ১৯১৪ সালের ২৮ জুলাই অস্ট্রিয়া–হাঙ্গেরি সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার পর অস্ট্রিয়া–হাঙ্গেরিকে সার্বিয়া আক্রমণ থেকে বিরত রাখার জন্য চাপ প্রদানের উদ্দেশ্যে রাশিয়া অস্ট্রিয়া–হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে আংশিক সৈন্য সমাবেশের ঘোষণা প্রদান করে। অস্ট্রিয়া–হাঙ্গেরির মিত্ররাষ্ট্র জার্মানি রাশিয়ার সৈন্য সমাবেশ বন্ধ করার দাবি জানিয়ে রাশিয়াকে একটি চরমপত্র প্রদান করে। রাশিয়া এই চরমপত্র উপেক্ষা করলে ১ আগস্ট জার্মানি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।
৬ আগস্ট অস্ট্রিয়া–হাঙ্গেরি জার্মানির পদাঙ্ক অনুসরণ করে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ২৯ অক্টোবর জার্মানির মিত্ররাষ্ট্র ওসমানীয় রাষ্ট্রের নৌবাহিনী কৃষ্ণসাগরের তীরে অবস্থিত রাশিয়ার ওদেসা, সেভাস্তোপোল, ফেয়োদোসিয়া, ইয়ালতা ও নভোরোসিয়স্ক বন্দরের ওপর বোমাবর্ষণ করে এবং প্রত্যুত্তরে ১ নভেম্বর রাশিয়া ওসমানীয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯১৫ সালের অক্টোবরে বুলগেরিয়া কেন্দ্রীয় শক্তিতে যোগদান করে এবং রাশিয়ার মিত্র সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, ফলে ১৯ অক্টোবর রাশিয়া বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই মহাযুদ্ধ চলাকালে রাশিয়া প্রধানত ইউরোপের পূর্ব রণাঙ্গন (Eastern Front) ও পশ্চিম এশিয়ায় কেন্দ্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। অবশ্য ইউরোপের পশ্চিম রণাঙ্গন, বলকান, এমনকি সুদূর দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়াতেও রুশরা কেন্দ্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে সামরিক কার্যক্রম পরিচালনা করে।
কিন্তু যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি রাশিয়ার অনুকূলে ছিল না। পশ্চিম এশিয়ায় ওসমানীয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এবং পূর্ব রণাঙ্গনে অস্ট্রিয়া–হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে রুশরা ব্যাপক সাফল্য অর্জন করে, কিন্তু জার্মানদের কাছে তারা বারবার পরাজিত হয়। ১৯১৫ সাল নাগাদ রুশ পোল্যান্ড ও রাশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলের অংশবিশেষ কেন্দ্রীয় শক্তির দখলে চলে যায় এবং যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে রুশ সরকারের অকর্মণ্যতা, যুদ্ধের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি, অর্থনৈতিক সঙ্কট, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও কেন্দ্রীয় শক্তির গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কার্যক্রমের ফলে রাশিয়ায় ব্যাপক রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি হয়। ১৯১৭ সালের মার্চে সেইন্ট পিটার্সবার্গে সংঘটিত একটি বিপ্লবের ফলে রাশিয়ার ক্ষমতাসীন রোমানভ রাজবংশের পতন ঘটে এবং একটি অস্থায়ী সরকার রাশিয়ার শাসনভার গ্রহণ করে। নতুন সরকার যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয়, কিন্তু রাশিয়ায় বিরাজমান অরাজকতা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে তারা ব্যর্থ হয় এবং এই সুযোগে কেন্দ্রীয় শক্তি রাশিয়ার বাল্টিক অঞ্চলের বৃহদাংশ দখল করে নিয়ে রাজধানী সেইন্ট পিটার্সবার্গের কাছাকাছি উপস্থিত হয়।

নভেম্বরে বলশেভিকরা একটি বিপ্লব/অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাশিয়ার শাসন ক্ষমতা দখল করে। তারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে রাশিয়াকে প্রত্যাহার করে নেয়ার ঘোষণা দেয়, এবং ১৯১৮ সালের জানুয়ারিতে বলশেভিকদের ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে মিত্রশক্তি রাশিয়ার ওপর আক্রমণ চালায়। এদিকে বলশেভিকরা শান্তি স্থাপনের বিনিময়ে কেন্দ্রীয় শক্তি রাশিয়ার ওপর যে কঠোর শর্তাবলি আরোপ করেছিল সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে, ফলে ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে কেন্দ্রীয় শক্তি পুনরায় আক্রমণাভিযান শুরু করে। বলশেভিকরা তাদের বিপ্লবী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে রুশ সশস্ত্রবাহিনীকে বিলুপ্ত করে দিয়েছিল, সুতরাং তারা বাধ্য হয়ে ৩ মার্চ কেন্দ্রীয় শক্তির সঙ্গে ‘ব্রেস্ত–লিতোভস্ক চুক্তি’তে স্বাক্ষর করে। এই চুক্তি অনুসারে বলশেভিকরা রুশ পোল্যান্ড, বাল্টিক অঞ্চল, ফিনল্যান্ড, বেলারুশ, ইউক্রেন, কার্স, বাতুম ও আরদাহান কেন্দ্রীয় শক্তির কাছে হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়।
অর্থাৎ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মিত্রশক্তির সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে রাশিয়া ছিল চূড়ান্তভাবে পরাজিত একমাত্র রাষ্ট্র। এই মহাযুদ্ধে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ রুশ সৈন্য কেন্দ্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে ২২,৫৪,৩৬৯ জন নিহত এবং প্রায় ৩৭,৪৯,০০০ জন আহত হয়। অবশ্য ১৯১৮ সালের মার্চে রাশিয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে নিজেকে চূড়ান্তভাবে প্রত্যাহার করে নিলেও রাশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। রাশিয়া জুড়ে এক রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায় এবং ১৯২৫ সাল পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মিত্রশক্তির এক বা একাধিক সদস্য রাষ্ট্র রাশিয়ার ভূখণ্ডে দখলদারিত্ব বজায় রাখে।
ফ্রান্স
‘ফরাসি প্রজাতন্ত্র’ (ফরাসি: République française) ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মিত্রশক্তির অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। সেসময় ব্রিটেন ও রাশিয়ার পর ফ্রান্স ছিল বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র এবং তাদের ছিল বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী সেনাবাহিনী ও বিশ্বের বৃহত্তম বিমানবাহিনী। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকা জুড়ে ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্সের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সের উপনিবেশগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়ে। মহাযুদ্ধ চলাকালে ফ্রান্স তার উপনিবেশগুলোর সম্পদকে পূর্ণ মাত্রায় কাজে লাগায় এবং ফ্রান্সের উপনিবেশগুলো থেকে আগত লক্ষ লক্ষ সৈন্য কেন্দ্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

বিশ্বব্যাপী বিদ্যমান ফরাসি ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখা ও সাম্রাজ্যটির পরিধি সম্প্রসারণ করার আকাঙ্ক্ষা এবং জার্মানির সঙ্গে ফ্রান্সের তীব্র রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও ঔপনিবেশিক প্রতিযোগিতা ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্সের অংশগ্রহণের প্রধান কারণ। এই যুদ্ধে ফ্রান্সের অংশগ্রহণের পশ্চাতে এগুলোর বাইরেও নানাবিধ কারণ ছিল, কিন্তু এই কারণগুলোই ছিল প্রণিধানযোগ্য। উল্লেখ্য, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী বছরগুলোতে ফ্রান্স ‘রুশ–ফরাসি মৈত্রী’ (১৮৯৪) এবং ‘ইঙ্গ–ফরাসি আঁতাত’ (১৯০৪) সম্পাদনের মধ্য দিয়ে যথাক্রমে রাশিয়া ও ব্রিটেনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল।
ফ্রান্সের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রবেশের আনুষ্ঠানিক কারণ ছিল রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানির ‘আগ্রাসন’। ফ্রান্স ও রাশিয়া ছিল আনুষ্ঠানিকভাবে একে অপরের সামরিক মিত্র এবং তাদের এই মৈত্রীর মূল লক্ষ্যবস্তু ছিল জার্মানি। জনসম্পদ এবং অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির দিক থেকে ফ্রান্স ক্রমশ জার্মানির চেয়ে পিছিয়ে পড়ছিল, এবং এজন্য রাশিয়ার সঙ্গে তাদের মৈত্রীকে ফ্রান্স সম্ভাব্য জার্মান আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজেদের রক্ষাকবচ হিসেবে বিবেচনা করত। ১৯১৪ সালের ১ আগস্ট জার্মানি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফ্রান্সের আশঙ্কা ছিল, জার্মানি ও অস্ট্রিয়া–হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে রাশিয়াকে একাকী ছেড়ে দিলে জার্মানিক রাষ্ট্র দুইটি যদি রাশিয়াকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়, সেক্ষেত্রে সম্ভাব্য ফরাসি–জার্মান যুদ্ধে ফ্রান্সকে কার্যকরভাবে সহায়তা করার মতো কোনো মিত্র অবশিষ্ট থাকবে না। এজন্য রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানির যুদ্ধ ঘোষণার প্রত্যুত্তরে ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশের ঘোষণা প্রদান করে। এর ফলে ৩ আগস্ট জার্মানি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।
১২ আগস্ট ফ্রান্স জার্মানির মিত্র অস্ট্রিয়া–হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, এবং অক্টোবরে ওসমানীয় নৌবাহিনী রাশিয়ার কৃষ্ণসাগরীয় বন্দরগুলোতে আক্রমণ চালালে ৫ নভেম্বর ফ্রান্স ওসমানীয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। সর্বশেষ ১৯১৫ সালের অক্টোবরে বুলগেরিয়ার কেন্দ্রীয় শক্তিতে যোগদানের পর ১৬ অক্টোবর ফ্রান্স বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই মহাযুদ্ধ চলাকালে ফ্রান্স প্রধানত ইউরোপের পশ্চিম রণাঙ্গন, বলকান, পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকায় কেন্দ্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। অবশ্য ইউরোপের পূর্ব রণাঙ্গন থেকে শুরু করে দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলেও তারা কেন্দ্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত সামরিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে।

যুদ্ধের প্রথম পর্যায়েই জার্মানি ফ্রান্সের একাংশ দখল করে নেয়, কিন্তু এরপর তাদের অগ্রযাত্রা থেমে যায় এবং পশ্চিম রণাঙ্গনের যুদ্ধ কার্যত স্থবির পরিখার যুদ্ধে পরিণত হয়। পরবর্তী বছরগুলোতে ব্রিটেন ও অন্যান্য মিত্ররাষ্ট্রের সহায়তায় ফ্রান্স জার্মানির অগ্রযাত্রা রুখে দিতে সমর্থ হয়। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর ১৯১৮ সালের জানুয়ারিতে মিত্রশক্তি রাশিয়ায় আক্রমণ চালায় এবং ফ্রান্স এই আক্রমণে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে, কিন্তু এই আক্রমণ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এদিকে প্রায় সাড়ে চার বছরব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর নাগাদ জার্মানি ও কেন্দ্রীয় শক্তির অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্র মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং এর মধ্য দিয়ে এই মহাযুদ্ধের অবসান ঘটে।
ফ্রান্স ও ফ্রান্সের উপনিবেশগুলো থেকে আগত প্রায় ৮৬,৬০,০০০ সৈন্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে ১৩,৯৭,৮০০ জন নিহত এবং প্রায় ৪২,৬৬,০০০ জন আহত হয়। উল্লেখ্য, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে ফ্রান্স জার্মানির কাছ থেকে আলসেস–লোরেন, টোগোল্যান্ড ও জার্মান ক্যামেরুন এবং ওসমানীয় রাষ্ট্রের কাছ থেকে সিরিয়া ও লেবানন লাভ করে। এর ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য তাদের সম্প্রসারণের শিখরে পৌঁছে যায়।
জাপান
‘জাপান সাম্রাজ্য’ (জাপানি: 大日本帝國, ‘দাই নিপ্পন তেইকোকু’) ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মিত্রশক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ সদস্য রাষ্ট্র। জাপানকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ছয়টি ‘মুখ্য মিত্রশক্তি’র মধ্যে একটি হিসেবে বিবেচনা করা হয়, কিন্তু কার্যত অন্য পাঁচটি মুখ্য মিত্রশক্তির তুলনায় এই মহাযুদ্ধে জাপানের অংশগ্রহণ ছিল খুবই সীমিত মাত্রার। সেসময় জাপান ছিল একটি উদীয়মান শক্তি এবং রুশ–জাপানি যুদ্ধে রাশিয়াকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করার মধ্য দিয়ে তারা নিজেদেরকে একটি শীর্ষ স্থল ও নৌশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এসময় কোরীয় উপদ্বীপ ও তাইওয়ান এবং চীনা ভূখণ্ডে অবস্থিত কিছু ক্ষুদ্র উপনিবেশ জাপানের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। জাপানের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে জাপানের উপনিবেশগুলোও স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই মহাযুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়ে। অবশ্য জাপান বা তার উপনিবেশগুলোর এই যুদ্ধে বিশেষ শক্তিক্ষয় করার প্রয়োজন হয়নি।

চীনে জাপানি প্রভাব বিস্তার ও একটি বৃহৎ শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভের আকাঙ্ক্ষা এবং চীন ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অবস্থিত জার্মান উপনিবেশগুলোকে হস্তগত করার ইচ্ছা ছিল জাপানের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণের মূল কারণ। এগুলোর বাইরে জাপানের এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের আরো কিছু কারণ ছিল, কিন্তু এই কারণগুলোই এক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল। উল্লেখ্য, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী বছরগুলোতে ‘ইঙ্গ–জাপানি মৈত্রী’ (১৯০২) সম্পাদনের মধ্য দিয়ে জাপান ব্রিটেনের সঙ্গে মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। এই মৈত্রীর প্রকৃত লক্ষ্যবস্তু ছিল রাশিয়া, কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর জার্মানি এই মৈত্রীর লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়।
জাপানের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রবেশের আনুষ্ঠানিক কারণ ছিল ব্রিটেনের সঙ্গে তাদের মৈত্রীচুক্তির প্রেক্ষাপটে ব্রিটেন কর্তৃক জাপানের কাছে জার্মানির বিরুদ্ধে সহায়তা আহ্বান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর পর ব্রিটেন ইঙ্গ–জাপানি মৈত্রীর শর্তানুযায়ী জার্মানির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়ার জন্য জাপানকে আহ্বান জানায়। জাপান এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯১৪ সালের ২৩ আগস্ট জার্মানির বিরুদ্ধে এবং ২৫ আগস্ট জার্মানির মিত্র অস্ট্রিয়া–হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১১ নভেম্বর জার্মানির মিত্র ওসমানীয় রাষ্ট্র জার্মানির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশের লক্ষ্য জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। সর্বশেষ ১৯১৫ সালের অক্টোবরে বুলগেরিয়া কর্তৃক কেন্দ্রীয় শক্তিতে যোগদানের কারণে ১৬ অক্টোবর জাপান বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।
এই মহাযুদ্ধ চলাকালে জাপান প্রধানত পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে কেন্দ্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। অবশ্য আটলান্টিক মহাসাগর থেকে দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে জাপানিরা কেন্দ্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে সামরিক কার্যক্রম পরিচালনা করে। পরবর্তীতে রুশ বিপ্লবের পর মিত্রশক্তি রাশিয়ায় আক্রমণ চালালে জাপান এই আক্রমণে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং রাশিয়া আক্রমণের জন্য মিত্রশক্তি কর্তৃক প্রেরিত সৈন্যদলগুলোর মধ্যে জাপানি সৈন্যদলটি ছিল সর্ববৃহৎ। অবশ্য শেষ পর্যন্ত মিত্রশক্তির রাশিয়া আক্রমণ সফল হয়নি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে জাপান চীনা ভূখণ্ডে এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বিষুবরেখার উত্তরে অবস্থিত জার্মান উপনিবেশগুলোতে আক্রমণ চালিয়ে সেগুলো দখল করে নেয়। এরপর জাপান এই যুদ্ধের আর কোনো বড় মাত্রার অভিযানে অংশগ্রহণ করেনি। অবশ্য জাপানি নৌবাহিনী কেন্দ্রীয় শক্তির সামরিক নৌ কার্যক্রমের বিরুদ্ধে বিশ্বের মহাসাগরগুলোতে টহল প্রদানে অংশগ্রহণ করে এবং সিঙ্গাপুরে একটি ব্রিটিশবিরোধী বিদ্রোহ দমনে অংশ নেয়।
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানি সশস্ত্রবাহিনীতে প্রায় ৮ লক্ষ সৈন্য ছিল, কিন্তু যুদ্ধ চলাকালে কেন্দ্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে বড় ধরনের কোনো অভিযান পরিচালনা থেকে তারা বিরত ছিল। এজন্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এদের মধ্যে ৪১৫ জন সৈন্য নিহত এবং ৯০৭ জন সৈন্য আহত হয়। উল্লেখ্য, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে চীনে অবস্থিত জার্মান উপনিবেশগুলো এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বিষুবরেখার উত্তরে অবস্থিত সকল জার্মান উপনিবেশ জাপানের হস্তগত হয়।

.jpeg?w=600)