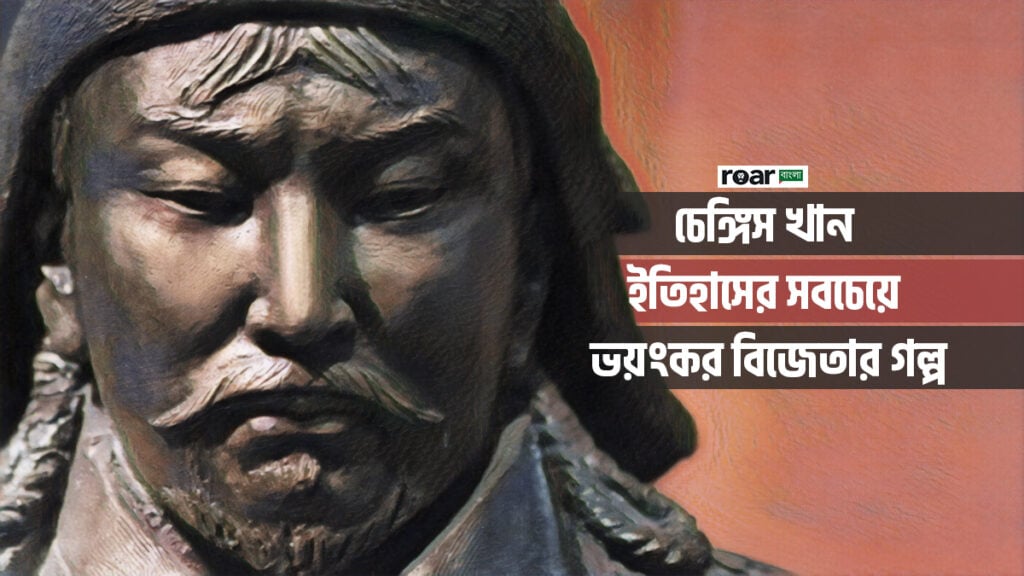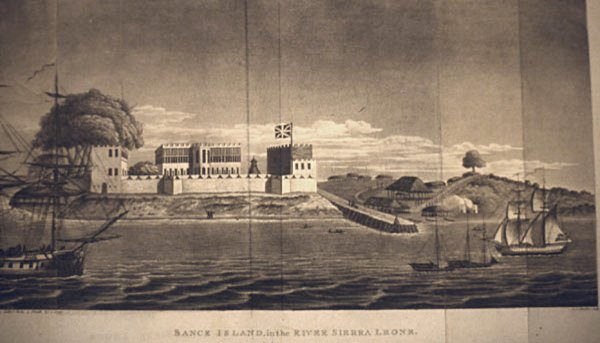১০ অক্টোবর, ৭৩২ খ্রিষ্টাব্দ। ভোর হয়েছে মাত্র।
ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চলের বিশাল এক প্রান্তর। নতুন আরেকটি দিন শুরু হয়েছে ক্ষণকাল পরে হতে যাওয়া রক্তপাতের আশঙ্কা বুকে নিয়ে। সদ্য উঁকি দেয়া সূর্যের আলোয় চকচক করছে সারি সারি ধাতব শিরস্ত্রাণ। তাদের ভেতর দিয়ে এগিয়ে এলেন চার্লস মার্টেল (Charles Martel), ফ্রাঙ্কিশ বাহিনীর সেরা জেনারেল। হালকা চিন্তার ভাঁজ তার কপালে। প্রতিপক্ষের থেকে উঁচুতে তার শিবির, সেই হিসেবে সুবিধাজনক অবস্থান তাদের। কিন্তু বর্মাচ্ছাদিত অশ্বারোহী সৈনিক আবার প্রতিপক্ষের বেশি। সংখ্যার দিক থেকেও তারা এগিয়ে।
চার্লসের হাতে ২০,০০০ ইউরোপীয় সেনা, সবাই এসেছে আন্দালুসিয়া থেকে ঝড়ের গতিতে এগিয়ে আসা উমাইয়া অনুপ্রবেশ ঠেকাতে। এই যুদ্ধে পরাস্ত হলে পশ্চিম ইউরোপ উন্মুক্ত হয়ে পড়বে উমাইয়াদের সামনে।
কে এই চার্লস মার্টেল?
বর্তমান ফ্রান্স, বেলজিয়াম এবং নেদারল্যান্ডসের বিশাল এলাকা জুড়ে এককালে বিস্তৃত ছিল ফ্রাঙ্ক জাতির সাম্রাজ্য, ফ্রান্সিয়া (Francia)। ষষ্ঠ থেকে নবম শতক পর্যন্ত স্থায়ী ছিল ফ্রাঙ্কিশ শাসন, যদিও সাম্রাজ্যের সীমানা পরিবর্তন হয় কয়েকবারই। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষদিকে ফ্রাঙ্কিশ রাজাদের অন্যতম উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, মেয়র অব দ্য প্যালেস ছিলেন পেপিন (Pippin II/ Pippinof Herstal) নামে এক অভিজাত। ক্ষমতার কলকাঠি নড়তো তার হাত দিয়েই। পেপিন সাম্রাজ্যের সীমানা বাড়ান এবং জার্মানির বেশ কিছু অংশকে নিয়ে আসেন ফ্রাঙ্কিশদের অধীনে।
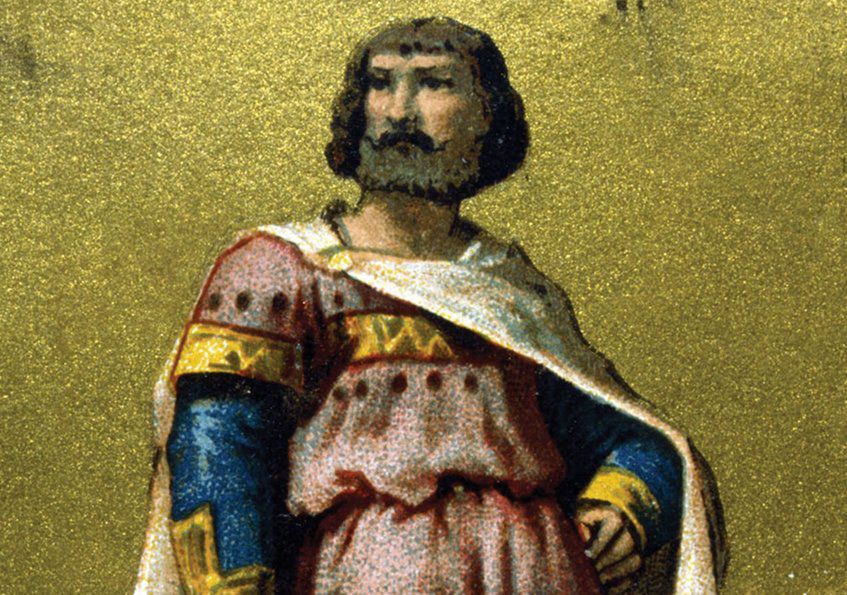
৭১৪ খ্রিষ্টাব্দে মারা যান এই পেপিন। তার পদ ছিল বংশানুক্রমিক। জ্যোষ্ঠ সন্তান গ্রিমোল্ড (Grimoald) ছিলেন তার উত্তরাধিকারী। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাবা বেঁচে থাকতেই তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হন। পেপিনের প্রথম স্ত্রী প্লেক্ট্রুড (Plectrude) স্বামীকে প্রভাবিত করেন গ্রিমোল্ডের একমাত্র ছেলে থিউডোল্ডকে (Theudoald) উত্তরাধিকারী ঘোষণা করতে।
থিউডোল্ডের বয়স ছিল মাত্র আট বছর, ফলে পেপিনের মৃত্যুর পর প্লেক্ট্রুডই হর্তাকর্তা হন। তিনি ভয় পেলেন পেপিনের দ্বিতীয় স্ত্রী, আল্পেইডার (Alpaida) ছেলে চার্লস মার্টেল ক্ষমতা দাবী করে বসতে পারেন। ফলে তাকে জেলে পাঠানো হলো। কিন্তু চার্লস গেলেন পালিয়ে, একত্র করলেন নিজের সমর্থকদের। ফ্রাঙ্কিশদের মধ্যে আরম্ভ হয়ে গেল গৃহযুদ্ধ। অনেক অঞ্চল বিদ্রোহ করে বসল, যার অন্যতম নিউস্ট্রিয়া আর বারগ্যান্ডি।
চার্লসের লোকেরা কোলন শহরে প্লেক্ট্রুডকে অবরোধ করে। ওদিকে ফ্রাইজিয়ান রাজ্যের সাথে মিলে নিউস্ট্রিয়া তখন ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত। পেপিনের হাতে বেশ কয়েকবার নাজেহাল হওয়ার জ্বালা জুড়োতে চার্লসের ওপর আক্রমণ করে বসে তারা। এখন পর্যন্ত জানা ইতিহাসে এই একবারই পরাজিত হন চার্লস মার্টেল। তিনি পিছিয়ে গেলে কোলন দখলে নেয় নিউস্ট্রিয়ার সেনারা, প্লেক্ট্রুড বাধ্য হন ক্ষমতা ছেড়ে দিতে, এবং প্রতিশ্রুতি দেন তার বংশধরেরা আর কখনো ফ্রাঙ্কিশ সাম্রাজ্যের উচ্চপদ দাবী করবে না। কোলনের কোষাগারও হানাদারদের জন্য খুলে দিতে বাধ্য হন তিনি।
বিপুল যুদ্ধলব্ধ মালামাল নিয়ে মনের সুখে নিউস্ট্রিয়ার সেনারা যখন দেশে ফিরছে, তখন অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লেন চার্লস। শত্রুদের ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে বিপুল অর্থ ছিনিয়ে নেন তিনি। সেই টাকা দিয়ে সেনাবাহিনী পুনর্গঠন করে দ্রুতই আধিপত্য বিস্তার করেন পুরো ফ্রান্সিয়ায়। ৭২৪ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ চার্লস পরিণত হলেন ফ্রাঙ্কিশদের প্রধান নেতায়।

আন্দালুসিয়ার ঘটনাপ্রবাহ
৭১০ খ্রিষ্টাব্দে ভিসিগথ রাজা উইটিজার (Witiza) মৃত্যুর পর স্পেনের সিংহাসন নিয়ে গণ্ডগোল আরম্ভ হয়। উইটিজার তরুণ সন্তান আখিলার বদলে অভিজাতরা সমর্থন করলেন বেটিকার (Baetica) ডিউক রডারিককে (Roderick)। ওদিকে সাধারণ মানুষদের একটা বড় অংশ আবার জড়ো হলো আখিলার (Akhila) পিছে। বাস্ক অঞ্চল তার পক্ষে বিদ্রোহ করে বসে।
রডারিক দলবল নিয়ে বিদ্রোহ দমনে রওনা দিলেন। রাজকীয় বাহিনীর মোকাবেলায় অসমর্থ বিদ্রোহীরা সাহায্যের অনুরোধ পাঠালেন আফ্রিকার মাগ্রেবের (Maghreb) উমাইয়া গভর্নর মুসা ইবনে নুসাইরের (Mūsā ibn Nuṣayr) কাছে। কেউ কেউ দাবী করেন- মাগ্রেবের গভর্নরকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন এক অভিজাত, বিদ্রোহীরা নয়। সেই অভিজাতের মেয়েকে নাকি ধর্ষণ করেছিলেন রডারিক।
উত্তর আফ্রিকা ততদিনে উমাইয়া খেলাফতের অধীনস্থ। তারা আগে থেকেই স্পেনের ব্যাপারে আগ্রহী ছিল, কাজেই সুযোগ পেয়ে কাজে লাগাতে ভুল করলেন না মুসা। ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে তারিক বিনা জিয়াদের (Ṭāriq ibn Ziyād) নেতৃত্বে ৭,০০০ সৈন্য পা রাখলো স্পেনে। গুয়াডালেটের (Battle of Guadalete) যুদ্ধে ভিসিগথরা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

পরিকল্পনা অনুযায়ী উমাইয়া সেনাদল নিজেরাই স্পেনের নিয়ন্ত্রণ নিতে থাকে। গুয়াডালেটের পরে তারিক রাজধানী টলেডো অধিকার করেন। পরের বছর মুসা ইবনে নুসাইর ১২,০০০ অতিরিক্ত সৈন্য নিয়ে এসে সম্পূর্ণ করেন স্পেনের অভিযান। মুসা আর তারিককে এরপরই ডেকে নেয়া হয় তৎকালীন উমাইয়া খেলাফতের রাজধানী দামেস্কে। স্পেনের দেখভালের দায়িত্ব পান মুসার ছেলে আবদ আল-আজিজ ইবনে মুসা (Abd al-Aziz ibn Musa)।
আবদ আল-আজিজ ছোটখাট প্রতিরোধের মুখোমুখি হন, তবে খুব সহজেই সেগুলো কাটিয়ে ওঠেন তিনি। যুদ্ধের বদলে আলোচনার দিকে মনোযোগ দেন নতুন শাসক। ভিসিগথ অভিজাতদের সয়সম্পত্তি ও ধর্মীয় নিরাপত্তার বদলে কর আর অন্যান্য সুবিধা আদায় করে নেন তিনি।
ফ্রান্সের পথে
ভিসিগথদের অন্যতম একটি ঘাঁটি ছিল সেপ্টিম্যানিয়া (Septimania)। এর অবস্থান ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যবর্তী পিরেনিজ (Pyrenees) পর্বতমালায়, ভূমধ্যসাগরের কোল জুড়ে। রাজধানী নার্বোনে বসে শাসন করেন রাজা। সেপ্টিম্যানিয়া নিয়ে কয়েকবারই ফ্রাঙ্ক আর ভিসিগথদের লড়াই হয়েছিল। শেষবার সংঘর্ষের পর এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় ভিসিগথ আধিপত্য।
স্পেনে যখন উমাইয়া শাসনের সূচনা হয় তখন সেপ্টিম্যানিয়ার রাজা ছিলেন আর্ডো। ৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে তার ওপর আক্রমণ শুরু হয়। তিন বছরের মাথায় নার্বোন চলে যায় উমাইয়াদের হাতে। এখান থেকে সেপ্টিম্যানিয়া এবং ফ্রাঙ্কিশ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ঝটিকা অভিযান পরিচালনা করতে থাকে উমাইয়ারা। নার্বোনে তাদের ঘাঁটি ক্রমেই ফ্রাঙ্কদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
৭২১ খ্রিষ্টাব্দের আশেপাশে উমাইয়া সেনারা হামলা করে ট্যুলুজ শহরে (Toulouse )। অ্যাকুয়াটাইনের অন্যতম শক্তিশালী এই নগরী বাঁচাতে চার্লস মার্টেলের কাছে আবেদন জানান শাসনকর্তা ডিউক ওডো। তাকে ফিরিয়ে দেন ফ্রাঙ্কিশ জেনারেল। নিজেই এরপর একদল সেনা জোগাড় করে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন ডিউক। ততদিনে শহর পতনের দ্বারপ্রান্তে, অতি আত্মবিশ্বাসী উমাইয়া সেনারা সেই আনন্দে নিজেদের পেছন দিক সুরক্ষিত রাখতে ভুলে গেছে।

সুযোগ কাজে লাগিয়ে ওডো অতর্কিত হামলা করে বসেন। তৎকালীন স্পেনের গভর্নর আল-খাওলানি (Al-Samh al-Khawlani) এই সময় নিহত হন। তার স্থলাভিষিক্ত হলেন আব্দ আল-রহমান (Abd ar-Rahman)। তিনি পরাজয় সুনিশ্চিত বুঝে যুদ্ধ বন্ধ করে নিরাপদে সেনাবাহিনী নিয়ে পিছিয়ে আসেন স্পেনে। তবে নার্বোনে মুসলিম আধিপত্য বজায় ছিল, এবং ৭২৫ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ পুরো সেপ্টিম্যানিয়াই চলে আসে আব্দ আল-রহমানের অধীনে।
ডিউক ওডো
বর্তমান ফ্রান্সের দক্ষিণ-পশ্চিমে উমাইয়া স্পেন আর খ্রিষ্টীয় ফ্রাঙ্কিশ সাম্রাজ্যের মাঝে অ্যাকুয়াটাইন রাজ্য। দুই শক্তিশালী প্রতিবেশির মাঝে খুব হিসেব করে চলতে হয় তাদের। ফ্রাঙ্করা অ্যাকুয়াটাইনকে নিজেদের অংশ বলেই মনে করত, তবে অধিকাংশ সময়ে তারা কার্যত স্বাধীনভাবে শাসনকাজ পরিচালনা করত।
চার্লস আর উমাইয়ারা যখন মুখোমুখি অবস্থানে, তখন অ্যাকুয়াটাইনের অধিকর্তা ডিউক ওডো (Duke Odo)। তার সামনে দুটি পথ খোলা, হয় মুসলিম স্পেন, নয় খ্রিষ্টীয় ফ্রাঙ্কদের বশ্যতা স্বীকার। কিন্তু ওডো চান অ্যাকুয়াটাইনের স্বাধীনতা ধরে রাখতে। ৭৩০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ পরিষ্কার হয়ে গেল দুই পক্ষই তার রাজ্যকে টার্গেট করছে।
ঠিক এমন সময় হাতে যেন চাঁদ পেলেন ডিউক ওডো। কাতালুনিয়ার (Cataluya) শক্তিশালী বার্বার গভর্নর মুনুজা (Munuza) বিদ্রোহ করে বসেন উমাইয়া শাসনের বিরুদ্ধে। তার ঘাঁটি ছিল পিরেনিজের সার্ডানিয়াতে (Cerdanya)। ওডো একা কারো বিপক্ষে টিকতে পারবেন না, কিন্তু তিনি যদি মুনুজার সাথে জোট করেন তাহলে সেটা সম্ভব। অ্যাকুয়াটাইনের ডিউক ঠিক সেই কাজই করলেন। মৈত্রী পাকা করতে নিজের কন্যার বিয়ে দেন মুনুজার সাথে।
জোটের খবর পেয়েই চার্লস অ্যাকুয়াটাইনের এলাকায় হামলা জোরদার করেন। ওদিকে কর্ডোবাকে কেন্দ্র করে জমায়েত হয় উমাইয়া ফৌজ। আব্দ আল-রহমান সোজা সার্ডানিয়া অবরোধ করে বসেন। অল্প সময়ের মধ্যেই পতন হয় মুনুজার। মুসলিম সেনাদল এবার এগিয়ে যায় অ্যাকুয়াটাইন বরাবর। বোর্দো শহরের কাছে তাদের বাধা দেন ওডো। গ্যাহোন নদীর তীরবর্তী যুদ্ধে (Battle of Bordeaux) চরম পরাজয় বরণ করে ওডোর সেনারা। বোর্দো চলে যায় আল-রহমানের হাতে, ওডো প্রাণ হাতে নিয়ে পালিয়ে যান চার্লসের দরবারে, প্রার্থনা করলেন ফ্রাঙ্কিশ সহায়তা।

ওদিকে বোর্দো দখল করে কিন্তু বসে ছিলেন না আল-রহমান। তিনি জানতেন অ্যাকুয়াটাইন নিয়ন্ত্রণে নিতে হলে ওডোর একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে। কাজেই ডিউককে ধাওয়া করেছিলেন তিনি, সম্পদশালী ট্যুরস নগরীতে লুটতরাজ চালানোও একটা উদ্দেশ্য বটে।
ওডো চার্লসের কাছে যাচ্ছেন জানা থাকলেও পাত্তা দেননি আল-রহমান। চার্লস নিজেও আগে ওডোকে আক্রমণ করেছিলেন, তাই উমাইয়া গভর্নর মনে করেছিলেন তিনি তাকে সাহায্য করবেন না। তবে হিসেবে ভুল করে ফেলেছিলেন উমাইয়া শাসক। চার্লস ওডোকে পছন্দ করেন না সত্য, তবে তিনি এটাও চান না তার ঘর পর্যন্ত বিস্তৃত হোক মুসলিম স্পেনের সীমানা। তিনি ক্ষীণশক্তির ওডোকেই অ্যাকুয়াটাইনের সিংহাসনে দেখতে আগ্রহী ছিলেন। তাছাড়া ট্যুরসের উপচে পড়া কোষাগার হাতে প্রতিপক্ষের হাতে চলে গেলে বিপাকে পড়তে হবে ফ্রাঙ্কদের, সেটাও হতে দেয়া যাবে না।
চার্লস দ্রুত লোকজন জড়ো করে ট্যুরসের কাছাকাছি এসে পৌঁছেন। নিজের অশ্বারোহীদের পাঠিয়ে দেন শহর রক্ষা করতে। এরপর এগিয়ে এসে শিবির ফেলেন ট্যুরসের দক্ষিণে কোনো এক ময়দানে। ঠিক কোথায় এই রণক্ষেত্র তা নিয়ে মতভেদ আছে। জনশ্রুতি আছে পঁয়তিয়ের্স নগরীর উপকণ্ঠে ছিল এই স্থান।
সিংহভাগ গবেষকের মতে, মূল লড়াইয়ের আগে দুই দলের অগ্রবর্তী বাহিনীর মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে বেশ কিছু সংঘর্ষ হয়ে যায়। সবাই অন্তত একটি ব্যাপারে একমত যে আল-রহমান চার্লসের রাজকীয় বাহিনীর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি চিন্তাই করেননি যে ফ্রাঙ্কিশ জেনারেল ওডোর ডাকে সাড়া দেবেন। কাজেই চার্লসকে পুরো শক্তিতে মাঠে দেখে হকচকিয়ে যান তিনি।