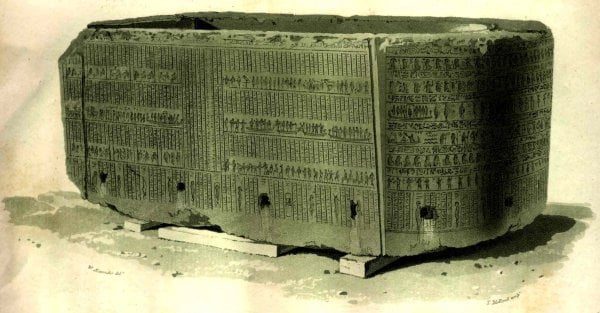নাৎসি শাসন জার্মানি থেকে বিদায় নিয়েছে অনেক বছর হয়ে গিয়েছে। তবে এখনো নাৎসি শাসনের প্রভাব রয়ে গিয়েছে দেশটির উপর। দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ও চোখে পড়ার মতো খাতে নয়, আজ কথা বলছি জার্মানির শিশু এবং তাদের বাবা-মায়ের ব্যবহার নিয়ে। নাৎসি জার্মানি কঠোরভাবে বড় করার চেষ্টা করেছিল শিশুদের। সেই অনুযায়ীই চলছিল সবকিছু। শিশুদের সাথে বাবা-মায়ের ব্যবহার, শিশুকে দেওয়া সুযোগ-সুবিধা, তাকে করা শাসন- সব কিছুতেই একটি নিয়ম বেঁধে দিয়েছিল নাৎসিরা।
এরপর এতগুলো বছর চলে গিয়েছে। এখনও কি আগের মতো, স্বাভাবিক হতে পেরেছে জার্মান মায়েরা এখনো তাদের শিশুর সাথে? শিশুরা কি নিজেদের শৈশবে ফিরে যেতে পেরেছে পুরোপুরি? না, সেটি এখনো হয়নি। কেন? চলুন বিস্তারিতভাবে ব্যাপারটিকে বিশ্লেষণ করা যাক।

রেনাট ফ্লেন জার্মানির বাসিন্দা। ফ্লেনের বয় এখন ৬০ বছর। অসম্ভব হতাশ হয়ে পড়েছিলেন এই নারী। নিজের মনোবিজ্ঞানীর কাছে নিজের এই হতাশার কথা জানান ফ্লেন। তিনি ইচ্ছে করলেও নিজ সন্তানকে ভালোবাসতে পারেননি। এমনকি, অন্য কাউকেই নিজের কাছে ঘেঁষতে দেন না। কিন্তু তিনি মানুষের কাছেও যেতে চান। সপূর্ণ আলাদা এমন মানসিক অবস্থানের গোড়া কোথায় সেটা খুঁজতে গিয়ে জানা যায়, ফ্লেনের জন্ম হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপর। আর তখন সেখানকার পরিস্থিতি কেমন ছিল তা জানা যায় জোহানা হারেরের লেখায়।
১৯৩৪ সালে লেখক জোহানা হারের ‘দ্য জার্মান মাদার এন্ড হার ফার্স্ট চাইল্ড’ প্রকাশ করেন। তার লেখা বইটি তখন ১.২ মিলিয়ন কপি বিক্রি হয়। যুদ্ধের পর বিক্রি হয় এর অর্ধেক। নিজের বইয়ে হারের উল্লেখ করেন, সেসময় নাৎসি শাসনে বাবা-মাকে শিশুদের সাথে যতটা সম্ভব কম ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তুলতে নির্দেশ দেওয়া হতো। ফলে, কোনো শিশু কান্না করলে তাতে তার মায়ের মাথা ঘামানোর কোনো কারণ ছিল না। স্নেহ ও ভালোবাসাজাতীয় কোনো রকম সংশ্লিষ্টতা পরিহার করাটাই ছিল কাম্য। হারেরও ঠিক এমনটাই করতে মায়েদের উৎসাহ দেন নিজের বইয়ে। এর প্রভাব শুধু সেসময় শিশুদের সামাজিক ও মানসিক সম্পর্কেই নয়, পরবর্তীতেও গভীরভাবে পড়েছে।
ফ্লেনের যতদূর মনে পড়েছিল, তার নিজের বাড়িতেও ঠিক এমন একটি বই দেখেছিলেন তিনি। শুধু ফ্লেন নয়, সেসময়ের আরো অনেক শিশুর মাথাতেই এই মানসিক প্রভাব পাকাপাকিভাবে গেঁথে গিয়েছিল। কোনো না কোনোভাবে নাৎসি শাসন এবং হারেরের এই বই নিজেদের কাজ সফলভাবেই করতে সমর্থ হয়েছে। নাৎসিরা এমনটা চেয়েছিল কেন তার কারণ পরিষ্কার। তারা নিজেরাও মানবিক এবং আবেগীয় বন্ধনে কারো সাথে আবদ্ধ থাকেনি। একইসাথে তারা চেয়েছিল পুরো একটা প্রজন্মকে আবেগীয় বন্ধনহীন করেই গড়ে তুলতে। কারণ, এতে করে শাসন টিকিয়ে রাখা আর জার্মানিকে শ্রেষ্ঠস্থানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল (তাদের কথানুসারে)। আর পুরো একটি প্রজন্ম যদি আবেগীয় বন্ধনকে এড়িয়ে যাওয়ার প্রশিক্ষণ পায়, তাহলে তার পরের প্রজন্মগুলোতেও তো তার কিছু ছাপ থাকবেই।

এখন প্রশ্ন হলো, কে এই জোহানা হারের? নাৎসি শাসনামলে কেন তার কথাকে এত গুরুত্ব সহকারে নেওয়া হয়েছিল? জোহানা হারের ছিলেন একজন পালমোনোলজিস্ট। কোনো প্রশিক্ষণ না থাকলেও শিশুদের লালন-পালনের ক্ষেত্রে তার কথাকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতো নাৎসিরা। ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হারেরের বইটি মায়েদের একটি প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে রাখা হয়। ফলে, ১৯৪৩ সালের মধ্যে অন্তত ৩ মিলিয়ন জার্মান মা এই বইটি পড়েন। তাদের শিশুর লালন-পালনও সেই অনুযায়ীই হয়।
সেসময়কার নার্সারি স্কুল এবং চাইল্ড কেয়ার প্রতিষ্ঠানগুলোতেও বইটি বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়। কেবল যে লিখে দেওয়া হয়েছিল বইটিতে তা নয়, মা শিশুকে কোলে নেওয়ার সময় কতটা দূরত্ব বজায়ে রাখবেন সেটা ছবি এঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হয় এতে। একটি শিশুর সবচাইতে বেশি প্রয়োজন হয় মানসিক ও আবেগীয় সংস্পর্শ। সেটা যেন ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে আসা যায় তা নিয়ে সতর্ক ছিলেন হারের। শিশুরা যদি কাঁদতে থাকে, তাহলে তাদের কাঁদতে দেওয়াই ভালো বলে মনে করতেন তিনি। সন্তান জন্মের পর তাদের সাথে আদুরে কোনো কথা বলার চাইতে কঠোর জার্মান ভাষায় কথা বলতে নির্দেশ দেন তিনি।“শিশুকে খাওয়ানো, গোসল করানো এবং শুকানো প্রয়োজন; বাকিটা সময় তাদেরকে একা ছেড়ে দেওয়াই উত্তম,” বলেন জোহানা হারের।

শিশুর জন্মের পরবর্তী ২৪ ঘন্টা শিশুকে আলাদা রাখা পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। এর কারণ হিসেব হারের জানান, একটি শিশু কান্না করলে যদি তাকে আদর করা হয়, কোলে নেওয়া হয় বা খাওয়ানো হয়, তাহলে সে আরো বেশি কান্না করবে। ঘরের ভেতরে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা চালাবে। সে মনে করবে, কোনো সমস্যা হলে কাঁদলেই তার সমাধান হয়ে যাবে। এমন কোনো চিন্তা যেন শিশুর মাথায় না আসে, সেজন্যই তাকে অবহেলা করা উচিৎ।
তবে, ‘দ্য জার্মান মাদার এন্ড হার ফার্স্ট চাইল্ড’ হারেরের প্রথম বই ছিল না। এর আগে শিশুদের জন্যও বই লেখেন এই নারী। ‘মাদার, টেল মি অ্যাবাউট অ্যাডলফ হিটলার’ নামক শিশুতোষ একটি বই লেখেন হারের। এটি অনেকটা রুপকথার গল্পের মতো ছিল। যেখানে শিশুদের ভাষায় তাদেরকে হিটলার সম্পর্কে, ইহুদী বিদ্বেষ এবং সমাজতন্ত্র বিরোধী মতবাদ সম্পর্কে জানানো হতো। ‘আওয়ার লিটল চিলড্রেন’ নামে আরেকটি বইও লেখেন হারের। ১৯৪৫ সালে জার্মানি পরাজিত হলে নিজের চিকিৎসকের লাইসেন্স হারান এই নারী। সেই সাথে তাকে জেলে বন্দী করা হয়। তবে এত কিছু হয়ে গেলেও নিজের মানসিকতার এতটুকু পরিবর্তন আনেননি জোহানা হারের। তার দুই মেয়ের কথানুসারে, মৃত্যুর আগপর্যন্ত নাৎসি সমর্থক হিসেবেই বেঁচেছিলেন হারের। ১৯৮৮ সালে এই নারীর মৃত্যু হয়।

তবে জোহানা হারের মারা গেলেও তার প্রভাব এখনও জার্মানির উপর থেকে যায়নি। জার্মানদের একাকীত্ব, হতাশা, কম জন্মহার- এগুলোর মূল কারণ হিসেবে বিশেষজ্ঞরা হারেরের বইকে দায়ী করে থাকেন। ইউনিভার্সিটি অব ক্যাসেলের হার্টমুট রেডেবোল্ড এবং অন্যান্যদের গবেষণানুসারে, এখনো অনেক নারী নিজেদের সন্তানের কাছে যাওয়া থেকে বিরত থাকেন এই ভয়ে, পাছে তাদের সন্তানের অভ্যাস খারাপ না হয়ে যায়। বর্তমান সময় এবং শিক্ষা এমন কিছু হওয়ার আশঙ্কা না করলেও জোহানা হারের সেটা করতেন। সচেতনভাবে না হলেও এখনো জোহানা হারেরের শিক্ষাকে নিজেদের মধ্যে জিইয়ে রেখেছে জার্মানরা।
গবেষক ও প্রাক্তন শিক্ষক লাউস গ্রসম্যানের করা এক গবেষণায় অনাথ শিশুদের দুটো ভাগ করা হয়। একটি ভাগকে রাখা হয় পালক পিতামাতার কাছে। আরেকটি ভাগকে এতিমখানায় রেখে দেওয়া হয়। একদিন তাদের সবার কাছেই একজন আগন্তুক গিয়ে নিজের সাথে আসতে বলেন। এক্ষেত্রে সবচাইতে বেশি শিশু কোনো কথা না বলেই আগন্তুকের সাথে এসেছিল এতিমখানা থেকে। মূলত, আবেগীয় সম্পর্কের সংস্পর্শে না থাকলে একজন মানুষের দ্বারা যুদ্ধ বা যেকোনো কাজে অংশগ্রহণ করানো সহজ হয়ে পড়ে। আর সেই চিন্তা থেকে হারের নিজের বই লিখেছিলেন এবং নাৎসি শাসকেরা তার কথা মেনেছিল বলে মনে করা হয়।
এই প্রভাব জার্মানবাসীর উপর থেকে কবে পুরোপুরি চলে যাবে তা বলা যায় না। জোর করে কিছু করাটাও সম্ভব নয়। তবে হ্যাঁ, এমনটা সম্ভব হলে একদিন জার্মানিতে মানসিক সমস্যা, একাকিত্ব আর হতাশায় ভোগা মানুষের পরিমাণ একটু হলেও কমে আসবে।