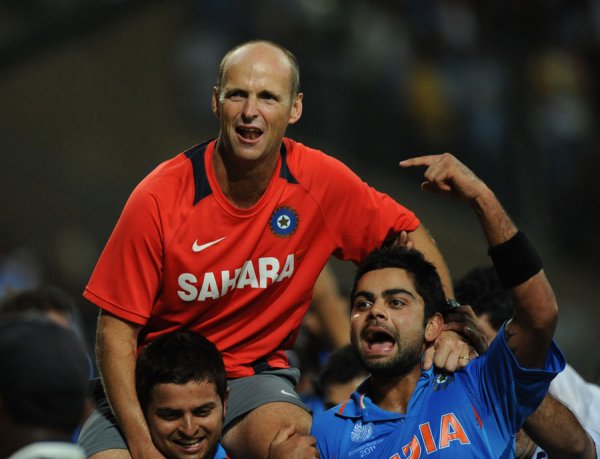রবার্ট লেভানডফস্কি বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির এক খেলোয়াড়। নাহ, একদম ভাল্লাগছেনা আমার এভাবে লিখতে। লেখা তো দূরে থাক, আমার এভাবে ভাবতেও প্রচণ্ড দ্বিধা হচ্ছে। আমাদের প্রিয় খেলাটি নানারকম পর্যায় পার করেছে, অনেকরকম চক্রের ভেতর দিয়ে গিয়েছে আজ পর্যন্ত, আর চলতি যুগ ফুটবলের সনাতনী সেন্টার-ফরওয়ার্ডদের জন্য খুব একটা সুবিধাজনক সময় নয়। খেলোয়াড়রা এখন অ্যাথলেট কম, জিমন্যাস্ট বেশি; আজকালকার ‘ফরওয়ার্ড’ বলতে সাধারণভাবে এমন কেউ নন যাকে ঘিরে দল আক্রমণের পরিকল্পনা সাজানো যায়; বরং এমন একজন খেলোয়াড়কে বুঝি, যিনি মাঠের সম্মুখভাগের যেকোনো অংশে খেলতে পারবেন। অন্য কথায়, একজন নাম্বার নাইন; যারা এখন আর অপরিহার্য নয়।
লেভানডফস্কি একজন সত্যিকারের নাম্বার নাইন, যা মিশে আছে তার আত্মার গহীনে; ঠিক যেমন এই নম্বরটি আমার হৃদয়েও নিয়ে আছে অনেকটা জায়গা। বাতাসে ভাসা বল নিয়ন্ত্রণে খুবই দক্ষ লেভানডফস্কি, স্বভাবতই দ্রুতগতিসম্পন্ন, দুই পা দিয়েই বল নিয়ন্ত্রণ করতে জানেন, দলের আক্রমণভাগের কেন্দ্রবিন্দুতে খেলে থাকেন, ঝুঁকি নিতে ভয় করেন না, ফ্রি কিক থেকে গোল করতে পারেন, পেনাল্টি নিতে ভালোবাসেন, এবং নিজের দেশ ও ক্লাবের হয়ে অবিশ্বাস্য সংখ্যক গোল করেছেন। সেন্টার ফরওয়ার্ডদের যদি বলি বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি, তবে লেভানডফস্কিকে বলতে টাইরানোসরাস রেক্স। আমি লেভানডফস্কির খেলা দেখতে ভালোবাসি। হয়তো অনুভব করতে পারি কিছু একটা।
ফেলে আসা দশকের দুই কিংবদন্তির (বলাই বাহুল্য, লিওনেস মেসি এবং ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো) গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে খেলা পর্যবেক্ষণ করলে ধরতে পারবেন,তাদের খেলার মূল থিমটা একই। দু’জনের গোলসংখ্যা দেখেই চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায়, রীতিমতো রাজসিক এক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে আছেন দীর্ঘসময় ধরে – ইতিহাসের পাতায় কে সর্বকালের সেরা হিসেবে পাকাপাকিভাবে জায়গা করে নেবেন। তাদের দু’জনের কেউই কিন্তু ‘ষোলআনা’ স্ট্রাইকার নন। একই কথা প্রযোজ্য লিভারপুলের মোহাম্মদ সালাহ এবং সাদিও মানের ক্ষেত্রেও। তবে হ্যারি কেইন, এডিনসন কাভানি, রোমেলো লুকাকু এবং আরলিং হালান্ড এখানে ব্যতিক্রম।

ফুটবল বরাবরই তার রূপ যুগে যুগে বদলায়, যেমন বদলায় আমাদের চারপাশের পরিবেশ, যেমন বদলায় পৃথিবীর রূপরস। আজকে যে টগবগে তরুণ, কাল সে-ই বুড়োটে হয়ে যাবে; স্মৃতির জাবর কাটবে আর ভাববে, তার সময়েই দুনিয়াটা বোধহয় সুন্দর ছিল। আমাদের সবার ক্ষেত্রেই এমনটা হয়ে থাকে আসলে। ফুটবল এখন আগের মতো অতটা শারীরবৃত্তীয় নয়, অতটা বর্বর নয়, ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতারও নয়। ফুটবল এখন বেশি সময় ধরে বলের দখল নিয়ে রাখার, প্রেস করে খেলার। আর এসব কিছুর মাঝে সেন্টার ফরওয়ার্ডরা হঠাৎই যেন সেকেলে হয়ে গেছেন।
আন্তর্জাতিক ফুটবলের দায় আছে এতে। বিজয়ী দলের ব্যাপক আধিপত্য থাকে খেলার ধরন ও ট্যাকটিক্স নিয়ন্ত্রণে। (শুধু ভাবুন, প্রিমিয়ার লিগের চেহারাটা কেমন হতো যদি কেভিন কিগ্যানের নিউক্যাসল ইউনাইটেড ট্রফি জিততো! আমি যে বছর সেখানে যোগ দিই, তার আগের বছরের কথা বলছি, যদিও সেটা অন্য প্রসঙ্গ।) যেমনটা ২০১২ সালে সেস ফ্যাব্রিগাসের স্পেন ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ জেতার পর লক্ষ্য করা গিয়েছে।
আমরা অল্প কিছুদিন আগেই চ্যাম্পিয়নস লিগে অল-ইংলিশ ফাইনাল দেখলাম। তাদের কেউই কিন্তু প্রোপার সেন্টার ফরোয়ার্ড নিয়ে খেলতে নামেনি। অথচ অল্প কয়েক বছর আগেও এরকম কিছু ভাবাই যেত না। চেলসির কাই হাভের্টজ নিজের পছন্দের পজিশন বলেন ‘ফলস নাইন’ এবং ‘স্ট্রাইকারদের মতো খেলা’ নয়। ম্যানচেস্টার সিটির পেপ গার্দিওলা তো সার্জিও আগুয়েরো ও গ্যাব্রিয়েল জেসুসকে শুরুর একাদশে রাখেনইনি ফাইনালে। অনেক দল আজকাল সেন্টার ফরোয়ার্ড ছাড়াই ম্যাচের পরিকল্পনা সাজিয়ে থাকে।

সবচেয়ে কৌতুহলোদ্দীপক ব্যাপার হলো – কিছুটা অপ্রাসঙ্গিকতা চলে আসছে যদিও, সেজন্য ক্ষমাপ্রার্থী – চেলসি এবং ম্যানচেস্টার সিটির স্কোয়াড দেখে মনে হয়, আসছে গ্রীষ্মের দলবদলের সময়ে দুটো ক্লাবই সেন্টার ফরোয়ার্ড খুঁজে বেড়াবে। হ্যারি কেইন এবং হালান্ড নিঃসন্দেহে তাদের তালিকার ওপরের দিকেই থাকবে, দাম যতই আকাশছোঁয়া হোক না কেন। এসব কি আমাদের কোনো ইঙ্গিত দিচ্ছে? গোল স্কোর করা আসলে ম্যাচের সবচেয়ে কঠিন কাজ, সন্দেহ নেই। সেটাই কি মূল কারণ, নাকি এসব আসলে তরুণ তারকাদের নিজেদের ক্লাবে ভেড়ানোর চলমান প্রতিযোগিতারই প্রতিফলন মাত্র?
আমার মনে হয়, এই দুটি দলের জন্য সেন্টার ফরোয়ার্ড আসলেই জরুরি। শেষের দিকে গার্দিওলা আগুয়েরোর উপর আর ভরসা ধরে রাখতে পারেননি। ইনজুরি আগুয়েরোকে বেশ ভোগাচ্ছে। এই আর্জেন্টিনিয়ানের বিকল্প একজন খুঁজে বের করতেই হবে ম্যানচেস্টার সিটিকে।
চেলসি অলিভিয়ের জিরু এবং ট্যামি আব্রাহামের ওপর ভরসা রাখতে পারে, কিন্তু টমাস টুখেল নিয়মিত তাদের শুরুর একাদশে রাখেননি। চেলসিতে হালান্ড থাকলে হালান্ড নিয়মিতভাবে খেলতেন, হ্যারি কেইনও হয়তো খেলতেন ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে। হালান্ড-হ্যারি কেইন দলবদলের পর ফুটবলে কোনো পরিবর্তন আসবে কি না, নাম্বার নাইনের গুরুত্ব বাড়বে কি না, এখনই বলাটা মুশকিল। তবে আমি প্রার্থনা করি, তা-ই যেন হয়।

আমি ইউরোতে হ্যারি কেইনকে সমর্থন দেব, খুব করে চাইব এবারে ও গোল্ডেন বুট জিতুক, যেমনটা জিতেছিল গত বিশ্বকাপে। লেভানডফস্কির ওপরেও আমার চোখ থাকবে। রোনালদো-মেসির মতো মুগ্ধতার ফেরিওয়ালা নন বটে, তবে গতবার বেশ কৃতিত্বের সঙ্গেই জিতে নিয়েছেন ইউরোপিয়ান গোল্ডেন শ্যু। (গোল্ডেন বুট,গোল্ডেন শ্যু – মাঝেমাঝে একটু ধন্দেই পড়ে যাই বটে!)
কী দারুণ একটা মৌসুমই না উপভোগ করলেন লেভানডফস্কি বায়ার্ন মিউনিখে। জার্ড মুলারের বুন্দেসলিগায় এক মৌসুমে সবচেয়ে বেশি গোলের রেকর্ড ভেঙেছেন। গার্ড মুলার, ‘ডার বোম্বার’ নামে যিনি জগৎবিখ্যাত, বুন্দেসলিগার তথা বায়া

লেভানডফস্কি দারুণ একটা ক্লাবে খেলেন – বায়ার্ন মিউনিখ। বায়ার্ন গেল মৌসুমে তাদের নয় নম্বর শিরোপা জিতল। এই ব্যাপারটা পাশে সরিয়ে রাখলেও লেভানডফস্কির ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান রীতিমতো বিস্ময়কর রকমের উদ্ভট মনে হতে পারে! পুরো ক্যারিয়ারজুড়ে দেশ ও ক্লাবের হয়ে ৬৯৬টি ম্যাচ খেলেছেন, গোল করেছেন ৪৮৪টি। কী অসাধারণ, দুর্দান্ত সংখ্যাটা! লেভানডফস্কি যেখানেই খেলেছেন, একের পর এক লক্ষ্যভেদ করে গেছেন, গোলের পর গোল করেছেন। তিনি যেন মহাভারতের অর্জুন; লক্ষ্যভেদ যার কাছে মামুলি এক ব্যাপারমাত্র।
পোল্যান্ডের হয়েও পরিসংখ্যানটা খুব পিছিয়ে নেই। পোল্যান্ডকে আর যাই হোক, ইউরোপের শক্তিশালী ফুটবল দেশগুলোর কাতারে ধরা হয় না। এরকম একটি দলের হয়েও ১১৯ ম্যাচে ৬৬টি গোল করা চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। এই পরিসংখ্যানগুলোই লেভানডফস্কি কত উৎকৃষ্ট মানের একজন ফুটবলার, তার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

লেভানডফস্কি একেবারে মেশিনের মতো, ধারাবাহিকতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার এক সুনিপুণ মডেল। গত ১১ মৌসুমে লেভানডফস্কি ৩০টির নিচে ম্যাচ একবারই খেলেছিলেন, সেবারেও নয় নয় করে ২৯টি ম্যাচ খেলে ফেলেছিলেন। এই ১১ মৌসুমে প্রায় প্রতিবারই ২০ বা তদোর্ধ্ব গোল করেছেন, দুইবার ছাড়া। লেভানডফস্কি খুব বেশি একটা ইনজুরিতে পড়েন না – আমি শুধু ঈর্ষার দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকি লেভানডফস্কির দিকে – কী দুর্দান্ত ফিট একজন খেলোয়াড়! আমি বরাবরই একটি কথা বলি, সেরার আসন দখল করা এক ব্যাপার আর দীর্ঘদিন ধরে সেটি ধরে রাখা অন্য ব্যাপার।
পুরো এপ্রিল মাসে ইনজুরির জন্য মাঠের বাইরে ছিলেন লেভানডফস্কি। এতে করে কিছুটা সুবিধা পেলেও পেতে পারেন লেভানডফস্কি ও পোল্যান্ড। নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। ইউরো ‘৯৬-এর আগে চার কি পাঁচ সপ্তাহের জন্য খেলতে পারিনি। হার্নিয়ার অস্ত্রোপচার করতে হয়েছিল। কঠিন পরিশ্রম করে আমি আমার আগের ফিটনেস ফিরে পেয়েছিলাম। ক্লাব ফুটবলে কঠিন একটা মৌসুম কাটানোর পর ঐ সময় খেলতে না পারাটা আদতে আমার জন্য শাপেবর হয়েছিল। (জানিয়ে রাখি, আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে ইউরো ‘৯৬-তে আমি গোল্ডেন বুট জিতেছিলাম। বলি, সানগ্লাসওয়ালা ইমোজিটা গেল কই?)

পোল্যান্ডকে নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন। তিন বছর আগে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা নিয়ে বিশ্বকাপ শেষ করেছে পোল্যান্ড। নিজেদের গ্রুপে চার নম্বর হয়ে বিদায় নিয়েছে তারা, লেভানডফস্কিও গোলের দেখা পাননি। তারপরও পোল্যান্ড ইউরো ২০২০-এর জন্য কোয়ালিফাই করেছে। কিন্তু জের্জি ব্রেজেককে তবু চাকরিচ্যুত হতে হয়েছে, নতুন নিয়োগ পেয়েছেন পাওলো সোউসা। এই গ্রুপ সম্পর্কে কিছু বলা মুশকিল। স্পেন নিঃসন্দেহে ফেভারিট, কিন্তু বাকি তিনটি দলেরও প্রত্যেকেই পরের রাউন্ডে খেলার যোগ্যতা রাখে।
(যখন লেখা পড়ছেন, ততদিনে গ্রুপপর্বের ফয়সালা হয়ে গেছে। পোল্যান্ড শেষ করেছে গ্রুপের তলানিতে থেকে; রাউন্ড অফ সিক্সটিনে গেছে সুইডেন আর স্পেন। সুইডেন যেমন চমক দেখিয়ে হয়েছে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন, স্লোভাকিয়াও সীমিত সামর্থ্যেই দেখিয়েছে দারুণ ইনটেন্ট। তবে লেভানডফস্কি খুব একটা ঝলক দেখাতে পারেননি, ক্লাবের আগুনে ফর্মটা কেন যেন টেনে আনতে পারেননি জাতীয় দলে।)
মনে রাখতে হবে, পোল্যান্ড যদি কিছু একটা করে দেখাতে চায় ইউরোতে, তার পুরো দায়িত্ব লেভানডফস্কিকেই নিতে হবে। তিনিই যে পোল্যান্ডের অধিনায়ক! কিন্তু এটাও বুঝতে হবে যে পোল্যান্ড বায়ার্ন নয়; বায়ার্নে লেভানডফস্কি যাদের পাশে খেলেন, পোল্যান্ডে তাদের পাবেন না। পোল্যান্ডের সাথে লেভানডফস্কির যে পরিস্থিতি, একইরকম অবস্থা গ্যারেথ বেল এবং ওয়েলসের মধ্যেও। তবে এক্ষেত্রে মানসিকতার পরিবর্তনও একটা বড় ব্যাপার। লেভানডফস্কি তার দেশের সবচেয়ে বড় ভরসার জায়গা। এই প্রত্যাশার ভার লেভানডফস্কি তার পেশাদার খেলোয়াড়ি জীবনের পুরোটাজুড়েই বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন তার কাঁধে, বেড়াতেও হবে।

আগুয়েরো সম্পর্কে কিছুদিন আগে লিখেছিলাম। বলেছিলাম, ভালো স্ট্রাইকারদের ভেতর একটা সহজাত প্রবৃত্তি থাকে, কখন কীভাবে কঠিন পরিস্থিতিতেও গোল করে ম্যাচ বাঁচানো যেতে পারে। লেভানডফস্কিও তা ভালোমতোই জানেন। প্রতিপক্ষের ডি-বক্সের ভেতরে যেভাবে শরীরটাকে ঘোরান, বল নিয়ন্ত্রণ করেন, তা একেবারেই ব্যতিক্রমধর্মী। মাঠের সবচেয়ে ব্যস্ততম জায়গায়ও তিনি এক গজ জায়গা যদি খুঁজে বের করতে পারেন, তবেও তিনি জালের ভেতরে বল পাঠাবেনই। এসব কালেভদ্রে পেয়ে যাওয়া গোল বলে উড়িয়ে দিতে পারবেন না। সময়নির্ধারণ, পুর্বানুমান এবং কৌশল – এই তিনের সমন্বয়েই এই অসাধারণ গোলগুলো দেখতে পাওয়া যায় লেভানডফস্কির পা থেকে। লেভানডফস্কি প্রতিনিয়ত গোল করে যাচ্ছেন, জাদুর মতো একেকবার বল প্রতিপক্ষের জাল ছুঁয়ে আসছে বল, কেউ ঠেকাতে পারছে না তাকে, এটাই যেন নিয়তি।
একজন স্ট্রাইকারের সহজাত গুণগুলো লেভানডফস্কির হাড়েমজ্জায় মিশে আছে। লেভানডফস্কি ডি-বক্সের ভেতরে গিয়ে গোল করায় যেমন অভ্যস্ত, তেমন ২০ গজ দূর থেকে গোল করায়ও সমান দক্ষ। সেখানেও লেভানডফস্কিকে জায়গা দেওয়া যাবে না। যদি লেভানডফস্কি সেখানেও জায়গা পেয়ে যান, তবে গোল করে বসতে পারেন তিনি। লেভানডফস্কি পায়ে বল পেলে মাঠে তরল পারদের মত খেলে বেড়ান। দূরপাল্লার যে শটগুলো তিনি নেন, তা এত অস্বাভাবিক জোর গতির সাথে মারেন যে বেশিরভাগ সময়েই গোলকিপার এবং ডিফেন্ডাররা প্রতিক্রিয়া দেখানোর সময় পান না। এটাও লেভানডফস্কির আরেক বড় অস্ত্র প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার। প্রতিক্রিয়া দেখানোর আগেই যা ঘটানোর ঘটিয়ে দেন ‘লন্ডভন্ডস্কি’; বল জালের ভেতর, এবং… গোল!
গতি এবং মাঠের স্পেস বা খোলা জায়গা – এই দুটোর সাথে যদি মেশান দুর্দান্ত পজিশনিং সেন্স, সাথে যোগ করা হয় ফিটনেস এবং ধারাবাহিকতা, ব্যস, তৈরি হয়ে গেল প্রতিপক্ষের জন্য সবচেয়ে বিষাক্ত অস্ত্র। লেভানডফস্কি যুগের সেরা খেলোয়াড়দের একজন। আমি আশা করি, হ্যারি কেইন এবং লুকাকুকেও প্রচুর গোল করতে দেখব। এরা সবাই ফুটবল বিশ্বকে মনে করিয়ে দিক, ফুটবল আরো একভাবে খেলা যায়, সেন্টার ফরোয়ার্ডদেরকে দলীয় পরিকল্পনার মূল অংশে রেখে।
নম্বর নাইন এখন মৃত। নম্বর নাইন দীর্ঘজীবী হোক।
(এই আর্টিকেলটি দ্য অ্যাথলেটিকে প্রকাশিত অ্যালান শিয়েরারের একটি কলামের অনুবাদ। এই লেখাটি যখন প্রকাশিত হবে, ততক্ষণে গ্রুপপর্বের খেলা শেষ। অ্যালান শিয়েরার, ফুটবলের সেরা নম্বর নাইনদের একজন, তাঁর চোখ দিয়ে যেভাবে দেখেছেন আজকের ফুটবল বিশ্বকে, যেভাবে বিশ্লেষণ করেন আজকের যুগের নম্বর নাইনদের, তা-ই এ লেখায় উঠে এসেছে। পোল্যান্ড খেলতে পারেনি শেষ ষোলতে, শেষ করেছে গ্রুপের তলানিতে থেকে। লেভানডফস্কিও এই ইউরোতে পারফর্ম করতে পারেননি সেই অর্থে। এসব কোনো কিছুই লেভানডফস্কি কিংবা আধুনিক যুগের নম্বর নাইন সম্পর্কে অ্যালান শিয়েরারের এই লেখাটির মূল্যমান কমিয়ে দেবে না বলেই বিশ্বাস করি।)