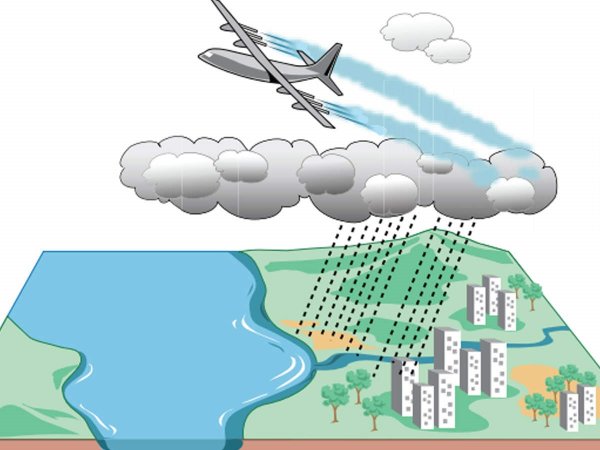“যা দেখছো তা তা না, সব দেখাই জানা না,
এক দুনিয়া, ফানা ফানা, আরেক দুনিয়া যাওয়া মানা।”
২০১৬ সালে মুক্তি পাওয়া ‘আয়নাবাজি’ চলচ্চিত্রটি যারা দেখেছেন, তারা উপরের গানের কলি দুটি চিনতে পারবেন। এটি এই চলচ্চিত্রের কাহিনী সঙ্গীতের প্রথম দুই লাইন। এই চলচ্চিত্রের মূল উপজীব্য ছিল জেল খেটে রোজগার করা একজন মানুষের বিভিন্ন সত্ত্বা, বিভিন্ন পরিচয়। মানে, তাকে চোখের সামনে একরকম দেখা গেলেও পশ্চাতে তার রুপ একেবারেই অন্যরকম।
আমাদের মাথার ভেতরে যে মস্তিষ্ক আছে, তার কার্যকলাপও অনেকাংশে এমনই। আমরা খালি চোখে যা দেখি, আর যা দেখি না, মানে বাস্তবে আসলে যা হচ্ছে, এর মধ্যে অনেক সময়ই রয়ে যায় বিস্তর ফারাক। এসব ক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে অনেক কিছু অসম্ভব, বা অবাস্তব মনে হলেও তা আসলে চোখের ভ্রম মাত্র। তবে ভ্রমটা চোখের কারণেই হচ্ছে তা নয়, আমাদের মস্তিষ্কই এর পেছনে দায়ী। নিচের ছবিটি দেখলেই এর একটি তাৎক্ষণিক প্রমাণ পাওয়া যাবে।

উপরের ছবিটিতে গায়ে গায়ে লাগানো দুটি আলাদা রঙের বার দেখা যাচ্ছে। উপরের বারটি ছাইরঙা আর নিচেরটি ধূসর। কিন্তু আসলেই কি তা-ই? আপাতদৃষ্টিতে দুটি বারের রঙ দু’রকম মনে হলেও আসলে রঙ দুটি এক এবং অভিন্ন। বিশ্বাস না হলে বার দুটির সংযোগস্থলে একটি আঙুল রেখে দেখলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে বিষয়টি। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, এর মতো আরও অনেক অপার রহস্যই প্রকৃতি রেখেছে আমাদের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির অন্তরালে, যার মূলে রয়েছে আমাদের মস্তিষ্কের অদ্ভুত আর জটিল এবং সীমাবদ্ধ কার্যবিধি। আর এ থেকেই জন্ম হয়েছে নিউরোসায়েন্সের।
নিউরোসায়েন্স কী?
নিউরোসায়েন্স হচ্ছে বিজ্ঞানের, বিশেষ করে জীববিজ্ঞানের, সেই শাখা, যা আমাদের স্নায়ুতন্ত্র নিয়ে কাজ করে। এ শাখাটি একাধারে অঙ্গসংস্থানবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, জীবকোষবিদ্যা, রসায়ন, দর্শন, প্রকৌশল, চিকিৎসা, মনস্তত্ত্ব ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত। মূলত আমাদের দেহের বিভিন্ন স্থানে থাকা স্নায়ু এবং মস্তিষ্কের সাথে তাদের স্নায়বিক সঞ্চালনের সম্পর্ক নিয়ে এর কাজকারবার। মোটা দাগে একে বলা যেতে পারে আমাদের অনুভূতির বিজ্ঞান।
নিউরোসায়েন্সের জন্ম ও বেড়ে ওঠা
আণবিক জীববিজ্ঞান এবং কম্পিউটারের ক্রমোন্নয়নের সাথে সাথে বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে স্নায়ুবিজ্ঞানের বিজ্ঞানভিত্তিক অধ্যয়ন শুরু হলেও আসলে এর চর্চা চলে আসছিল আরও অনেক আগে থেকে। খ্রিস্টের জন্মেরও পূর্বে এর পদচিহ্ন পাওয়া গেলেও একে ঠিক চর্চা বা অধ্যয়নের পর্যায়ে ফেলা যায় না কেননা, তখন এটি কেবল বিক্ষিপ্ত চিন্তাভাবনা এবং শল্যচিকিৎসার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিজ্ঞানচর্চার যে প্রধান পদ্ধতি অর্থাৎ কার্যকারণ অনুসন্ধান, সে দৃষ্টিকোণ থেকে এ শাখার উল্লেখযোগ্য অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল ফ্লেমিশ চিকিৎসক আন্দ্রেয়াস ভিসেলিয়াসের হাত ধরে, আরও ভালোভাবে বলতে গেলে তাঁর লেখা ‘On the Workings of Human Body’ বইয়ের হাত ধরে। তবে তার আগে, আরেকটু পেছনে ঘুরে আসা যাক।

প্রাচীন যুগে নিউরোসায়েন্স: হৃদযন্ত্র বনাম মস্তিষ্ক
অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ আগ্রহী ছিল চেতন, অচেতন, অবচেতন কিংবা স্মৃতি, কল্পনা, বিবেক, যেগুলোকে বর্তমান যুগে বিহেভিওরাল সায়েন্স বা আচরণগত বিজ্ঞান বলা হয়, ইত্যাদির ব্যাপারে। এসবের উৎস কোথায় এবং কেন হয় তার প্রেক্ষিতে প্রাচীন মিসরীয়রা মনে করত, হার্ট বা হৃদযন্ত্রই এসবের মূলে, এর প্রমাণও পাওয়া যায় তাদের মমিকরণের প্রক্রিয়া থেকে। মমি করার সময় মগজকে মাথা থেকে বের করে ফেলে দিত তারা, কিন্তু হৃদযন্ত্রকে সংরক্ষণের চেষ্টা করত সর্বপ্রকারে। গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটলেরও একই রকম ভুল ধারণাই ছিল। তিনিও ভাবতেন, সবকিছুর মূলে আছে আমাদের হৃদযন্ত্র, আর মস্তিষ্কের কাজ হচ্ছে এর জন্য প্রয়োজনীয় রক্তের শীতলীকরণ।
তবে উল্টো মত, মানে সঠিক মতও ছিল। যার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৭০০ খ্রিস্টপূর্বের মিসরে এডউইন স্মিথের প্যাপিরাস থেকে। এই প্যাপিরাসে যে ৪৮টি চিকিৎসার বর্ণনা পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ৭টি বিবরণ সরাসরি মস্তিষ্কের সাথে সম্পৃক্ত। যা থেকে বোঝা যায়, তখনও কেউ কেউ বিভিন্ন ব্যাধির সাথে মস্তিষ্কের সংযোগ সম্পর্কে অবগত ছিলেন।

সে যা-ই হোক, হৃদযন্ত্র যে সমস্ত শারীরিক ক্রিয়াকলাপের মূল, গ্রিক চিকিৎসাবিদ হিপোক্রেটিসের আগে কেউ এ ধারণাকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেনি। তিনি বিশ্বাস করতেন, শুধু অনুভূতিই নয়, বরং মানব বুদ্ধিবৃত্তির কেন্দ্রেও রয়েছে এই মস্তিষ্কই। যে হেরোফিলাসকে শারীরতত্ত্বের জনক ধরা হয়, তিনিও মনে করতেন, মস্তিষ্কের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ থেকেই আমাদের যাবতীয় বুদ্ধিবৃত্তির ব্যুৎপত্তি। প্লেটোও ছিলেন মস্তিষ্ক মতবাদের সমর্থক, কিন্তু এরিস্টটলের তুলনামূলক বেশি গ্রহণযোগ্যতার কারণে এরিস্টটলের মতটিই চলে আসছিল অনেককাল যাবত। অনেককাল পরে এটি খণ্ডন হয় রোমান চিকিৎসক গ্ল্যাডেনের মাধ্যমে। গ্ল্যাডেন ছিলেন গ্ল্যাডিয়েটরদের চিকিৎসক। গ্ল্যাডিয়েটরদের চিকিৎসা করার সময়ই তিনি খেয়াল করলেন যে, তাদের মানসিক অবস্থা অবনতির যে ঘটনাগুলো পাওয়া যায়, তার পেছনে মাথায় আঘাতপ্রাপ্তিই প্রধানত দায়ী।
প্রাক-মধ্যযুগ ও মধ্যযুগ: অগ্রগতি রয়েছে চলমান
পরবর্তীতে আনুমানিক ১০০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে প্রখ্যাত চিকিৎসক আবু আল কাসিম আল যাহরাউই (ল্যাটিন ভাষান্তরে আবুলক্যাসিস) তাঁর ৩৫ খণ্ডের কিতাব আল তাশরিফে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্নায়বিক রোগের চিকিৎসার বর্ণনা করে গেছেন। আল কাসিম ছাড়াও নিউরোসায়েন্সের সম্মুখযাত্রায় মধ্যযুগের মুসলিম বিশ্বের ইবনে রুশদ, ইবনে সিনা, ইবনে যুহরদের মতো চিকিৎসকদের অবদানও উল্লেখযোগ্য।

ইউরোপীয় নবজাগরণের সময় ভিসেলিয়াস, রেনে দেকার্ত, টমাস উইলিসের মতো বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকেরা বিজ্ঞানের এ শাখার চলার পথকে রেখেছেন সক্রিয়। ১৬৬৪ সালে প্রকাশিত ‘Anatomy of the Brain’ পুস্তকে টমাস উইলিস মৃগীরোগ, পক্ষাঘাত, বৈরাগ্য এবং শারীরিক প্রতিক্রিয়া (Reflex) এর মতো স্নায়বিক ক্রিয়াগুলো বিশ্লেষণ করেছেন। এই বইতেই তিনি সর্বপ্রথম স্নায়ুবিদ্যা শব্দের প্রচলন করেন। ১৭৭০ এর দশকে ফ্রানয অ্যান্টন মেযমার অ্যানিম্যাল ম্যাগনেটিজম নামক ত্রুটিপূর্ণ কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে কার্যকরী এক চিকিৎসা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন, যা থেকে পরবর্তীতে সম্মোহনের জন্ম হয়।
১৭৯১ সালে বিজ্ঞানী লুইজি গ্যালভানি প্রস্তাবনা দেন, আমাদের স্নায়ু তড়িৎ উদ্দীপনার মাধ্যমে কাজ করে। এর পেছনে অবশ্য ছিল দুটি কারণ: একটি বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে মৃত ব্যাঙের অকস্মাৎ জীবন-স্পন্দনের চিহ্ন এবং অপরটি ইউরোপে বিদ্যুৎ নামক রহস্য সমাধানের উন্মাদনা। আর এ প্রস্তাবনাই পরবর্তীতে বায়োইলেক্ট্রিসিটির শাখা উন্মোচন করে। এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও উল্লেখ্য, সেসময় এ প্রস্তাবনার বিপরীতে আরেক প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আলেসান্দ্রো ভোল্টার অবস্থান আমাদেরকে দেয় ব্যাটারীর আশীর্বাদ, তবে সে আরেক গল্প।
আধুনিক যুগে পদার্পণ: তড়িতের শুভাগমন ও সমগতিতে নিউরোসায়েন্সের ছুটে চলা
এখন যে আমরা জানি স্নায়বিক ক্রিয়ার সঞ্চলন হয় নিউরনের মাধ্যমে, এই নিউরনের সাথে আমাদের সুস্পষ্টভাবে পরিচয় হয় আনুমানিক ১৮৩৭ সালের দিকে, চেক শারীরতত্ত্ববিদ ইয়ান ইভানগেলিস্টা পুরকিনের মাধ্যমে। ১৮৪৩ সালে জার্মান চিকিৎসক এমিল ডু-বোয়া রেমন্ড স্নায়ুর সংকেতের তড়িৎ প্রকৃতির পরীক্ষামূলক প্রদর্শনী করে দেখান। ৬ বছর পরেই এই তড়িৎ সঞ্চলনের গতি মেপে দেখান আরেক প্রখ্যাত জার্মান পদার্থবিদ হারমান ভন হেল্মহোল্টয, ১৮৪৯ সালে।

এ পর্যায়ে এসেই আসলে স্নায়ুবিজ্ঞানের গবেষণা জীববিজ্ঞানের একটি নির্দিষ্ট শাখা হিসেবে গতিপ্রাপ্ত হয় এবং ১৮৬২ সালে পল ব্রোকা আমাদের কথোপকথনের জন্য অপরিহার্য মস্তিষ্কের যে অংশ তাকে চিহ্নিত করার মধ্য দিয়ে একে এগিয়ে নেন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।
১৮৭৩ এ ইতালিয়ান বিজ্ঞানী ক্যামিলো গোলজির হাত ধরে আমরা প্রথম নিউরনের বাস্তব বিবর্ধিত চিত্র দেখতে পাই। আর তাঁর কৌশল অবলম্বন করেই স্যান্টিয়াগো রামোন ই কাহাল প্রস্তাব করেন, আমাদের স্নায়ুতন্ত্র অনেকগুলো স্বতন্ত্র এককের সমন্বয়ে গঠিত আর বিভিন্ন স্নায়ুর নীতি-নির্ধারণী কাজে মস্তিষ্কের প্রধানতম চলকই হচ্ছে নিউরন। এর জন্য ১৯০৬ সালে গলজি এবং কাহাল যুগপৎভাবে নোবেল পুরস্কারও অর্জন করেন। অবশ্য ইতোমধ্যেই ১৮৭৮ সালে মস্তিষ্কের একটি ফোঁড়ার সফল অপসারণের মাধ্যমে স্নায়ুর কাটা-ছেঁড়ায় আধুনিক সময়ের একটি মাইলফলক স্থাপন করে ফেলেছেন স্কটিশ শল্যচিকিৎসক উইলিয়াম ম্যাকইউয়েন।
এসবের মধ্য দিয়েই বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে স্নায়ুবিজ্ঞান স্নায়ুতন্ত্রের একটি অংশ থেকে বের হয়ে বিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়, যা পূর্ণতা পায় ডেভিড রায়খ, ফ্র্যন্সিস শ্মিটদের হাত ধরে। ‘৫০ এর দশকে রায়খ মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকা Walter Reed Army Institute of Research প্রতিষ্ঠানের গবেষণাসূচীতে প্রাথমিক শারীরবৃত্তীয় গবেষণার সাথে মনোরোগের গবেষণাও অন্তর্ভুক্ত করেন। মোটামুটি একই সময়ে শ্মিটও এমআইটির জীববিজ্ঞান বিভাগে স্নায়ুবিজ্ঞানের গবেষণা তালিকাভুক্ত করেন। আর দুরন্ত গতিতে এগোতে থাকে স্নায়ুতন্ত্রের বিজ্ঞানভিত্তিক অধ্যয়ন, যা কি না পরবর্তীতে মস্তিষ্কের রোগের চিকিৎসায় আনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

ফিরে আসি প্রথম ছবির প্রসঙ্গে। এতে দেখা যাচ্ছে দুটি ভিন্ন রঙকে ভিন্ন দেখালেও আসলে তারা অভিন্ন। কিন্তু কেন? এটি জানা যাবে নিউরোসায়েন্স সিরিজের পরবর্তী পর্বে, সাথে থাকবে মস্তিষ্কের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিভ্রান্তিকর এরকম আরও কিছু নমুনা। অথবা এখনই দেখা শুরু করতে পারেন এই সিরিজটি।