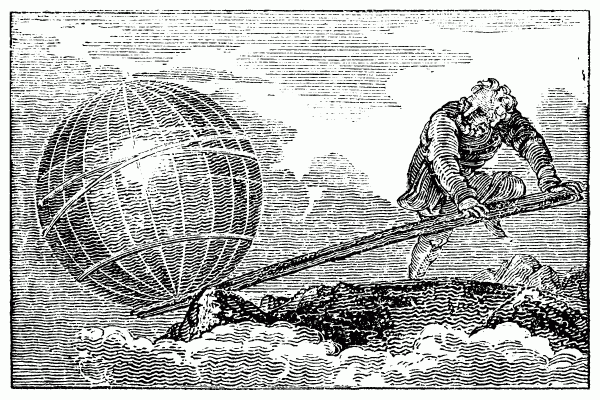এক্স-রে এর সাথে কম-বেশি সবাই পরিচিত। অধিকাংশ মানুষকেই কখনো না কখনো যেতে হয় এক্স-রে মেশিনের নিচে। হাড়-ভাঙ্গা, নিউমোনিয়া, হৃদরোগ সহ বহু রোগের চিকিৎসায় এক্স-রে রিপোর্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া এয়ারপোর্টে ব্যাগ স্ক্যানিং করা হয় এ মেশিন দিয়ে । উৎপাদনখাতে বিমান সহ বিভিন্ন যন্ত্রের বডিতে ত্রুটি খুঁজে বের করতেও ব্যবহৃত হয় এটি।
এক্স-রের গুরুত্ব আসলে বলে বোঝানোর প্রয়োজন নেই। জটিল সব রোগের ক্ষেত্রে এর গুরত্ব বর্ণনা না-ই করলাম, স্রেফ একটু ভাবুন- এটি আবিষ্কৃত না হলে, বেশিরভাগ সময় শরীর কাঁটাছেড়া ব্যতীত ডাক্তারদের পক্ষে জানা সম্ভবই হতো না আদৌ কারো কোনো হাড় ভেঙ্গেছে কী না। এক্স-রে আবিষ্কার যেন মানবজাতির জন্যে আক্ষরিক অর্থেই আশীর্বাদ হয়ে এসেছে। কারণ এ আবিষ্কারটি হয়েছিল অনেকটা সৌভাগ্যবশত, আকস্মিকভাবে। না চাইতেও এটি ধরা দিয়েছে মানুষের কাছে।
বর্তমানে এক্স-রে চিকিৎসাখাত সহ বিভিন্ন খাতে এর প্রয়োগ খুঁজে পেলেও, এটি এসেছে পদার্থবিজ্ঞানের জগৎ থেকে। এক্স-রে একধরনের তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ। এটি ছাড়াও এ রকম তরঙ্গ আরো আছে। যেমন দৃশ্যমান আলো, অতিবেগুনি রশ্মি, বেতার তরঙ্গ ইত্যাদি। এদের অধিকাংশ বৈশিষ্ট্য একইরকম, মূল তফাৎ কম্পাঙ্কে। দৃশ্যমান আলোর তুলনায় এক্স-রের কম্পাঙ্ক অনেক বেশি। দৃশ্যমান আলো ছাড়াও যে আরো অনেক তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের অস্তিত্ব থাকতে পারে এমনটা সর্বপ্রথম বলেছিলেন বিজ্ঞানী জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল। সেটি বলেছিলেন নানা গাণিতিক হিসেব কষে।

বাস্তবে এ ধরনের তরঙ্গের অস্তিত্ব আদৌ আছে কিনা তা তখনো জানতো না মানুষ। তবে সময়ের সাথে সাথে মানুষ এ ধরনের তরঙ্গের খোঁজ পেতে থাকে। হাইনরিখ হার্জ সর্বপ্রথম বেতার তরঙ্গ খুঁজে বের করেছিলেন। পরে এটিই সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছিল মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে। আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় সকল তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ নয়, বরং এক্স-রে। এটি কীভাবে আবিষ্কৃত হয়েছিল সে গল্প জানার জন্যে চলুন উনবিংশ শতকের শেষদিক থেকে একটু ঘুরে আসা যাক।
১৮৯৫ সালের কথা, জার্মান পদার্থবিদ উইলহেম রন্টজেন তখন ক্যাথোড রশ্মি নিয়ে গবেষণায় ব্যস্ত। পদার্থবিজ্ঞানের জগতে ক্যাথোড রে টিউব তখন বেশ সাড়া জাগানো বিষয়। এটি মূলত একটি বায়ুশূন্য টিউব, যার দুই প্রান্তে অ্যানোড ও ক্যাথোড নামে দুটি ধাতব পাত থাকে। এ পাত দুটির মধ্যে উচ্চ মাত্রার ভোল্টেজ প্রয়োগ করলে তাদের মধ্যে আলোর ঝলকানি সহ ক্যাথোড রশ্মির বিকিরণ হয়। এ রশ্মি ছিল মূলত ইলেকট্রনের প্রবাহ, কিন্তু সেটি তখনো জানা ছিল না। কারণ ইলেকট্রন আবিষ্কার হয়েছিল আরো দুই বছর পর। আর সেটি হয়েছিল ক্যাথোড রশ্মি নিয়ে গবেষণার সূত্র ধরেই। সে পথেই এগিয়ে যাচ্ছিলেন বিজ্ঞানীরা।
উৎসাহী পদার্থবিদ হিসেবে রন্টজেনও তাই ক্যাথোড রশ্মি নিয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। পরীক্ষা চালানোর জন্য তিনি সে সময়ের সবচেয়ে উন্নত যন্ত্রপাতি জড়ো করলেন। এর মধ্যে ছিল খুবই উচ্চ ভোল্টেজ সরবরাহ করতে সক্ষম বিদ্যুৎ শক্তির উৎস, বিশেষভাবে নির্মিত উচ্চ তাপ সহনশীল অ্যানোড ইত্যাদি। তিনি ক্যাথোড রশ্মির ফলে তৈরি হওয়া দুর্বল আলোক সংকেত পর্যবেক্ষণ করছিলেন। এ সময় একটি ছোট সমস্যা দেখা দিল। তিনি দেখলেন, কিছু ক্যাথোড রশ্মি এসে টিউবের দেয়ালে আঘাত করছে এবং সেখানে কিছুটা আলোর আভা তৈরি করছে। এটি তার মূল পর্যবেক্ষণকে বাধাগ্রস্ত করছিল।

পর্যবেক্ষণকে আরো সহজ করতে তিনি গোটা ঘরটিকে অন্ধকার বানিয়ে ফেললেন। এরপর মোটা কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলেন যন্ত্রপাতিগুলোকে। কেবল শেষপ্রান্তে একটু খোলা রাখলেন, যেখান দিয়ে তার কাঙ্ক্ষিত আলোক সংকেত আসার কথা। পরীক্ষাটি করার আগে, রন্টজেন একটি কার্ড-বোর্ডে ক্যাথোড রশ্মির প্রতি সংবেদনশীল ফ্লুরোসেন্ট পদার্থের প্রলেপ লাগিয়ে নেন, এগুলোর উপর ক্যাথোড রশ্মি পড়লে এগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠার কথা। এরপর এ কার্ড-বোর্ডের কিছু অংশ কেটে তিনি পরীক্ষায় কাজে লাগান, বাকিটা ফেলে রাখেন কিছুটা দূরের একটি চেয়ারে।
যখন পরীক্ষা শুরু হলো, রন্টজেন লক্ষ্য করলেন অন্ধকার ল্যাবের এক কোনায় কি একটা যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। দেখলেন তার চেয়ারে ফেলে রাখা সে কার্ড-বোর্ডটি। কিন্তু এমনটা কেন হচ্ছে? তার পরীক্ষায় ব্যবহার করা বিদ্যুতের সুইচটি বন্ধ করতেই দেখা গেল হারিয়ে গেছে কার্ড-বোর্ডের উজ্জ্বলতাও। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছিল তার পরীক্ষার সেট-আপ থেকে কোনো একটি শক্তি নির্গত হয়ে কক্ষে ছড়িয়ে পড়ছে, উজ্জ্বল করে তুলছে কার্ড-বোর্ডটিকে। কিন্তু সেটি কী হতে পারে, যা পুরু কালো কাপড়কেও ভেদ করে চলে যাচ্ছে?
এ রহস্যময় শক্তির উৎস যে ক্যাথোড রশ্মি নয়, তা জানতেন তিনি। কারণ এটি প্রমাণিত ছিল যে, ক্যাথোড রশ্মি সাধারণ বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে কয়েক সেন্টিমিটারের বেশি এগোতে পারে না। রন্টজেন আবার চালালেন পরীক্ষাটি। এবার কার্ড-বোর্ডের সামনে একটি মোটা বই রেখে এ রশ্মির গতিরোধ করার চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু লাভ হলো না তাতেও, এ রহস্যময় শক্তি অনায়াসেই ভারী বইটি ভেদ করে চলে গেল, উজ্জ্বল করে তুলল কার্ড-বোর্ডটিকে। একই সাথে তিনি দেখতে পেলেন, তার ল্যাবে রাখা সব ফিল্ম নেগেটিভগুলোও এক্সপোজ হয়ে গেছে। এটি যে এ অজানা শক্তিরই কর্ম, তা বুঝতে আর বাকি রইল না তার।

রন্টজেন বুঝতে পারলেন, সম্পূর্ণ নতুন একটি ঘটনার সাক্ষী হয়েছেন তিনি। কিন্তু তখনই এ নিয়ে শোরগোল না ফেলে তিনি এ ধাঁধার সমাধানে সচেষ্ট হলেন। রাত-দিন এক করে তিনি পড়ে রইলেন এই অজানা রশ্মি নিয়ে। একের পর এক পরীক্ষা চালিয়ে তিনি এর আচরণ পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। অবশেষে ১৮৯৫ সালের ক্রিসমাস ইভের দিন মোটামুটি প্রস্তুত হলেন তিনি। তার স্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানালেন গবেষণাগারে। যন্ত্রাদি চালু করে তার স্ত্রীর হাতটিকে রাখলেন একটি নতুন ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর। প্রায় চৌদ্দ মিনিট ধরে এক্স-রে ফেলা হলো তার হাতে।
ফিল্মটি যখন ডেভেলপ করা হলো, দেখা গেল একটি হাতের ছবি এসেছে, এসেছে আঙ্গুলে থাকা আঙটির ছবিও। তবে এটি সাধারণ কোনো হাত ছিল না, হাতের প্রত্যেকটি হাড় দেখা যাচ্ছিল বরং। আর আঙটিটি যেন ঝুলে আছে একটি হাড়ের চারিধারে। ছবিটি দেখামাত্র মিসেস রন্টজেন আর্তনাদ করে উঠেছিলেন , “হায় খোদা! আমি মৃত্যু দেখেছি।” রন্টজেনের আবিষ্কারের কথা প্রকাশিত হওয়ার পর, তার স্ত্রীর হাতের সেই ছবিটি পৃথিবীব্যপী ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল।
এক্স-রে আবিষ্কার করে ফেললেও, রন্টজেন এ রশ্মিকে সম্পূর্ণ বুঝতে পারেননি। তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি অকপটে স্বীকার করেছিলেন, “আমি আসলে ঠিক জানি না, এটি কী বা কেন। তাই এটিকে আমি ‘এক্স-রশ্মি’ নাম দিয়েছি।” যেহেতু এক্স (X) বীজগণিতে অজানা মান নির্দেশ করে, তাই এমন নামকরণ। তবে তিনি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন যে, তার এ আবিষ্কারটি চিকিৎসাবিজ্ঞানে বেশ উপযোগী হয়ে উঠতে পারে। এটি জেনেও একজন আদর্শ বিজ্ঞানীর মতো তিনি কোনো প্যাটেন্টের আবেদন করেননি। সকলের জন্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন তার এ আবিষ্কারকে।

শীঘ্রই জেনারেল ইলেকট্রিক, সিমেন্স সহ বিভিন্ন কোম্পানি বাণিজ্যিকভাবে এক্স-রে মেশিন তৈরি করতে শুরু করে। ডাক্তাররা ভাঙ্গা হাড়, শরীরে বুলেটের অবস্থান ইত্যাদি নির্ণয়ে রন্টজেনের এক্স-রশ্মি ব্যবহার করতে শুরু করেন। মেডিকেল ইমেজিংয়ের পথচলা শুরু হয় এই আবিষ্কারের মধ্য দিয়েই। যার ধারাবাহিকতায় বর্তমানে এসেছে এম.আর.আই, ই.সি.জি, সিটি স্ক্যান সহ অনেক পরীক্ষা পদ্ধতি, যেগুলো বর্তমানের চিকিৎসাখাতের অপরিহার্য উপাদান হয়ে ওঠেছে।
রন্টজেন নিজে না পারলেও, পরবর্তীকালের গবেষকরা এক্স-রের মূলনীতি জানতে সক্ষম হয়েছেন। রন্টজেনের পরীক্ষণে যখন শক্তিশালী ক্যাথোড রে অর্থাৎ অত্যন্ত উচ্চ গতিতে আসা ইলেকট্রনের প্রবাহ আঘাত হেনেছিল অন্যপ্রান্তের অ্যানোডে, তখন ইলেকট্রনগুলোর গতিশক্তি খুবই উচ্চ কম্পাঙ্কের তড়িৎ-চুম্বক শক্তি অর্থাৎ এক্স-রে আকারে নির্গত হয়েছিল। যেহেতু এদের কম্পাঙ্ক অনেক বেশি (বা তরঙ্গদৈর্ঘ্য অনেক ক্ষুদ্র) তাই এ রশ্মি বই, শরীরের মাংস ইত্যাদি ভেদ করে যেতে পারে। কিন্তু হাড় ভেদ করতে পারে না বলে তার ছায়া রেখে যায় ফটোগ্রাফিক প্লেটে।

এক্স-রে আবিষ্কারের জন্যে ১৯০১ সালে ইতিহাসের প্রথম নোবেল প্রাইজটি ধরা দেয় রন্টজেনের হাতে। যদিও এ আবিষ্কারটিকে রন্টজেনের জন্যে সৌভাগ্য হিসেবে দেখা যেতে পারে। এর আগে তাকে যদি বলা হতো, এমন কোনো তরঙ্গ আবিষ্কার করুন যা শরীরের মাংস ভেদ করে চলে যেতে পারবে, রন্টজেন হয়তো তা পারতেন না। তিনি জানতেনই না তাকে কী করতে হবে বা কীভাবে এগোতে হবে। তবে তিনি যে তার এ অদ্ভুতুড়ে পর্যবেক্ষণটির মাহাত্ম্য অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং এ নিয়ে আরো কাজ করতে লেগে ছিলেন সেটিও বেশ গুরুত্বপূর্ণ।
মজার বিষয় হচ্ছে, পরবর্তীতে টেসলা, লেনার্ড সহ বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানী দাবি করেছেন যে, তারা রন্টজেনের আগেই এক্স-রের ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেছেন। কিন্তু তাদের কেউই এটিকে গুরুত্ব দিয়ে অধিকতর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাননি, যেটি রন্টজেন করেছিলেন। এখানে তাই লুই পাস্তুরের কথাটি খাটে, তিনি বলেছিলেন, accidents favor the prepared mind! অর্থাৎ যারা প্রস্তুত থাকে, তারাই দৈবক্রমে পাওয়া সুযোগকে কাজে লাগাতে পারে। রন্টজেন প্রস্তুত ছিলেন বলেই, এক্স-রশ্মির ক্ষেত্রে এ সুযোগটি নিতে পেরেছিলেন তিনি। তাই এ আবিষ্কারের কৃতিত্ব পাওয়ার যোগ্য দাবিদারই তিনি।



.jpeg?w=600)