
১
প্যাচপ্যাচে কাঁদা আর বৃষ্টি মাথায় নিয়ে যখন কুতুপালং ক্যাম্পে ঢুকছিলাম, ততক্ষণে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে শুরু করেছে। ক্যাম্পের প্রবেশমুখে দাতা সংস্থাগুলোর গাদা গাদা সাইনবোর্ড। দু’ধারের গুটিকয়েক টং দোকান, সেখানে ভিড় করেছে পুরুষ রোহিঙ্গারা। ইটের রাস্তা দিয়ে যতই ভিতরে ঢোকা যায়, ততই যেন শরণার্থী শিবিরের পরিবেশটা গাঢ় করে ফুটে উঠতে শুরু করে। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষেরা তো আছেই, শিশু-কিশোরের সংখ্যাও যেন বেশি। সঙ্গে ছিল এক রোহিঙ্গা গাইড। কাজ চালানোর মতন বাংলা বলতে পারে সে। জিজ্ঞেস করলাম, ত্রাণ দিচ্ছে কোথায়? দুই মিনিটের মধ্যে সেখানে নিয়ে গেল। যা দেখলাম, তা কল্পনার বাইরে।
ত্রাণের জন্য একটি করে ট্রাক আসছে, সেটার পিছনে কয়েক হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থী। সারিবদ্ধ করে ত্রাণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে সেনাবাহিনী। কিন্তু সেটা করতে গিয়েও বিপত্তি। ঠেলাঠেলি তো রয়েছেই, ত্রাণের প্যাকেট ছিনিয়ে নেওয়া কিংবা একবার পেয়েও আরেকবার নিতে আসার ঘটনা হরহামেশাই ঘটছে। তরুণ সেনা সদস্যরাও যেন অসহায় তাদের সামলাতে গিয়ে। মাঝে এই লাঠি নিয়ে তাড়া দেন, পরক্ষণেই আবার মাথায় হাত বুলিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু যার পেটে ক্ষিধে, সে কি আর ভদ্রতা বোঝে!
এসব যখন ভাবছি, চোখের কোণ দিয়ে দেখলাম বাচ্চা বয়সী কেউ দাঁড়িয়ে আছে। ফিরতেই চোখ পড়ল সাত-আট বছরের এক বাচ্চা মেয়ে, কোলে এক-দুই বছরের একটি বাচ্চা। এক হাতে তাকে সামলাচ্ছে, আরেক হাতে ত্রাণের বাক্স। জিজ্ঞেস করতেই জানলাম, কোলের বাচ্চাটি তার ভাই। ক্যাম্প পর্যন্ত তার মা আসতে পেরেছে তাদেরকে নিয়ে। বাবার কোনো খোঁজ নেই। মায়ানমার সেনাদের অত্যাচারের খানিক আঁচ পেলাম তার কথাতেই। কথার মাঝে একটি কথা এখনও কানে বাজে, ‘আমি আর বার্মাত ফেরত ন যাইতে চাই।’
২
লিয়ার লেভিনের চিত্রগ্রহণ নিয়ে তারেক মাসুদের তৈরি ‘মুক্তির গান’ তৎকালীন মুক্তিযুদ্ধের সময় শরণার্থী শিবিরে বাংলাদেশিদের দুরাবস্থার কথা মনে করিয়ে দেয়। একটি সাংস্কৃতিক জোট ট্রাকে চড়ে যুদ্ধের পুরো নয়টি মাস কিভাবে সীমান্ত এলাকা ধরে ঘুরেছে, মুক্তিযোদ্ধা-শরণার্থীদের গানের মাধ্যমে উজ্জীবিত করেছে তার সত্যিকারের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন লেভিন। সেই প্রামাণ্যচিত্র থেকেই টের পাওয়া যায় শরণার্থী শিবিরের অবস্থা কতটা করুণ হতে পারে। রোহিঙ্গা ক্যাম্পে গিয়ে সেটা মনে পড়ে গেল আবারও। যতই ভিতরে ঢুকছিলাম, মাঝে মাঝে মায়ানমার আর্মিদের নির্যাতনের প্রমাণ দেখছিলাম নিজের চর্মচোখে। ক্যামেরা দেখে অনেকেই সামনে এগিয়ে আসছিল।

রোহিঙ্গাদের জন্মনিবন্ধন সনদ; Source: Islam Shami
গাইডকে বললাম, আর্মিদের কাছে সরাসরি নির্যাতনের শিকার হয়েছেন এমন কয়েকজনকে লাগবে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে তিনটি দলকে হাজির করলেন তিনি। এর মধ্যে একটি পরিবারও আছে। একটু খেয়াল করতেই দেখলাম, একজন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছেন। জিজ্ঞেস করতেই পরনের লুঙ্গিটা হাঁটু পর্যন্ত উপরে তুলে দেখালেন। কিন্তু বীভৎস সেই দৃশ্য মুহূর্তের বেশি দেখার ক্ষমতা হয়নি। জানা গেল, আরাকান আর্মিরা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে অত্যাচার করেছে তার উপর। একজনের কপাল আর মাথার মাঝ বরাবর সেলাইটা কাটা দেখলাম, কিন্তু শুকোয়নি পুরোপুরি। তাকে গুলি করেছিল সামরিক জান্তারা। কিন্তু ভাগ্যের জোরে বেঁচে গিয়েছেন। গুলি মাথায় লাগেনি, চামড়া খানিক গভীর করে ছিড়ে বের হয়ে গেছে। বাংলাদেশে আসতে পেরে এ যাত্রা জানে বেঁচেছেন তিনি।
এক লোক কিছু একটা বলতে চাইছিলেন বারবার। তাকে সুযোগ করে দিতেই হড়বড় করে কথা বলা শুরু করলেন, কান্নাকাটি শুরু করলেন। যা বলছিলেন তা বোঝা কষ্টসাধ্য । তখন গাইড বুঝিয়ে দিল সবকিছু। তার ছেলেকে গুলি করে হত্যা করেছে সেই দেশের সেনারা। এগিয়ে এসে মৃত সন্তানের ছেড়া ছবিও দেখালেন। পিঠজুড়ে রক্তে ভরা সেই ছবি বেশিক্ষণ দেখার মতো অবস্থা ছিল না। লোকটি জানালেন, কোনো কারণ ছাড়াই হত্যা করেছে আর্মি। ঘর থেকে বের হতেই গুলি করে। ঘরবাড়িও পুড়িয়ে দেয়।
লোকটির আরও একটি ছেলে আছে। তার অবস্থাও খারাপ। গুলি করে হত্যা না করলেও আধমরা করে দিয়েছে। ক্যাম্পে জায়গা পাওয়া পলিথিনের অস্থায়ী অন্ধকার ঘর থেকে যখন ছেলেটিকে তিনি বের করলেন, চেহারাটা যন্ত্রণায় কাতর ও ফ্যাকাশে হয়ে ছিল। ঠিকমতো হাঁটতেও পারছিল না। দু’পাশে দুজন ধরে খানিকটা সোজা হয়ে ছিল। জানলাম, মায়ানমারের আর্মিরা তার পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থেকেছে, পিটিয়েছে। বেঁচে গেলেও সেই থেকে জ্বর, এখনও সারেনি। শেষ পর্যন্ত তার ভাগ্যে কী হয়েছিল জানা হয়নি আমার।

বাবার ফোনে নিহত পুত্রের ছবি; Source: Islam Shami
এক মহিলা সাথে করে বড় একখানা কাগজ আনলেন। ওটাই মায়ানমারে আরাকানদের জন্ম নিবন্ধন সনদ। রোহিঙ্গারা কতটা নির্যাতিত আরাকানে সেটা জানা গেল তার কাছে। ওই মহিলা বলেন, ‘আমরা সন্তানদের বিয়ে দিতে পারি না। বিয়ে দিতে গেলে আর্মিদেরকে টাকা দিতে হয়। বাচ্চা নিতে গেলেও টাকা দিতে হয়। আরাকানের বাইরে যেতে হলে আগে থেকে কাগজপত্তর ঠিক করতে হয়।’
সেনাবাহিনীকে দেওয়ার মতন টাকা সবার থাকে না। তাই সন্তানদের বিয়েও দেওয়া হয় না। অনেকে আবার জমি বিক্রি করে বিয়ে দেন। এই মহিলার সে অবস্থা ছিল না। তাই চুরি করে পাঁচ ছেলেমেয়ের তিনজনকে পাঠিয়ে দিয়েছেন মায়ানমারের বাইরে। তিনজনের দুজন ভারতে, একজন নেপালে। সেখানেই বিয়ে করেছে তারা। এজন্যও বিপদে পড়তে হয়েছে তাদেরকে। সেনারা নিয়ম করে পরিবারের সদস্য সংখ্যা হিসাব রাখে। কম হলে কারণ দর্শাতে হয়। যখন তারা জেনেছে, তিন সন্তানকে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে তখন জন্ম সনদ থেকে নামই কেটে দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ আজীবনের জন্য মায়ানমারের পরিচিতি বাতিল করা হয়েছে। আর কখনই তারা নাড়ির কাছে ফিরতে পারবে না।
সন্ধ্যা গড়িয়ে আসছিল। ওদিকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে বলে দেওয়া হয়েছে পাঁচটার বেশি সময় না থাকতে। কিন্তু ততক্ষণে ছ’টা বেজে গেছে। তাই চাইলেও আর থাকা যাবে না। ফেরার পথ ধরলাম। নোংরা, স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশে অসহায়, করুণ মুখগুলো বারবার ঘুরেফিরে মনে আসছিল। সন্ধ্যাবাতি জ্বলেছে প্রত্যেকটি শরণার্থীর ঘরে। কিন্তু তাদের ঘরে ফেরার আলো কবে জ্বলবে তা বিধাতা ছাড়া আর কেউ জানে না।
৩
পরদিন সকাল সকাল রওয়ানা দিলাম বালুখালী ক্যাম্পের দিকে। কুতুপালং ছাড়িয়ে আরও অনেকখানি ভিতরে যেতে হবে। বলে রাখা ভাল, কুতুপালং সরকারীভাবে রেজিস্ট্রিকৃত স্থায়ী ক্যাম্প। বালুখালী এখনও অস্থায়ী। কুতুপালং দেখার পর বালুখালীর অবস্থা না দেখে পারছিলাম না। কক্সবাজারের লাবণী পয়েন্ট থেকে ঘন্টাখানেকের পথ। কুতুপালং ক্যাম্পের সামনে থেকে তুলে নিলাম আমার গাইডকে।
জায়গামত পৌঁছানোর পর হাঁটা শুরু করলাম। পাকা রাস্তা থেকে আরও প্রায় এক-দেড় কিলোমিটার ভিতরে হেঁটে মূল ক্যাম্প। কিন্তু শরণার্থীদের ভিড় মূল রাস্তা থেকেই। একটি কথা বলা হয়নি, যখন রাস্তা দিয়ে আসছিলাম ক্যাম্পের পথে, তখন রাস্তার দু’ধারে নারী রোহিঙ্গাদের বসে থাকতে দেখেছি, জেনেছি তারা ভিক্ষার জন্য বসে আছে। অথচ এই মানুষগুলো একসময় কতই না সচ্ছল ছিল!

ত্রাণ নেওয়ার জন্য লাইন ধরেছে শরণার্থীরা; Source: Islam Shami
বালুখালী ক্যাম্পের প্রবেশমুখে ছোট্ট টেবিল নিয়ে বসে আছেন দুই তরুণ। মূলত প্রতিদিন কতজন করে এই ক্যাম্পে আসছে তাদের হিসাব রাখাটাই তাদের কাজ। খাতা খুলে দেখালেন কবে, কতজন এখানে এসেছে। সেই তালিকায় ১০০ জনের নিচে যেমন আছে, হাজারের উপরেও আছে। এখানেও একই অবস্থা, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে পুরো ক্যাম্পের ত্রাণ বিতরণ ও নিয়ন্ত্রণ চলছে। চিকিৎসকদের দলও দেখলাম, যারা কলেরা সহ বিভিন্ন রোগের প্রতিরোধে শরণার্থীদের সাহায্য করতে এসেছে। ঘুরে ঘুরে দেখার এক পর্যায়ে এক সেনাসদস্য পইপই করে বলে দিলেন, পাঁচটা মানে পাঁচটাই। আগের দিনও নাকি রোহিঙ্গা শরণার্থীরা নিজেদের মধ্যে নিজেরা মারামারি করে ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা করেছে। বাইরের অনেকে নাকি ছিনতাইয়ের অভিযোগও করেছে। তাই সূর্য ডোবার আগেই যেন ফিরে আসি।
আশ্বাস দিয়ে গাইডকে সঙ্গে নিয়ে সামনের পথ ধরলাম।
৪
হাঁটতে হাঁটতে বাজারের মধ্যে দিয়ে যেতে হল। যেখানে তরিতরকারি তো বটেই, মাছের বাজার পর্যন্ত আছে। সবই এই রোহিঙ্গাদের। ত্রাণের আশায় বসে না থেকে নিজেরা নিজেরাই শুরু করে দিয়েছে ব্যবসা। তাতে যদি কিছু আর্থিক যোগ হয়!
শুনেছিলাম, এখানে নাকি অস্থায়ী স্কুল গড়েছে ইউনিসেফ। রোহিঙ্গা শরণার্থী শিশুদের পড়াশোনা ও মনন বিকাশের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতেই এই উদ্যোগ নিয়েছে আন্তর্জাতিক সংস্থাটি। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার। শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন হওয়ায় স্কুলের কার্যক্রমটা দেখা হল না। কিন্তু বাইরে থেকে স্কুল দেখলাম, বিভিন্ন পোস্টারের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম বোঝার চেষ্টা করলাম। এখানে পড়ে এমন কয়েকজনের সাথে কথাও বলা হল। তারা জানাল, স্কুলে মূলত ইংরেজি ও বার্মিজ ভাষায় পড়াশোনা করানো হয়। অথচ আরাকানে তাদের কোনো স্কুলই ছিল না!

কুতুপালং রোহিঙ্গা ক্যাম্প; Source: Islam Shami
শিক্ষার্থীদের একজন বলল, ‘আরাকানে আমাদের পড়াশোনা বলতে মক্তবের আরবি শিক্ষা। এর বাইরে আমাদের পড়াশোনার কোন সুযোগ নেই। কোন স্কুল নেই।’
এই দুর্যোগের মধ্যেও তাদের নতুন কিছু শেখা হচ্ছে। এটাও অনেক আনন্দ দিচ্ছে তাদের। দুই-তিনজন মিলে গলা মিলিয়ে খানিক গেয়েও শোনালো নতুন স্কুলের পড়া। আহা চোখে কী স্বপ্ন, কী সরলতা, কী নিষ্পাপ!
সময় ফুরিয়ে আসছে, যেতে হবে। কী মনে হতেই পাশের উঁচু টিলা উঠলাম। উপর থেকে পুরো ক্যাম্পটা দেখা যায়। কী বিস্তৃত, কী অসামান্য। অথচ কী করুণ। এখানকার প্রত্যেকটি মানুষ একেকটি নির্যাতনের গল্প নিয়ে ঘুরছে, যা লিপিবদ্ধ করার ক্ষমতা নেই কারও। নিজের মাটি ছেড়ে সীমান্তের ওপারে এসে কতটা কষ্ট আর ফেরার টান অনুভূত হচ্ছে তা মুখপানে তাকালেই কাঁচের মতো সহজে দেখা যায়।
অন্ধকার হয়ে গেছে, হাঁটা শুরু করলাম। প্রার্থনা করি, এ মানুষগুলোর সূর্য একদিন ঠিকই উঠবে।
ফিচার ইমেজ: United Nations News

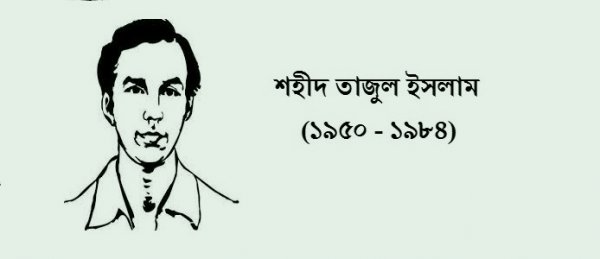






.jpg?w=600)