
কাজের ফাঁকে, ক্লাসের ফাঁকে অথবা অবসর সময়ে এক কাপ ধূমায়িত চা না হলে কাজে যেমন মনোযোগ আসতে চায় না, ঠিক তেমনি আবার অবসরও কাটতে চায় না। আর আড্ডার কথা তো বলাই বাহুল্য, আড্ডায় বসে ঠিক কত কাপ চা পান করা হয় সেটার বোধহয় হিসেব থাকে কারোরই। অবসর সময়ে এক হাতে গল্পের বই বা পত্রিকা থাকলে আরেক হাতে চায়ের কাপ থাকাটাই যেন স্বাভাবিক। চা পান করার সাথে সাথেই যেন ক্লান্তি হয় উধাও। শুধু ক্লান্তিই নয়, চায়ের রয়েছে নানা উপকারী ক্ষমতাও। তবে চীন দেশের এই পানীয় ঠিক কবে বাঙালীর সারাদিনের সঙ্গী হয়ে উঠলো? আর সেটা চীন থেকে এ দেশে এলোই বা কীভাবে?

ক্লান্তি দূর করতে চাই এক কাপ চা; Source: Wiro.Klyngz
চীনা পানীয় হলেও চা এ দেশে চীনারা আনেনি, এনেছে ব্রিটিশরা। এ কথা অবশ্য কারোরই অজ্ঞাত নয়। বাঙালীকে ব্রিটিশদের ‘চা খাওয়া শেখানো’ এই গল্প তো মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত। প্রথমে এ দেশীয় স্থানীয় মানুষদেরকে ডেকে এনে ফ্রি চা পান করানো হতো এবং এভাবে একপর্যায়ে বাঙালি চা পানে অভ্যস্ত হয়ে গেলে এরপর ব্রিটিশ সাহেবরা বললেন, “চা খেতে চাও? বেশ তো, কিনে খাও না!” বলাই বাহুল্য, লোকমুখে প্রচলিত এই গল্পের সত্যতা যাচাই করা সম্ভব নয় আজ।
তবে বাংলাদেশ তথা এই উপমহাদেশে চা পানের প্রচলন ঘটাতে ব্রিটিশরা হাতে নিয়েছিল বিশাল বিজ্ঞাপনী আয়োজন, যা ছিল সেই যুগের সবচেয়ে বড় বিপণন কৌশল। চমক দেওয়া ভাষায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতিরঞ্জিতভাবে চায়ের গুণকীর্তন করে প্রচারপত্রে ছেয়ে ফেলা হয় রাস্তাঘাট, রেলস্টেশন সর্বত্র। বিজ্ঞাপনী চটকে মানুষকে চা পান করাতে মরিয়া হয়ে ওঠে ব্রিটিশ কোম্পানিগুলো।

চায়ের প্রসার ঘটাতে ব্রিটিশরা চটকদার বিজ্ঞাপনে ছেয়ে ফেলেছিলো সর্বত্র; Source: bdscraps
চীনে চায়ের নাম ছিলো চীনা উচ্চারণে ‘চি’, এই ‘চি’ আমাদের এই অঞ্চলে এসে হয়ে যায় ‘চা। চীনে চায়ের প্রচলন ছিলো আরো আগে থেকে, তবে ১৬৫০ সালে প্রথম এর বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়। ভারতবর্ষে ১৮০০ সালের প্রথমদিকে চা চাষ শুরু হয়, ইংরেজরাই শুরু করে, আসামের পাহাড়ি ঢালে। এর ধারাবাহিকতায় ১৮২৮ সালে চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর তীরে চা চাষের জন্যে জমি বরাদ্দ নেয় তারা। কিন্তু বিভিন্ন কারণে চাষ শুরু করতে বিলম্ব হয়। এরপর ১৮৪০ সালে চট্টগ্রাম ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় একটা চা বাগান বানানো হয়েছিলো বটে, কিন্তু সে বাগান টেকেনি, বন্ধ হয়ে যায় চালুর পরপরই।
১৮৩৯ সালে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের সাথে এ দেশীয় কিছু ধনাঢ্য ব্যবসায়ী মিলে প্রতিষ্ঠা করেন ‘অসম টি কোম্পানী’, যাদের মধ্যে ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রপিতামহ), বাবু মতিলাল শীল, হাজী হাশেম ইস্পাহানী (এদেশের ইস্পাহানী গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা) প্রমুখ। আমাদের দেশে সিলেটের মালনীছড়ায় প্রথম ১৮৫৪ সালে চা বাগান গড়ে তোলা হয়। ঐ সময় উপমহাদেশে চা চাষে চীন থেকে চারা কলকাতা বোটানিক্যাল গার্ডেনে আনা হয় এবং চা বাগানগুলোতে পাঠানোর জন্যে চারা উৎপাদন করা হয়, কিন্তু অধিকাংশ চারাই মারা যেতো। ফলে স্থানীয় জাত খুঁজতে শুরু করেন বিশেষজ্ঞরা।

দেশের প্রথম চা বাগান, সিলেটের মালনীছড়া; Source: Hason Raja
এরই মধ্যে ১৮৫৬ সালের ৪ জানুয়ায়ি সিলেটের চাঁদখালি টিলা, খাসি ও জৈন্তা পাহাড়ে বন্য প্রজাতির চা গাছের সন্ধান পাওয়া যায়। এ আবিষ্কারের ফলে ইউরোপীয় চা বণিক ও ব্রিটিশ প্রশাসনে সাড়া পড়ে যায়। প্রাকৃতিক পরিবেশে চা গাছ পাওয়া যাওয়ায় বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিত হন যে সিলেটই চা চাষের জন্যে উপযুক্ত জায়গা। এরপর শুরু হয় ব্যাপকভাবে চায়ের চাষ। মজার ব্যাপার হলো, আমরা যে চা পান করি তা চীন থেকে আগত চা নয়, সেটা মূলত এ দেশীয় চা, যেটা কিনা চীনা চায়ের থেকেও অনেক উৎকৃষ্ট মানের বলে প্রমাণিত।

পাহাড় থেকে নেমে আসা একটি চা বাগান; Source: Asif Mahmud Anik
চা চাষের জন্যে চাই মৌসুমী জলবায়ু, প্রচুর বৃষ্টিপাত আর পাহাড়ের ঢালু জমি। কেননা চা গাছের গোড়ায় পানি জমে থাকলে চা গাছ বাঁচে না। পাহাড়ের ঢালু জমি বৃষ্টির পানি জমতে দেয় না। তবে পানি নিষ্কাশনের ভাল ব্যবস্থা যদি করা যায় তবে সমতল ভূমিতেও চা চাষ করা যায়, যে কারণে আমাদের দেশে পঞ্চগড় জেলার সমভূমিতেও গড়ে উঠেছে চা বাগান।
চা গাছ যদি না ছাঁটা হয় তবে তা প্রায় ২০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। তবে চা বাগানের গাছকে এতো বড় হতে দেওয়া হয় না, কারণ এতে গাছ হাতের নাগালের বাইরে চলে যাবে। গাছকে ছেঁটে ৪ ফুট উচ্চতায় সীমিত রাখা হয়, যা দেখতে অনেকটা ঝোপের মতো হয়। ফলে চা শ্রমিকরা গাছের উপরকার পাতা হাত দিয়ে ছিঁড়তে পারে।

দুটি পাতা একটি কুঁড়ি ছিঁড়তে হয় চা শ্রমিকদের; Source: anandabazar
চা পাতা ছেঁড়ার নিয়ম হলো দুটি পাতা ও একটি কুঁড়ি একইসঙ্গে তোলা। এটি ঠিকভাবে করতে না পারলে চায়ের মান নষ্ট হয়ে যায়। কাজটি খুবই শ্রম ও ধৈর্য্য সাপেক্ষ এবং দক্ষতার ব্যাপার। একইসঙ্গে এই তিনটি জিনিস মহিলারাই ভাল দেখাতে পারেন। ফলে বাগান কর্তৃপক্ষ এ কাজে সবসময় মহিলাদেরই নিয়োগ দিয়ে থাকে। চায়ের পাতাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়- Broken, Fannings এবং Dust। এগুলো যথাক্রমে বড় থেকে ছোট আকারের পাতাকে নির্দেশ করে। সবথেকে ছোট আকারের পাতা মূল্যবান হিসেবে বিবেচিত।

যথাক্রমে Broken, Fannings এবং Dust। ছোট পাতার চাহিদা ও মূল্য বেশি; Source: Arne Hückelheim
উনিশ শতকের ষাটের দশকের পর থেকে চা শিল্প দারুণভাবে বিকশিত হতে শুরু করে। ভাল মানের রপ্তানিযোগ্য এ দেশের চা শিল্পে ব্রিটিশ শ্বেতাঙ্গরা ব্যাপকভাবে বিনিয়োগ করা শুরু করে। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে চা শিল্পে বিনিয়োগ ক্যালিফোর্নিয়ার গোল্ডরাশের সাথে তুলনীয় হতে থাকে। অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, নাবিক সবাই চা শিল্পে বিনিয়োগ করা শুরু করেন।
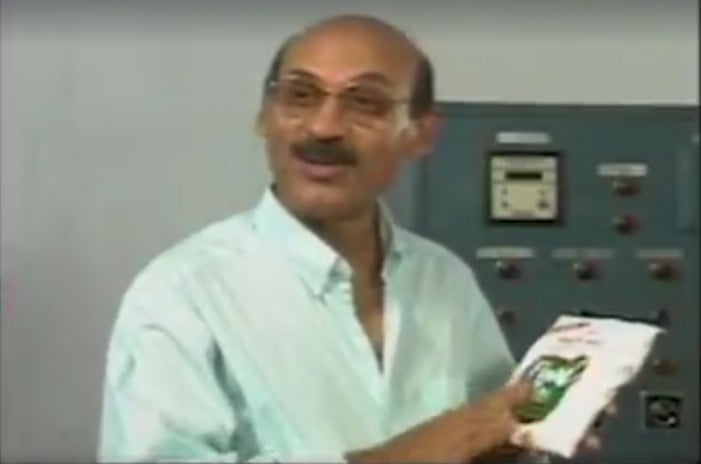
নব্বইয়ের দশকের জনপ্রিয় টিভি বিজ্ঞাপন ‘ফিনলে চা, আসল চা’; Source: Finlay Tea
ইউরোপের নামীদামি নানা কোম্পানি এ দেশের চা বাগানগুলোতে বিনিয়োগ করে, যার মধ্যে রয়েছে জেমস ফিনলে (নব্বই দশকের জনপ্রিয় বিজ্ঞাপন ‘ফিনলে চা, আসল চা’ এই জেমস ফিনলে কোম্পানির চা), ডানকান ব্রাদার্স, অক্টাভিয়াস স্টিল, ম্যাকলিওড এন্ড কোম্পানি ইত্যাদি সহ প্রায় আঠারটি বিদেশী কোম্পানি। এসব কোম্পানি সিলেট অঞ্চলে আরো প্রতিষ্ঠা করে বিলেতি প্রযুক্তির কারখানা আর চমৎকার সব বাংলো, যার তুলনা কোনো রিসোর্টের সাথেই চলে না।

চা বাগানের বাংলো, চা কারখানা এবং চা গবেষণা ইনস্টিটিউট; Source: Asif Mahmud Anik
এখন বাংলাদেশে আছে মোট ১৬২টি চা বাগান। এর ভেতরে মৌলভিবাজারেই ৯০টি, হবিগঞ্জে ২৩, সিলেটে ১৮, চট্টগ্রামে ২১ আর সমতল জেলা পঞ্চগড়ে ৯টি। সারা বিশ্বে বাংলাদেশের চায়ের ব্র্যান্ডিং ‘সিলেট টি’ নামে পরিচিত। এ দেশের চা সারা বিশ্বে আরো জনপ্রিয় করতে বাংলাদেশ চা বোর্ড ‘শ্রীমঙ্গল টি’, ‘বান্দরবান টি’ আর ‘পঞ্চগড় টি’ নামে তিনটি ব্র্যান্ড তৈরীর পরিকল্পনা নিয়েছে।
চায়ের বিপণন ব্যবস্থা অন্য পণ্যের থেকে আলাদা। সাধারণত অন্য কোনো কৃষি পণ্য সরাসরি বাগান বা ক্ষেত থেকে নিয়ে বাজারে বিক্রি করা হয়। চায়ের ক্ষেত্রে সমস্ত চা বাগানের মালিকগণ তাদের উৎপাদিত চা নিয়ে আসেন চট্টগ্রামের ‘চা নিলাম কেন্দ্র’তে। এরপর নিলাম কেন্দ্রে তারা যে যার উৎপাদিত চায়ের নমুনা প্রদর্শন করেন, নমুনা দেখে নিলামে আসা নিলামকারীরা দাম হাঁকেন এবং লট ধরে চা কিনে নেন। কিনে নেয়ার পর ক্রেতা কেনা চায়ের মান অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেন তিনি সেগুলো রপ্তানি করবেন নাকি স্থানীয় বাজারে ছাড়বেন। চট্টগ্রামের পাশাপাশি সম্প্রতি শ্রীমঙ্গলেও দেশের দ্বিতীয় চা নিলাম কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

চট্টগ্রামের চা নিলাম কেন্দ্রে চলছে নিলাম; Source: প্রথম আলো
বাংলাদেশে চা নিয়ে গবেষণা, চা উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সহ নীতি প্রণয়নের কাজ করে থাকে ‘বাংলাদেশে চা বোর্ড’। চট্টগ্রামের নাসিরাবাদে ১৯৫১ এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করার মতো যে, আমাদের জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন চা বোর্ডের প্রথম বাঙালী চেয়ারম্যান। তিনি ১৯৫৭-৫৮ সাল পর্যন্ত চা বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। পাকিস্তান আমলে গড়া শ্রীমঙ্গলের একটি ছোট চা গবেষণা কেন্দ্রকে তিনিই ইনস্টিটিউটে রূপান্তর করে তৈরী করেন ‘বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট’, যার ফলে এ দেশে সুযোগ হয় চা নিয়ে ব্যাপক গবেষণার।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন তৎকালীন পাকিস্তান চা বোর্ডের প্রথম বাঙালি চেয়ারম্যান। বঙ্গবন্ধু সেসময় যে চেয়ারে বসতেন, তা আজও সংরক্ষিত আছে শ্রীমঙ্গলের চা জাদুঘরে; Source: লুৎফর রহমান
চায়ের সাথে বঙ্গবন্ধুর আরেকটি মজার স্মৃতি জড়িয়ে আছে। ১৯৭৩ সালে আরব-ইসরায়েল যুদ্ধে মুসলিম দেশগুলো মিসরে বিভিন্ন সহায়তা পাঠাচ্ছিলো। ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার সমর্থক বাংলাদেশেরও উচিত কিছু পাঠানো। কিন্তু সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ কী আর পাঠাবে? সে সামর্থ্যই বা কোথায়? বঙ্গবন্ধু নিলেন এক চমৎকার উদ্যোগ। তিনি মিসরের সামরিক বাহিনীর জন্য এক লাখ পাউন্ড উৎকৃষ্ট মানের বাংলাদেশি চা পাঠিয়ে দিলেন সহায়তা হিসেবে। যুদ্ধক্ষেত্রে একজন সৈনিকের কাছে এক কাপ চা যে কত দরকারী তা সদ্য যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থাকা বাঙালীর চেয়ে ভাল কে বুঝবে! মিসর সাদরে গ্রহণ করে এ সহায়তা এবং যুদ্ধ শেষ হলে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ বাংলাদেশকে ৩২টি ‘টি-৫৪’ ট্যাংক আর ৪০০ রাউন্ড ট্যাংকের গোলা উপহার দেয়, যা বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী গঠনে অনেক কাজে এসেছিলো।

যুদ্ধক্ষেত্রেও এক কাপ চা সৈনিককে এনে দেয় সাময়িক স্বস্তি; Source: Imperial war museum
চায়ের রয়েছে অনেক স্বাস্থ্যগত উপকারিতা। চায়ে থাকে প্রচুর এন্টিঅক্সিডেন্ট। হৃদরোগ, ক্যান্সার, অ্যালঝেইমার ইত্যাদি রোগ প্রতিরোধে রয়েছে চায়ের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। গবেষণায় দেখা গেছে, দিনে দু’কাপ চা পানের অভ্যাস যাদের আছে, তাদের মধ্যে হৃদরোগ, স্ট্রোকের প্রবণতা কম। শরীরে চাঙ্গা ভাব এবং চাপমুক্তি আনতেও চা পানের প্রয়োজন।
বাংলাদেশ একসময় প্রথম সারির চা রপ্তানীকারক দেশ ছিলো, যা ছিলো পাটের পরে সবথেকে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী পণ্য। এখনও চা বিদেশে রপ্তানী করা হয়। কিন্তু রপ্তানির চার গুণ চা এখন আমদানী করতে হয় শুধু অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে। মজার ব্যাপার হলো, রপ্তানি কমার কারণ উৎপাদন কম হওয়া নয়। চা উৎপাদন বেড়েছে আগের থেকে অনেক, কিন্তু দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা বেড়ে যাওয়াই রপ্তানি কমার কারণ। তবে চা বাগান মালিক-ব্যবসায়ী সবাই চেষ্টা করে চলেছেন রপ্তানি পণ্য হিসেবে চায়ের অবস্থান ফিরে পেতে।
ফিচার ছবি- Bustle






.jpeg?w=600)

