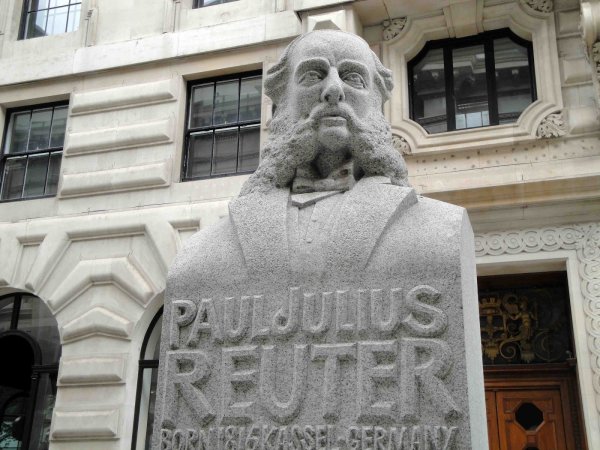পরনে জরাজীর্ণ কোট-টাই, ঢিলেঢালা মলিন প্যান্ট, মাথায় কালো রঙের ডার্বি হ্যাট, হাতে একটি ছড়ি, পায়ে পুরোনো এক জোড়া বুট এবং ঠোঁটের উপর খাটো অথচ প্রশস্ত একটুখানি টুথব্রাশ গোঁফ – এই লোকটাকে কে না চেনে! তিনি আর কেউ নন, আমাদের সকলের প্রিয় মূকাভিনেতা চার্লি চ্যাপলিন। এক শতাব্দী পূর্বে তার অমর কাজগুলো আজকের দিনেও আমাদের বিনোদনের খোরাক জোগায়, আজও আমাদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলে। বিশ্বের ইতিহাসে সর্বকালের সেরা ও সবচেয়ে জনপ্রিয় চলচ্চিত্র ব্যক্তিদের তালিকা করা হলে নিঃসন্দেহে চার্লি চ্যাপলিনের নাম একদম উপরের দিকেই থাকবে।

শৈশব: শুরুটাই যেখানে সংগ্রাম দিয়ে
চার্লি চ্যাপলিনের প্রকৃত নাম ‘চার্লস স্পেনসার চ্যাপলিন’। যদিও তাকে বিশ্বব্যাপী ‘শার্লট’, ’কার্লিটোস’, ‘দ্য লিটল ট্র্যাম্প (ভবঘুরে)’ ইত্যাদি নামেও ডাকা হয়।। তার জন্মতারিখ ও জন্মস্থান নির্ভুলভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। তবে ধারণা করা হয়, তিনি ১৮৮৯ সালের ১৬ এপ্রিল লন্ডনের ওয়ালউওর্থে জন্মগ্রহণ করেন। অবশ্য তার মৃত্যুর অনেক পর ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থার অনুসন্ধানে এমন কোনো প্রমাণ মেলেনি যে, চার্লি চ্যাপলিন ব্রিটেনেই জন্মগ্রহণ করেছেন। তার জন্মস্থান, এমনকি ফ্রান্সও হতে পারে বলে অনুমান করা হয়! আবার, ২০১১ সালে উদ্ধারকৃত একটি পুরোনো চিঠিতে পাওয়া তথ্যমতে, ইংল্যান্ডের স্ট্যাফোর্ডশায়ারের একটি ক্যারাভ্যানে তিনি ভূমিষ্ঠ হন।
চার্লি চ্যাপলিনের বাবা ছিলেন ‘চার্লস চ্যাপলিন সিনিয়র’ এবং তার মায়ের নাম ‘হানাহ চ্যাপলিন’। তারা দুজনই একাধারে মঞ্চে অভিনয় করতেন এবং পাশাপাশি গানও গাইতেন। চার্লি চ্যাপলিনের শৈশব কেটেছে চরম অভাব-অনটন ও নিদারুণ কষ্টের মাঝে। বারো বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তিনি যেসব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন, অনেক মানুষকে পুরো জীবদ্দশাতেও সেসব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয় না। তার বয়স তিন বছর হওয়ার পূর্বেই তার বাবা-মা আলাদা বসবাস করা শুরু করেন; যদিও তাদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়নি। শিশু চ্যাপলিন তার মায়ের সাথে থাকতেন; সাথে ছিলো তার সৎ বড় ভাই ‘সিডনি চ্যাপলিন’।

কিন্তু কয়েক বছর যেতে না যেতেই তার মা শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি হলে চ্যাপলিন অসহায় হয়ে পড়ে। তার ভরণপোষণ ও দেখাশোনার দায়িত্বে কেউ না থাকায় তাকে প্রাথমিকভাবে লন্ডনের একটি অনাথাশ্রমে এবং পরবর্তীকালে অসহায় ও দুঃস্থ শিশুদের জন্য তৈরি ‘সেন্ট্রাল লন্ডন ডিস্ট্রিক্ট স্কুল’-এ পাঠানো হয়। তার বয়স তখন মাত্র সাত বছর। এভাবে প্রায় দুই বছর ঘরের বাইরে কাটানোর পর অল্প সময়ের জন্য চ্যাপলিন পুনরায় তার মায়ের দেখা পান। তবে সেটা বেশি দিনের জন্য নয়। কারণ তার মা তখনো সুস্থ হয়ে ওঠেননি।
প্রকৃতপক্ষে চার্লি চ্যাপলিনের মা হানাহ চ্যাপলিন আর কোনোদিনই পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেননি। মৃত্যুর আগপর্যন্ত তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। এরপর চ্যাপলিনকে কিছুদিনের জন্য তার বাবার কাছে পাঠানো হয়, যিনি তখন ছিলেন মদ্যপ। সেখানে বেশি দিন ঠাঁই হয়নি বালক চ্যাপলিনের। বাবা-মা দুজনের পেশাই মঞ্চের সাথে জড়িত হওয়ার সুবাদে চার্লি চ্যাপলিন নিজেও এদিকটায় ঝোঁকেন। অভাবের তাড়নায় ও মঞ্চে অভিনয় করার আগ্রহ থেকে মাত্র আট বছর বয়সেই তিনি যুক্ত হন ‘দ্য এইট ল্যাঙ্কাশায়ার ল্যাডস’ নামক একটি যাত্রাদলের সাথে, যার সদস্যরা সবাই ছিলো অল্পবয়সী।
মূলত এখান থেকেই তার কর্মজীবন শুরু হয় এবং প্রথম থেকেই বালক চার্লি চ্যাপলিনের মঞ্চাভিনয় দর্শক ও আয়োজকদের নজর কাড়তে শুরু করেন। এরপর চ্যাপলিন ছোটখাট আরও নানা মঞ্চে, নানা প্লাটফর্মে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করে সুনাম কুড়াতে থাকেন। ফলস্বরূপ তার পরবর্তী জীবনে তৎকালের কিছু নামকরা চলচ্চিত্র নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে অভিনয় ও চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। শুরু হয় তার জীবনের নতুন ও কর্মব্যস্ত এক অধ্যায়। এরপর চার্লি চ্যাপলিন নামক এই দুঃখী বালকটিকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি; অন্তত অর্থ-কড়ির ব্যাপারে।
পেশাগত জীবন
মাত্র আট বছর বয়সে কর্মজীবনে প্রবেশ করে চ্যাপলিন যখন একের পর এক অভিনয় দিয়ে মানুষের মন জয় করে নিচ্ছিলেন, তখনও তার আর্থিক দুর্দশা পুরোপুরি কাটেনি; কেবল কোনোরকম জীবিকা নির্বাহ করার মতো ব্যবস্থা হয়েছিলো মাত্র। তাই তিনি হন্যে হয়ে কাজ খুঁজছিলেন। তিনি যেহেতু অভিনয় পছন্দ করতেন, তাই তার আকাঙ্ক্ষা ছিলো অভিনয় সংক্রান্ত কোনো একটি পেশা বেছে নেওয়া।

কর্মজীবনে প্রবেশের দীর্ঘদিন পর, অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ১৯০৮ সালে তিনি সেরকম একটি সুযোগ পেয়ে যান। তার বয়স যখন আঠারো পেরিয়েছে, তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি তখন ঘটে; ‘দ্য কার্নো কোম্পানি’তে তিনি যোগদান করেন। তখনকার দিনে ব্রিটেনের এই স্বনামধন্য কোম্পানিটি হাস্যরসাত্মক নাটক তৈরি করতো ও দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থানে সেগুলোর প্রদর্শনী করে বেড়াতো। এই কোম্পানিতে যোগদান চ্যাপলিনকে একটি বড় সুযোগ এনে দেয় নিজেকে প্রমাণ করার ও বিশ্ববাসীর সামনে নিজেকে মেলে ধরার, যা তিনি ভালোভাবেই কাজে লাগিয়েছিলেন।
তার অসাধারণ স্টেজ পারফর্মেন্সে মুগ্ধ হয়ে ১৯১০ সালে তাকে মঞ্চনাট্য প্রদর্শনীর জন্য যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরণ করে ‘দ্য কার্নো কোম্পানি’। প্রায় দুই বছর যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে নিজের অসাধারণ অভিনয় প্রতিভা প্রদর্শন করার পর তিনি ইংল্যান্ড ফিরে আসেন। তবে এর কয়েক মাস পরই আবারও যুক্তরাষ্ট্রে যেতে হয় তাকে।

এবার ভাগ্য তার দিকে মুখ তুলে তাকালো; যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক চলচ্চিত্র নির্মাতা প্রতিষ্ঠান চ্যাপলিনকে তাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। অনেক ভেবেচিন্তে চ্যাপলিন ‘কিস্টোন স্টুডিও’তে কাজ করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। তার সাপ্তাহিক পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা হয়েছিলো ১৫০ ডলার। এই স্টুডিওর অধীনেই তার প্রথম চলচ্চিত্র ‘মেকিং এ লিভিং’ (১৯১৪) মুক্তি পায়, যার কেন্দ্রীয় চরিত্রে ছিলেন চ্যাপলিন নিজে।
আমি বিশ্বাস করি, যেদিন আমি কোনো কাজ করবো না, সেদিনের রাতের খাবারটা আমার প্রাপ্য নয়।
–চার্লি চ্যাপলিন
চার্লি তার কাজকে ভালোবাসতেন। দিন দিন তার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সাথে সাথে তার পারিশ্রমিকের পরিমাণ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে লাগলো; প্রথম তিন বছরে তার পারিশ্রমিক প্রায় দশগুণের মতো বেড়ে যায়! চার্লি চ্যাপলিনের বিখ্যাত বেশভূষা ‘দ্য লিটল ট্র্যাম্প’ বা ‘ভবঘুরে’ ছিলো জগদ্বিখ্যাত। এই বেশভূষার সাহায্যে তিনি নিজেকে এক হাস্যকর চরিত্র হিসেবে ফুটিয়ে তুলতে পেরছেন। এই চরিত্রটি একইসাথে আবার রাজকীয় ব্যক্তিত্বও প্রদর্শন করতে চায় সবখানে, তবে পদে পদে অপদস্থ হয়, যা তাকে আরও হাস্যকর করে তোলে।
প্রথমদিকে, তিনি অন্যান্য পরিচালকদের পরিচালনায় অভিনয় করলেও পরবর্তীতে পরিচালনার ভার নিজের হাতে তুলে নেন এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করতে থাকেন। ফলস্বরূপ, চলচ্চিত্র নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে তার পরবর্তী চুক্তিগুলো স্বাক্ষর করার সময় তিনি কয়েকটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতেন –
- পারিশ্রমিক। তিনি তার জনপ্রিয়তা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই তিনি আশা করতেন ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিগুলো তার কাজের উপযুক্ত মূল্যায়ন করবে।
- পরিচালনার দায়িত্ব। তিনি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পছন্দ করতেন। তাই নিজেই পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে চুক্তিবদ্ধ হতেন।
- সময়। চার্লি চ্যাপলিন ছিলেন ‘পারফেকশনিস্ট’। কাজের গুণগত মান তার কাছে মুখ্য ছিলো। সেজন্য তিনি তাড়াহুড়া না করার জন্য উপযুক্ত সময় চাইতেন।
এসব শর্ত বজায় রেখে তিনি একের পর এক স্বনামধন্য চলচ্চিত্র-নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে বিভিন্ন মেয়াদে চুক্তিবদ্ধ হতে থাকলেন। তিনি কাউকে হতাশ করেননি; একের পর এক মাস্টারপিস তার হাত ধরে বের হতে লাগলো। তিনি তখন বিশ্বের সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিক পাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম।
চ্যাপলিনের জনপ্রিয়তা ও তার কাজের গুণগত মান সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার জন্য একটি তথ্য উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি মার্কিন চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশের মাত্র তিন বছর পর, ১৯১৬ সালে ‘দ্য মিউচুয়াল ফিল্ম কর্পোরেশন’ এর সাথে একটি চুক্তি সম্পন্ন করেন। যার শর্ত হলো, চার্লি চ্যাপলিন নিজের ইচ্ছামতো ১২টি চলচ্চিত্র তৈরি করে দেবেন এবং বিনিময়ে কাজ শেষ হওয়ার আগপর্যন্ত তৎকালীন মুদ্রায় বার্ষিক ‘ছয় লক্ষ সত্তর হাজার’ মার্কিন ডলার করে পাবেন! তিনি আঠারো মাসে চুক্তির শর্ত পূরণ করেন এবং মিউচুয়াল কর্পোরেশনকে উপহার দেন ১২টি মাস্টারপিস চলচ্চিত্র।

এরপর তিনি ‘ফার্স্ট ন্যাশনাল’ কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন, তখন তাদের সহায়তায় নিজস্ব স্টুডিও তৈরি করেন চ্যাপলিন এবং আরও স্বাধীনভাবে কাজ করতে শুরু করেন। উল্লেখ্য, তার কাজের মান ও সময় দিন দিন বাড়তেই থাকে। এটাই ছিলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকা অবস্থায় বাইরের কোনো কোম্পানির অধীনে তার করা সর্বশেষ কাজ। তিনি সহসাই অনুধাবন করলেন, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য তিনি নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারেন এবং সে সামর্থ্যও তার ছিলো। অবশেষে ১৯১৯ সালের চার্লি চ্যাপলিন আরও কয়েকজন অংশীদারকে সাথে নিয়ে গড়ে তুলেন ‘ইউনাইটেড আর্টিস্টস’ নামক চলচ্চিত্র-নির্মাতা প্রতিষ্ঠান। তার পরবর্তী কাজগুলো এর অধীনেই হয়েছিলো। সারা বিশ্বব্যাপী চার্লি চ্যাপলিনের জনপ্রিয়তা তখন তুঙ্গে ছিলো।
তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি চলচ্চিত্র হলো:
- মেকিং এ লিভিং (১৯১৪)
- দ্য কিউর (১৯১৭)
- দ্য অ্যাডভেঞ্চারার (১৯১৭)
- এ ডগ’স লাইগ (১৯১৮)
- দ্য কিড (১৯২১)
- দ্য গোল্ড রাশ (১৯২৫)
- দ্য সারকাস (১৯২৮)
- সিটি লাইটস (১৯৩১)
- মডার্ন টাইমস (১৯৩৬)
- দ্য গ্রেট ডিক্টেটর (১৯৪০)
চার্লি চ্যাপলিনের চলচ্চিত্রগুলোর একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদে তার বাকি সবগুলোই নির্বাক কমেডি চলচ্চিত্র। তিনি মূলত হাস্যরসাত্মক ঘরানার সিনেমা বানালেও, পরবর্তীতে তার চলচ্চিত্রে অন্যান্য মাত্রা যেমন ট্রাজেডি, রোম্যান্স ইত্যাদি যোগ হতে থাকে। তিনি যখন আমেরিকা থেকে ফিরে পুনরায় ইউরোপে বসবাস শুরু করেন, তখন উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধার অভাবে বেশি সংখ্যক চলচ্চিত্র তৈরি করতে পারেননি। ইউরোপ চলে আসার পর তিনি মাত্র দুটি উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রের কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন- ‘এ কিং ইন নিউইয়র্ক’ ও ‘এ কাউন্টেস ফ্রম হংকং’।
চার্লি চ্যাপলিনের একটি বিশেষ কৃতিত্ব হলো, তিনি অভিনয়শিল্পকে রাতারাতি থিয়েটারের মঞ্চ থেকে টেলিভিশনের পর্দায় নিয়ে এসে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে অসামান্য ভূমিকা রাখেন। এর জন্য তিনি বিশেষ সম্মাননায় ভূষিত হয়েছিলেন।
ব্যক্তিগত জীবন
শৈশবে কঠোর সংগ্রাম করে পরবর্তীতে বিশ্বমঞ্চে সেরাদের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়া চার্লি চ্যাপলিন সারাটা জীবন ‘সুখ পাখি’র পেছনে দৌড়ে গেছেন, কিন্তু সেই পাখির নাগাল পাননি কখনোই। জীবন তার জন্য সবসময়ই বয়ে এনেছে দুঃখ আর কষ্ট। গগনচুম্বী খ্যাতির সাথে সাথে তার কপালে অনেক অপবাদও জুটেছে। শৈশবের দুঃসহ স্মৃতিকে পেছনে ফেলে এসে যখন তিনি খ্যাতির সিংহাসনে আরোহণ করছিলেন, তখন কিছু বিতর্কিত কান্ডকারখানাও ঘটিয়েছিলেন, যা তার ক্যারিয়ারে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিলো।

চার্লি চ্যাপলিনকে ঘিরে বিতর্কের কথা উঠলে প্রথমেই আসে তার অস্থিতিশীল ও বহু নারীঘটিত সম্পর্কের বিষয়। চার্লি চ্যাপলিন তার কর্মজীবনে কমপক্ষে দশজনেরও বেশি নারীর সঙ্গে জটিল সম্পর্কে জড়িয়েছেন। এর মধ্যে কয়েকটি সম্পর্কের পরিণতি ছিলো ভয়াবহ এবং সেগুলোর মীমাংসা আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে।
চার্লি ১৯১৮ সালে প্রথম বিয়ে করেন ‘মিল্ড্রেড হ্যারিস’ নামক এক মার্কিন অভিনেত্রীকে। যদিও এ বিয়েটা স্বতঃস্ফূর্ত ছিলো না। ১৬ বছর বয়সী হ্যারিস দাবি করেন, তিনি অন্তঃসত্ত্বা এবং তার সন্তানের পিতা চার্লি চ্যাপলিন। ১৬ বছর বয়সী একজন মেয়েকে নিয়ে আইনী ঝামেলা এড়ানোর জন্য তিনি তাকে অনেকটা গোপনেই বিয়ে করে ফেলেন। অবশ্য পরবর্তীতে জানা যায়, মিল্ড্রেড হ্যারিস গর্ভবতী ছিলেন না। যদিও পরবর্তীতে এই হ্যারিসই চার্লি চ্যাপলিনের সর্বপ্রথম সন্তানকে জন্মদান করেন। কিন্তু সেই সন্তান জন্মের তিনদিন পরই মারা যায়। চার্লি ও হ্যারিসের সংসার বেশি দিন টেকেনি। ১৯২১ সালে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে।

১৯২৪ সালে ঠিক একই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। এবারে বাস্তবতার নাট্যমঞ্চের নায়িকার নাম ‘লিটা গ্রে’। তিনিও ১৬ বছর বয়সে চার্লির সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেন। চার্লি আদালত এড়াতে এবারও লিটা গ্রেকে বিয়ে করতে বাধ্য হন। পূর্বের মতো এ সংসারটিও টেকেনি। বরং এবারের বিচ্ছেদ আরও ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সম্পন্ন হয়। লিটা গ্রে চার্লির বিরুদ্ধে ভয়ানক কিছু অভিযোগ করেন, যা চার্লির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে এবং তাকে খুব অস্বস্তিকর ও লজ্জাজনক পরিস্থিতিতে ফেলে।
চার্লির তৃতীয় বিয়েটি ছিলো অভিনেত্রী পলেট গডার্ডের সাথে, ১৯৩৬ সালে। এ বিয়েটি টিকেছিলো ৬ বছর। তবে এবারের বিচ্ছেদটি সংঘটিত হয় শান্তিপূর্ণভাবে ও উভয়ের সম্মতিতে। সর্বশেষ, চার্লি থিতু হন উওনা চ্যাপলিনের সাথে। ১৯৪৩ সালে এ জুটির বিয়ে হয়। চার্লির এ সংসারটি টিকেছিলো জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। চার্লির ভাষ্যমতে, উওনা ছিলো তার জন্য আদর্শ জীবনসঙ্গিনী, যে তাকে সুখে রেখেছিলো এবং সর্বদা তার পাশে ছিলো।

চলচ্চিত্র ও জীবন-দর্শন
তীব্র বেদনাদায়ক শৈশব চার্লি চ্যাপলিনকে জীবন সম্পর্কে অন্যভাবে ভাবতে শিখিয়েছিলো। চার্লি নিজেকে নিয়ে ভাবতেন, নিজের চারপাশের মানুষ নিয়ে ভাবতেন এবং সমাজকে এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতেন। সমাজ সম্পর্কে তার দর্শন ছিলো অতি সাধারণ। অথচ তার পর্যবেক্ষণ ছিলো অত্যন্ত গভীর। চার্লির জীবন সম্পর্কে জানলে দেখা যায়, তার প্রায় প্রতিটি চলচ্চিত্রেই তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, জীবনদর্শন ও পর্যবেক্ষণ কোনো না কোনোভাবে উঠে এসেছে।
তার সর্বপ্রথম সন্তানটি জন্মের পর বেঁচে ছিলো মাত্র তিনদিন। তার প্রথম সন্তানের মৃত্যুর দুই বছর পরই মুক্তি পায় ‘দ্য কিড’ চলচ্চিত্রটি। যেখানে দারিদ্র্য, বাবা-মা’র বিচ্ছেদ ও এক শিশুর অসহায়ত্ব ফুটিয়ে তোলা হয়। স্বাভাবিক চিন্তাভাবনা থেকেই অনুধাবন করে নেওয়া যায়, এই চলচ্চিত্রটির অণুপ্রেরণা চার্লির শৈশব ও পৃথিবীর বুক থেকে বিদায় নেওয়া তার সন্তানের স্মৃতি থেকেই এসেছে।

চার্লি বড় হয়েছেন তীব্র অভাব অনটনের মাঝে। তাই তার প্রথমদিকের প্রায় প্রতিটি চলচ্চিত্রে সমাজের সবচেয়ে নিম্নবিত্ত শ্রেণীটি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে এবং তার চলচ্চিত্রে এরা বারবার চিত্রায়িত হয়েছে। ‘এ ডগস লাইফ’, ‘মডার্ন টাইমস’, ‘দ্য গ্রেট ডিক্টেটর’ ইত্যাদি চলচ্চিত্রেও তার ব্যক্তিগত চিন্তাধারার প্রতিফলন সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্যণীয়।
রাজনৈতিক বিতর্ক ও স্বেচ্ছা-নির্বাসন
ইতোমধ্যেই আমরা জেনেছি, চার্লি তার চলচ্চিত্রে নিজের অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি ফুটিয়ে তুলতেন। তার জীবনদর্শনে রাজনীতিও অন্তর্ভুক্ত ছিলো। তিনি জীবন থেকে রাজনীতিকে আলাদা করতে পারতেন না। তার বিশেষ রাজনৈতিক দর্শনের কারণে তিনি বেশ বিতর্কিত হয়েছেন। সমালোচনার বানে জর্জরিত হয়েছেন বহুবার। ক্ষেত্রবিশেষে তাকে কখনো কখনো দুর্দশা বরণ করতে হয়েছিলো।
তাকে নিয়ে প্রথম রাজনৈতিক সমালোচনা শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। তিনি তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকায় ব্রিটেনব্যাপী তীব্র সমালোচনা করা হয় তার। তিনি নিজের মাতৃভূমির পক্ষে যুদ্ধে যোগ না দেওয়ায় তাকে কাপুরুষ হিসেবে অভিহিত করা হয়। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমগুলো তাকে একপ্রকার তুলাধুনো করেই ছেড়েছিলো। এরপর আবার ১৯৩৬ সালে তিনি শিরোনাম হন ‘মডার্ন টাইমস’ প্রকাশিত হওয়ার পর।
১৯২৯ সালের বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার প্রেক্ষাপটে তৈরি করা হয়েছিলো এই মাস্টারপিস চলচ্চিত্রটি। এতে তিনি বেকারত্বের উপর শিল্পায়নের প্রভাব তুলে ধরেন এবং পুঁজিবাদের সমালোচনা করেন। আমেরিকানরা এতে রাজনীতির গন্ধ খুঁজে পায় এবং চলচ্চিত্রকার হিসেবে তিনি রাজনৈতিক সমালোচনার শিকার হন। একইসাথে তিনি রাজনীতিবিদদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হন। মোটামুটি তখন থেকে তিনি রাজনীতিবিদ ও গোয়েন্দা সংস্থার সতর্ক নজরদারীর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান।

১৯৪০ সালে ‘দ্য গ্রেট ডিক্টেটর’ প্রকাশিত হয়। এতে তিনি অ্যাডলফ হিটলারকে ব্যঙ্গ করেন এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে নিজের অবস্থান তুলে ধরেন। কিন্তু মার্কিনীরা এতে ‘বামপন্থা’ খুঁজে পান এবং তার দিকে অভিযোগের তীর আরও দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে চার্লি চ্যাপলিন নানাভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নকে সমর্থন যোগানোর চেষ্টা করেন। এতে কম্যুনিজমের পক্ষে তার অবস্থান আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এতদিন পর মার্কিন কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে, তারা অনুধাবন করতে পারে চার্লি চ্যাপলিনের পূর্বের চলচ্চিত্রগুলো, যেগুলোতে শোষিত শ্রেণীর দুর্দশা তুলে ধরা হয়েছে, সমাজের শ্রমিক শ্রেণীর মানুষজনদের উপর বিশেষ আলোকপাত করা হয়েছে, সেগুলোতেও ‘সমাজতন্ত্রের উপাদান’ নিহিত আছে।
তদুপরি, তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার বৈশ্বিক নেতৃত্ব দেওয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্নায়ুযুদ্ধ পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করে তোলে। দিন দিন মার্কিন সমাজে চ্যাপলিনকে বয়কট করা মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং রাজনীতিবিদরা তাকে কোনো প্রকারে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিতাড়িত করার জন্য বাহানা খুঁজতে থাকেন। অবশেষে ১৯৫২ সালে সেই সুযোগ আসে।

চার্লি নিজেও বুঝতে পেরেছিলেন কিছু একটা হতে চলেছে। আর তার জন্য তিনি মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন। মার্কিন সমাজে তার প্রতি তৈরি হওয়া বিদ্বেষী মনোভাব তিনি আঁচ করতে পেরেছিলেন। তার শৈশব এবং আমেরিকায় তার ক্যারিয়ার ও জনপ্রিয়তার উত্থান-পতনের উপর আলোকপাত করে নির্মিত চলচ্চিত্র ‘দ্য লাইমলাইট’ ১৯৫২ সালে মুক্তি পায়। তিনি সিদ্ধান্ত নেন, এটি আমেরিকায় মুক্তি না দিয়ে ইংল্যান্ডে মুক্তি দেবেন। এই লক্ষ্য নিয়ে তিনি ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।
এর পরপরই ‘এফবিআই’ এর তরফ থেকে তাকে জানানো হলো, তিনি পুনরায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরতে চাইলে তাকে জেরার সম্মুখীন হতে হবে। বিশেষ করে তার রাজনৈতিক মতাদর্শের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। চার্লি চ্যাপলিন ছিলেন অভিমানী। তাই যুক্তরাষ্ট্রে ফেরা হয়নি তার। তবে ধারণা করা হয়, তিনি আবেদন করলেই যুক্তরাষ্ট্র সরকার হয়তো তাকে পুনরায় প্রবেশাধিকার দিতো। কিন্তু তিনি তার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি। অবশ্য এ ঘটনার ২০ বছর পর তিনি বিশেষ সম্মাননা গ্রহণ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন।
নাটকীয় জীবনের শেষভাগ
একজন প্রতিভাবান ব্যক্তির প্রতিভা সাধারণত একটি নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। একাধিক কাজে তিনি তার প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে যান। চার্লি চ্যাপলিন নিজে তার চলচ্চিত্র একাধারে পরিচালনা, অভিনয় ও অর্থায়ন করতেন এবং সেগুলোতে ব্যবহৃত গান বা সুর তিনি নিজেই রচনা করতেন। এই কাজগুলোর প্রত্যেকটিতেই তিনি উন্নত রুচির পরিচয় দিয়েছেন।
তার জীবনী থেকে আমরা একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের শিক্ষা পাই। প্রাচুর্য ও সফলতার শীর্ষে আরোহণ করেও তিনি তার শৈশবের স্মৃতিকে ভুলে যাননি। এজন্য প্রচুর অর্থবিত্তের মাঝে থেকেও তিনি বিলাসীতায় গা ভাসিয়ে দেননি। হাজার প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি হাল ছেড়ে দেননি, জীবনকে তিনি ইতিবাচকভাবে নিয়েছেন, বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখেছেন।
এমনকি একটি জেলীফিশের কাছেও জীবন অনেক সুন্দর ও দারুণ একটা জিনিস।
– চার্লি চ্যাপলিন
নিজের উপর তার এতই বিশ্বাস ছিলো যে, তিনি নিজের চলচ্চিত্রের যাবতীয় কাজ এককভাবে নিজেই সম্পাদন করে সেই চলচ্চিত্রকে সাফল্যমন্ডিত করে দেখিয়েছেন।

তিনি বহুবার উল্লেখ করেছেন, তার মা’ই তার অনুপ্রেরণার উৎস। এর প্রমাণ চার্লি দিয়েছেন; আমেরিকায় যখন তিনি আর্থিক সচ্ছলতার দেখা পেলেন, তখন তার মাকে ব্রিটেন থেকে আমেরিকায় নিয়ে যান। মায়ের মৃত্যুর আগপর্যন্ত চার্লি চ্যাপলিন তাকে অপরিসীম মমতা ও যত্নে আগলে রেখেছিলেন; কোনো কষ্ট তাকে স্পর্শ করতে পারেনি।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ইউরোপে চলে আসার পর চার্লি চ্যাপলিন সুইজারল্যান্ডে বসবাস শুরু করেন। সেখানেই ১৯৭৭ সালের বড়দিনে এই অবিস্মরণীয় মানুষটির মহাপ্রয়াণ ঘটে।