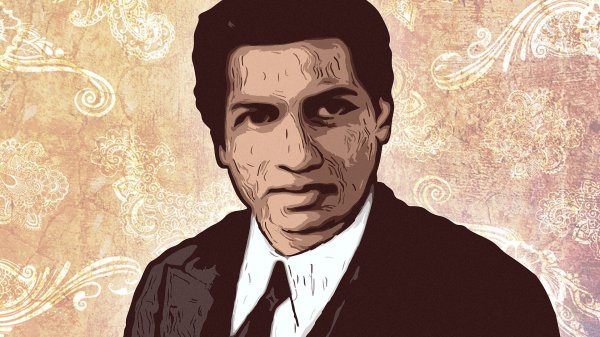আধুনিক যান্ত্রিক বিশ্বের আত্মকেন্দ্রিক মানুষদের মধ্যে ‘আর্তমানবতার জন্য সেবা’- এই বার্তা নিয়ে আসা এক মহৎপ্রাণ মানবী মাদার তেরেসার জীবনের অনেক গল্প আমরা শুনেছিলাম প্রথম পর্বে। তাঁর জীবনের বিশাল কর্মযজ্ঞের গল্প অল্প কথায় বলা সম্ভব নয়। তাঁর সুবিশাল জীবনের শৈশব-কৈশোর, সেবার পথে তাঁর পথচলার প্রথম দিককার গল্প আমরা শুনেছি আগেই। আজ শুনবো কীভাবে ভারতের সীমানা পেরিয়ে তিনি ছড়িয়ে পড়েন দেশে দেশে, কীভাবে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনেন বিভিন্ন দেশের ভাগ্যাহত শিশুদের। আর জানবো কীভাবে মুক্তিযুদ্ধের ভীষণ কষ্টের সময় তিনি বিপুল স্নেহ আর মমতা নিয়ে দাঁড়ান এ দেশের যুদ্ধাহত মানুষের পাশে।

ছুটে এসেছিলেন দূর দেশ থেকে আর্ত মানবতার টানে; source: flipquiz.me
১৯৭০ সাল পর্যন্ত তাঁর প্রতিষ্ঠিত ‘মিশনারিজ অব চ্যারিটি’র কর্মকান্ড পরিচালিত হতে থাকে ভারতের বিভিন্ন এলাকায়, বিশেষ করে কলকাতায়। কিন্তু ১৯৭০ সালের পর থেকে অন্যান্য অনেক দেশ পর্যন্ত তাঁর এই প্রতিষ্ঠানের কর্মের পরিধি বাড়তে থাকে। পরবর্তী বছরগুলোতে সেইন্ট তেরেসা উন্নত পশ্চিমা দেশগুলোতে তাঁর ধর্মীয় ও সেবামূলক কাজ পরিচালনা করতে থাকেন। এই প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন “পশ্চিমে মানুষগুলো কেবল সুযোগ-সুবিধার দিক থেকে ধনী কিন্তু আত্মিকভাবে তারা খুবই গরীব।” ১৯৭১ সালে তিনি আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে যান এই দাতব্য সংস্থার শাখা খুলতে। সেখান থেকে গোপনে তিনি পাড়ি জমান লেবাননে। সকল পার্থক্যের ওপরে উঠে তিনি সেখানে মুসলিম ও খ্রিস্টান, উভয় ধর্মের শিশুদের সাহায্যে এগিয়ে যান।
এই লেবাননেই মাদার তেরেসার জীবনের সবচেয়ে চমকপ্রদ ঘটনাগুলোর একটি ঘটে। ১৯৮২ সালে লেবাননের বৈরুতে রেডক্রসের মাত্র কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবীর সহায়তায় তিনি একটি যুদ্ধাঞ্চলে প্রবেশ করেন এবং একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হাসপাতাল থেকে প্রায় ৩৭ জন আহত শিশুকে উদ্ধার করেন। তাঁর নেতৃত্বে খুব দ্রুতই ‘মিশনারিজ অব চ্যারিটির’ শাখা ছড়িয়ে পড়তে থাকে রোম, তানজানিয়া, অস্ট্রিয়া সহ এশিয়া, আমেরিকা, ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন জায়গায়। যদিও প্রথমে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে তাঁর এই প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি পায়নি, কিন্তু ১৯৮০ সালের দিকে সেই প্রতিবন্ধকতাও তিনি জয় করে নেন। সেই থেকে আর কখনোই তাঁকে পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। বর্তমানে বিশ্বের ৬টি মহাদেশের ১২৩টি দেশে ৪৫০টি কেন্দ্র ও ৬১০টি সংস্থার মাধ্যমে ‘মিশনারিজ অব চ্যারিটির’ প্রায় ৪,৫০০ জন স্বেচ্ছাসেবী কর্মী কাজ করে যাচ্ছে। তবে ভারতের বাইরে ‘মিশনারিজ অব চ্যারিটি’র প্রথম আশ্রমটি তৈরি হয় ভেনেজুয়েলাতে, ১৯৬৫ সালে। এটি গড়ে ওঠে মাত্র ৫ জন সেবিকা নিয়ে। তেরেসা এরপর আমেরিকায় গড়ে তোলেন এইডস আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য আশ্রম।

সেবার আরেক নাম মাদার তেরেসা; source: thetitanic.com
মানবসেবার জন্য তাঁর আত্মত্যাগ ছিল আসলেই অতুলনীয়। মানবতার সেবায় বহুবার তিনি ভুলে গিয়েছেন তার ব্যক্তিজীবনের ছোটখাৎ স্বার্থ থেকে বড় অনুভূতিকেও। তাঁর জীবনের সবচেয়ে কাছের মানুষ তাঁর মায়ের সাথে সেই ১৮ বছর বয়সে গৃহত্যাগের পর আর দেখা হয়নি কখনো। তাঁর বোনদের সাথেও আর কখনো দেখা হয় না।
ভারতসহ পুরো পৃথিবীজুড়ে তিনি তাঁর কাজের ব্যাপক স্বীকৃতি পান। ভারতে তিনি সর্বোচ্চ নাগরিক পুরষ্কার ‘ভারত রত্ন’ উপাধিতে ভূষিত হন। ‘নেহেরু পুরষ্কার’ পান ১৯৭২ সালে। আন্তর্জাতিক শান্তি আর সম্প্রীতিতে অবদানের জন্য ১৯৭১ সালে তিনি পান ‘পোপ তেইশতম জন শান্তি পুরষ্কার’। ১৯৭৯ সালে তিনি নোবেল শান্তি পুরষ্কারে ভূষিত হন। কিন্তু তাঁর পুরষ্কারের সব টাকা তিনি দান করে দেন তাঁর আশ্রমে। এমনকি তার সম্মানে নোবেল কমিটি যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, তা-ও তিনি বাতিল করার অনুরোধ করেন। তাই সে টাকাও তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ভারতের দরিদ্র মানুষদের মধ্যে দান করা হয়।
ধর্মের প্রতি তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস আর নিবেদনের কথা সবার জানা। কিন্তু সেই সাথে তাঁর শক্ত বিশ্বাস ছিল জন্মান্তরবাদে। জন্মনিয়ন্ত্রণ আর গর্ভপাতের তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। এত বিশ্বাসী হওয়ার পরও তিনি প্রায়ই স্রষ্টার প্রতি নিজের বিশ্বাসের ব্যাপারে প্রশ্ন তোলেন। বোধহয় সবসময়ই তাঁর চিন্তা-ভাবনা ছিল সবার চেয়ে অনেকটাই আলাদা।
নিজের কর্ম আর কর্তব্যের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আপোষহীন। একবার ১৯৬৫ সালে পোপ ষষ্ঠ পল তাঁর সাথে দেখা করতে আসলে তিনি গরিবদের জন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় দেখা করতে পারবেন না বলে জানান। পোপ তেরেসার কর্তব্যবোধে অত্যন্ত মুগ্ধ হন।
বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার শরীর ভাঙতে থাকে। তিনি বারবার হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়া ছাড়াও ফুসফুস ও কিডনির সমস্যায় আক্রান্ত হন। ১৯৯৭ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর ৮৭ বছর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন। ভারত সরকার ভারতের দরিদ্র মানুষদের জন্য তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করে তাঁর জন্য রাষ্ট্রীয় সম্মানমূলক শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। তাঁকে ১৮ বার পৃথিবীর সবচেয়ে প্রশংসনীয় ১০ নারীর একজন হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। আলবেনিয়ার একমাত্র আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরটি তাঁর নামে নামকরণ করা হয়।

মানুষের কষ্ট নিবারণের জন্য এসেছিলেন বাংলাদেশেও; source: slideplayer.es
ভারতের পাশাপাশি এই বাংলাদেশের অসহায়, দরিদ্র মানুষদের পাশেও তিনি দাঁড়িয়েছেন বারবার। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় যে মানুষগুলো বাধ্য হয়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে কলকাতায় পাড়ি জমান, তাদের পাশে তিনি দাঁড়ান সেবার অঙ্গীকার নিয়ে। তাদের আশ্রয়হীন, নিঃস্ব, অসহায় অবস্থা তাঁর কোমল হৃদয়কে গভীরভাবে নাড়া দেয়। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময়ও নির্যাতিত মানুষদের পাশে দাঁড়াতে তিনি পিছপা হননি। মাদার তেরেসা আর তাঁর সাথীরা অবিশ্রান্তভাবে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেয়া হাজার হাজার শরণার্থীদের সাহায্য করে যান যুদ্ধের পুরো সময়। বিশেষ করে শরণার্থীদের মধ্যে খাদ্য, বস্ত্র আর প্রয়োজনীয় ওষুধের যোগান দেওয়ার ওপর গুরুত্ব দেন তিনি। যুদ্ধে এতিম হওয়া শিশু আর ধর্ষণের ফলে গর্ভবতী হওয়া মেয়েদের পাশে দাঁড়ানোকেই এসময় নিজেদের লক্ষ্য হিসেবে বেছে নেন তেরেসা আর তাঁর সিস্টাররা।

কলকাতায় শিশু ভবন; source: thelifeofmotherteresa.blogspot.com
১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হওয়ার একদম পরপরই এ দেশের বিপর্যস্ত মানুষদের পাশে দাঁড়ান তেরেসা। নিশ্চিতভাবেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, যুদ্ধবিধ্বস্ত এই দেশে মানবতা তখন কতটা বিপর্যস্ত। তাই এদেশের ক্যাথলিক চার্চ কর্তৃপক্ষ যখন তাঁকে এখানকার মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য এ দেশে আসার আমন্ত্রণ জানান, তিনি আর কোনো দ্বিধা করেননি। খুলনাতে প্রথম কেন্দ্র খোলার মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশে মিশনারিজ অব চ্যারিটির কাজ শুরু করেন।
১৯৭২ সালের প্রথম দিকে মাদার তেরেসা ও তাঁর সাথীরা যখন প্রথম বাংলাদেশে আসেন, তখন তাঁরা এদেশের মানুষের করুণ অবস্থা দেখে দারুণ মর্মাহত হন। ঢাকার ইসলামপুরে তেরেসা তখনই একটি বাড়ির ব্যবস্থা করে সেখানে ‘শিশু ভবন’ নামে এক আশ্রয়কেন্দ্র গড়ে তোলেন। মিশনারিজ অব চ্যারিটি সেখানে শুধু উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সমাজচ্যুত, নিরাশ্রয় বীরঙ্গনা ও যুদ্ধশিশুদের আশ্রয় দেওয়া ও দেখাশোনা করে নি, বরং এই ভাগ্যাহত শিশুদের যাতে ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া আর পশ্চিমা অন্যান্য দেশে দত্তক নেওয়া হয়, সে ব্যবস্থাও করে। ফলে সেসব শিশুর জীবন একটু হলেও সহজ হয়। বর্তমানে সেখানে অনাথ এবং মানসিকভাবে অসুস্থ শিশুদের দেখাশোনা করা হয়। এর কয়েক বছরের মধ্যেই মিশনারিজ অব চ্যারিটি ঢাকার তেজগাঁওয়ে ‘নির্মল হৃদয়’ নামে বৃদ্ধ ও রুগ্নদের জন্য আরেকটি কেন্দ্র খোলে। এভাবে সেবার বার্তা বয়ে তারা দেশে দেশে নিজেদের সাধ্যমতো অসহায় ও দুস্থ মানুষদের পাশে দাঁড়ায়। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর সাহায্যের কথা ভোলার নয়। ধীরে ধীরে চট্টগ্রাম, খুলনা, ময়মনসিংহ, সিলেট, দিনাজপুর ও বরিশালের বিভিন্ন জায়গাতেও এই প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র খোলা হয়।

মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত এক দেবদূত; source: tweez.net