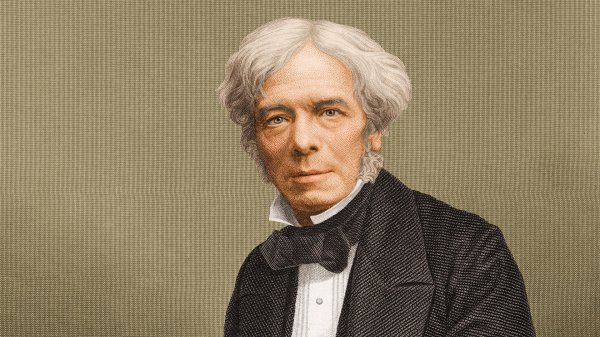যুদ্ধ শেষ হয়েছে। স্বাধীন হয়েছে গোটা একটি দেশ। অনেক প্রাণ আর সম্মানের বিনিময়ে কেনা এই স্বাধীন দেশে পুরস্কৃত হয়েছেন অনেক বীর যোদ্ধা। কেউ বা ইতিহাসের অতলে হারিয়ে গেছেন। কেউ মনে রাখেনি তাদের। কিন্তু যে বিশাল সংখ্যক নারী যুদ্ধ শেষেও নিজের সাথে যুদ্ধ করে গেছেন, নিজের পরিবার, সমাজের ভয়ে সেই অন্ধকার দিনগুলোর কথা মুখ ফুটে কাউকে বলতে পারেননি, তাদের যুদ্ধটা কিন্তু একেবারেই ভিন্ন ছিল। মুক্তিযুদ্ধের পর তখন পার হয়ে গেছে প্রায় ২৮ বছর। প্রতিনিয়ত মানসিক যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে পার হয়েও প্রথম যে নারী বলিষ্ঠ কণ্ঠে একাত্তরের সেই অন্ধকার দিনগুলোর কথা জনসমক্ষে বলেছিলেন, তিনি ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী। তিনি শুধু একজন মুক্তিসেনাই নন, বিখ্যাত ভাস্করও। ২৮ বছর তো অনেকটা সময়। এতদিন পরে কেন জানালেন? এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন,
“২৮ বছর পালাতে পালাতে নিজেকে সমাজ থেকে প্রত্যাখ্যান করলাম। কেন জানি না মনে হলো, যে দেশে মুক্তিযুদ্ধের এত বড় সাক্ষী ও নির্যাতন সহ্য করার পরও সমাজ আমার দিকে তর্জনি উঠিয়ে অপমানিত করে, লাঞ্ছিত করে সে সমাজের আমার আর প্রয়োজন রইল না। তারপর আমি চিন্তা করলাম আমি নিজে কতটুকু দায়ী, তখন সেই পরিণত বয়সটাও আমার ছিল না। যখন একটা পরিণত বয়স হলো, আমি বুঝতে পারলাম এ বিষয়ে এক বিন্দু পরিমাণ অপরাধ আমার ছিল না। নিজের সাথে বোঝাপড়া করে যখন পুরো মাত্রায় আস্থাশীল হলাম আমার নিজের প্রতি, তখনই বলার সিদ্ধান্ত নিই, এদেশের নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানাতে।”

মুক্তিযোদ্ধা ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী; Source: Asia Society
কেমন ছিল তার গোটা জীবনটা? চলুন জেনে নেওয়া যাক!
এলাকার যেকোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পুরস্কার জেতা ছোট্ট মেয়েটার নিত্য অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সাথে ছিল চারপাশের প্রতি ভালোবাসা। নিজের আশেপাশের সবকিছুকে মায়া ভরে দেখতেন। সে হোক না স্কুলের বেঞ্চে হিজিবিজি লিখে খুকির সাথে রমজানের নাম যোগ করা, অথবা বাড়ির সদর দরজার সামনে দিয়ে রোজ ডেকে যাওয়া বায়োস্কোপওয়ালা। টেলিভিশন তখনও জাঁকিয়ে বসেনি বাংলাদেশে। বায়োস্কোপের সেইসব লাল নীল ছবির প্রেমই হয়তো তাঁকে ভাস্কর ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী হিসেবে দাঁড় করিয়েছিল।
১৯৪৭ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি খুলনায় নানাবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি। ডাকবাংলোর মোড়ে এই বাড়িটির নাম ছিল ‘ফেয়ারি কুইন’ বা পরীর রানী। বাড়ির সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তাঁকেও সংস্কৃতি চর্চায় উৎসাহী করেছিল। উপমহাদেশের বিখ্যাত সব মানুষদের কাছ থেকে পুরস্কার নেওয়ার অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাঁর। নানা ছিলেন প্রভাবশালী কংগ্রেস সদস্য। বাবা সৈয়দ মাহবুবুল হক দৌলতপুর কলেজে শিক্ষকতা করতেন। বাবার চাকরির সুবাদে কলেজ মাঠে ছোট্ট ফেরদৌসীর সারাদিনের ছুটোছুটি তার এক মধুর স্মৃতি। শৈশবের স্মৃতি পরবর্তী জীবনের শক্তি সঞ্চয়ে কাজে লেগেছিল। ১৯৫২ সালে নানা সুপ্রিমকোর্টের জন্য বদলি হয়ে ঢাকা আসেন। সাথে আসেন ফেরদৌসীরাও। প্রথম প্রথম টিকাটুলি নারী শিক্ষা মন্দিরে লেখাপড়া শুরু করেন। এরপর যুক্তফ্রন্টের আমলে ফেরদৌসীর নানা স্পিকার হন। এবার তিনি ভর্তি হলেন সিদ্ধেশ্বরী গার্লস স্কুলে। ফলাফল আর যা-ই হোক, রোজ তাঁকে স্কুলে যেতেই হবে। প্রধান শিক্ষিকা শহীদ জননী জাহানারা ইমামের স্নেহময়ী মুখ না দেখে থাকতে পারতেন না তিনি। বাবার কাছে এসে ভর্তি হয়েছিলেন বীণাপাণি বিদ্যাপিঠে। এরপর খুলনার পাইওনিয়ার স্কুল থেকে মাধ্যমিক পাস করেন ।
একদিনে কিন্তু তার সংগ্রামী হয়ে ওঠা হয়নি। জন্মের পর থেকেই দেখেছেন বাবা-মায়ের ঝামেলা। বাবা সৈয়দ বংশের অহংকারী পুরুষ ছিলেন। প্রায়ই মারধোর করতেন স্ত্রীকে। নয় বছর বয়সে নানাবাড়ি ছেড়ে দাদার বাড়িতে উঠলেন ফেরদৌসী। ইংরেজ ঘরানায় তৈরী সেই বাড়িতেও তার কতশত স্মৃতি। ছোট ভাইবোনকে কোলে পিঠে মানুষ করতে হতো। ঘরের কাজে সাহায্যও করতেন মাকে। বয়স ষোল হতেই ভালোবেসে ঘর ছাড়লেন তিনি। কিন্তু পালিয়ে এসে অথই জলে পড়তে হল তাঁকে। লোকটিকে শিক্ষিত বলেই জানতেন তিনি, যা ছিল স্রেফ মিথ্যাচার। কিন্তু মিথ্যুক এই লোকটিকে ছেড়ে যাননি তিনি। তাঁকে সুযোগ দিলেন। স্কুলে ভর্তি করালেন। নিজের হাতে তুলে নিলেন সংসারের সব দায়িত্ব। ছোটখাট চাকরি আর তিন-চারটা টিউশন করে আধপেটা খেয়ে কেটেছে অনেক দিন। ততদিনে তিনি এক সন্তানের মা। সারাদিন চাকরি আর সংসার সামলেও অলস স্বামীর মারধোর সহ্য করে গেছেন মুখ বুজে। কিন্তু একটা সময় বুঝে গেলেন, যথেষ্ট হয়েছে, আর পারবেন না তিনি। অবশেষে ১৯৭১ সালে আলাদা হলেন দুজন।

বড় ছেলের সাথে ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী; Source: The Daily Star
তিন সন্তানকে নিয়ে যখন একটু ঠিকঠাক মতো জীবন শুরু করতে যাচ্ছিলেন তখনই দেশে যুদ্ধ শুরু হল। পাকসেনাদের হাতে ধরা পড়লেন। পরবর্তী সাত মাস তাঁকে অসহনীয় যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে। যুদ্ধশেষে শুরু হলো তার একার লড়াই। বঙ্গবন্ধু নির্যাতিত নারীদের ‘বীরাঙ্গনা’ বলে সম্মান দিয়েছিলেন। কিন্তু যে জাতি নিজে জাতির পিতাকে খুন করতে পারে, তারা বীরাঙ্গনাকে সম্মান দেবে এটা বোধহয় একটু বেশিই চাওয়া। রাস্তাঘাটে চলতে লোকজন শুনিয়ে বলত ‘বারাঙ্গনা’। দমে যেতেন না তিনি। পারিবারিক অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেওয়া হতো না তাঁকে। দাওয়াত দিলেও অস্পৃশ্যের মতো একঘরে করে রাখা হতো। ছোটবেলায় নানাবাড়িতে মামা-খালাদের সাথে একসাথে খেলাধুলা করে বড় হয়েছেন। তারাই দূরে সরিয়ে দিল তাঁকে। এসব উপেক্ষা মাঝে মাঝে সহ্য হতো না তাঁর। চলে যেতেন স্মৃতির গভীরে একাত্তরের সেই ভয়াবহ দিনগুলোতে। অসুস্থ হয়ে পড়তেন ভাবতে গেলেই। দ্বিতীয় স্বামী আহসান উল্লাহ আহমেদ বেগতিক দেখে কোথাও যাওয়াই বন্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ফেরদৌসী কেন লুকিয়ে থাকবেন? তার তো কোনো দোষ ছিল না। স্বামী ছিলেন সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। স্বামীর অগোচরে তার বাড়ির লোকজন সুযোগ পেলেই দু’কথা শুনিয়ে দিতে ভুলত না। প্রিয়ভাষিণী ঠিক করলেন, চাকরি করবেন। ঘরে বাচ্চা রেখে চাকরি করা দুঃসাধ্য ছিল। কিন্তু এই কাজকেও সম্ভব করেছিলেন তিনি।
বড় মামা নাটক লিখতেন। গান কবিতাও চলত সমানে। জনসম্মুখে একাত্তরে নিজের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা তুলে ধরবেন, একথা প্রথমেই জানিয়েছিলেন বড় মামাকে। তিনি তখন মৃত্যুশয্যায়। সে অবস্থাতেই উৎসাহ দিয়েছিলেন প্রিয়ভাষিণীকে। তিনি সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা মাথায় রেখেই এগিয়েছিলেন। ধারণা ছিল, সন্তানেরাও ছেড়ে যাবে তাঁকে।

ভাস্কর্য ‘মেঘের সঙ্গী’; Source: The Daily Star
সমাজ, পরিবার আর নিজের সাথে লড়তে লড়তে যখন বিষণ্ণ, ক্লান্ত হয়ে পড়তেন, তার মন খুলে দিতেন প্রকৃতিকে। গাছের গুড়ি, বাঁশ, নষ্ট হতে থাকা কাঠে তিনি তার কষ্টগুলো তুলে রাখতেন। তিনি বলতেন, এই কষ্টগুলো তিনি সবসময় ইতিবাচকভাবে নিয়েছেন। সাজানো সব স্মৃতি আর কষ্ট কাঠের উপর হয়ে উঠত শিল্প। এসব কিছুই ছিল তার নিজের জন্য। প্রদর্শন বা খ্যাতির ধার ধারেননি কখনো। তার এই শিল্প আবিষ্কার করেন এস এম সুলতান। জাতির কাছে তিনি ভাস্কর ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণীর পরিচয় দেন। যশোর শিল্পকলা একাডেমিতে প্রথম প্রদর্শনীর মাধ্যমে শুরু হয় তার যাত্রা। প্রিয়ভাষিণী বলেন,
“সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা প্রকৃতি থেকে পেলেও সবসময় একজনের অনুপ্রেরণা মাথায় করে রাখি, তিনি হলেন শিল্পী এস এম সুলতান।”

প্রিয়ভাষিণীর একক প্রদর্শনী; Source: alochetron.com
২০১০ সালে তিনি প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মাননা পান। প্রতিবার পুরস্কার পাওয়ার মুহূর্তে শিশুর মত উচ্ছ্বসিত হতেন আনন্দে। দেশে-বিদেশে ভাস্কর হিসেবে নন্দিত হয়েছেন বারবার। তার শিল্পের সাথে জড়িয়ে আছে তার ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প। ক্ষয়ে যাওয়া কাঠ যেভাবে সুন্দর হয়ে ওঠে, তার জীবনটাও যেন তেমনি। ২০১০ সালে সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার স্বাধীনতা পদক পান। ২০১৬ সালে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে মুক্তিযোদ্ধা খেতাব দেয়।

নিজের কাজের সাথে ভাস্কর; Source: swapno71
গত কয়েক বছর ধরেই ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, কিডনির সমস্যা চলছিল তাঁর। গত বছরের নভেম্বর থেকে বেশ কয়বার বাড়ি-হাসপাতাল করার পর সর্বশেষ ২৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকার ল্যাবএইড হাসপাতালে ভর্তি হন। ৬ মার্চ সকালবেলা কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হওয়ার পর জীবনের সব যুদ্ধ শেষ করে পরপারে পাড়ি জমান তিনি। সকল শুভবুদ্ধির মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকবেন প্রিয় সংগ্রামী ভাস্কর, ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী।
ফিচার ইমেজ: liberation.com