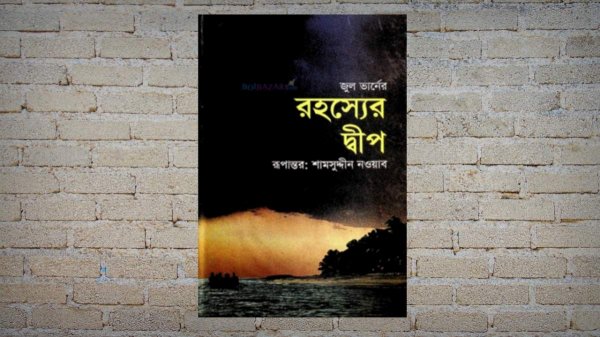চল্লিশের দশকে হলিউড ডার্ক সাবজেক্ট নিয়ে মুভি বানাতে শুরু করে। এই মুভিগুলোর ঘটনাবলি ঘটত কোনো অন্ধকারাচ্ছন্ন সরু গলি-ঘুপচি বা টুইস্টেড সিটি স্কেপে, সর্বত্রই দেখা যেত শ্যাডো বা ছায়ার প্রাধান্য। মুভিগুলো যে কেবল দেখতেই ডার্ক ছিল, তা নয়, গল্পও ছিল ডার্ক এলিমেন্টে ভরা। এসব গল্পের চরিত্ররা ছিল স্বার্থপর, দুর্নীতিপরায়ণ এবং নৈতিকভাবে নমনীয়। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলমান এ ধারা ফিল্ম নোয়ার নাম পায়। এটি একটি ফরাসি প্রত্যয়, যার ইংরেজি অর্থ ‘ডার্ক ফিল্ম’।
১৯৪১ সালে মুক্তি পাওয়া ‘দ্য মলটিস ফ্যালকন’ ফিল্ম নোয়ার জনরার প্রথম দিককার সিনেমাগুলোর একটি এবং এটিকে সবচেয়ে সেরা ফিল্ম নোয়ারের তকমাও দেন অনেকে। কারো কারো মতে, এ সিনেমার মাধ্যমেই এ জনরার জন্ম হয়েছে। সেই বিতর্কে না গিয়েও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রভাবশালী সিনেমার তালিকায় সিনেমাটির নাম উপরের দিকেই থাকবে। হলিউড সিস্টেম থেকে মুক্তি পাওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিনেমাগুলোর একটি এটি। এদিক থেকে এটিকে সমসাময়িক সময়ে মুক্তি পাওয়া ‘সিটিজেন কেইন’-এর সাথে তুলনা করা যায়।
মূলত এ চলচ্চিত্র নির্মাণের মাধ্যমে পরবর্তী সময়ে ফিল্ম নোয়ার জনরার চলচ্চিত্রগুলো কীভাবে নির্মিত হবে, তার একটি কাঠামো তৈরি করে দেন পরিচালক জন হিউস্টন। এ সিনেমা পরবর্তীকালে অপরাধ জনরার সিনেমাসমূহের আলোকসজ্জা, শ্যুটিং ইত্যাদিরও একটি আদর্শ অবকাঠামো স্থাপন করে দেয়।
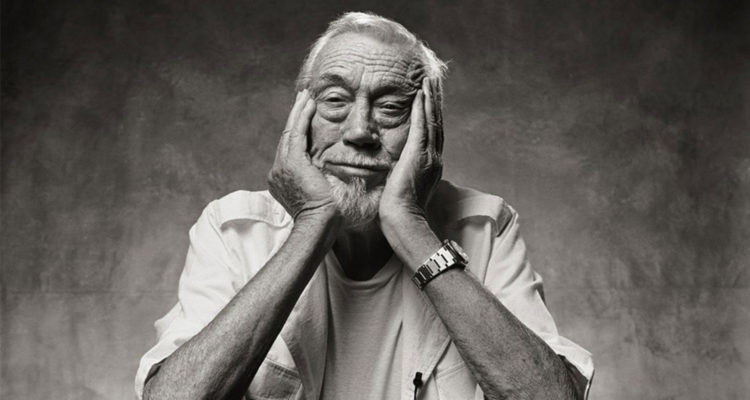
এ সিনেমার মাধ্যমেই পরিচালনায় অভিষেক ঘটে জন হিউস্টনের, যিনি সবচেয়ে বেশি সম্মানিত বা পূজিত আমেরিকান চলচ্চিত্র নির্মাতাদের একজন। অভিনেতা হামফ্রে বোগার্টের ক্যারিয়ারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিনেমা এটি। এটি তার ক্যারিয়ারের গ্রাফ পুরোপুরি বদলে দেয় এবং বি-গ্রেডের পার্শ্বচরিত্র-ভিলেন থেকে এ-গ্রেডের প্রধান চরিত্রে পরিণত করে তাকে। এছাড়া, এই সিনেমায় হিউস্টন বাঁকে বাঁকে টুইস্টে পরিপূর্ণ একটি চিত্তাকর্ষক গল্প বলেন; যার আবেদন মুক্তির সাত দশক পরেও দর্শকের কাছে এতটুকুও কমেনি। এটির আইএমডিবি রেটিং ৮ এবং রটেন টমাটোজের টমেটোমিটারে অবস্থান করছে ১০০ শতাংশ ‘ফ্রেশনেস’ নিয়ে।
দ্য মলটিস ফ্যালকন নির্মিত হয়েছে ড্যাশিয়েল হ্যামেট রচিত একই নামের গোয়েন্দা উপন্যাস থেকে। সম্পূর্ণ উপন্যাস ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হলেও এর আগে উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ‘ব্ল্যাক মাস্ক’ নামক এক স্বল্পমূল্যের পাল্প ম্যাগাজিনে। প্রথম অংশ প্রকাশিত হয় ব্ল্যাক মাস্কের ১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যায়। প্রথমদিকের ফিল্ম নোয়ার সিনেমার বেশিরভাগই এসব ম্যাগাজিনে প্রকাশিত গল্প থেকে অনুপ্রাণিত। গল্পগুলোতে প্রধানত রক্তারক্তি, হানাহানি, প্রতিশোধস্পৃহার মতো বিষয়গুলো স্থান পেত।
এই পাল্প নভেলকে সিনেমায় রূপ দেওয়ার সময় জন হিউস্টন ঐ উপন্যাসের ভিজ্যুয়াল স্টাইলকে পর্দায় নিয়ে এসেছেন এবং এর মাধ্যমে সিনেমাটিতে উদ্ভাবিত হয় এক নতুন ধরনের লাইটিং স্টাইল। নির্দিষ্ট করে বললে, এর নাম ‘লো-কি লাইটিং’। এর বিশেষত্ব হলো, এ ব্যবস্থায় আলোর উৎস থাকে কেবল একটি। তাই, এই লাইটিংয়ের ফলে প্রচুর ছায়ার সৃষ্টি হয়, যা আমরা দেখতে পাই এ সিনেমার বিভিন্ন দৃশ্যে। পরিচালক এখানে আলো-ছায়ার ব্যবহার করেছেন অনবদ্যভাবে। যার ফলে আমরা কেবল রাতে শ্যুটিং হয়েছে এমন একটি মুভিই দেখতে পাই না; বরং ছায়ার সুচিন্তিত ব্যবহারের ফলে আমাদের কাছে মনে হয়, এই পৃথিবীর কালো আর অন্ধকার ব্যাপারগুলোকে যেন নিজের মাঝে টেনে নিয়েছে ‘দ্য মলটিস ফ্যালকন’।
তবে মূল উপন্যাসের সাথে মুভিটির বৈসাদৃশ্যও রয়েছে। মূল উপন্যাসে পুরো গল্পটি বলা হয়েছে তৃতীয় পুরুষের জবানিতে। গল্পের চরিত্ররা কে কী ভাবছে বা তাদের মনের ভেতর কী চলছে, তা বর্ণনা করা হয়নি। কেবল গল্পে কী ঘটছে, সে বিবরণই ছিল। পক্ষান্তরে, জন হিউস্টন তার সিনেমায় প্রত্যেকটি চরিত্রকে নিজেদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন এবং তাদের মনের ভেতরের চিন্তাভাবনাকে তুলে ধরেছেন। আবার পুরো মুভিতে আমরা আলো-আঁধারির আধিক্য দেখলেও কিছু অংশে উজ্বল আলোকসজ্জাও দেখা গেছে। যেমন, গুরুত্বপূর্ণ দুই চরিত্রের একজনের অফিসে এবং আরেকজনের ড্রয়িংরুমে। এই দুই সেটে আলোর উপস্থিতি স্বাভাবিকই ছিল।

‘থার্ড টাইম’স আ চার্ম’, এই ইংরেজি বাগধারাটি এ সিনেমার রূপালি পর্দার সফলতার ক্ষেত্রে পুরোপুরি সত্যি। কারণ, এর আগেও দু’বার হ্যামেটের উপন্যাসটি নিয়ে সিনেমা বানানো হয়েছিল। ওয়ার্নার ব্রাদার্সের হ্যামেটের পটবয়লারটি পছন্দ হয়েছিল এবং উপন্যাস মুক্তি পাওয়ার দুই বছর পর, অর্থাৎ, ১৯৩১ সালে তারা এটির উপর ভিত্তি করে চলচ্চিত্র নির্মাণ করে। সেই সংস্করণে গল্পের মূল চরিত্র স্যাম স্পেডের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল তার উপন্যাসের প্রতিরূপের অনেকটা বিপরীত। হ্যামেটের বাস্তবানুগ, দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরকে ওয়ার্নার ব্রাদার্স পরিণত করেছিল রমণীমোহন ব্যক্তিতে। মধ্যমরকম বাণিজ্যিক সফলতা পেলেও সমালোচকদের কাছ থেকে এ সিনেমা পেয়েছিল তীব্র ভর্ৎসনা।
ওয়ার্নার ব্রাদার্সের পাঁচ বছর পর, ১৯৩৬ সালে হ্যামেটের উপন্যাস অবলম্বনে ‘স্যাটান মেট আ লেডি’ নামে সিনেমা তৈরি করেন উইলিয়াম ডিটার্লি। এটি একটি কমেডি ছিল, যেখানে বেটি ডেভিস অভিনীত ভ্যালেরি পার্ভিস চরিত্রকে দেখা গেছে ‘ফেম ফেটাল’ বা ‘ম্যানইটার’ হিসেবে। মূল উপন্যাসের কাহিনীকে এমনভাবে বদল করা হয়েছিল, যাতে করে নারী চরিত্রটিই প্রধান চরিত্রে পরিণত হয়। সিনেমা এবং এর চরিত্রদের নামধাম পরিবর্তন করা হলেও হ্যামেটকে তার প্রাপ্য কৃতিত্ব দেওয়া হয়েছিল। ডিটার্লির প্রজেক্টটি মুখ থুবড়ে পড়েছিল। অবশেষে, ১৯৪১ সালে হিউস্টন-বোগার্ট যুগলবন্দীতে তৈরি হয় ‘দ্য মলটিস ফ্যালকন’। এটিরও প্রোডাকশন কোম্পানি ছিল ওয়ার্নার ব্রাদার্স। হিউস্টন প্রোডাকশনের খরচ কমাতে কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ অভিনেতাদের ব্যবহার করেন এবং স্বল্পদৈর্ঘ্যের শ্যুটিং শিডিউল নির্ধারণ করেন। তা পরবর্তী সময়ে পুরো হলিউডের গতিপথ বদলে দেয়।
‘দ্য মলটিস ফ্যালকন’ যে কেবল ভিজ্যুয়াল স্টাইলের ক্ষেত্রে নতুনত্ব এনেছিল, তা নয়; বরং এই সিনেমা এক নতুন ধরনের প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরের সাথে দর্শকের পরিচয় করিয়েছে। সিনেমার মুক্তির আগে দর্শক সাধারণত যে ধরনের গোয়েন্দাদের সাথে পরিচিত ছিল, তারা অনেকটা ক্যারিকেচার প্রকৃতির ছিল। হয় তারা চার্লি চ্যানের মতো অতিমাত্রায় বুদ্ধিমান, নয়তো ‘দ্য থিন ম্যান’ সিরিজের নিক আর নোরা চার্লসের মতো অভিজাত এবং অবাস্তব ধরনের ছিল। তাদের অঢেল সম্পত্তি ছিল এবং নিজেরা তেমন কোনো নোংরা না ঘেঁটে পুলিশকে রহস্য উদঘাটনে সাহায্য করত। ‘দ্য থিন ম্যান’ সিরিজ এরকম গোয়েন্দা গল্পের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যদিও এই সিরিজটি ড্যাশিয়েল হ্যামেটের রচিত গল্প থেকেই নির্মিত হয়েছিল, তবু এর সাথে ‘দ্য মলটিস ফ্যালকন’-এর কোনো মিল নেই।

স্যাম স্পেড ছিলেন এদের পুরোপুরি বিপরীত। তিনি কোনো ধনী অনুসন্ধানকারী ছিলেন না, যিনি অবসরে শখের বসে রহস্যের মীমাংসা করতেন। তিনি ছিলেন মুখরা, রূঢ় এক গোয়েন্দা; যিনি সবকিছুর আগে নিজের কথা ভাবতেন। এ গল্পের মূল চরিত্র হলেও তাকে কিছুতেই নায়ক বলা যায় না। হয়তো বড়জোর অ্যান্টি-হিরো বলা যায়। গল্পে একসময় নিজের লাভ দেখে তিনি ভিলেনদের দলেও যোগ দেন। যাদের একজন আবার তার পার্টনারকে হত্যাও করেছে। তবু দর্শক তাকে পছন্দ করে ফেলে এবং এর কারণ তার অকপটতা। তার কার্যকলাপ, এই দুনিয়া এবং তাতে তার ভূমিকার ব্যাপারে রাখঢাক না রেখে সরাসরি কথা বলেন তিনি। তিনি সাথে পিস্তল রাখেন না, তবে প্রয়োজনে পিস্তল ব্যবহার করতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না।
১৯৪১ সালের আগে এ ধরনের গোয়েন্দাও যে হতে পারে, তা দর্শকের ভাবনাতেও ছিল না। এবং এ সিনেমার মুক্তির পর ক্রাইম বা ডিটেকটিভ জনরার চলচ্চিত্রে গোয়েন্দাদের এরূপ আচরণ করা একটি স্ট্যান্ডার্ডে পরিণত হয়। হামফ্রে বোগার্টের অনবদ্য পারফর্ম্যান্স ‘স্যাম স্পেড’কে দিয়েছে অমরত্ব।
এবারে সিনেমার প্লটের দিকে নজর দেওয়া যাক। সিনেমার শুরুতে আমরা দেখি, প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর স্যাম স্পেড (হামফ্রে বোগার্ট) তার অফিসে সেক্রেটারি এফি (লি প্যাট্রিক)-এর সাথে খুনসুটি করছেন। এ সময় সেখানে আসেন ফেম ফেটাল ব্রিজিড ও’শনেসি (ম্যারি অ্যাস্টর)। এই ‘ফেম ফেটাল’ শব্দগুচ্ছকে ক্রাইম জনরার সিনেমায় প্রায়শই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এটি দ্বারা মূলত সেসকল নারীদেরকে বোঝানো হয়, যারা তাদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করা পুরুষদের জীবনে দুর্দশা নিয়ে আসেন। যা-ই হোক, ব্রিজিড, স্যাম এবং তার পার্টনার মাইলস আর্চারকে (জেরোম কাওয়ান) কাজে নিযুক্ত করতে চান।
তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার বোনকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে সান ফ্রান্সিসকো নিয়ে এসেছে। তারা যদি তার বোনকে ঐ লোকের কবল থেকে মুক্ত করতে পারেন, তাহলে তিনি তাদেরকে ২০০ ডলার দেবেন। তবে এ কাজ করতে গিয়ে তাদের বিপদ হতে পারে। এই কেইস সংক্রান্ত কাজে গোপনে নজরদারি করতে গিয়ে মাইলস খুন হন। তবে মাইলসের মৃত্যু স্যামকে তেমন একটা বিচলিত করে না। বরং এটিকে তিনি একটি সুযোগ হিসেবে দেখেন। এতে করে পুরো এজেন্সির একচ্ছত্র মালিকে পরিণত হলেন তিনি। উপরন্তু, মাইলসের স্ত্রীর সাথে পরকীয়ার সম্পর্ক ছিল তার। এতে করে তিনি এই ঝামেলা থেকেও বেঁচে গেলেন!

তথাপি, স্যাম যে কোড বা নিয়ম মেনে জীবন পরিচালনা করেন; সে অনুযায়ী, মাইলসের খুনীদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি পাওয়া প্রয়োজন। আর স্যামও তাদেরকে বিচারের সম্মুখীন করতে কাজে নেমে পড়েন। এক্ষেত্রে তার কাছে থাকা সবচেয়ে বড় সূত্র হলো ব্রিজিড। তাই তার ব্যাপারে ভালোমতো জেনে অনুসন্ধান শুরু করবেন বলে ঠিক করেন তিনি। অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে তিনি বুঝতে পারেন, ব্রিজিডের কোনো বোন আসলে নেই! বরং এই পুরো ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু কালো রংয়ের ক্ষুদ্রাকৃতির একটি বাজপাখির মূর্তি। অমূল্য এই মূর্তিটি বর্তমানে কোথায় আছে, তা কেউ জানে না। মূর্তিটির অনুসন্ধানের পথে স্যামের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড়িয়ে যান জোয়েল কাইরো (পিটার লোরি), ‘ফ্যাট ম্যান’ ক্যাসপার গাটম্যান (সিডনি গ্রিনস্ট্রিট) এবং গাটম্যানের চ্যালা ‘লিটল বয়’ উইলমার কক (এলিশা কুক জুনিয়র)।
মূর্তি সংক্রান্ত রহস্যের পুরোপুরি খোলাসা হতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগে এবং এটির সাথে ব্রিজিড কীভাবে সংশ্লিষ্ট, তা-ও জানা যায়। জটিল হলেও স্যাম শেষপর্যন্ত এ রহস্যের যবনিকাপাত করতে পারেন। ইতিহাসে উৎসাহী ব্যক্তিরা হয়তো ইতোমধ্যেই বুঝে গেছেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকা জাপানে যে দু’টি পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করেছিল; সেগুলোর নাম গাটম্যান এবং ককের নাম থেকেই নেওয়া হয়েছিল। গাটম্যানকে ‘লার্জার দ্যান লাইফ’ ভিলেনের রূপ দিতে হিউস্টন আর সিনেম্যাটোগ্রাফার আর্থার এডেসন মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। পর্দায় তাকে বেশিরভাগ সময়ই দেখা গেছে নিচু অ্যাঙ্গেল থেকে। এর ফলে ডায়লগ ডেলিভারির সময় তাকে টাওয়ারের মতো বা দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখা গেছে; যা বিদ্যমান পরিস্থিতির তার কর্তৃত্বের প্রকাশক।
এ সিনেমার পর বোগার্ট পরিচালনায় সদ্য অভিষিক্ত জন হিউস্টনের সাথে অনেকটা প্যাকেজ ডিলে পরিণত হন৷ এই জুটিকে ‘কি লার্গো’ (১৯৪৮), ‘দ্য আফ্রিকান কুইন’ (১৯৫১) সহ আরো পাঁচটি সিনেমায় একসাথে কাজ করতে দেখা গেছে। আগেই বলা হয়েছে, এ লেখায় ‘দ্য মলটিস ফ্যালকন’ই প্রথম ফিল্ম নোয়ার কি না- সে তর্কে আমরা যাব না। জন হিউস্টন একাই এই জনরা আবিষ্কার না করলেও তিনি সিনেমা তৈরির হলিউডি কলাকৌশলের সাথে জার্মান এক্সপ্রেশেনিজমের উপাদানের সংযুক্তি ঘটান। ফলে এ সিনেমা সমকালীন অন্যান্য সিনেমা থেকে ভিন্ন রূপ লাভ করে। পরে ৪০ এবং ৫০-এর দশকে অপরাধ এবং গোয়েন্দা ঘরানার সিনেমা পরিচালনার ক্ষেত্রে সকলের কাছে ফিল্ম নোয়ারই একমাত্র পন্থা বলে বিবেচিত হয়। চলচ্চিত্র সাদা-কালো থেকে রঙিন জগতে প্রবেশ করলেও এ পদ্ধতির অপরিহার্য অংশগুলো নতুন যুগের পরিচালকদের দ্বারা এখনো ব্যবহৃত এবং পরিশীলিত হচ্ছে।
এখানকার কুশীলবদের মধ্যকার রসায়ন অনন্য। মূল পাঁচ চরিত্রকে (স্যাম, ব্রিজিড, গাটম্যান, কাইরো, কুক) মুভির শেষের দিকে ২০ মিনিট একই কক্ষে দেখতে পাই আমরা। এ সময়ে তাদের অভিনয়ে দর্শক মোহিত হতে বাধ্য। ‘দ্য মলটিস ফ্যালকন’-এই প্রথমবারের মতো ক্যামেরার সামনে দাঁড়ান সিডনি গ্রিনস্ট্রিট। বোগার্ট, লোরি এবং গ্রিনস্ট্রিট ত্রয়ীর রসায়ন এতটাই মোহনীয় যে এদেরকে ‘ক্যাসাব্লাঙ্কা’ (১৯৪২) এবং ‘প্যাসেজ টু মার্শেই’ (১৯৪৪) সিনেমায় একসাথে আরো দু’বার পর্দায় দেখা গেছে।
এ সিনেমাতেই স্যাম এবং গাটম্যানের যখন প্রথম দেখা হয়, তখন লম্বা, বিরতিহীনভাবে টেক করা একটি দৃশ্য রয়েছে। এ দৃশ্যের মাহাত্ম্য নিয়ে খুব একটা আলোচনা হতে দেখা যায় না। কারণ, দৃশ্যটি হিউস্টনের গল্প বলার সাথে খুব ভালোভাবে মিশে গেছে। আর পুরো সিনেমার গল্প বলার ধরন এত ভালো যে এই দৃশ্যকে আলাদাভাবে কৃতিত্ব দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সিনেমাপ্রেমী মাত্রই এই দু’জন যে কত বড় মাপের অভিনেতা ছিলেন, সে পরিচয় পাবেন এই দৃশ্যে।
ব্রিজিড চরিত্রের জন্যে ম্যারি অ্যাস্টর প্রথম পছন্দ ছিলেন না হিউস্টনের। তিনি এ চরিত্রে জেরল্ডিন ফিটজেরাল্ডকে নিতে চেয়েছিলেন। তবে সেই সময়ে পর্দার বাইরে অ্যাস্টরের বেশ কুখ্যাতি ছিল। যার ফলে এই চরিত্রে সম্পূর্ণভাবে তিনি মিশে যেতে পারবেন বলে মনে করেন এই পরিচালক। আর পরে যা হলো, তা তো ইতিহাস।

এত বছর পরে স্যাম স্পেডের চরিত্রে বোগার্টের বদলে অন্য কাউকে চিন্তাই করা যায় না। তাই এইউপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত বাকি দু’টি সিনেমা দেখতে গেলে দর্শকের অদ্ভূত অনুভূতি হতে পারে। বোগার্ট যেন হ্যামেটের বর্ণিত এই চরিত্রকে পুরোপুরি নিজের মধ্যে ধারণ করেছেন। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত স্যামকে এতটাই অনুভূতিহীন করে ফেলেছে, যে ভালোবাসাও তার ভেতর প্রাণরস সঞ্চার করতে পারে না। তারপরও তার ভেতর কোথাও না কোথাও মনুষ্যত্ব বাস করে, যা মাঝেমধ্যে উঁকি দেয় তার চোখের ভেতর দিয়ে।
স্যামের চিত্রায়ণে বোগার্টের দ্রুতগতির ছাঁটা ছাঁটা সংলাপ পরিণত হয়েছে সিনে ইতিহাসের আইকনিক ব্যাপারে। বোগার্টকে নিয়ে ভাবতে গেলে চলচ্চিত্রপ্রেমীদের মনে আসে তার অভিনীত ‘ক্যাসাব্লাঙ্কা’র রিক চরিত্রটি। তবে এই রিকের ভেতর স্যামের বেশকিছু বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়। ‘দ্য মলটিস ফ্যালকন’ মুক্তি পাওয়ার আগে বোগার্ট তেমন কোনো তারকা ছিলেন না। এই সিনেমা তাকে হলিউডের আকাশের অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্রে পরিণত করে। এবং তারপর প্রায় দেড় দশক পর্দা এবং পর্দার বাইরে তিনি হলিউডে রাজত্ব করেন।
প্রথমদিকে এ সিনেমাকে প্লট-ড্রিভেন বলে মনে হয়। দর্শক ভাবতে পারেন, প্লটই এই সিনেমার সবচেয়ে শক্তিশালী অংশ। কিন্তু কেউ যদি এই সিনেমার বাজপাখি বা ফ্যালকনের মূর্তিকে একটি ‘ম্যাকগাফিন’ বলে বিবেচনা করেন, তাহলে দেখতে পাবেন, এটি আসলে অনেকটা ক্যারেক্টার স্টাডির মতো। ম্যাকগাফিন বলতে কোনো সিনেমা বা বইয়ের গল্পে বিদ্যমান কোনো একটি বস্তু বা যন্ত্রকে বোঝায়; যেটি গল্প বা প্লট অথবা কোনো চরিত্রকে একটি নির্দিষ্ট দিকে পরিচালনা করে।
এ সিনেমায় কোনো চিরাচরিত ‘ভালো মানুষ’ নেই। আইনকে সমুন্নত রাখতে স্যাম স্পেড এ রহস্যের উদঘাটন করতে নামেন না। বরং তিনি এই রহস্য উদঘাটন করতে চান নিজের একান্ত ব্যক্তিগত কোডকে সমুন্নত রাখতে। আর তা করতে গিয়ে তিনি নিজের এবং আশেপাশের অন্যদের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলেন। তার কার্যকলাপকে দর্শকরা সমর্থন করে, কারণ স্যামের মতো তাদেরও মনে হয়, স্যাম কিছুটা ভিন্নপথে হলেও এখনও ভালোদের দলে বা তিনি কিছুটা ‘কম খারাপ’। তারই মতো তাদেরও হয়তো মনে হয়, বাঁকা পথে হলেও এ ঘটনার একটা সুখকর সমাপ্তি সম্ভব। কিন্তু সিনেমা বা বাস্তবিক দুনিয়া; কোনোক্ষেত্রেই তা সঠিক নয়।
‘দ্য মলটিস ফ্যালকন’ই ডিটেকটিভ জনরার সবচেয়ে সেরা সিনেমা কি না, সে নিয়ে তর্ক করা যায়। কিন্তু এ তর্কের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। এই সিনেমাকে আধুনিক ক্রাইম বা ডিটেকটিভ জনরার সিনেমার পূর্বপুরুষ বলা যায় নিঃসন্দেহে। এসকল সিনেমার বেশকিছুকে এই সিনেমার সাথে একই স্তরে রাখা যায়। কিছু হয়তো মানের দিক থেকে এটিকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে।
আজ ৭০ বছর পর এটি হয়তো নতুন সিনেমাপ্রেমীদেরকে টেকনিকের দিক থেকে ততটা অভিভূত করতে পারবে না। তবে এই সিনেমার মাধ্যমে চলচ্চিত্র নির্মাণে কারিগরি দিক থেকে যে নতুনত্ব এসেছিল, তা পরে চলচ্চিত্র শিল্পের অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়। তাই বর্তমান প্রজন্মের দর্শকরা হয়তো এ ধরনের টেকনিকে নির্মিত সিনেমা আগেই দেখে ফেলেছেন। এতকিছুর পরও চিত্রনাট্যে হ্যামেটের মূল উপন্যাসের সংলাপসমূহের অপরিবর্তিত সংযোজন, বোগার্টের টপ নচ পার্ফম্যান্স, পরিচালক হিসেবে জন হিউস্টনের শৈল্পিক স্বাধীনতা এবং পৃথিবীর প্রথম নির্মিত ফিল্ম নোয়ারগুলোর একটি হিসেবে এই সিনেমা দেখার অভিজ্ঞতা তুলনাহীন।

এই সিনেমার মূল আকর্ষণ সম্ভবত এর গল্প এবং চরিত্রদের অস্পষ্টতা বা রহস্যময়তা। মূল রহস্য কেবল কে স্যামের পার্টনারকে হত্যা করেছে, তা নয়; বরং মূল রহস্য এখানে কে আসল, আর কে নকল? যারা ইতোমধ্যেই এটি দেখে ফেলেছেন, তারা এ গল্পের অস্পষ্টতা নিয়ে আরেকবার ভাবুন।
প্লটের এগিয়ে যাওয়ার মূল চালিকাশক্তি কে স্যামের পার্টনারকে হত্যা করেছে, সে রহস্যের উদঘাটন করা। কিন্তু, পাশাপাশি আরো বেশকিছু রহস্য থেকে যায় এখানে। স্যামের এজেন্সিতে এসে তাকে কাজে নিযুক্ত করা এই অজ্ঞাত নারীটি আসলে কে? তিনি কি তাকে আসলেই ভালোবাসেন, না কি ভালোবাসার অভিনয় করেছেন? স্যামের ব্যাপারটাইবা কী? তিনি কি তাকে ভালোবাসেন, না কি তিনিও কেবল অভিনয় করছেন? মূর্তির পেছনে হন্যে হয়ে লেগে পড়া এই মানুষগুলো কারা?
আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দু’টি প্রশ্ন তো রয়েছেই। কোথায় আছে মলটিস ফ্যালকন? কেনইবা এটির জন্য কিছু মানুষ হত্যা করতেও পিছপা হচ্ছে না? আর যখনই মনে হয়, এখন দর্শকরা তাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন, তখনই আরো নানা প্রশ্ন এসে ভিড় করে তাদের মনে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে আমরা বুঝতে পারি, স্যাম স্পেডের অনুভূতি ছাড়াও এই দুনিয়াতে আরো বহু জিনিস আছে, যেগুলো মেকি। এটি ফিল্ম নোয়ারের একটি অনবদ্য উদাহরণ, পাশাপাশি অসাধারণ একটি মার্ডার মিস্ট্রি। তাই সাদা-কালো সিনেমা দেখতে সমস্যা না থাকলে নির্দ্বিধায় দেখে ফেলা যায় ‘দ্য মলটিস ফ্যালকন’।