.jpg?w=1200)
১৯৯০ সালের ২ আগস্ট ইরাক কুয়েত দখল করে নেয় এবং এর মধ্য দিয়ে উপসাগরীয় যুদ্ধ (১৯৯০–১৯৯১) শুরু হয়। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বৃহদাংশ ইরাকের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে এবং জাতিসংঘ ইরাকের ওপর কঠোর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে। সম্ভাব্য ইরাকি আক্রমণের আশঙ্কায় সৌদি আরব নিজ ভূমিতে মার্কিন সৈন্য মোতায়েনের অনুমতি প্রদান করে। ইরাকি দখলদারিত্ব থেকে কুয়েতকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ৩৫টি রাষ্ট্রের সমন্বয়ে একটি আন্তর্জাতিক সামরিক জোট গঠিত হয়। এই জোটের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ছিল ১৩টি মুসলিম রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রগুলো ছিল: কুয়েত, সৌদি আরব, মিসর, সিরিয়া, মরক্কো, ওমান, পাকিস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, নাইজার, সেনেগাল, বাহরাইন এবং বাংলাদেশ।
বাংলাদেশ উপসাগরীয় যুদ্ধে মার্কিন–নেতৃত্বাধীন জোটের অংশ ছিল এবং এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ২,৩০০ সৈন্য প্রেরণ করেছিল। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর এটি ছিল বাংলাদেশি সৈন্যদের জন্য প্রথম বৈদেশিক যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ নিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উপসাগরীয় যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে ইরাক, কুয়েত ও সৌদি আরব এই তিনটি উপসাগরীয় আরব রাষ্ট্রের সঙ্গেই বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। এই প্রেক্ষাপটে উপসাগরীয় যুদ্ধে বাংলাদেশের জন্য ৩টি পথ খোলা ছিল– ইরাকের পক্ষ অবলম্বন করা, নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করা, অথবা কুয়েত ও সৌদি আরবের পক্ষ অবলম্বন করা। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রথম দুইটি পথ গ্রহণ না করে শেষটিকেই কেন বেছে নিয়েছিল?
এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে উপসাগরীয় যুদ্ধ বাংলাদেশের ওপর কেমন প্রভাব ফেলেছিল সেটির আলোচনা করা যাক। উপসাগরীয় যুদ্ধের ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল। উপসাগরীয় যুদ্ধ শুরুর আগে কুয়েতে প্রায় ৭০,০০০ বাংলাদেশি নাগরিক কর্মরত ছিল এবং তাদের প্রেরিত রেমিট্যান্স ছিল বাংলাদেশের জন্য একটি বৃহৎ আয়ের উৎস। ১৯৯০ সালের ২ আগস্ট ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখলের ফলে কুয়েতে অবস্থানরত বাংলাদেশিরা বিপজ্জনক এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। ১৯৯০ সালের ২২ আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে সৌদি আরব ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (International Organization for Migration, ‘IOM’) সহায়তায় বাংলাদেশি সরকার এই অভিবাসীদের দেশে ফিরিয়ে আনে। এর ফলে কুয়েত থেকে রেমিট্যান্স আসা বন্ধ হয়ে যায় এবং কুয়েতফেরত অভিবাসীদের পুনর্বাসনের জন্য বাংলাদেশকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়।

তদুপরি, উপসাগরীয় যুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে বিশ্বব্যাপী জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং জ্বালানি তেল আমদানিকারক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাংলাদেশি সরকারের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, উপসাগরীয় যুদ্ধের ফলে বাংলাদেশের ১৪০ কোটি (বা ১.৪ বিলিয়ন) মার্কিন ডলার সমমূল্যের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। একটি দরিদ্র ও অনুন্নত রাষ্ট্র হিসেবে এটি ছিল বাংলাদেশের জন্য অর্থনৈতিক বিপর্যয়স্বরূপ।
উপসাগরীয় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বাংলাদেশি সরকার তাদের পরবর্তী কার্যপ্রণালী নিয়ে দ্বিধার সম্মুখীন হয়। কুয়েতের বিরুদ্ধে ইরাকের খোলাখুলি আগ্রাসন ছিল এই যুদ্ধ শুরুর মূল কারণ। কিন্তু সরাসরি ইরাকের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করা বাংলাদেশের জন্য সহজ ছিল না।
প্রথমত, আরব সমাজতন্ত্রী ও ইরাকি জাতীয়তাবাদী ‘বাআস’ দলের (Ba’ath Party) অধীনস্থ ইরাক ছিল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম আরব রাষ্ট্র। ইরাকে প্রচুর বাংলাদেশি কর্মরত ছিল, ইরাক ছিল বাংলাদেশের জ্বালানি তেলের অন্যতম প্রধান উৎস, এবং ১৯৮৮ সালের বন্যার সময়েও ইরাক বাংলাদেশকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সহায়তা প্রদান করেছিল। এক কথায়, ইরাকের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক ছিল খুবই ভালো এবং রাষ্ট্র দুইটির মধ্যে কোনো উল্লেখযোগ্য বিরোধ ছিল না।
দ্বিতীয়ত, ইরাকি রাষ্ট্রপতি সাদ্দাম হুসেইন তার ইসলামপন্থী, ফিলিস্তিনপন্থী এবং ইসরায়েলবিরোধী বক্তব্যের জন্য বাংলাদেশি জনসাধারণের মধ্যে বিপুলভাবে জনপ্রিয় ছিলেন এবং এজন্য বাংলাদেশি সরকারের জন্য ইরাকের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করা ছিল রাজনৈতিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সাদ্দাম এবং তার ‘বাআস’ দল ছিল মূলত ধর্মনিরপেক্ষ, কিন্তু বিশেষ করে ইরাক–ইরান যুদ্ধের সময় থেকে সাদ্দাম রাজনৈতিক স্বার্থে ইসলামকে ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন।

তৃতীয়ত, ইরাক ‘কুয়েত সমস্যা’র সমাধানের সঙ্গে ‘ফিলিস্তিন সমস্যা’ সমাধানের বিষয়টি সম্পর্কযুক্ত করেছিল এবং ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বাধীন ‘ফিলিস্তিনি মুক্তি সংস্থা’ (Palestine Liberation Organization, ‘PLO’) উপসাগরীয় যুদ্ধে ইরাকের পক্ষ অবলম্বন করেছিল। বাংলাদেশ প্রথম থেকেই ফিলিস্তিনিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের পক্ষে ছিল এবং এজন্য ইরাকের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলে বাংলাদেশ কার্যত ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে (এবং ইসরায়েলের পক্ষে) অবস্থান নিচ্ছে বলে ধরে নেওয়া হতে পারে, এই সম্ভাবনাও ছিল।
সর্বোপরি, বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সঙ্গে ইরাকি রাষ্ট্রপতি সাদ্দামের ব্যক্তিগত সম্পর্কও ছিল ভালো। ফলে বাংলাদেশের জন্য ইরাকের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণের ব্যাপারটি ছিল অস্বস্তিকর। বলাই বাহুল্য, ইরাক এই যুদ্ধে ইরাকের পক্ষ অবলম্বন অথবা অন্ততঃপক্ষে নিরপেক্ষ থাকার জন্য বাংলাদেশকে চাপ দিচ্ছিল।
অর্থাৎ, উপসাগরীয় যুদ্ধে ইরাকের পক্ষাবলম্বন বা নিরপেক্ষ থাকার জন্য বাংলাদেশের যথেষ্ট কারণ ছিল। কিন্তু এর বিপরীতে মার্কিন–নেতৃত্বাধীন জোটে যোগদানের জন্যও বাংলাদেশের যথেষ্ট কারণ ছিল।
প্রথমত, অনেক বিশ্লেষকের মতে, বৃহৎ রাষ্ট্র ইরাক কর্তৃক প্রতিবেশী ক্ষুদ্র রাষ্ট্র কুয়েত দখলকে সমর্থন করা নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের পক্ষে সম্ভব ছিল না। বাংলাদেশ নিজেই একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র এবং প্রতিবেশী বৃহৎ রাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে ১৯৭৫ সালের পর বাংলাদেশের সম্পর্ক তেমন ভাল ছিল না। এই প্রেক্ষাপটে বৃহৎ রাষ্ট্র কর্তৃক বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে দখলের প্রতি সমর্থন প্রদান বাংলাদেশের জন্য ভবিষ্যতে ‘বুমেরাং’ হয়ে দেখা দিতে পারত। কিন্তু এই যুক্তিটি পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ এর আগে বাংলাদেশ ১৯৭৫–১৯৭৬ সালে ইন্দোনেশিয়া (বৃহৎ রাষ্ট্র) কর্তৃক পূর্ব তিমুর (ক্ষুদ্র রাষ্ট্র) দখলকে সমর্থন জানিয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের সঙ্গে কুয়েত ও সৌদি আরবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এবং সৌদি–কুয়েতি জোটের পক্ষ অবলম্বন করলে তাদের কাছ থেকে বাংলাদেশের প্রচুর পরিমাণ অর্থনৈতিক সহায়তা লাভের সম্ভাবনা ছিল। ১৯৯০ সালের আগস্টে সৌদি বাদশাহ ফাহাদের একজন বিশেষ দূত ঢাকায় এসেছিলেন এবং বাংলাদেশকে সৌদি–মার্কিন জোটের পক্ষ অবলম্বনের জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন।
তৃতীয়ত, ইসলামের পবিত্র স্থান মক্কা ও মদিনা সৌদি আরবে অবস্থিত এবং এজন্য বাংলাদেশের জনসাধারণের একাংশ সৌদি আরবের প্রতি নমনীয়। তাই সৌদি আরবকে সহায়তার জন্য সৈন্য প্রেরণ করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশি জনসাধারণের এই অংশের সমর্থন লাভ করাও বাংলাদেশি সরকারের একটি উদ্দেশ্য ছিল।
চতুর্থত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্বের পক্ষ অবলম্বনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ পশ্চিমা আর্থিক সহায়তা লাভ করতে পারত এবং পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের উন্নতি হত। বস্তুত ১৯৭৫ সালের পর থেকে বাংলাদেশ পশ্চিমামুখী পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করেছিল এবং উপসাগরীয় যুদ্ধে মার্কিন–নেতৃত্বাধীন জোটে অংশগ্রহণ ছিল এরই স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ।

সর্বোপরি, উপসাগরীয় যুদ্ধ যখন শুরু হয়, তখন বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ অবনতির দিকে যাচ্ছিল এবং রাষ্ট্রপতি এরশাদ বিরোধী দলগুলোর আন্দোলনের ফলে ক্ষমতাচ্যুত হতে পারেন, এমন একটি সম্ভাবনাও ছিল। স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালে পশ্চিমা বিশ্ব তৃতীয় বিশ্বের বহু স্বৈরশাসককে (যেমন: এরশাদ) তাদের কমিউনিজম–বিরোধিতার কারণে সমর্থন করেছিল। কিন্তু ১৯৮৯–১৯৯০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপে কমিউনিজমের পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল এবং এজন্য তৃতীয় বিশ্বের অগণতান্ত্রিক সরকারগুলোকে সমর্থন করার প্রয়োজন ফুরিয়ে এসেছিল। কিছু কিছু বিশ্লেষকের মতে, এই অবস্থায় নিজস্ব ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে এরশাদ উপসাগরীয় যুদ্ধে ইরাকের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন।
বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদের মতে, উপসাগরীয় যুদ্ধে অংশগ্রহণের বিষয়টি ছিল বাংলাদেশের জন্য ‘অত্যন্ত কঠিন ও সূক্ষ্ম’ একটি বিষয়। কিন্তু বাংলাদেশের সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় স্বার্থ (এবং ক্ষমতাসীন সরকারের স্বার্থ) বিবেচনা করে বাংলাদেশ শেষ পর্যন্ত ইরাকের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে এবং মার্কিন–নেতৃত্বাধীন জোটে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়।
এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সৌদি আরবে ২,৩০০ সৈন্য প্রেরণ করে। প্রেরিত বাংলাদেশি সৈন্যদের সিংহভাগই ছিল সাপোর্ট ইউনিটের সদস্য, তাছাড়া ২টি ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্স ইউনিটও ছিল। এই অভিযানটিকে ‘অপারেশন মরু প্রান্তর’ নামকরণ করা হয়েছিল। প্রেরিত বাংলাদেশি সৈন্যদলটিকে সৌদি সামরিক কমান্ডের অধীনে রাখা হয়েছিল এবং তাদেরকে সৌদি–ইরাকি সীমান্ত থেকে দূরে দাহরান শহরের পূর্বে মোতায়েন করা হয়েছিল। বস্তুত বাংলাদেশি সৈন্যরা কোনো যুদ্ধে সরাসরি অংশ নেয়নি। সেসময় সৌদিদের পর্যাপ্ত লজিস্টিক্স বা কমব্যাট সাপোর্ট ইউনিট ছিল না, এবং বাংলাদেশি সৈন্যরা এই ঘাটতি পূরণ করেছিল। এজন্য যুদ্ধ শেষে সৌদি সরকার বাংলাদেশের প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিল। বাংলাদেশি সরকারের তথ্যমতে, এই অভিযান চলাকালে কোনো বাংলাদেশি সৈন্য প্রাণ হারায়নি।
মার্কিন–নেতৃত্বাধীন জোটে সৈন্য প্রেরণের সিদ্ধান্তকে বাংলাদেশের জনসাধারণ ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেনি। সরকারের এই সিদ্ধান্তটি তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল। ১৯৯০ সালের ৩ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো (বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় জোট এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট) উপসাগরীয় যুদ্ধে সৈন্য প্রেরণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করে। জনরোষকে প্রশমিত করার জন্য বাংলাদেশি সরকার জানায় যে, বাংলাদেশি সৈন্যরা সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেবে না এবং কেবল সৌদি আরব আক্রান্ত হলেই বাংলাদেশি সৈন্যদের সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণের সম্ভাবনা দেখা দেবে।
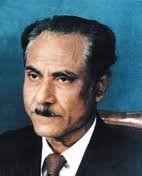
ইতোমধ্যে বাংলাদেশে সরকারবিরোধী আন্দোলন ক্রমশ তীব্র হতে থাকে এবং অবশেষে আন্দোলনের চাপে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি এরশাদ পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। শাহাবুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বাংলাদেশের শাসনক্ষমতা গ্রহণ করে। কিন্তু সরকারের পরিবর্তন ঘটলেও উপসাগরীয় যুদ্ধের প্রতি বাংলাদেশের নীতির পরিবর্তন ঘটেনি। বাংলাদেশি সৈন্যরা সৌদি আরবে অবস্থান করতে থাকে এবং বাংলাদেশের নতুন সরকারও এই সিদ্ধান্তের প্রতি জনসমর্থন আদায়ের জন্য প্রচেষ্টা চালায়, কিন্তু তাদের এই প্রচেষ্টা মোটের ওপর সফল হয়নি।
১৯৯১ সালের ১৭ জানুয়ারি কুয়েত থেকে ইরাকি সৈন্য প্রত্যাহারের বিষয়ে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রদত্ত সময়সীমা শেষ হয় এবং মার্কিন–নেতৃত্বাধীন জোট ইরাকের ওপর ব্যাপক আকারে ‘কৌশলগত বিমান হামলা’ শুরু করে। বাংলাদেশে এর তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। প্রায় ১০,০০০ বাংলাদেশি নাগরিক রাজধানী ঢাকায় ইরাকি রাষ্ট্রপতি সাদ্দামের ছবিসহ ইরাকের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে বিক্ষোভ করে। বিক্ষোভকারীরা মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশের কুশপুত্তলিকা দাহ করে, মার্কিন, সৌদি ও মিসরীয় দূতাবাসে পাথর নিক্ষেপ করে, ১টি মার্কিন ক্লাব ও ১টি সৌদি স্কুল ভাঙচুর করে এবং কিছু পশ্চিমা নাগরিকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। এর ফলে প্রায় ৪৫০ জন মার্কিন ও ব্রিটিশ নাগরিক নিরাপত্তা সঙ্কটের কারণে বাংলাদেশ ত্যাগ করে। ঢাকার বাইরে অন্যান্য শহরেও ইরাকের ওপর আক্রমণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়।
বিদেশি দূতাবাসের ওপর আক্রমণের ফলে বাংলাদেশের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি হয় এবং বাংলাদেশি সরকার এজন্য বিদেশি দূতাবাসের আশেপাশে মিছিল করার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। কূটনৈতিক অঞ্চলগুলোতে আগ্নেয়াস্ত্র বা অন্য যে কোনো ধরনের অস্ত্রশস্ত্র বহনের ওপরেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বিষয়ে বিক্ষোভ অব্যাহত থাকে।

ইতোমধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, ইরাকি স্কাড ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় সৌদি আরবে শতাধিক বাংলাদেশি সৈন্য নিহত হয়েছে। এর ফলে সৌদি আরবে প্রেরিত বাংলাদেশি সৈন্যদের পরিবারের সদস্যরা ঢাকায় ‘শান্তির মার্চ’ বের করে এবং উপসাগরীয় যুদ্ধের অবসান ও সৌদি আরব থেকে বাংলাদেশি সৈন্য প্রত্যাহারের দাবি জানায়। বাংলাদেশি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় তাদেরকে এই বলে আশ্বস্ত করে যে, সৌদি আরবে বাংলাদেশি সৈন্য নিহত হওয়ার সংবাদটি মিথ্যা এবং সেখানে প্রেরিত সকল বাংলাদেশি সৈন্য নিরাপদেই আছে।
১৯৯১ সালের ২১ জানুয়ারি তুরাগ নদীর তীরে আয়োজিত বিশ্ব ইজতেমাও ইরাকপন্থী একটি জনসমাগমে পরিণত হয়। প্রায় ৫ লক্ষ মানুষ এই ইজতেমায় অংশ নিয়েছিল এবং এদের মধ্যে প্রায় ১০,০০০ বিদেশি নাগরিকও ছিল। এই ইজতেমায় ইরাকি পতাকা উত্তোলন করা হয়, সাদ্দামের ছবি প্রদর্শিত হয় এবং ইরাকের জন্য মোনাজাত করা হয়।
বাংলাদেশি জনসাধারণের এই প্রতিক্রিয়া বহুলাংশে স্বতঃস্ফূর্ত হলেও এর পিছনে ইরাকি কূটনীতিবিদদেরও কিছু ভূমিকা ছিল বলে মনে করা হয়। বাংলাদেশি সরকার এই বিক্ষোভগুলো উস্কে দেওয়া ও বিদেশি দূতাবাসগুলোর ওপর আক্রমণ চালানোর জন্য বাংলাদেশে অবস্থানরত ইরাকি দূতাবাসকে দায়ী করে এবং কিছু কিছু ইরাকি কূটনীতিককে বহিষ্কার করার হুমকি দেয়। ইরাকি দূতাবাস কর্মকর্তারা এসব অভিযোগ অস্বীকার করেন, যদিও তারা স্বীকার করেন যে, বিক্ষোভকারীদের মধ্যে তারা ইরাকি রাষ্ট্রপতি সাদ্দামের ১,০০০ ছবি বিতরণ করেছেন।

অবশ্য ইরাকের পক্ষে বিক্ষোভের প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশে কুয়েত ও সৌদি আরবের পক্ষেও কিছু কিছু মিছিল বের হয়। এই দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষও হয়েছিল। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশি সরকারের সিদ্ধান্তের ওপর এসবের কোনো প্রভাব পড়েনি। উপসাগরীয় যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশি সৈন্যরা সৌদি আরবে অবস্থান করে এবং কুয়েত থেকে ইরাকি সৈন্য অপসারণের পর কুয়েতকে মাইনমুক্ত করার কাজে তাদেরকে নিযুক্ত করা হয়। একটি কুয়েতি পত্রিকার তথ্যমতে, শতাধিক বাংলাদেশি সৈন্য এই কাজে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় নিহত হয়েছে।
উপসাগরীয় যুদ্ধে বাংলাদেশের অবস্থানের প্রতি বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান ছিল মূলত দলীয় স্বার্থনির্ভর। প্রথমে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং তাদের সহযোগী দলগুলো সৌদি আরবে বাংলাদেশি সৈন্য প্রেরণের বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তারা এই অবস্থান থেকে সরে আসে এবং শান্তি স্থাপনের জন্য উভয় পক্ষকে আহ্বান জানানোর মধ্যে তাদের প্রতিক্রিয়া সীমাবদ্ধ রাখে। বাংলাদেশের অধিকাংশ ইসলামপন্থী দল উপসাগরীয় যুদ্ধে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের বিরোধী ছিল। এদিক থেকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা ছিল ব্যতিক্রম; কারণ তারা কুয়েতে ইরাকি আক্রমণ ও ইরাকে মার্কিন–নেতৃত্বাধীন জোটের আক্রমণ উভয়েরই নিন্দা জানিয়েছিল। কিন্তু সামগ্রিকভাবে, একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টি অফ বাংলাদেশ (সিপিবি) ছাড়া আর কোনো বাংলাদেশি রাজনৈতিক দল উপসাগরীয় যুদ্ধের ব্যাপারে তেমন কোনো আগ্রহ দেখায়নি।
উপসাগরীয় যুদ্ধে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ ছিল আদর্শিক নীতির ওপর ‘বাস্তববাদী’ রাষ্ট্রচিন্তার বিজয়। একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ নিজস্ব রাষ্ট্রীয় স্বার্থ এবং ক্ষমতাসীন সরকারের স্বার্থের ভিত্তিতে মার্কিন–নেতৃত্বাধীন জোটে অংশ নিয়েছিল। সর্বোপরি, পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে জনমতের প্রভাব যে তুলনামূলকভাবে সীমিত, সেটিও এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট।







