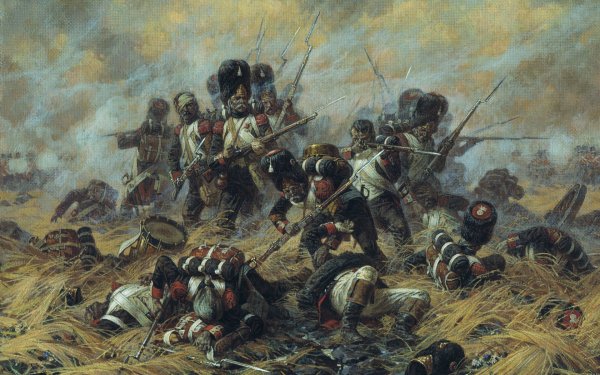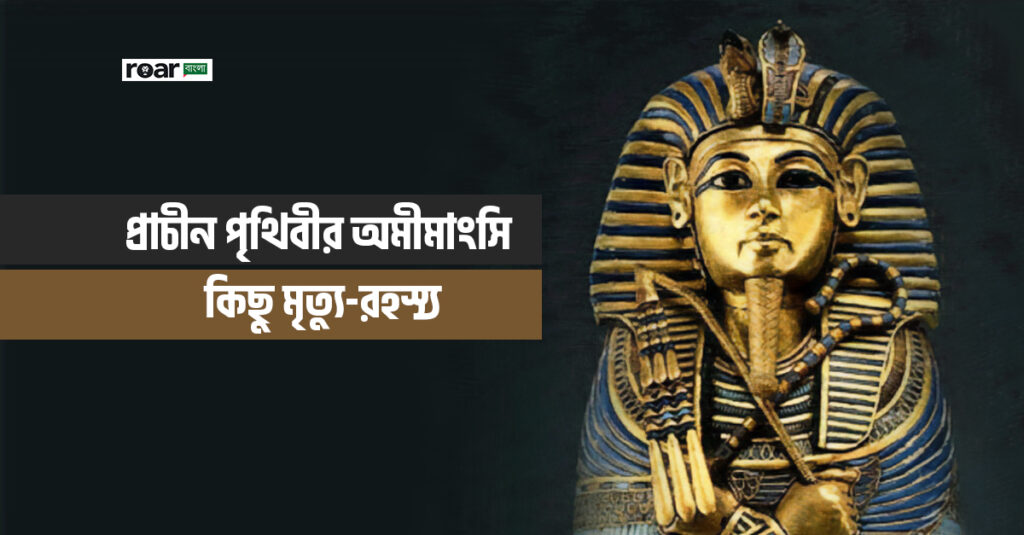হ্যালোইন শব্দটি শুনলেই অদ্ভুতুড়ে সব পোশাক, বিশাল সব মিষ্টি কুমড়া, ট্রিক অর ট্রিট ইত্যাদির কথা ঘোরে মাথায়। পশ্চিমা সংস্কৃতির অংশ হলেও, ইদানিংকালে বাংলাদেশেও জনপ্রিয় হচ্ছে হ্যালোইন উৎসব, তবে বেশ সীমিত পরিসরে আর মূলত অভিজাত এলাকায়। আর এর পেছনে কারণ হিসেবে দাঁড়া করানো যায় বিদেশি মুভি আর টিভি সিরিজের প্রভাবকে, যেগুলো নিয়মিত দেখবার কারণে হ্যালোইনের ধারণাটিকে এখন বেশ পরিচিতই মনে হয়। হ্যালোইন উপলক্ষ্যে এই অদ্ভুত সব কার্যকলাপের উৎস কী? কবে থেকে শুরু হয় এগুলো? এবং কেন? হ্যালোইন উৎসবের সূচনার ইতিহাস নিয়েই আজকের এ লেখা।

‘হ্যালোইন’ (Halloween) শব্দের পূর্ণ রূপ ‘হ্যালো’জ ইভনিং’ (Hallows’ Evening) বা ‘হ্যালোড ইভনিং’, অর্থ ‘পবিত্র সন্ধ্যা’। শব্দটি এসেছে স্কটিশ ‘অল হ্যালো’জ ইভ’ (All Hallows’ Eve) থেকে। ‘হ্যালো’ শব্দটি হ্যালোইন ছাড়াও জে কে রোলিং-এর লেখা হ্যারি পটার মূল সিরিজের শেষ বই ‘হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য ডেথলি হ্যালোজ’ দ্বারা বিখ্যাত হয়। ‘হ্যালো’ (Hallow) বলতে বোঝায় ‘পবিত্র কিছু’ কিংবা ‘সাধুজন’ (Saint)। এ কারণে এ দিনটিকে ‘অল সেইন্টস ইভ’-ও (All Saints’ Eve) বলা হয়। হ্যালোইন শব্দটির অতীত ঘাঁটতে গেলে আমরা দেখতে পাই, প্রথম ১৭৪৫ সালে এটি ব্যবহার করা হয়, ওদিকে ১৫৫৬ সালে দেখা যায় ‘অল হ্যালো’জ ইভ’ কথার প্রচলন। হ্যালোইনের বিশ্বাসগুলো খ্রিস্টধর্মজাত। এর সাথে পৌত্তলিক (pagan) প্রথার কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু একই কথা অবশ্য পরবর্তীতে হ্যালোইনে যুক্ত হওয়া নানা প্রথার ক্ষেত্রে বলা যায় না, সে বিষয়টি আসবে একটু পরে।

৩১ অক্টোবর পালিত হয় হ্যালোইন, যে রাতে বিগত সাধুদের আত্মার স্মরণে গির্জায় গির্জায় জ্বালানো হয় মোমবাতি। তার পরদিন পহেলা নভেম্বর পশ্চিমা খ্রিস্টানদের ভোজ (feast) ‘অল হ্যালোজ ডে’ (All Hallows’ Day) বা ‘হ্যালোমাস’ (Hallowmas), যেদিন ইতিহাসের সকল জানা-অজানা সাধুদের স্মরণ করা হয়। আর সবশেষে ২ নভেম্বর ‘অল সোল’জ ডে’ (All Souls’ Day), এ দিন স্মরণ করা হয় পরলোকগত খ্রিস্টানদের আত্মাকে। এ তিন দিন মিলিয়ে পালিত হয় পশ্চিমা খ্রিস্টানদের ‘অলহ্যালোটাইড’ (Allhallowtide) বা শুধু ‘হ্যালোটাইড’ (Hallowtide)।
এবার আসা যাক হ্যালোইনের প্রথায় পৌত্তলিক প্রভাব নিয়ে, যেটি নিয়ে হয়েছে বিস্তর গবেষণা, অনেকের মনেই আছে এ নিয়ে প্রশ্ন। সেটি বুঝবার আগে আমাদের জানতে হবে কেল্টিকদের নিয়ে। কেল্টিক (Celtic) ভাষায় যারা কথা বলে থাকেন তাদের বসবাস মূলত পশ্চিম ইউরোপের ছয়টি অঞ্চলে- ওয়েলস, আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, কর্নওয়াল, ব্রিটানি এবং আইল অফ ম্যান। সম্মিলিতভাবে এদের বলা হয় কেল্টিক (বা সেল্টিক) অঞ্চল। কেল্টিক ভাষার একটি শাখা হলো গেলিক ভাষা- স্কটিশ, ম্যানক্স ও আইরিশদের ভাষার একটি মিলিত রূপ। এ ভাষায় কথা বলা মানুষের সংখ্যা বর্তমানে ১৯ লক্ষ।
কেল্টিক জাতির নানা পৌত্তলিক বা প্যাগান উৎসবের প্রভাব পড়েছিল সদ্য খ্রিস্টধর্মের সাথে পরিচিত হওয়ার পর। তাই প্যাগান কিছু প্রথার ছায়া দেখা যায় হ্যালোইনে। ইতিহাসবিদ নিকোলাস রজার্সের এ বিষয়ে গবেষণা করে মন্তব্য করেন যে কেবল কেল্টিকই নয়, আরও কিছু প্যাগান ধর্ম অনুসারীদের প্রথাতেও আছে হ্যালোইনের উৎসব প্রথার শিকড়। তার মাঝে প্রধান তিনটি হলো-
১) পোমোনা (Pomona) ভোজ
প্যাগান রোমানদের প্রাচুর্যের দেবী পোমোনা। তিনি ছিলেন ফলের গাছ, বাগান ইত্যাদিরও দেবী। অনেক রোমান দেব-দেবীর গ্রিক অস্তিত্ব থাকলেও পোমোনা কেবলই রোমান দেবী ছিলেন। তার স্মরণে যে ভোজের অনুষ্ঠান হতো, তাতে প্রচলিত কিছু প্রথার সাথে মিল পাওয়া যায় হ্যালোইনের।

২) সাউইন (Samhain)
এটি একটি গেলিক ছুটির দিন। গেলিক জাতির ফসল ঘরে তোলা শেষে যে উৎসব হয় তার নাম সাউইন, প্রাচীন আইরিশ ভাষায় যার অর্থ ‘গ্রীষ্মের ইতি’। সূর্যাস্ত হবার সাথে কেল্টিকদের নতুন দিন গণনা শুরু হয়। ৩১ অক্টোবর সূর্য ডুবে গেলে তাদের সাউইন শুরু, আর একইসাথে সূচনা হয় শীতের। প্রাচীনকাল থেকেই কেল্টিক বা গেলিক প্যাগানদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল এ দিনটি। এ দিন তারা বনফায়ার জ্বালাতো, যা বর্তমানে হ্যালোইন উৎসবেও করা হয়। নবম শতকে পশ্চিমা চার্চ অল সেইন্টস ডে এর তারিখ মে মাস থেকে সরিয়ে ১ নভেম্বরে নিয়ে আসে পোপ চতুর্থ গ্রেগোরির নির্দেশে। ধীরে ধীরে সাউইন আর এই অল সেইন্টস ডে মিলিত হয়ে তৈরি হয় আধুনিককালের হ্যালোইন। ঐতিহাসিকগণ গেলিক হ্যালোইনকে বোঝাতে সাউইন শব্দটা ব্যবহার করতেন উনিশ শতক পর্যন্ত।

৩) প্যারেন্ট্যালিয়া (Parentalia)
প্রাচীন রোমে ৯ দিন ধরে উদযাপিত হতো প্যারেন্ট্যালিয়া উৎসব। ১৩ ফেব্রুয়ারি শুরু হওয়া এ উৎসবে সম্মান জানানো হতো পূর্বপুরুষদের।
তবে এ তিনটির মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সাউইন (Samhain)। বছরকে দুই ভাগ করে তারা এক ভাগ বা ঋতুকে বলত উজ্জ্বল ঋতু, যা আসলে গ্রীষ্ম। আর পরের ভাগ হলো শীত, যা আঁধারের ঋতু। এই আলো-আঁধারির সংযোগ মুহূর্ত ৩১ অক্টোবর বা সাউইন, বা হ্যালোইন। এ সময়, গেলিক বিশ্বাস অনুযায়ী, বাস্তব জগৎ আর আত্মার জগতের মাঝের পর্দা দুর্বল হয়ে যায়। ফলে পূর্বপুরুষদের আত্মা সহজেই ভ্রমণ করে যেতে পারেন জীবিতদের। বাড়ির বাহিরে খাবার, পানীয়, শস্যের অংশ ইত্যাদি রেখে দেয়া হতো। রাতের খাবারের সময় টেবিলে পূর্বপুরুষের আত্মার জন্য বসার চেয়ারও পেতে রাখা হতো। উনিশ শতকের আয়ারল্যান্ডেও এ প্রথা প্রবলভাবে প্রচলিত ছিল।

আয়ারল্যান্ড আর ব্রিটেন জুড়ে এ উৎসবের সময় নানা খেলাধুলো করা হতো, যেমন আপেল-ববিং, বাদাম পোড়ানো, আয়নাতে দেখে সুদূর কোথাও কী হচ্ছে বলা (Scrying), পানিতে গলিত সীসা বা ডিমের সাদা অংশ ছেড়ে দেয়া, স্বপ্নের অর্থ বলা, ভবিষ্যৎ বলা ইত্যাদি। তাছাড়া বনফায়ার জ্বালানো তো ছিলই।ধারণা করা হতো এ বনফায়ারের ধোঁয়া যতদূর যাবে ততদূর কোনো প্রেতাত্মার ক্ষমতা থাকবে না। সূর্য ওঠা পর্যন্ত জ্বালিয়ে রাখা হতো আগুন। পরে অবশ্য চার্চ স্কটল্যান্ডে এসব বনফায়ার আর ভবিষ্যৎ বলা নিষিদ্ধ করে।

বিংশ শতাব্দীতে এসে ধীরে ধীরে নানা রকমের অদ্ভুত পোশাক বা কস্টিউম পরে হ্যালোইনের রাতে ঘুরে বেড়ানোর রীতি প্রচলিত হয় ইংল্যান্ডে। একই সময়ে প্র্যাংক বা কাউকে বোকা বানানোর খেলাও শুরু হয় ইংল্যান্ডে, যেটি কি না আরো দু’শ বছর আগেই স্কটল্যান্ডে হতো। তারা বিভিন্ন রকমের জিনিসে খোদাই করে মুখমণ্ডল আঁকতো, আর ভেতরটা ফাঁপা করে আলো জ্বালানো হতো। এ লণ্ঠনগুলো আত্মার বহিঃপ্রকাশ আর প্রেতাত্মা তাড়াবার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতো আইরিশরা, আর স্কটিশরা উনিশ শতক থেকেই। মিষ্টি কুমড়াকে (কিংবা অন্য বড়সড় সবজি) ফাঁপা করে খোদাই করার প্রচলন হয় সমারসেটে বিংশ শতকে, যা ধীরে ধীরে পুরো ইংল্যান্ডেই ছড়িয়ে যায়। একে বলা হয় জ্যাক-ও-ল্যান্টার্ন (jack-o’-lantern) কিংবা উইল-ও-দ্য-উইস্প (will-o’-the-wisp)।

তবে এই সব প্রথাই অনেক পরে চালু হয় এবং এর সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক ছিল না, চার্চও এর প্রচলন করেনি। গেলিকদের থেকে প্যাগান প্রথাগুলো অন্য সমাজে প্রবেশ করার সময় হারিয়ে ফেলে তাদের প্যাগান শিকড়, জন্ম নেয় নতুন অর্থের।
এমনিতে ৬০৯ সালে থেকেই আমরা অল হ্যালো’জ ডে-র অস্তিত্ব পাই, এ নামে না হলেও। পোপ চতুর্থ বনিফেইস রোমের প্যাগান প্যান্থিয়নকে সেইন্ট মেরি ও অন্যান্য সাধুদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন, সেটি ছিল মে মাসের ১৩ তারিখ। ১৩ মে একই সাথে ছিল রোমানদের মৃতদের উৎসব লেমুরিয়ার তারিখ, এ দিন রোমানরা বিগত সাধুদের স্মরণ করতো। পরে গেলিকদের সাউইন উৎসবের প্রভাব পরিলক্ষিত করে মে মাস থেকে এ দিনটি ৩১ অক্টোবর নিয়ে আসা হয় ৮৩৫ সালে। কেউ কেউ অবশ্য বলেন কেল্টিক বা গেলিকদের জন্য নয়, বরং জার্মানদের মৃত্যু উৎসবের জন্য এমনটা করা হয়েছিল।
দ্বাদশ শতকে এ সময় চার্চের ঘণ্টা বাজানো হতো বিগত আত্মাদের জন্য। তখন এটা উৎসবের কিছু ছিল না, এ সময় কাঁদতে থাকা অনুরাগীরা রাস্তায় কালো কাপড় পরে মিছিল করত। বানানো হতো ‘আত্মা কেক’, এ কেক খেয়ে মৃতদের আত্মাদের স্মরণ করা হতো। ফ্রান্সে এ রাতে খ্রিস্টান পরিবারেগুলো যেত গোরস্থানে, প্রিয়জনের কবরের পাশে প্রার্থনা করতেন। কবরের ওপর তারা মৃতের জন্য দুধেল খাবার নিয়ে যেত।

অষ্টাদশ কিংবা উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকেও আমেরিকাতে হ্যালোইন পালিত হতো না। ১৯ শতকে যখন ব্যাপক হারে স্কটিশ ও আইরিশরা আমেরিকায় বসত গড়তে লাগলো, তখনই শুরু হয় হ্যালোইন উৎসব, তবে অভিবাসীদের মাঝেই সীমিত ছিল সেটি। বিশ শতকের প্রথমদিকে এসে পুরো মার্কিন সমাজেই শুরু হলো হ্যালোইন পালন।
কেন অদ্ভুত পোশাক পরা হতো এর ব্যাখ্যা আরও অদ্ভুত। ঐ পোশাকগুলো পরিধান করে নিজের স্বাভাবিক চেনা চেহারা থেকে ভিন্ন কিছু হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করত মানুষ, কেউ বা মুখোশ পরতো। কারণ, এ রাতে মৃত আত্মাদের শেষ সুযোগ দেয়া হতো জীবিত থাকাকালে আক্রোশ থাকা কারও উপর প্রতিশোধ নেবার। যেন কোনো আত্মা তাকে চিনতে না পারে প্রতিশোধের আগুন নেভাতে, সেজন্য লোকে মুখোশ বা ভিন্ন চেহারার পোশাক নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে যেত। এ প্রথা আজও আছে বটে, কিন্তু বিশ্বাসটুকু নেই, বরং মজার ছলেই চলে কসপ্লে।

শিশুরা হ্যালোইনের রাতে ‘ট্রিক অর ট্রিট?’ (Trick or treat?) খেলে থাকে। যদি ‘ট্রিট’ না দেয় কোনো বাসার মালিক, তবে তার উপর কোনো ‘ট্রিক’ খাটানো হবে, যা শুভ কিছু হবে না। ইউরোপের মধ্যযুগীয় (দ্বাদশ শতক থেকে) একটি প্রথা ছিল এই ট্রিক অর ট্রিট, অবশ্য তখন এর নাম ছিল মামিং (mumming)।

হ্যালোইন উপলক্ষ্যে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের ব্যবসা হয় প্রতি বছর পশ্চিমা বিশ্বে। ধীরে ধীরে বাংলাদেশেও জায়গা করে নিচ্ছে হ্যালোইন উৎসব। সেটা কতটা বিস্তৃত হয় সময়ের সাথে সাথে, সেটাই দেখবার বিষয়।
হ্যালোইন সম্পর্কে আর জানতে পড়বেন যে বইগুলো।