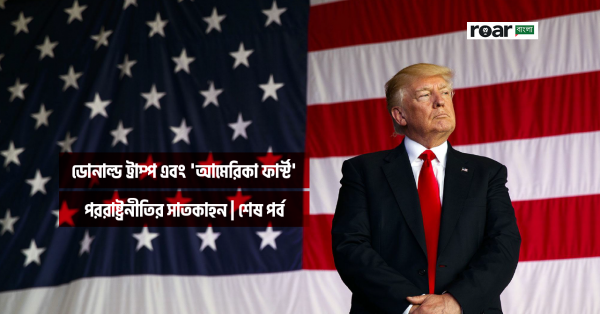মানুষ রাজনীতিতে জড়ায় দুটি কারণে: রাজনৈতিক আদর্শ আর অর্থনৈতিক স্বার্থ। আদর্শিক কারণে রাজনীতি করা রাজনৈতিক দলগুলোও রাজনৈতিক সংঘাতে জড়ায়, অভ্যন্তরে আর আন্তঃদলীয় সংঘাত হয় অর্থনৈতিক স্বার্থকে কেন্দ্র করেও। বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর মধ্যে তৈরি হওয়া সংঘাত সংলাপের মাধ্যমে সমাধান হতে পারে, একপক্ষ আরেক পক্ষের বিরুদ্ধে হুমকি প্রদর্শনের মাধ্যমে ভয়ের সংস্কৃতি তৈরি করে স্বার্থের সংঘাতের সমাধান আনতে পারে, স্বার্থ আদায় করতে পারে শারীরিক সংঘাত তৈরির মাধ্যমেও।
আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের যুগে বুলেটের চেয়ে ব্যালটকে বেশি শক্তিশালী মনে হয়, স্বার্থের কারণে তৈরি হওয়া সংঘাত সমাধানে জোর দেওয়া হয় সংলাপের উপর। সম্পদের কর্তৃত্বমূলক প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য পাবলিক অফিসগুলোর নির্বাহী ক্ষমতার অংশ হওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়, সম্পদের উপর কর্তৃত্ব আইনসভা এনে দিতে পারে সুবিধাজনক আইন তৈরির মাধ্যমেও। আইনসভা কিংবা স্থানীয় পাবলিক অফিস নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার উপায় হচ্ছে নির্বাচন।
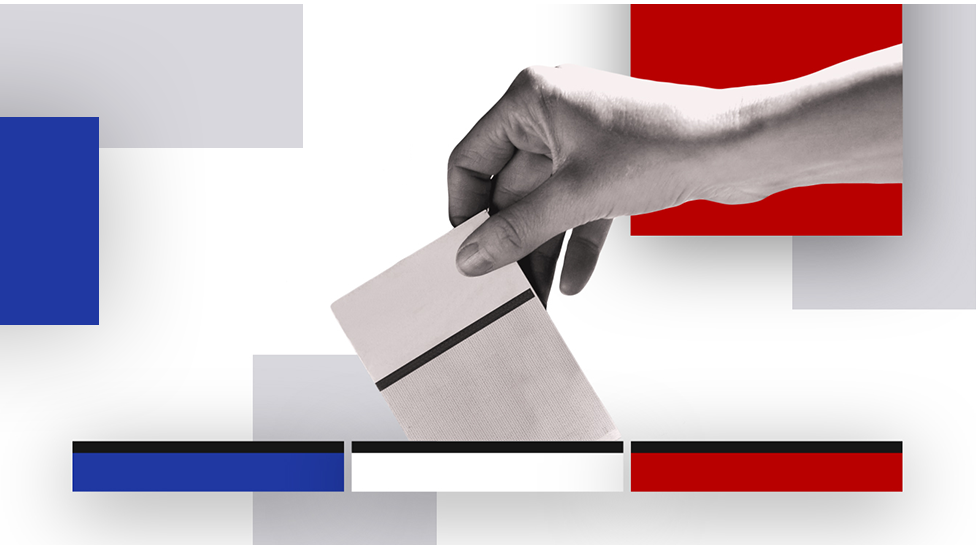
গণতান্ত্রিক কাঠামোতে নির্বাচনকে মৌলিক একটি মূল্যবোধ হিসেবে গণ্য করা হয়। নির্বাচনের মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে নির্ধারিত হয় কেন্দ্রীয় সরকার, স্থানীয় সরকার, নির্ধারিত হয় রাষ্ট্রের লক্ষ্য। নির্বাচনের মাধ্যমে ভোটাররা পরোক্ষভাবে প্রার্থীদের জবাবদিহিতার সংস্কৃতিতে নিয়ে আসতে পারেন, সরকারের নীতির ব্যাপারে নিজেদের মতামত জানাতে পারেন, জানাতে পারেন প্রার্থীর ক্ষেত্রে পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারটি। রাজনৈতিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নির্বাচনের ভূমিকা আরো বহুমুখী। নির্বাচনের মাধ্যমে নিশ্চিত হয় নাগরিকদের বাকস্বাধীনতার পরিসর, রাজনৈতিক অধিকারের নিশ্চয়তা আর নাগরিক অধিকারের সামগ্রিকতা।
ভোটে কারচুপি
একটি দেশে গণতন্ত্র আছে নাকি নেই, সেটি কখনোই বাইনারি স্কেলে মাপা সম্ভব না। যেমন: কানাডায় গণতন্ত্র আছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গণতন্ত্র আছে, এবং ভারতে গণতন্ত্র আছে। এই তিনটি বাক্য একই অর্থ তুলে ধরলেও একই রাজনৈতিক বাস্তবতা তুলে ধরে না। আবার, উগান্ডাতে গণতন্ত্র নেই, উত্তর কোরিয়ায় গণতন্ত্র নেই, এবং সৌদি আরবে গণতন্ত্র নেই। এই তিনটি বাক্যও একই রাজনৈতিক বাস্তবতা তুলে ধরে না। কারণ, তিনটি দেশেরই রাজনৈতিক কাঠামো আলাদা, রয়েছে ভিন্ন রাজনৈতিক সংস্কৃতি, এবং ভিন্নতর রাজনৈতিক অধিকারের ধারণা।

এ ধরনের রাজনৈতিক বাস্তবতাকে সামনে রেখেই একটি দেশের গণতন্ত্রকে বাইনারি স্কেলে না মেপে ০ থেকে ১ এর মধ্যে স্কোরিং করা যায়, স্কোর দেওয়া যায় ০ থেকে ১০০ এর মধ্যেও। এই ধরনের স্কেলে মাঝামাঝি থাকা দেশগুলো, যেগুলোতে স্নায়ুযুদ্ধের সমাপ্তির পরে গণতন্ত্রায়ন হয়েছে, দোআশলা শাসনব্যবস্থা রয়েছে, সেসব দেশে পাবলিক অফিস এবং আইনসভার নিয়ন্ত্রণ নিতে ভোটে কারচুপি করা হয় বিভিন্নভাবে। ব্রুকিংস ইন্সটিটিউশনের গবেষণানুযায়ী, নির্বাচনে কারচুপি হতে পারে তিনভাবে। নির্বাচনে ক্রিয়াশীল গোষ্ঠীগুলো ভোটচুরির মাধ্যমে নির্বাচনের ফলাফল বদলে দিতে পারে, ভোট গ্রহণের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার মাধ্যমে নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করে, প্লেয়িং ফিল্ডের অনুঘটকগুলোকে বদলে দিয়ে নির্বাচনে কারচুপি করতে পারে।
ভোট চুরি
গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া হিসেবে নির্বাচনের ইতিহাস যতদিনের, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী গোষ্ঠীগুলোর মাধ্যমে ভোট চুরির ইতিহাসও ততদিনের। ভোট চুরির ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি হচ্ছে মৃত ব্যক্তিদের হয়ে ভোট দেওয়া, নির্বাচনের সময় অনুপস্থিত থাকা ব্যক্তিদের হয়ে ভোট দেওয়া। এই প্রক্রিয়াতে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তিকে নিয়োজিত করে, যারা মৃত ব্যক্তি কিংবা অনুপস্থিত ব্যক্তিদের হয়ে ভোট দিয়ে দেয়।
এর বাইরেও, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী গোষ্ঠীগুলো ভোটারদের হুমকি দেয়ার ঘটনা ঘটায়, অর্থের মাধ্যমে ভোট কিনে নেয়, মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে দেয়, ভোটারকে কেন্দ্রে নিয়ে নির্দিষ্ট প্রার্থীকে ভোট দিতে বাধ্য করে। অনেক সময় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে অস্ত্রের ব্যবহার করে, ভোটকেন্দ্রের দখল নিয়ে নির্বাচনী কর্মকর্তাকে অবরুদ্ধ করে, প্রার্থীর পক্ষের লোকেরা ব্যালট বক্স পূর্ণ করে দিয়ে আসে। অনেক সময় ভোটের ভুল রেকর্ডিংয়ের ঘটনা ঘটে, আবার কেন্দ্র দখল করে ব্যালট বাক্স ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে, ঘটে ব্যালট নষ্ট করে দেওয়ার ঘটনাও।

জেমস সি. স্কটের বর্ণনায় মেশিন পলিটিক্সেও দেখা যায় ভোট চুরির বিভিন্ন প্রক্রিয়া। যেমন, মেশিন পলিটিক্সে গডফাদারের নিয়ন্ত্রণে থাকা এলাকার সবাইকে একই প্রার্থীকে ভোট দিতে বাধ্য করা হয়, বিনিময়ে ভোটাররা রাষ্ট্রের বদলে গডফাদারের কাছ থেকে সুবিধা পান। গডফাদারদের নিয়ন্ত্রণ নিরঙ্কুশ না হলে তার অনুগতদের কেবল ভোটকেন্দ্রে আসতে দেওয়া হয়, বাকিদের আসতে দেওয়া হয় না ভোটকেন্দ্রে। বিভিন্ন প্রক্রিয়া ব্যবহার করে তাদের দূরে রাখা হয় ভোটকেন্দ্র থেকে। গত শতাব্দীর শুরুতে শিকাগোতে এই ধরনের মেশিন পলিটিক্সের উপস্থিতি দেখা যেত। বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দেখা যাচ্ছে এটি।
প্রাতিষ্ঠানিক ভোট কারচুপি
বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক বিকাশ ঘটেছে। কেন্দ্র দখল করে ভোট দেওয়ার সুযোগ কমেছে, সুযোগ কমেছে মৃত ব্যক্তিদের হয়ে কিংবা অনুপস্থিত ব্যক্তিদের হয়ে ভোট দেওয়ার সুযোগ। সামষ্টিকভাবে নির্বাচনের দিন ভোট কারচুপির সুযোগ কমেছে, বেড়েছে নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারী সংস্থার সংখ্যাও। নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতা সামনে রেখে ক্ষমতায় যেতে আগ্রহী দলগুলো প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়াগুলোকে প্রভাবিত করে নির্বাচনে জিতে যাওয়ার চেষ্টা করছে। আগে যেখানে ভোটের দিন নির্বাচনে কারচুপি হতো, বর্তমানে নির্বাচনে কারচুপির প্রক্রিয়া শুরু হয় কয়েক বছর আগে। এই প্রক্রিয়া চলমান থাকে নির্বাচনের পরেও। সাধারণত, ক্ষমতাসীন দলগুলো এই প্রক্রিয়া ব্যবহারের সুযোগ পায়।
লেভিতস্কি ও জিবলেটের মতে, এই প্রক্রিয়া ঘটে তিনটি ধাপে। শুরুতেই সরকার রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়। সেখানে বসায় নিজেদের অনুগত ব্যক্তিদের। প্রশাসন, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগে একটি অনুগত শ্রেণী তৈরি করে ক্ষমতাসীন দল। পরবর্তীতে সেই কর্মকর্তারা রাজনৈতিক আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ দলীয় স্বার্থরক্ষায় সবকিছু করে। এই পর্যায়েই কোট প্যাকিং চলে, ভেঙে দেওয়া হয় বিচারব্যবস্থার মেরুদণ্ড।

দ্বিতীয় ধাপে সরকার বিরোধী পক্ষগুলোকে আক্রমণ করে, বিরোধী দলের নেতাদের বিভিন্নভাবে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে বের করে দেওয়া শুরু হয়, দুর্বল করে দেয়া হয় প্রতিপক্ষ দলগুলোকে, দায়ের করা হয় বানোয়াট মামলা। ক্ষমতাসীন দলের এই প্রক্রিয়ায় সহযোগী হয় মিডিয়া আর বুদ্ধিজীবীরা, বিরোধী দলকে নির্মূলের পক্ষে এরা যুক্তি তৈরি করে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক নির্যাতনের বৈধতা তুলে ধরে।
তৃতীয় ধাপে শাসনতান্ত্রিক আইন, সংবিধান আর নির্বাচনী ব্যবস্থার মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে স্থাপন করা হয় ক্ষমতাসীন দলের নিরঙ্কুশ আধিপত্য। এই তিনটি ধাপ সম্পন্ন করার পরেই ক্ষমতাসীন দল নির্বাচন আয়োজন করে, যেখানে পুরো রাষ্ট্রযন্ত্র সরকারের পক্ষে কাজ করে, এবং ক্ষমতাসীন দলের পছন্দের প্রার্থীকে জিতিয়ে নিয়ে আসে।
প্লেয়িং ফিল্ড প্রভাবিত করা
নির্বাচনী কাঠামোতে আইন তৈরির মাধ্যমে, আইন পরিবর্তনের মাধ্যমে বা অনুঘটকগুলোকে প্রভাবিত করে কোনো নির্দিষ্ট প্রার্থীকে সুবিধা দেওয়া যায়, নির্বাচনী প্লেয়িং ফিল্ডকে অন্য প্রার্থীদের জন্য প্রতিকূল করে তোলা হয়। এই প্রক্রিয়াগুলো অনেক সময়ই সরাসরি নির্বাচনের সাথে সম্পর্কিত থাকে না।
গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে থাকা দেশগুলোতে সাধারণত কেন্দ্রীয় নির্বাচনের মতো স্থানীয় নির্বাচনেও দলীয় প্রার্থী নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। পরিণত গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে ডেলিগেটদের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ে দলীয় প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়া হলেও, তৃতীয় বিশ্বে সাধারণত কেন্দ্রীয় কাঠামো থেকে ইচ্ছামতো প্রার্থীকেই দলীয় মনোনয়ন দেওয়া হয়।
এই প্রক্রিয়ায় অধিকাংশ সময়ই দলীয় ডেলিগেটদের জনমতের প্রতিফলন ঘটে না, মনোনয়ন নিয়ে চলে বিশাল বাণিজ্য। ফলে, জনপ্রিয় প্রার্থী কতিপয়তন্ত্রের বলি হয়ে অনেক সময়ই নির্বাচন করতে পারেন না, নির্বাচনে দাঁড়ালেও দলীয় কাঠামোর সহযোগিতা পান না।
নির্বাচনী সংঘাত
নির্বাচনের মাধ্যমে নির্ধারিত হয় পরবর্তী কয়েক বছর আইনসভার নিয়ন্ত্রণ কাদের কাছে থাকবে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ কারা ভোগ করবে, রাষ্ট্রীয় সম্পদের উপর কর্তৃত্বমূলক নিয়ন্ত্রণ কার কাছে থাকবে। হাফনার ব্রুটন, হাইড এবং জেবলোনস্কির গবেষণায় প্রমাণ করা হয়েছে- নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নির্বাচনের আগে এবং পরে সংঘাতের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি, নির্বাচনে যদি ক্ষমতাসীল দল বা প্রার্থী অংশগ্রহণ করে, তাহলে সংঘাতের সংখ্যা এবং মাত্রা তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পায়।

আবার, কক্স এবং লিটন গেইম থিওরি ব্যবহার করে এক গবেষণায় প্রমাণ করেছেন, নির্বাচনের সময় স্বল্প মেয়াদের সংঘর্ষ বাড়লেও, দীর্ঘ মেয়াদে সুষ্ঠু নির্বাচনে সংঘাতের পরিমাণ কমে আসে। আবার, নির্বাচনে কারচুপি হলে সেটি দীর্ঘমেয়াদে সংঘাতের একটি চক্র তৈরি করে।
নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্র দখল করে ভোট চুরি বা জালিয়াতি করলে প্রভাব বিস্তারকারী গোষ্ঠীকে অবশ্যই সংঘাত উৎপাদন করতে হয়। এই সংঘাতের যারা ভিক্টিম হন, তারা পরবর্তীতে একই প্রক্রিয়ায় সংঘাত উৎপাদন করে প্রতিশোধ নিতে চান। এই প্রতিশোধের কাঠামোর সাথে অনেক সময় রাজনৈতিক দলও যুক্ত হয়ে যায়। নির্বাচনের আগে-পরে তৈরি হওয়া সংঘাতগুলো একই রকম একটি চক্র তৈরি করে। চক্র তৈরি হয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগুলো প্রভাবিত করে নির্বাচন কারচুপির ক্ষেত্রেও।
নির্বাচনে কারচুপির পর সংঘাতের চক্র তৈরির প্রক্রিয়া তিনটি ধাপে বিভক্ত। প্রথম ধাপে নির্বাচন, নির্বাচনী কাঠামো, নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়, তৈরি হয় উত্তেজনা। এই উত্তেজনার বিস্ফোরণ ঘটে, যদি নির্বাচনে কারচুপি ঘটে। পরবর্তী পর্যায়ে দু’পক্ষ সংঘাতে জড়ায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব সংঘাত হয় সশস্ত্র, ঘটে হতাহতের ঘটনা। এই ধরনের সংঘাত সাধারণত কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে।
তৃতীয় পর্যায়ে সাধারণত দুই পক্ষই কিছুটা নিশ্চুপ হয়ে যায়। যে গ্রুপ আগে নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করতে পারে, তারা পুনরায় উত্তেজনা তৈরি করে, সংঘাতে জড়িয়ে প্রতিপক্ষকে নির্মূল করে দিয়ে চায়। কারচুপির নির্বাচনে পরাজিত কিন্তু জনপ্রিয়, এমন পক্ষগুলো অধিক আবেগ এবং আগ্রহ নিয়ে সংঘাতের চক্র তৈরি করে।

কারচুপির নির্বাচনের ফলে বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিগুলো অনুভব করতে পারে, নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে তাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতের সুযোগ নেই, সুযোগ নেই মত প্রকাশের। ফলে, বিরোধী শক্তিগুলো সশস্ত্র পথে মনোযোগ আকর্ষণের দিকে ঝুঁকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৮৭ সালে কাশ্মীরে কারচুপির নির্বাচনের পরই কাশ্মীরে মিলিট্যান্সির উত্থান ঘটে তরুণদের হাত ধরে। কারণ, তরুণরা মনে করছিল, নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে তাদের মত প্রকাশের সুযোগ নেই। কাশ্মীরের মিলিট্যান্সি তিন যুগ পেরিয়ে গেলেও পুরোপুরি নির্মূল করা যায়নি।
রাজনৈতিক এলিটরা নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করতে অনেক সময় সংঘাতকে ব্যবহার করে, ব্যবহার করে ভোটের উপস্থিতি আর ভোটারদের পছন্দকে প্রভাবিত করতে। নির্বাচনে একবার সংঘাতের ব্যবহার শুরু হলে সেটি সংস্কৃতিতে পরিণত হয়, তৈরি হয় সংঘাতের চক্র।
নির্বাচনের কী দরকার?
নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সংঘাত বাড়ে, বাড়ে ক্ষমতায় টিকে থাকা আর ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে হতাহতের সংখ্যাও। রাজনৈতিক এলিটরা সংঘাতকে রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে ব্যবহার করেন, হতাহতের সংখ্যাকে ব্যবহার করেন রাজনৈতিক ফায়দা হিসেবে। কারচুপির নির্বাচন আবার সংঘাতের চক্র তৈরি করে মিলিট্যান্সির উত্থান ঘটাতে পারে। সামগ্রিকভাবে, একটি দেশকে নিয়ে যেতে পারে হবসের প্রকৃতির রাজ্যের মতো অবস্থায়। এত সংঘাতের মধ্যে। ভোটাররা হয়তো ভাবেন, রাজনীতিতে নির্বাচন না থাকলে রাজনীতি নিশ্চয় অনেক শান্তিপূর্ণ হতো। আবার, নির্বাচনকেন্দ্রিক সংঘাত এবং সংঘাতের চক্র তৈরির কাঠামো দেখে পাঠকের মনেও নিশ্চয়ই প্রশ্ন আসছে, “নির্বাচন কি একটি অভিশাপ? নির্বাচনের কী দরকার?”