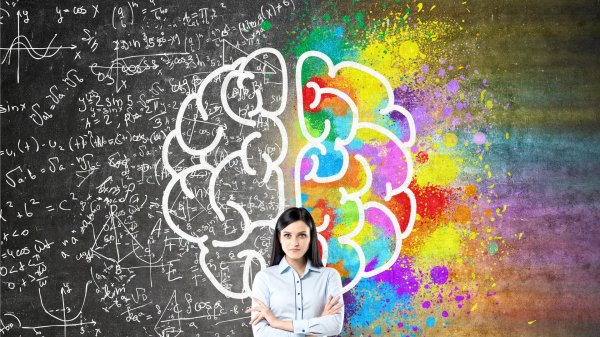একধরনের বাঁধাকপি আছে, নাম Skunk Cabbage, বৈজ্ঞানিক নাম Symplocarpus foetidus। উত্তর আমেরিকা এবং এশিয়ার কিছু কিছু জায়গায় এদের জন্ম। উত্তর আমেরিকায় শীতকালে এই সবজি দেখতে পাওয়া যায়। নিচু ভূমি এবং আর্দ্র পরিবেশে এরা জন্মে থাকে। কিন্তু একটি আশ্চর্য বিষয় এখানে দেখতে পাওয়া যায় যে, যখন শীতকালে বরফ পড়ে, তখন এই বাঁধাকপির কাছাকাছি যে বরফ পড়ে থাকে সেগুলো গলে যায়। এমনকি যখন অনেক বেশি পরিমাণে বরফ পরে তখনও এই বাঁধাকপির আশেপাশের বরফে গর্ত তৈরি হয়। বরফের এরকম অবস্থা শুধুমাত্র এই ধরনের বাঁধাকপি জন্মানোর স্থানেই দেখা যায়, অন্য কোথাও নয়। এই আশ্চর্য প্রক্রিয়াতে বিজ্ঞানীরাও অবাক হয়েছে। শীতকালে কেন এরকম হয়, শুধু এই ধরণের বাঁধাকপির ক্ষেত্রেই কেন এমন ঘটে, আরও কোনো এই ধরনের উদ্ভিদ আছে কিনা তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা গবেষণা শুরু করেন এবং এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেন।
অনেকদিন পর্যন্ত খোঁজ করে দেখা গিয়েছে যে, প্রকৃতিতে এরকম তিন ধরনের উদ্ভিদ আছে যাদের ক্ষেত্রে এরকম তাপমাত্রা বৃদ্ধির ব্যাপারটি লক্ষ্য করা গিয়েছে। Skunk Cabbage ছাড়াও আরও দুটি উদ্ভিদ আছে। একটির বৈজ্ঞানিক নাম Philodendron selloum এবং অপরটির নাম Nelumbo nucifera যা একটি লোটাস ফুলের গোত্রের (Sacred lotus)।

Philodendron selloum নামক উদ্ভিদ; Source: Scientific American
বাঁধাকপির ক্ষেত্রে দেখা যায়, আশেপাশের পরিবেশের তাপমাত্রা যদি -১৫ থেকে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে তবুও এই উদ্ভিদের নিজস্ব তাপমাত্রা ১৫ থেকে ২২ ডিগ্রি পর্যন্ত উঠে যায়। লোটাস নামের উদ্ভিদের ক্ষেত্রে দেখা যায় আশেপাশের তাপমাত্রা ১০-২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকলেও এই উদ্ভিদের স্ব-তাপমাত্রা ৩০-৩৭ ডিগ্রি পর্যন্ত বেড়ে যায়। এবং সর্বশেষ Philodendron selloum নামক উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও দেখা যায় পরিবেশের তাপমাত্রা ৪-১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকলেও এর নিজস্ব তাপমাত্রা ৩৮-৪৬ ডিগ্রি পর্যন্ত উঠে যায়।
পরীক্ষা করে এই উদ্ভিদগুলোর আরও একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গিয়েছে। এসব উদ্ভিদ উষ্ণরক্ত বিশিষ্ট প্রাণীর মতো আচরণ করে। ঠাণ্ডা পরিবেশের মধ্যেও এরা নিজেদের শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। Philodendron selloum একভাবে প্রায় ১৮ থেকে ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত, বাঁধাকপি জাতীয় উদ্ভিদটি দুই সপ্তাহ বা তার থেকেও বেশী এবং লোটাস জাতীয় উদ্ভিদটি দুই থেকে চার দিন পর্যন্ত নিজেদের শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং এই তাপমাত্রা বজায় রাখতে পারে।

বাঁধাকপি (Skunk Cabbage) বৈজ্ঞানিক নাম Symplocarpus foetidus; Source: Scientific American
এরকম ঠাণ্ডা পরিবেশে কোনো একটি শারীরবৃত্তীয় কারণে এই উদ্ভিদগুলো এরকম বৈরি পরিবেশেও নিজেদের তাপ উৎপাদনের হার বাড়িয়ে দেয়। বিজ্ঞানে এই ধরনের উদ্ভিদকে থারমোজেনিক উদ্ভিদ বলা হয়। এরা যে পরিবারের সদস্য সেই পরিবার বর্গের উৎপত্তি অনেক পুরনো দিনের এবং মনে করা হয়ে থাকে যে একটি বিশেষ ধরনের পরাগায়নের কারণে এসব উদ্ভিদ নিজেদের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। একধরনের বিটল জাতীয় প্রাণী এই পরাগায়ণে সাহায্য করে। এই প্রাণীগুলোর নিজেদের কাজ সম্পাদনের জন্য উষ্ণ পরিবেশের প্রয়োজন পড়ে। সেজন্য এই উদ্ভিদগুলোর নিজেদের সৃষ্ট তাপমাত্রা এই প্রাণীগুলোতে অতিরিক্ত শক্তি প্রদান করতে সাহায্য করে।

Nelumbo nucifera প্রজাতির লোটাস ফুল; Source: Scientific American
আজকের লেখায় শুধুমাত্র বাঁধাকপির জন্য এদের কৃত কাজগুলো বর্ণনা করা হলো। বাকি দুটি উদ্ভিদেও একই প্রক্রিয়া কাজ করে। এই প্রজাতির বাঁধাকপির চারপাশে বরফ গলে যাওয়ার কারণ হচ্ছে বাঁধাকপিটি নিজের ভিতরকার তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয় বলে এর শরীর থেকে অবলোহিত রশ্মি বাইরে বেরিয়ে নিঃসরিত হয় এবং এই কারণে আশেপাশের বরফগুলো গলে যায়। পাখি বা স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মতো এদেরকেও Thermoregulating জীব বলা যায়। আশেপাশের পরিবেশের তাপমাত্রার পরিবর্তনের সাথে সাথে এরা নিজেদের তাপামাত্রাও বাড়িয়ে ফেলতে পারে।

এই প্রজাতির বাঁধাকপির চারপাশে বরফ গলে যাওয়ার কারণ হচ্ছে বাঁধাকপিটি নিজের ভিতরকার তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয় বলে এর শরীর থেকে অবলোহিত রশ্মি বাইরে বেরিয়ে নিঃসরিত হয়; Source: deanswidflowiers.com
এই ধরনের উদ্ভিদ বিষয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গবেষক হচ্ছে রজার এস. সেইমোর। তিনি এই ধরনের উদ্ভিদ নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাপত্র বের করেছেন। উদ্ভিদবিদ্যার ইতিহাস ঘেঁটে জানলে অবাক হতে হয় যে প্রায় ২৫০ বছর আগে ১৭৭৮ সালে প্রথম ফ্রান্সের প্রকৃতিবিদ জিন ব্যাপটিস্ট দে লেমারক প্রথম এই ধরনের উদ্ভিদের খোঁজ পান যেগুলো নিজেরা নিজেরাই নিজেদের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে। প্রায় দু’শ বছর পরে কোনো কোনো গবেষক পরীক্ষা করে দেখেন যে, আসলে উদ্ভিদের কোষের ভিতর কিছু একটা হয় যে কারণে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ১৯৬৬ সালে বিখ্যাত বিজ্ঞান ভিত্তিক ম্যাগাজিন Scientific American এ এই বিষয়ে একটি গবেষণাপত্র বের হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্টিয়ান জে. ডি. মিউজ প্রথম এই উদ্ভিদগুলোর এরকম আচরণের কারণ প্রকাশ করেন।

ATP তৈরির পর তা ভেঙ্গে উদ্ভিদ নিজের জন্য যে শক্তির সঞ্চয় করে, সেটা করার সময়ই তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। এই প্রক্রিয়া অন্যান্য উদ্ভিদের মধ্যেও দেখা গেলেও এই ধরনের উদ্ভিদের এরয়েড কোষগুলোতে এই প্রক্রিয়া সংগঠিত হয় বিধায় উদ্ভিদের নিজেদের শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়; Source: fosc.org
তাদের গবেষণায় প্রকাশ পায়, উদ্ভিদের মাইটোকন্ড্রিয়া, যাকে শক্তি উৎপাদনের কারণে জীবের ‘পাওয়ার হাউজ’ বলা হয়, সেখানে দুই ধরনের জীব-রাসায়নিক প্রক্রিয়া সংগঠিত হয়। এই দুটি প্রক্রিয়াকে আলাদা করার জন্য সায়ানাইড নামক রাসায়নিক পদার্থের প্রতি উদ্ভিদের উদ্দীপনার ব্যাপারটি নিয়ে কাজ করা হয়। একধরনের উদ্দীপনা হচ্ছে যখন সায়ানাইডের মাধ্যমে উদ্ভিদগুলোতে বিষক্রিয়া হয়, এবং আরেক ধরনের উদ্দীপনা হচ্ছে যখন উদ্ভিদে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজ শুরু হয় তখন এই সায়ানাইড সেই উদ্ভিদের উপর আদৌ কোনো উদ্দীপনার সৃষ্টি করে কিনা, কিন্তু সেই শারীরবৃত্তীয় কাজে তা অংশ নেয় না। এই দুই প্রক্রিয়াতেই ATP বা এডিনোসিন ট্রাই ফসফেট নামক অণু তৈরির জন্য পুষ্টিদায়ক পদার্থ এবং অক্সিজেন ব্যবহার করা হয় যা উদ্ভিদে শক্তি তৈরি করে। এই ATP তৈরির পর এটা ভেঙ্গে উদ্ভিদ নিজের জন্য যে শক্তির সঞ্চয় করে তা করার সময়ই তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। এই প্রক্রিয়া অন্যান্য উদ্ভিদের মধ্যেও দেখা গেলেও এইধরনের উদ্ভিদের এরয়েড কোষগুলোতে এই প্রক্রিয়া সংগঠিত হয় বিধায় উদ্ভিদের নিজেদের শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়।
তথ্যসূত্র
[১] Walker, J. (2007). Flying Circus of Physics. John Wiley & Sons, Inc
[২] Seymour, R. S., and P. Schultze-Motel. (1996) Thermoregulating lotus flowers, Nature, Volume. 383, No. 6598, page. 305, (26 September 1996)
[৩] Seymour, R. S., P. Schultze-Motel, and I. Lamprecht. (1998) Heat production by sacred lotus flowers
depends on ambient temperature, not light cycle, Journal of Experimental Botany, Volume. 49, page. 1213-1217, (1998)
[৪] Seymour, R. S., and P. Schultze-Motel. (1997) Heat-producing flowers, Endeavour, Volume. Vol. 21, No. 3, page. 125-129, (1997)
ফিচার ইমেজ সোর্সঃ Earth.com