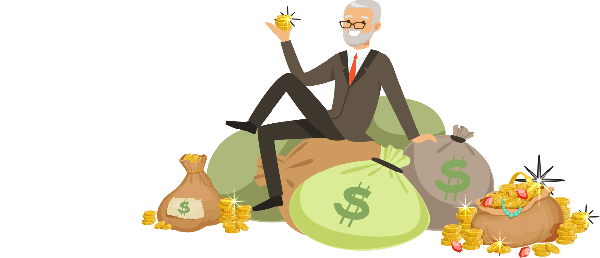যুদ্ধ মানবজাতির জন্য হুমকিস্বরূপ হলেও কখনো কখনো যুদ্ধ অধিকার আদায়ের একমাত্র উপায় হয়ে ওঠে। শোষকের হাত থেকে মুক্তির জন্য অনেক সময় শোষিতের হাতে যুদ্ধ ভিন্ন আর অন্য কোনো উপায় থাকে না। সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই যুদ্ধ-বিগ্রহ এর অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে আছে। অনেক সভ্যতা যুদ্ধের কারণে পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। যুদ্ধের কারণে যে শুধু মানুষ বা সম্পদের ক্ষতি হয় তা নয়, বরং যুদ্ধ পরিবেশ ও প্রকৃতির জন্যও মারাত্মক ক্ষতিকর।
পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মে যুদ্ধ প্রসঙ্গে বিভিন্ন নিয়মকানুনের উল্লেখ আছে। ইসলামে যুদ্ধের বেশকিছু নিয়মনীতিতে বলা হয়েছে যুদ্ধের কারণে যাতে সাধারণ জনগণ, নারী-শিশু, অসহায় ব্যক্তি, পশুপাখি, পরিবেশের কোনো ক্ষতি না হয়। বাইবেলে যুদ্ধের সময় যেন অপ্রয়োজনে গাছ না কাটা হয় সেই ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। বৌদ্ধধর্মে অহিংসার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে যুদ্ধ শুরু হলে তখন আর এসব নিয়ম পালনের কথা মানুষের মাথায় থাকে না, তাই এগুলো রক্ষা করাও হয়ে ওঠে না। কারণ যুদ্ধের প্রভাব এতটাই ভয়ংকর যে এর আঁচ চারপাশের পরিবেশকেও নিতে হয়।

রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়, এরকম একটা কথা বেশ প্রচলিত আছে। অর্থাৎ বড় বড় রাঘববোয়ালদের ঝগড়ার মাঝে পড়ে সর্বসান্ত হয় নিরীহ মানুষ। কিন্তু একইসাথে যে নলখাগড়া অর্থাৎ পরিবেশেরও দফারফা হয়ে যায় সেটার খবর কয়জনে রাখে! যুদ্ধের বিভীষিকা সাময়িক কিন্তু পরিবেশের ওপর সেই যুদ্ধের প্রভাব দীর্ঘমেয়াদি হতে পারে আর তার জ্বলজ্বলে প্রমাণ হচ্ছে হিরোশিমা ও নাগাসাকি। যুদ্ধের ফলে একটি দেশ বা অঞ্চলের সামগ্রিক পরিবেশগত প্রভাব নিয়ে আজকের আয়োজন।
যুদ্ধ ও পরিবেশ
যুদ্ধ জয়ের জন্য পরিবেশ বিনষ্ট করার প্রচেষ্টা প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। প্রাচীন রোমান ও অ্যাসিরিয়দের বিরুদ্ধে শত্রুদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করার জন্য তাদের আবাদযোগ্য জমিতে লবণ ছিটিয়ে তা চাষের অনুপযোগী করে দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। আধুনিক যুগে যুদ্ধের ধরণ বদলেছে, এসেছে নতুন নতুন প্রযুক্তি। ওয়াশিংটনের এনভায়রনমেন্টাল ল ইনস্টিটিউটের ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রাম বিভাগের সহপরিচালক কার্ল ব্রুচ বলেন, ‘প্রযুক্তির পরিবর্তন হয়েছে এবং প্রযুক্তির সম্ভাব্য প্রভাবও এখন যথেষ্ট ভিন্ন’। ‘যুদ্ধের পরিবেশগত প্রভাব: নৈতিক, অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ’ বইয়ের লেখক ব্রুচ মনে করেন, আধুনিক রাসায়নিক, জৈবিক ও পারমাণবিক অস্ত্রের পরিবেশের ওপর মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনার নজিরবিহীন ক্ষমতা রয়েছে। নজিরবিহীন এই কারণে যে মানুষ এখনো এই ক্ষমতার প্রয়োগ প্রত্যক্ষ করেনি। সৌভাগ্যক্রমে যুদ্ধের কারণে মারাত্মক পরিবেশ বিপর্যয়ের কোনো ঘটনা এখনো না ঘটলেও এটা সভ্যতার জন্য গুরুতর হুমকি বলে উল্লেখ করেন ব্রুচ।

কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে আধুনিক সমরাস্ত্র ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে পরিবেশের ওপর তেমন নেতিবাচক প্রভাব না ফেলে যুদ্ধের উদ্দেশ্য হাসিল করা যায়। শুধু নির্দিষ্ট লক্ষবস্তুর ওপর আক্রমণ হেনে আশপাশের অঞ্চলকে যুদ্ধের আঁচ থেকে রক্ষা করা যায়। অবশ্য এই যুক্তি তর্কসাপেক্ষ বলে মনে করেন ওয়াশিংটনের ‘এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জেস এন্ড সিকিউরিটি প্রোগ্রাম’র পরিচালক জিওফ্রে ডেবেলকো।
যুদ্ধ যে শুধু দুটো ভিন্ন দেশের মধ্যে হয় এমনটা নয়। কখনো কখনো একটি দেশে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। দেশের ভেতর একাধিক পক্ষ তৈরি হয়ে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। তখন সেখানে স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধের নিয়মকানুন মানা হয় না। আর আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোও অনেক সময় একটি দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলাতে পারে না বা চায় না। তখন ওই গৃহযুদ্ধরত দেশের পরিবেশগত বিপর্যয়ের ওপর কারও কোনো নজর পড়ে না।

আবাসস্থল ধ্বংস
ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যরা জঙ্গলের মধ্যে ও জলাভূমিতে এজেন্ট অরেঞ্জ ব্যবহার করেছিল। এজেন্ট অরেঞ্জ হচ্ছে একপ্রকার রাসায়নিক উদ্ভিদনাশক পদার্থ। জঙ্গল আর জলাভূমিতে ভিয়েতনামিজ গেরিলারা ওঁৎ পেতে থাকত, তাই এই ব্যবস্থা। মার্কিন বাহিনী প্রায় সাড়ে চার মিলিয়ন একর পরিমাণ স্থানের ওপর আনুমানিক ২০ মিলিয়ন গ্যালন রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার করেছিল। কিছু কিছু অঞ্চলে এই পরিবেশগত বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে কয়েক দশক লেগেছিল। এর ফলে মানুষের জন্য ওই অঞ্চলগুলো যেমন বসবাসের অনুপযোগী হয়ে গিয়েছিল তেমনিভাবে সেখানকার বাস্তুসংস্থানও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

এছাড়া যখন যুদ্ধের কারণে বিশাল সংখ্যক মানুষ এক স্থান ত্যাগ করে অন্য স্থানে আশ্রয় নেয়, তখন নতুন স্থানের ওপর ব্যাপক চাপ পড়ে। মানুষের আশ্রয়ের জন্য বিশাল পরিমাণ বনাঞ্চল কাটার প্রয়োজন হতে পারে। অনিয়ন্ত্রিত শিকার, ভূমি ক্ষয়, মানববর্জ্য ইত্যাদির কারণে পরিবেশের বিপর্যয় ঘটে। ১৯৯৪ সালে রুয়ান্ডার গণহত্যার সময় দেশটির একটি ন্যাশনাল পার্ক শরণার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল। ফলে ঐ পার্কের স্থানীয় কৃষ্ণসার হরিণের জাত বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এক কোটি শরণার্থীদের ভার বহন করতে গিয়ে ভারতের পরিবেশকে যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল।

নতুন প্রজাতির কর্তৃত্ব
যুদ্ধের সময় একটি দেশের গাছপালা বা প্রাণীর প্রজাতি অন্য দেশে বাহিত হতে পারে। যুদ্ধজাহাজ, কার্গো প্লেন, স্থলযান ইত্যাদিতে করে অনেক সময়ই সৈন্য ও গোলাবারুদের পাশাপাশি গাছপালা, বীজ, প্রাণী ইত্যাদিও পরিবাহিত হয়ে যেতে পারে। এই নবাগত প্রজাতিগুলো স্থানীয় প্রজাতিকে বিলুপ্তির মুখে ঠেলে দিয়ে নিজেরা তাদের স্থান দখল করতে পারে।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে প্রশান্ত মহাসাগরের লেসান দ্বীপ কিছু বিলুপ্ত গাছ ও প্রাণীর আবাসস্থল ছিল। কিন্তু যুদ্ধের পরে এই দ্বীপের বাস্তুসংস্থান পুরোপুরি পাল্টে যায়।
অবকাঠামো ধ্বংস
যুদ্ধ শুরু হলে শত্রুদেশের রাস্তাঘাট, সেতু, ঘরবাড়ি সবচেয়ে বড় টার্গেট হয়ে ওঠে। এগুলো ধ্বংস হওয়ার সাথে পরিবেশের ক্ষতির সরাসরি কোনো সম্পর্ক না থাকলেও পরোক্ষ সম্পর্ক আছে। যেমন, একটি রাসায়নিক কারখানা ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেখান থেকে নির্গত রাসায়নিক উপাদান পরিবেশের বায়ু, পানি, মাটির ক্ষতি করে।

উৎপাদন বৃদ্ধি
যুদ্ধ মানেই বাড়তি খরচ। যুদ্ধের এই বাড়তি ব্যয় বহনের জন্য প্রয়োজন হয় বাড়তি উৎপাদনের। শিল্প কারখানা ও কৃষিক্ষেত্রে অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য প্রকৃতি থেকে স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে বেশি সম্পদ আহরণ করা লাগে। বাড়তি চাপ সৃষ্টির ফলে পরিবেশের স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়। এমনকি যেসব অঞ্চল সরাসরি যুদ্ধের প্রভাব থেকে মুক্ত, সেসব অঞ্চলও এই অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বন কেটে গম, তুলা ও অন্যান্য ফসল চাষ শুরু হয়। যুদ্ধে কাঠের চাহিদা মেটানোর জন্য বিশাল পরিমাণ গাছ কাটার প্রয়োজন হয়। মধ্যপ্রাচ্যে ক্ষমতাধর জঙ্গিগোষ্ঠীরা অর্থ সংগ্রহের জন্য তাদের দখল করা তৈলের খনিগুলো থেকে যাচ্ছেতাই পরিমাণ তৈল আহরণ করে। এভাবেই যুদ্ধের খরচ মেটানোর জন্য প্রকৃতির ওপরই চড়াও হয় মানুষ।
স্কর্চড আর্থ পলিসি
স্কর্চড আর্থ পলিসি সামরিক বাহিনীগুলোর মধ্যে বহুল প্রচলিত একটি যুদ্ধকৌশল। স্কর্চড আর্থ বলতে মূলত জমির ফসল পোড়ানো ও বাড়িঘর ধ্বংস করানোকে বোঝানো হলেও বর্তমানে এটি যেকোনো ধরনের পরিবেশগত ধ্বংসের কৌশলকে বোঝায়। ধরা যাক, ‘ক’ ও ‘খ’ দুটো প্রতিবেশি দেশ। ‘ক’ কোনো কারণে ‘খ’ এর ওপর আক্রমণ চালায়। ‘খ’ দেশের ভেতরে ‘ক’ দেশের সেনাবাহিনী প্রবেশ করে যুদ্ধ শুরু করে। ‘ক’-এর সেনাবাহিনী এগোতে এগোতে তাদের চলার পথের সব জমির ফসল পুড়িয়ে দেয়, পানির উৎসে বিষ ঢেলে দেয়, বাড়িঘর ধ্বংস করে দেয়, যোগাযোগ ব্যবস্থা বিকল করে দেয় যাতে শত্রুসেনারা এগুলো থেকে কোনো সুবিধা না পেতে পারে। এভাবে সামরিক বাহিনী যখন আশপাশের পরিবেশের ব্যবহার উপযোগী সবকিছু বিনষ্ট করে দেয় যাতে শত্রুরা তা ব্যবহার করতে না পারে, তখন তাকে স্কর্চড আর্থ পলিসি বলে।

স্কর্চড আর্থ পলিসির এই প্রয়োগ শুধু যে শুধু শত্রু দেশের অভ্যন্তরে প্রয়োগ করা হয় ব্যাপারটা মোটেই তা না বরং নিজের দেশের সম্পদ ধ্বংসও করা হয় অনেক সময়। আর এই প্রক্রিয়ায় কখনো কখনো স্থানীয় মানুষকেও নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়। সামরিক বাহিনী কোনো স্থানে অগ্রসর হওয়ার সময় যেমন এই পদ্ধতিটি প্রয়োগ করে তেমনিভাবে কোনো স্থান থেকে পিছু হঠার সময়ও ঐ স্থানের সবকিছু ধ্বংস করে দিয়ে যায় যাতে করে শত্রুবাহিনী তাদের পরিত্যক্ত স্থান থেকে কোনো উপকার না পায়।
আমেরিকার গৃহযুদ্ধের ইউনিয়ন আর্মির জেনারেল উইলিয়াম টি. শেরম্যান সর্বপ্রথম যুদ্ধকে যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়িয়ে তার বাইরে শত্রুপক্ষের অবকাঠামো পর্যন্ত নিয়ে যান। শেরম্যান মনে করতেন যুদ্ধ জেতার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে শত্রুর যুদ্ধ চালানোর সামর্থ্যকে ধ্বংস করে দেওয়া। গৃহযুদ্ধের সময় দক্ষিণের ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, রেলপথ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, কলকারখানা ইত্যাদি ধ্বংস করে দেওয়ার ফলে কনফেডারেশন আর্মি মনস্তাত্ত্বিকভবে হেরে গিয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশান রেড আর্মি ও জার্মান ভারমাত বাহিনী উভয়ই স্কর্চড আর্থ পলিসি অবলম্বন করে। ইউক্রেন থেকে পিছু হঠার সময় রেড আর্মি ইউক্রেনে হাজার হাজার কারখানা, বাঁধ, সড়ক ধ্বংস করে দেয় যাতে অগ্রসরমান জার্মান বাহিনী এগুলো থেকে কোনো সুবিধা নিতে না পারে। ফার্মগুলোকে আদেশ দেওয়া হয় সব ফসল ও গবাদিপশু নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে নাহয় রেড আর্মিকে দিয়ে দিতে। এরপর ১৯৪৩-৪৪ সালের দিকে যখন জার্মান বাহিনী ইউক্রেন ত্যাগ করে পিছু হটে তখন হিটলার সেখানে স্কর্চড আর্থ পলিসি প্রয়োগের আদেশ দেন। জার্মানরা প্রায় ২৮,০০০ গ্রাম পুড়িয়ে দেয়। এভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দু-দুবার স্কর্চড আর্থ পলিসির শিকার হয়ে পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায় ইউক্রেন।
দ্বিতীয় সাইনো-জাপানি যুদ্ধের সময় জাপানি বাহিনীকে ঠেকাতে চীনারা ইয়েলো নদীর ওপর একটি বাঁধ ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয়। এর ফলে হাজারো জাপানি সৈনিক যেমন মারা যায় তেমনিভাবে কয়েক হাজার চীনা কৃষকও ডুবে মরে।
স্কর্চড আর্থ পলিসিকে সফল করার একটি আধুনিক পদ্ধতি হলো কার্পেট বম্বিং। কার্পেট বম্বিং হচ্ছে বিশাল অঞ্চল জুড়ে বোমাবর্ষণ, যার লক্ষ্য হচ্ছে ঐ অঞ্চলের প্রতিটি ইঞ্চি পুরোপুরি ধ্বংস করে দেওয়া।

আধুনিক যুগে ইন্টারনেট, টেলিভিশন ইত্যাদির যুগে কার্পেট বম্বিং খুব একটা গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে না। কারণ অনেকেই মনে করেন এটি আদৌ যুদ্ধের কোনো কৌশলই নয়, বরং ধ্বংসের একটি বৈধকৃত উপায়। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন হেনরি কিসিঞ্জারের পরামর্শে উত্তর ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ায় কার্পেট বম্বিংয়ের নির্দেশ দেন। ফলে প্রচুর বেসামরিক ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং টেলিভিশনের কল্যাণে মানুষ মার্কিন আগ্রাসন প্রত্যক্ষ করে। ধীরে ধীরে কার্পেট বম্বিংয়ের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে ওঠে। অনেক দেশ মার্কিন আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়।
শিকার
বিশাল সংখ্যক সৈন্যবাহিনীর খাবার জোগাড়ে অনেক সময় শিকারের প্রয়োজন হয়। চাহিদার কারণে পোচিং বেড়ে যায়। আবার স্থানীয় গৃহপালিত পশুর অতিরিক্ত জবাইয়ের সাথে উৎপাদনের হার পাল্লা দিয়ে উঠতে পারে না। সুদানের যুদ্ধে চোরাশিকার বেড়ে যাওয়ার ফল ভুগতে হয় পাশের দেশ কঙ্গোকে। কঙ্গোর গারাম্বা ন্যাশনাল পার্কের হাতির সংখ্যা ২২,০০০ থেকে ৫,০০০-এ নেমে যায় এবং সবমিলিয়ে মাত্র ১৫টি শ্বেতগন্ডার বেঁচে থাকে।
জীবাণু, রাসায়নিক ও পারমাণবিক অস্ত্র
এই ধরনের অস্ত্রের উৎপাদন, পরীক্ষা, পরিবহন ও ব্যবহার সবই পরিবেশের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। যদিও এগুলোর ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা ও বিধিনিষেধ আছে, তবুও সামরিক বিশেষজ্ঞরা এই অস্ত্রের ব্যবহার নিয়ে উদ্বিগ্ন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমার ফলে সৃষ্ট পরিবেশগত বিপর্যয় মানুষ নিজের চোখে দেখেছে।

প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে ৩৪০ টনের মতো ডিপ্লিটেড ইউরেনিয়াম (depleted uranium) সমৃদ্ধ মিসাইল নিক্ষেপ করে। ডিইউ হচ্ছে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন উপজাত। সীসার চেয়ে দ্বিগুণ ঘনত্বসম্পন্ন এই উপাদানটি ট্যাংক আর্মার ভেদ করার ক্ষমতা রাখে বিধায় সামরিক ক্ষেত্রে এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। ইরাকে এই রাসায়নিক উপাদান ব্যবহারের ফলে পরিবেশের মৌলিক উপাদানগুলো যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তেমনিভাবে মানুষও এর নেতিবাচক প্রভাব থেকে বাঁচতে পারেনি। কয়েকটি গবেষণায় দেখা যায় ইরাকে যুদ্ধের পর ইরাকিদের মাঝে ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনার হার আগের তুলনায় কিছুটা বেড়ে গেছে। কারণ এই মিসাইল থেকে সৃষ্ট রেডিয়েশন ইরাকের মাটি ও পানিকে দূষিত করে পরিবেশকে ক্যান্সারের জন্য উপযোগী বানিয়ে ফেলেছে। অবশ্য যুক্তরাজ্য সরকার এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

আধুনিক হাইড্রোজেন বোমাগুলো আরও বেশি ধ্বংসাত্মক ক্ষমতাসম্পন্ন। ফলে যদি কখনো কোনো জায়গায় এসব বোমা ব্যবহার করা হয় তাহলে সেখানে আর পরিবেশ বলে আদৌ কিছু থাকবে না। তেমনিভাবে জীবাণু অস্ত্রগুলো একটি পরিবেশের সকল জৈবিক উপাদানকে বিলুপ্তির পথে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পারমাণবিক বোমা হামলার ফলে জাপানের (নাগাসাকি) জনসাধারণ ও পরিবেশের ওপর কী প্রভাব পড়েছিল তা জানতে এখানে ক্লিক করুন।
প্রকৃতি বাঁচিয়ে যুদ্ধ?
২০০৭ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে, ঐ বছর মার্কিন সশস্ত্র বাহিনী ২০.৯ বিলিয়ন লিটার ফসিল ফুয়েল ব্যবহার করেছে। এর ফলে যে পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়েছে তার পরিমাণ ছিল ডেনমার্কে এক বছরে নিঃসৃত কার্বন ডাইঅক্সাইডের সমতুল্য। কিন্তু এটা স্বাভাবিক সময়ে ব্যবহৃত জ্বালানির হিসেব। যুদ্ধের সময় এর পরিমাণ অবিশ্বাস্যভাবে বেড়ে যায়। আরেকটি গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় ইরাক যুদ্ধের সময় মার্কিন বাহিনী এর ট্যাংক ও ব্রেডলি ফাইটিং ভেহিকলের জন্য প্রতি মাসে ১৯০.৮ মিলিয়ন লিটার জ্বালানি খরচ করেছে। এই পরিমাণ জ্বালানির আনুমানিক তিন ভাগের দুই অংশ আবার খরচ করা হয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে জ্বালানি সরবরাহের কাজে।

ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত হলেও অনেকেই মনে করেন সামরিক সংঘাতের শেষে প্রকৃতি ঠিকই টিকে থাকে। অনেক গবেষক উল্লেখ করেছেন, ভিয়েতনামের যুদ্ধে উদ্ভিদনাশক রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে যে পরিমাণ জঙ্গল ধ্বংস করা হয়েছে, যুদ্ধের পর সম্পদ আহরণ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে তার চেয়েও বেশি পরিমাণ বন বিনষ্ট করা হয়েছে।
তবে তা-ই বলে এই তত্ত্ব কিন্তু মোটেও যুদ্ধকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নয় বলে একমত হয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলে পরিবেশের ওপর যে প্রভাব পড়ে তার চেয়ে যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট প্রভাব বেশি দীর্ঘস্থায়ী হয়।
শেষ কথা
যুদ্ধের যদি লক্ষ্য হয় কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চল দখল করা, তাহলে ঐ অঞ্চলের পরিবেশটা যেন ঠিক থাকে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হয়। কারণ যদি যুদ্ধের কারণে পরিবেশই বসবাসের অনুপযোগী হয়ে ওঠে তাহলে আর সেই অঞ্চল জয় করার ফায়দা কী? পরিবেশ ধ্বংস করে যে পরিমাণ লাভ করা যায়, তা রক্ষা করে তার চেয়ে বেশি পরিমাণ অর্জন করা যায়। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে প্রাকৃতিক সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রকৃতি বেঁচে থাকলেই না সভ্যতা বেঁচে থাকবে।
সুতরাং পাঠক, আপনার যদি আপনার প্রতিবেশির সাথে সাপে-নেউলে সম্পর্ক হয়, তবুও তার বাগানের কলাগাছ রাতের বেলা গিয়ে কেটে দিয়ে আসবেন না, তার ধানখেতে নিজের বাছুরটিকে ছেড়ে দেবেন না। কারণ আপনার যুদ্ধ তার সাথে, তার বাগানের কলার মোচার সাথে না। আপনি হয়তো তার পরিবেশে ধ্বংস করে আত্মতুষ্টিতে ভুগবেন কিন্তু দিনশেষে আপনিও কিন্তু ঐ একই পরিবেশের বাসিন্দা।