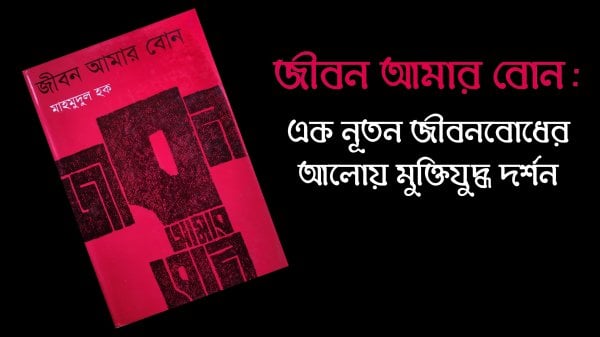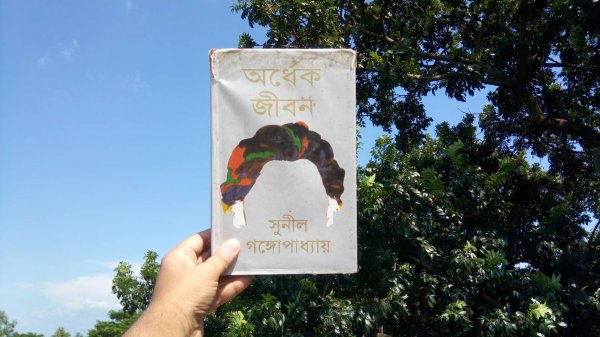চলতি বছরের প্রথম চার মাসে মুক্তি পাওয়া ব্যবসাসফল বাংলাদেশি সিনেমাগুলোর লিস্ট খুঁজছিলাম। আলাদা করে তাদের নাম না বলে শুধু জনরা বা ক্যাটাগরির দিকে তাকালে দেখা যাবে কমেডি, রোমান্স, ড্রামা ছাড়া সেখানে অন্য কোনোকিছুর অস্তিত্ব নেই। এসব সিনেমার টার্গেট অডিয়েন্স মূলত তরুণ প্রজন্ম। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে যে বিনোদনের পাশাপাশি চেতনা এবং বিবেকবোধও গড়ে তোলা যায়- আমাদের দেশের তরুণ সমাজ তা কিভাবে জানবে? আমাদের চলচ্চিত্রে তো নায়ক-নায়িকার প্রেম আর গুন্ডাদের সাথে নায়কের ব্যাপক মারামারি ছাড়া আর তেমন কিছু পাওয়া যায় না। বাংলাদেশ ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের এখন খারাপ সময় চলছে। এ নিয়ে বিস্তর লেখালেখি, আলোচনা-সমালোচনাও হতে বাকি নেই। তা চলুক, আমরা বরং ঘুরে আসি বাংলা চলচ্চিত্রের স্বর্ণালি দিনগুলো থেকে।

বাংলাদেশে ২০১৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের তালিকা, wikipedia.com
দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে গণমানুষের হৃদয়ে স্বাধীনতার জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা, তৃষ্ণা তৈরি করার প্রয়োজন ছিল। এই যুদ্ধ তো কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না বরং জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী, পেশা নির্বিশেষে সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়েই দেশ স্বাধীন করেছে। স্বাধীনতার সেই বোধ জাগ্রত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম ছিল চলচ্চিত্র। আমাদের দেশে মোটামুটি সব শ্রেণীর মানুষই চলচ্চিত্র দেখেন। চলচ্চিত্রকে হাতিয়ার বানিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান রাখা ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম একজন জহির রায়হান।
আমাদের দেশের সর্বকালের সেরা চলচ্চিত্র নির্মাতাদের তালিকা করতে গেলে নিঃসন্দেহে জহির রায়হানের নাম সেখানে শুরুর দিকেই থাকবে। ক্ষণজন্মা এই প্রতিভাবান নির্মাতা তার সংক্ষিপ্ত জীবনে চলচ্চিত্র থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে এমন এক শ্রেণীর দর্শক তৈরি করে রেখে গেছেন। বাংলা সিনেমার জগতে তিনি নতুন একটি যুগের জন্ম দিয়েছেন, অনেকে তাকে তাই ‘বাংলাদেশি বাংলা সিনেমার জনক’ বলেও আখ্যা দিয়ে থাকেন। জাতি হিসেবে আমাদের পৃথক একটি সত্ত্বার কথা ফুটে উঠেছে জহির রায়হানের চলচ্চিত্রে। জীবন যখন তাকে যে পরিস্থিতি দেখিয়েছে, তিনি জীবনের সেই গল্পই ক্যামেরা এবং কলমে ধারণ করেছেন। সেলুলয়েড আর কাগজের ডায়েরিতে তিনি অবিরাম বন্দি করেছেন সাধারণ মানুষের নিপীড়নের চিত্র, বলিষ্ঠ প্রতিবাদের গল্প। তার সাহিত্য আর চলচ্চিত্র থেকে যেন মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার এক দৃঢ় প্রত্যয়ের স্ফুলিঙ্গ স্ফুরিত হতে থাকে। বীরদর্পে তিনি বলে গেছেন মুক্তিযুদ্ধের কথা, যে যুদ্ধ কেড়ে নিয়েছে তাঁর প্রাণ।

জহির রায়হান, jaijaidinbd.com
১৯৩৫ সালের ১৯ আগস্ট মজুপুর নামের একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন জহির রায়হান, তখন তাঁর নাম রাখা হয় মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ। স্বাধীন বাংলাদেশে মজুপুর গ্রামটি ফেনী জেলার অন্তর্ভুক্ত। জহির তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার পর্ব শেষ করেন কলকাতার মিত্র ইন্সটিটিউট এবং পরবর্তীতে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের সময় বাবা-মার সাথে কলকাতা ছেড়ে বাংলাদেশে নিজ গ্রামে চলে আসেন তিনি। ১৯৪৯ সালে সাহিত্য ম্যাগাজিনে তাঁর প্রথম কবিতা ‘ওদের জানিয়ে দাও’ প্রকাশিত হয়। ১৯৫০ সালে ফেনীর আমিরাবাদ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস করে ঢাকা কলেজে ভর্তি হন। ১৯৫৩ সালে এখান থেকে আইএসসি পাস করেন জহির। এরপর তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন কিন্তু সেখানে পড়ালেখা চালিয়ে না গিয়ে চলে আসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে তিনি বাংলায় স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি লাভ করেন।
শুরুর দিকে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতি বেশ ঝোঁক ছিল জহির রায়হানের। কমিউনিস্ট পার্টিগুলো যখন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়, পার্টির নেতারা তখন গা ঢাকা দিতে বাধ্য হন। সেই সময় জহির চিঠিপত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য নিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় বিলি করতেন, পার্টির নেতাদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করার প্রধান মাধ্যম হয়ে পড়েন তিনি। লুকিয়ে থাকা নেতাদের মুখে মুখে তিনি রায়হান নামে পরিচিতি লাভ করেন এবং জহিরুল্লাহ নামটি পরিবর্তন করে জহির রায়হান নাম ধারণ করেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনেও ছিল তাঁর সক্রিয় ভূমিকা। ২১শে ফেব্রুয়ারি যাবতীয় নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মিছিল বের করা প্রথম ১০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। সেখান থেকে তাকে গ্রেফতার করে থানায় পাঠানো হয়।
ছাত্রজীবনে জহির রায়হান সাহিত্যচর্চার প্রতি খুব আগ্রহী ছিলেন। তাঁর প্রথম বই ‘সূর্য গ্রহণ’, যা আসলে অনেকগুলো গল্পের সমন্বয়ে রচিত একটি গল্পগুচ্ছ, ১৩৬২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। তাঁর লেখা অন্যান্য বইগুলোর মধ্যে ‘শেষ বিকেলের মেয়ে’, ‘হাজার বছর ধরে’, ‘আরেক ফাল্গুন’, ‘বরফ গলা নদী’, ‘আর কটা দিন’ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৭০ সালে তিনি ও তাঁর কয়েকজন সঙ্গী মিলে ‘এক্সপ্রেস’ নামের একটি সাপ্তাহিক ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এছাড়া সাংবাদিক হিসেবে ‘যুগের আলো’, ‘যান্ত্রিক’ সহ বেশ কিছু সিনেমা ম্যাগাজিনেও কাজ করেছেন তিনি। ‘প্রবাহ’ নামের একটি মাসিক পত্রিকার তিনি ছিলেন সম্পাদক। কয়েকটি পত্রিকার সাহিত্য পাতার দেখাশোনার ভারও ছিল জহিরের উপর।
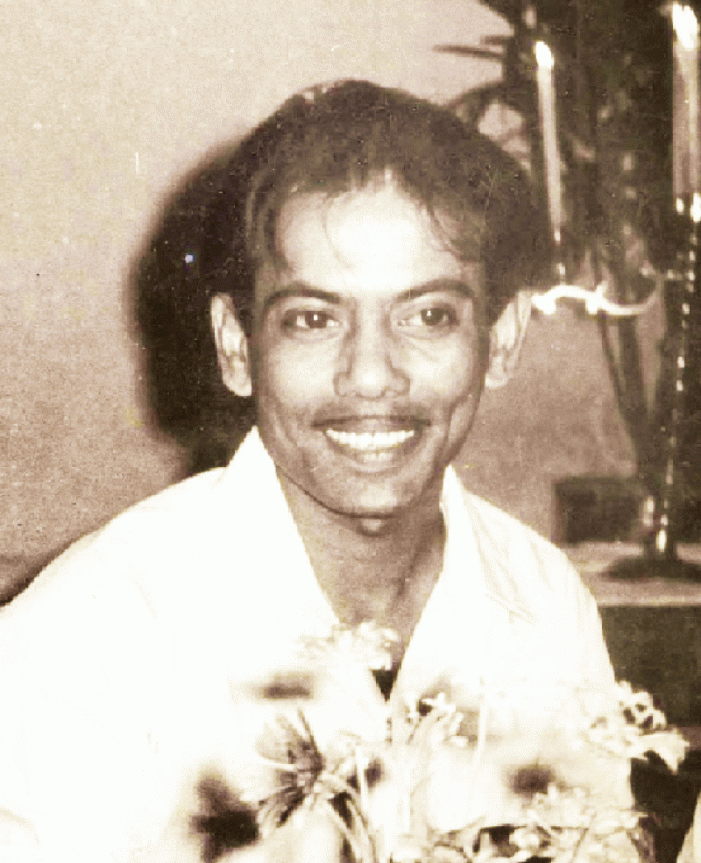
সাহসের অপর নাম জহির রায়হান, prothom-alo.com
১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর জহির রায়হান ফটোগ্রাফি শিখতে কলকাতা যান। সেখানে তিনি ‘প্রমথেশ বড়ুয়া মেমোরিয়াল ফটোগ্রাফি স্কুলে’ ভর্তি হন। ১৯৫৬ সাল থেকে শুরু হয় তাঁর চলচ্চিত্র জগতের যাত্রা। শুরুতে তিনি পরিচালক এ জে কারদারের সাথে ‘জাগো হুয়া সাবেরা’ চলচ্চিত্রে সহকারী হিসেবে কাজ করেন। ১৯৬০ সালে মুক্তি পায় জহির রায়হান পরিচালিত প্রথম চলচ্চিত্র ‘কখনো আসেনি’। এরপর একে একে তিনি নির্মাণ করেন ‘কাজল’, ‘কাঁচের দেয়াল’, ‘বেহুলা’, ‘জীবন থেকে নেয়া’, ‘আনোয়ারা’, ‘সঙ্গম’ এবং ‘বাহানা’। ‘জীবন থেকে নেয়া’ চলচ্চিত্রে পাকিস্তানি স্বৈরাচারীদের বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ অবস্থান তৈরি করে জনগণের মধ্যে ‘স্বাধীন হতেই হবে’ এই বোধটি জাগিয়ে তোলেন জহির। শুধু চিত্রনাট্যই নয় গানের দিক থেকেও এই সিনেমাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত ‘আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি’ গানটি প্রথমবারের মতো কোনো চলচ্চিত্রে ব্যবহার করেন জহির রায়হান। এছাড়া খান আতাউর রহমানের কণ্ঠে ‘এ খাঁচা ভাঙবো আমি কেমন করে’ গানটি যেন লাখো মানুষের মনের কথাই প্রতিধ্বনিত করেছে।
‘লেট দেয়ার বি লাইট’ নামের একটি ইংরেজি চলচ্চিত্র নির্মাণে হাত দেন তিনি তবে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় কাজটি আর শেষ করতে পারেননি। ১৯৭১ সালের ভয়াল ২৫ মার্চের পর জহির কলকাতায় গিয়ে ‘স্টপ জেনোসাইড’ নামে একটি ডকুমেন্টারি তৈরি করেন। এখানে বাংলাদেশের উপর পাকিস্তানিদের বর্বরোচিত হামলার কাহিনী হৃদয়বিদারকভাবে বর্ণনা করেছেন তিনি। সারা পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই ডকুমেন্টারিটি বিশ্ব জনতার কাছে বাংলাদেশের দুরবস্থার বার্তাবাহকের কাজ করে। জহিরের উর্দু সিনেমা ‘সঙ্গম’ ছিল পাকিস্তানের প্রথম রঙিন সিনেমা। ‘বাহানা’ চলচ্চিত্রটির জন্য তিনি ভিন্ন একটি সিনেমাস্কোপ ব্যবহার করেন। লেন্স ও ফ্রেমের ব্যবহারের ক্ষেত্রে জহির তাঁর সুনিপুণতা দেখান এই চলচ্চিত্রে।
‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসটির জন্য আদমজী সাহিত্য পদক ও ১৯৭২ সালে বাংলা অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেন জহির রায়হান। এছাড়া ‘কাঁচের দেয়াল’ চলচ্চিত্রটির জন্যও নানা পদকে ভূষিত হন তিনি। তাঁর ‘জীবন থেকে নেয়া’ চলচ্চিত্রটির প্রশংসা করেন সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক এবং তপন সিনহা।
ব্যক্তিগত জীবনে জহির রায়হান দুবার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৬১ সালে তিনি সুমিতা দেবীকে বিয়ে করেন এবং তার সাথে ডিভোর্স হয়ে যাওয়ার পর ১৯৬৮ সালে জহির সুচন্দাকে বিয়ে করেন। তাঁর দুই স্ত্রীই ছিলেন নামকরা অভিনেত্রী। সুমিতা এবং জহিরের সংসারে দুই পুত্রসন্তানের জন্ম হয় যাদের নাম বিপুল রায়হান এবং অনল রায়হান। সুচন্দা এবং জহির রায়হানের একটিই পুত্র, তপু রায়হান।

অসংখ্য পুরস্কার অর্জন করেছেন ক্ষণজন্মা এই শিল্পী, bmdb.com.bd
জহির রায়হানের মৃত্যু কিংবা অন্তর্ধান একটি রহস্যজনক ঘটনা। বলা হয়, একটি সংঘবদ্ধ চক্রের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে অকালে প্রাণ হারান এই সম্ভাবনাময় সাহিত্যিক ও চলচ্চিত্র নির্মাতা। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিজেদের পরাজয় নিশ্চিত বুঝতে পেরে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের নিধন করে একটি পঙ্গু স্বাধীন রাষ্ট্র ফেলে যাওয়ার পরিকল্পনা করে। সেই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ১৪ ডিসেম্বর গোবিন্দ চন্দ্র দেব, মুনির চৌধুরী, আনোয়ার পাশা প্রমুখ আরো ১১১০ জন বুদ্ধিজীবীর সাথে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় শহিদুল্লাহ কায়সারকে। বাংলা সাহিত্যের আরেক উজ্বল নক্ষত্র শহিদুল্লাহ কায়সার ছিলেন জহির রায়হানের বড় ভাই।
ভাই শহিদুল্লাহ কায়সার মারা গেছেন না তাকে কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে সে ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন না পরিবারে কেউ। স্বাধীনতার একেবারে পূর্ব মুহূর্তে এতো বড় শোক সামলে উঠতে পারেননি তারা। তাই যখন জহির রায়হানের কাছে একটি ফোনকল আসে যে মিরপুরেরই কোন একটি জায়গায় আটকে রাখা হয়েছে শহিদুল্লাহকে, তখন ভাই বেঁচে আছে এই আশাতেই ছুটে চলে যান জহির রায়হান। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হয়ে গেলেও সম্পূর্ণ দেশ কিন্তু তখনো শত্রুমুক্ত হয়নি। বিশেষ করে মিরপুরের এলাকাগুলো বিহারি অধ্যুষিত হওয়ায় স্থানীয় বিহারি এবং মুক্তিযুদ্ধে বাঙালিদের সহায়তা করা বিহারিদের মধ্যে এক ধরণের আঁতাত হয় ঐ এলাকাটিতে। ধারণা করা হয় তার পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি ষড়যন্ত্রের শিকার হন জহির রায়হান।
সাংবাদিক জুলফিকার আলী মানিক ‘ভোরের কাগজ’ পত্রিকায় ১৯৯৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর জহির রায়হানের অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে একটি অনুসন্ধানীমূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। একই বছর জহির রায়হানের ছেলে অনল রায়হান ‘সাপ্তাহিক ২০০০’ এর ১৩ আগস্ট সংখ্যার জন্য একটি কভার স্টোরি লেখেন যার শিরোনাম ছিল ‘পিতার অস্থির সন্ধানে’। এই প্রতিবেদন অনুযায়ী, অনল রায়হান খুঁজে বের করেন একজন প্রত্যক্ষদর্শীকে। এই প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন বাংলাদেশ আর্মির একজন সাবেক সৈনিক আমির হোসেইন। আমিরের ভাষ্যমতে, ক্যাপ্টেন হেলাল মুর্শিদ খানের নেতৃত্বে এক প্লাটুন সামরিক সৈন্যের সাথে মিরপুরের এক বাড়িতে যান জহির রায়হান। ভাইয়ের খোঁজে উপস্থিত একমাত্র পারিবারিক সদস্য হিসেবে সাথে রাখা হয় তাকে। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাড়িটিতে তারা পৌঁছানো মাত্র চারদিক থেকে গুলি বর্ষণ করে বিহারি মুসলিম শরণার্থীরা। স্বাধীনতার পর মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে সব অস্ত্র তখনো সংগ্রহ করতে পারেনি সদ্য স্বাধীন দেশটির সামরিক বাহিনী। কাজেই বিহারিদের কাছে লুণ্ঠিত বা অবৈধ অস্ত্রের কোনো অভাব ছিল না। আমির দেখেন কয়েক রাউন্ড গুলি ঝাঁঝরা করে দিয়ে যায় জহির রায়হানের শরীর। জুলফিকারের আলী মানিকের রিপোর্টেও একই কথা বলা হয়।

জহির রায়হানের অন্তর্ধান আজো এক রহস্য, banglatribune.com
ঘটনাস্থলে নিহত হন প্রায় ৪২ জন সামরিক সদস্য। বাকিরা মারাত্মক আহত অবস্থায় ফিরে আসেন। লোকবল কম থাকায় পাল্টা কোনো অপারেশনে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না বাংলাদেশি সামরিক সেনাদের পক্ষে। বিনা প্রস্তুতিতে এমন হামলায় কোনমতে প্রাণ নিয়ে বেঁচে আসা সৈনিকরা পরদিন পূর্ণ প্রস্তুতিতে আবার রেকি করেন ঐ মিরপুরের সেই বাড়িটি। কিন্তু সেখানে গিয়ে ৩-৪ জন সৈনিকের মৃতদেহ ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পাননি তারা। জহির রায়হানের কোনো চিহ্নও সেখানে ছিল না। তাই জহির রায়হান মারা গেছেন না তাকে কোথাও আটকে রাখা হয়েছে তা নিয়ে বিস্তর খোঁজাখুঁজি চলেছে দীর্ঘদিন যাবত। পরবর্তীতে অনল রায়হানের এই প্রতিবেদনে সবাই মোটামুটি নিশ্চিত হন যে জহির রায়হান আর বেঁচে নেই। তারপরও প্রতি বছর ৩০ জানুয়ারি দিনটিকে জহির রায়হানের অন্তর্ধান দিবস হিসেবে পালন করা হয়।
জহির রায়হান যখন মারা যান কিংবা হারিয়ে যান তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৩৬ বছর। এই স্বল্প সময়ে তিনি তাঁর সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনে যে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন, তাঁর উত্তরসূরী হিসেবে আমাদের নৈতিক দায়িত্ব সেই দেশ থেকে যাবতীয় পঙ্কিলতা দূর করে দেশটির ভাবমূর্তি বিশ্বদরবারে উজ্জ্বল করে তোলা।
Featured image: Team Roar