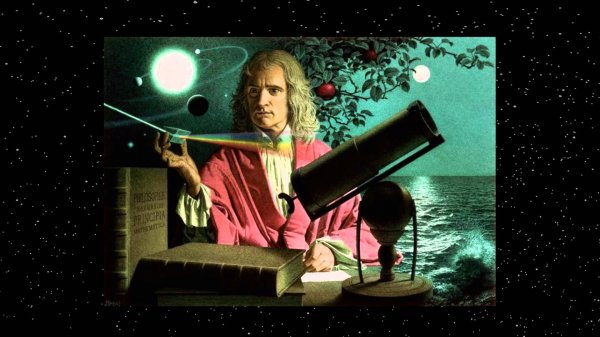ছেলেটির বয়স মাত্র ৫ বছর ৫ মাস। হঠাৎ বাবার মৃত্যু হলো। মা শশিমুখী দেবী শক্ত হাতে সংসারের হাল ধরলেও দুঃখ-দারিদ্র্য তাদের ছেড়ে গেল না। এরই মধ্যে পাঠশালার পাঠ শেষ করে ছেলেটি ভর্তি হলো স্কুলে। মা এবং ছোট তিন ভাইয়ের সংসারের ভার সামলানোর জন্য শুরু হলো ছোট ছেলেটির জীবন সংগ্রাম।
বাবা অম্বিকাচরণ ছিলেন গ্রামের জমিদারবাড়ির কূল পুরোহিত। ব্যস্ত থাকতেন যজন-যাজন ও সংস্কৃতিচর্চা নিয়ে। সংসারের চাপে বাবার এই যজন-যাজন রক্ষার জন্য ৯ বছর বয়সেই উপনয়ন হয় ছেলেটির। দুর্গম পথ পেরিয়ে যজমানের বাড়িতে পুরোহিতের কাজ সেরে বাড়ি ফিরে কোনোমতে খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার তাকে ছুটতে হতো স্কুলে। এভাবেই পড়া ও যজমানি দুটো কাজ একই সঙ্গে চলতে থাকে ছেলেটির। কষ্ট করে পড়াশোনা চালানোর পর, ছেলেটি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফরিদপুর জেলায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়।
সেদিনের সেই ছেলেটিই প্রকৃতিবিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য । জন্ম ১৮৯৫ সালের ১ আগস্ট। বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার লনসি গ্রামে। জীবনের অর্ধেকের বেশি সময় তিনি ব্যয় করেছেন কীটপতঙ্গ এবং গাছপালা নিয়ে গবেষণা করে। আজীবন চেষ্টা করেছেল সহজভাবে মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে বিজ্ঞানকে সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে।

প্রকৃতিবিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য; Source: bigyan.org.in
শিক্ষকতা
ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর গোপালচন্দ্র ভর্তি হলেন ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে। এরই মধ্যে চারদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বাজতে শুরু করে। যুদ্ধে প্রভাবে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে গোপালচন্দ্রের কলেজে পড়া অর্ধসমাপ্ত থেকে গেল। ফরিদপুর জেলায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে ম্যাট্রিক পাস করায় মেধাবী গোপাল চন্দ্র একটি চাকরি জুটিয়ে ফেললেন। নিজ গ্রামের এক উচ্চ বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষকতার চাকরি পেলেন। সেখানে ১৯১৫ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত ৪ বছর শিক্ষকতা করেন।
স্কুলে পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে ঘুরে বেড়াতেন বনে-জঙ্গলে। নিবিষ্ট মনে লক্ষ্য করতেন কীটপতঙ্গের গতিবিধি। গাছপালা নিয়ে করতেন নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। অজানাকে জানার এই আগ্রহই তাকে বিজ্ঞান সাধনায় অনুপ্রাণিত করেছিল। তাই তাকে বলা হয় স্বভাববিজ্ঞানী।
জগদীশ চন্দ্রের সাথে পরিচয়
গোপালচন্দ্রের সাথে অদ্ভুতভাবে যোগাযোগ ঘটে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর। কৌতূহলবশত গোপালচন্দ্র এক বৃষ্টিঝরা সন্ধ্যায় গ্রামের পাঁচির মার ভিটের ভৌতিক আলোর রহস্য ভেদ করতে চললেন। ঝোপঝাড়ের মধ্যে পাঁচির মায়ের ভিটেতে প্রায়ই আগুন জ্বলতে দেখে গ্রামবাসীরা রীতিমতো ভয় পেতো। টিপটিপে বৃষ্টির মধ্যে গোপালচন্দ্র একদিন সেখানে গেলেন। চারপাশে বড়-বড় গাছের মাথায় জমাট বাঁধা অন্ধকার, মাঝেমাঝে ছোট ছোট ঝোপ, আলোটা বের হচ্ছে সেখান থেকেই, মনে হয় মাঝে মাঝে দপ করে জ্বলে উঠেই নিভে যাচ্ছে।
কাছে যেতেই দেখা গেল যেন গনগনে আগুনের একটা কুণ্ডু। কিন্তু আলোটা স্নিগ্ধ নীলাভ, তাতে চতুর্দিক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। একটা কাটা গাছের ভেজা গুঁড়ি থেকেই আলোটা বের হচ্ছিল। গুঁড়িটা জ্বলজ্বলে এক অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়েছিল। আর তার ঠিক পাশে একটা কচুগাছের পাতা হাওয়ায় তার ওপর এমনভাবে হেলে পড়ছিল যে, দূর থেকে মনে হচ্ছিল আলোটা জ্বলছে, নিভছে। এ দৃশ্য কিন্তু দিনে দেখা যেত না। কিছুদিন পর এক রাত্রে বড় একটা পুকুরের পাশের রাস্তার ধারে গোপালচন্দ্র একই দৃশ্য দেখলেন। সেই আলোর কিছুটা তুলে এনে দেখেন কিছু ভেজা লতাগুল্ম থেকে আলোটা বের হচ্ছে।
ভেজা পচা গাছপালার এই আলোর বিকিরণ সম্বন্ধে গোপালচন্দ্র সেই সময়ের বিখ্যাত বাংলা মাসিক প্রবাসীতে লেখা পাঠান (১৩২৬ বঙ্গাব্দ), যা অচিরেই জগদীশ চন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাসের সহায়তায় গোপালচন্দ্রকে ডেকে পাঠালেন বসু বিজ্ঞান মন্দিরে। ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিজ্ঞানাচার্যের ডাকে সেখানে শুরু হলো গোপালচন্দ্রের গবেষণা।

আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু; Source: siliconeer.com
কীটপতঙ্গ নিয়ে গবেষণার সূত্রপাত
গোপালচন্দ্র প্রথমদিকে উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। গাছের কাণ্ডের স্থায়িত্ব নিয়ে গবেষণার ওপর ভিত্তি করে ১৯৩২ সালে প্রকাশিত হয় তার প্রথম গবেষণাপত্র। এরপর নিয়মিতভাবে জৈব আলো এবং উদ্ভিদবিদ্যার ওপর বিভিন্ন নিবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে। তবে পরবর্তীতে তার সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয় কীটপতঙ্গের গতিবিধির উপর।
তিনি ছিলেন প্রচারবিমুখ। কুমোরে পোকা সম্পর্কে তার গবেষণালব্ধ তথ্য প্রকাশের সময়টিও তিনি লিখে রাখেননি। মানুষের মতো পতঙ্গরাও বাচ্চা চুরি করে, এ এক অভিনব ঘটনা, জানা যায় গোপালচন্দ্রের গবেষণা থেকে। তার ‘ভীমরুলের রাহাজানি’ পড়লে জানা যায়, কীভাবে দৈহিক শক্তি ও দুষ্টবুদ্ধি নিয়ে কয়েকটি ভীমরুল শত-শত বোলতার সামনে থেকে বাচ্চা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। দিনের পর দিন সম্ভাব্য বিপদ তুচ্ছ করে পোকামাকড়দের আচরণ লক্ষ্য করতেন এই বিজ্ঞানী।
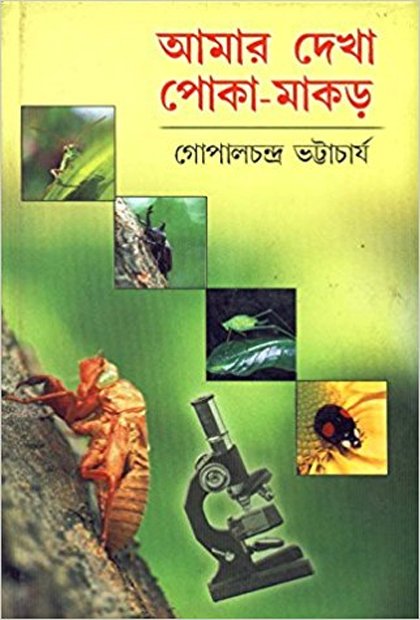
বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র রচিত বই আমার দেখা পোকা-মাকড়; Source: Amazon.com
পিঁপড়ের ‘ব্লিৎসক্রিগ’ সম্বন্ধে নানা তথ্য প্রকাশ করে বিজ্ঞানী গোয়েটস খ্যাতিলাভ করেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রকৃত প্রচারের অভাবে ওই একই বিষয় নিয়ে গবেষণা করলেও বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্রের কথা জানে খুব কম মানুষ। ‘ক্রিগ’ অর্থাৎ, ‘যুদ্ধক্ষেত্রে ঝটিকা বাহিনীর দুর্ধর্ষ আক্রমণ’, ব্লিৎস শুধু মানুষই নয়, প্রাণী-পতঙ্গেরাও করে থাকে, এই বিষয়টিও এই প্রকৃতিবিজ্ঞানীর গবেষণা থেকে বাদ যায়নি। তার সুদীর্ঘ অধ্যবসায় এই সত্য উদঘাটন করেছিল যে, ডানাবিহীন লাল রঙের নালসো শ্রমিক পিঁপড়েরা যুদ্ধের সময় যেমন সৈনিকের কাজ করে, তেমনই রানী ও পুরুষের সংসারের যাবতীয় কাজও তাদের করতে হয়।
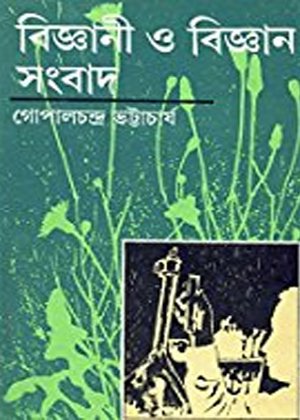
বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র রচিত বই বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান সংবাদ; Source: amazon.in
সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা
গোপালচন্দ্র পরাধীন দেশের মুক্তিকামী বিপ্লবীদের প্রতি একনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি গুপ্ত সমিতির জন্য নানা বিস্ফোরক পদার্থের ফর্মূলা সরবরাহ করতেন এবং পরোক্ষভাবে নানা উপায়ে তাদের সাহায্য করতেন। এছাড়াও তিনি গ্রামের অবহেলিত মানুষদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য স্থাপন করেছিলেন ‘কমল কুটির’। বিনা বেতনে সেখানে লেখাপড়ার সাথে মেয়েদের শেখানো হতো হাতের কাজ। সামাজিক কুসংস্কার ও জাতপাতের বিরুদ্ধেও ছিলেন সবসময় প্রতিবাদমুখর।

স্বভাববিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য; Source: Veethi
বিজ্ঞান সম্পর্কিত রচনা
উদ্ভিদ আর কীটপতঙ্গ নিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে গবেষণার জন্য সেই সময়ে এই উপমহাদেশে গোপালচন্দ্র ছিলেন পথিকৃত। ‘উদ্ভিদের রাহাজানি’, ‘গাছের আলো’, ‘শিকারি গাছের কথা’ ইত্যাদি তার উদ্ভিদ সম্বন্ধে লেখা উল্লেখযোগ্য বই। এছাড়াও ‘বাংলার গাছপালা’, ‘বিজ্ঞানের আকস্মিক আবিষ্কার’ , ‘বিজ্ঞান অমনিবাস’, ‘পশুপাখি কীটপতঙ্গ’, ‘বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান সংবাদ’ ইত্যাদি বইগুলো তার আশ্চর্য গবেষণার সাক্ষ্য বহন করে। তার ভাবনার জগতে শিশুরা অনেকটা জায়গা জুড়ে ছিল।
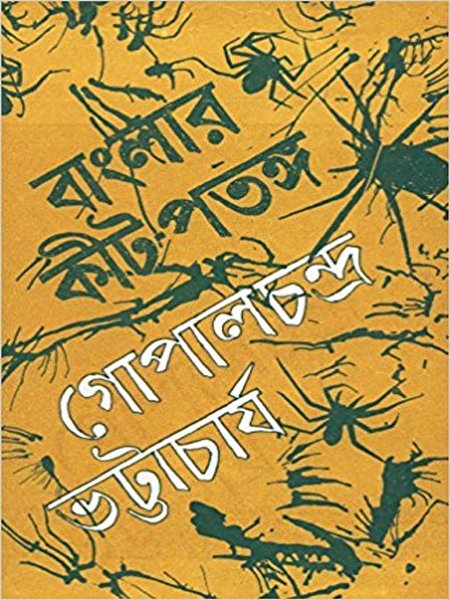
বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র রচিত বই বাংলার কীট পতঙ্গ; Source: Amazon.in
ছোটদের মেধা আর মননকে শাণিত করবার জন্য বিভিন্ন স্বাদের গ্রন্থ রচনা করেছেন তিনি। এগুলো আজও মূল্যবান আর প্রশংসনীয়। শিশুদের জন্য তিনি লিখেছেন এক মজার বই, ‘করে দেখ’। বাংলায় জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখায় দক্ষ তো ছিলেনই পাশাপাশি ইংরেজিতেও তিনি লিখেছেন বহু প্রবন্ধ। ২২টির মতো নিবন্ধ তার ইংরেজী বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশ পায়। তিনি দীর্ঘদিন অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে মাসিক বিজ্ঞান পত্রিকা ‘জ্ঞান ও বিজ্ঞান’-এর সম্পাদনা করেছিলেন। বাংলার সেসময়ের স্বনামধন্য বিজ্ঞান লেখকেরা এই পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন।

বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র রচিত বই করে দেখ; Source: readbengalibooks
কাজের স্বীকৃতি
অসাধারণ এই প্রকৃতিবিজ্ঞানী সম্মানিত হয়েছেন বহুবার। ১৯৭৪ সালে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু ফলক পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৭৪ সালের ২২ সেপ্টেম্বর তাকে দেওয়া হয় জাতীয় সংবর্ধনা। কীটপতঙ্গের জীবনযাত্রা সম্পর্কে লেখা তার বই ‘বাংলার কীটপতঙ্গ’ ১৯৭৫ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করে। ১৯৭৯ সালে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের পক্ষ থেকে তাকে জুবিলি মেডেল প্রদান করা হয়। ১৯৮০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ডিএসসি ডিগ্রি প্রদান করে। ১৯৮১ সালের ৮ এপ্রিল কলকাতায় তার বাসভবনে এই স্বভাববিজ্ঞানী লোকান্তরিত হন।
ফিচার ইমেজ: youtube.com