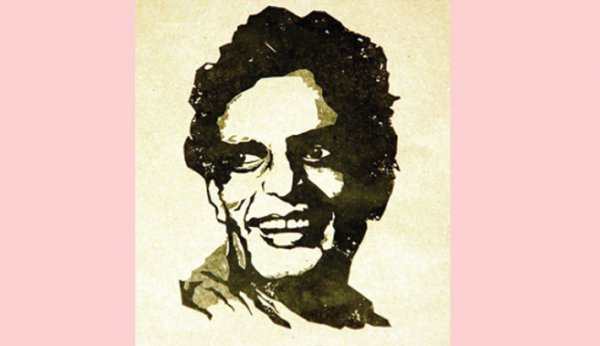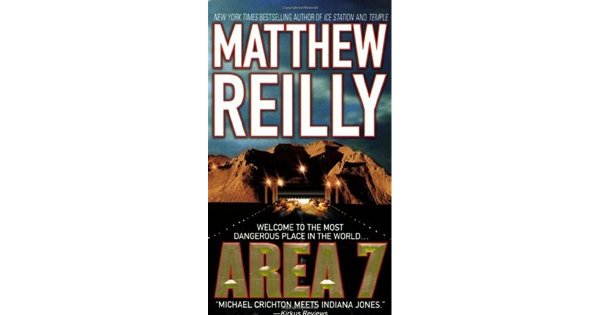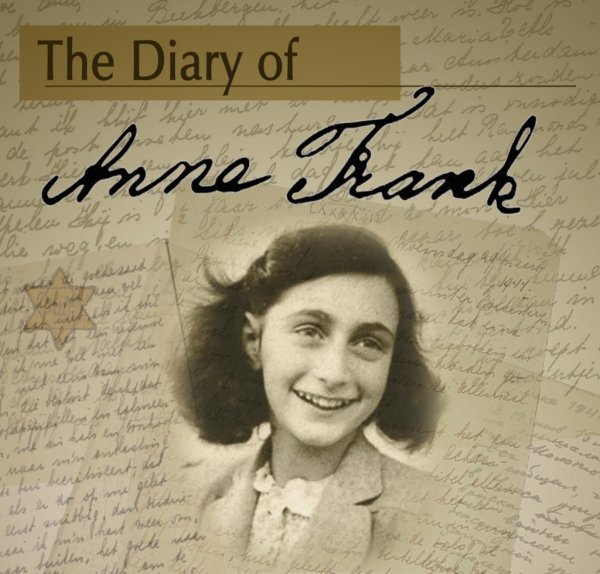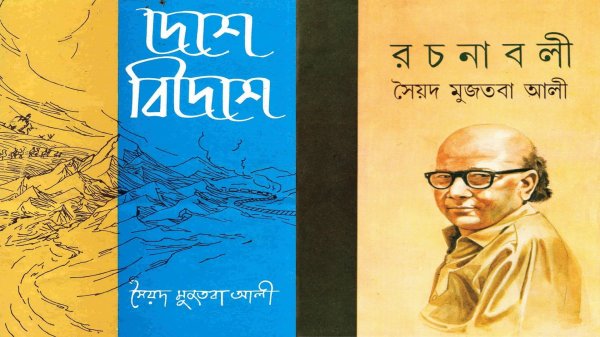বিস্তৃত অরণ্য কিংবা সীমাহীন উন্মুক্ত প্রান্তর, সেখানে কাতারে কাতারে জন্তুর দল নিজেদের জগৎ নিয়ে ব্যস্ত। তারা ফিরেও তাকায় না উৎসুক মানুষের দিকে। এমন দৃশ্য কেবল একটি মহাদেশেই সম্ভব। যে মহাদেশে নীল নদের উৎস খুঁজতে ছুটে বেড়িয়েছেন স্কটিশ ডাক্তার ডেভিড লিভিংস্টোন। আরেক অভিযাত্রী হেনরি স্ট্যানলির অনুরোধও যাকে সভ্য জগতে ফেরাতে পারেনি। সেই মহাদেশের নাম আফ্রিকা। সভ্য ইউরোপীয়রা যাকে বলত অন্ধকারের মহাদেশ, চিররহস্যময় মহাদেশ। অবশেষে বিশুদ্ধ প্রকৃতির বুকে একদিন তারা পা রাখল। আফ্রিকার বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল ধ্বংস করে প্রান্তরে প্রান্তরে গড়ে উঠতে থাকল ইউরোপীয় ধাঁচের শহর। তৈরি হলো উপনিবেশ।
উপনিবেশ গড়ে ওঠার পর থেকেই সমগ্র বিশ্বের কাছে একটু একটু করে পরিচিত হতে থাকে জঙ্গলাকীর্ণ মহাদেশটি। আর উপনিবেশ গড়ে তোলার সাথে সাথেই শুরু হয় চূড়ান্ত ঔপনিবেশিক শোষণ। আফ্রিকার কালো মানুষদের পরিণত করা হয় ক্রীতদাসে। অসহায় মানুষগুলোর উপর নেমে আসে মধ্যযুগীয় বর্বরতা। আফ্রিকার প্রাকৃতিক সম্পদকে নিজেদের কুক্ষিগত করে নেয় সভ্য শক্তি। আর এর সাথে যুক্ত হয় ট্রফির লোভে বড় বড় জানোয়ারকে গুলির ঘায়ে পায়ের নীচে এনে ফেলার প্রতিযোগিতা।
তাই সমকালীন ইউরোপীয় সাহিত্যে আফ্রিকাকে দেখানো হয়েছে জয়ী ইউরোপীয়দের চোখ দিয়েই। সেখানে আদিবাসী মানুষকে জংলি, অসভ্য ইত্যাদি নানা বিশেষণে সম্বোধন করেছেন শ্বেতাঙ্গ লেখকগণ। গাছের উপর থেকে রাইফেলের বুলেটে সিংহের কপাল ফুঁড়ে দেওয়ার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে বীর-রসের প্রাচুর্যে।
এমনকি আফ্রিকার উপর লেখা সর্বাধিক জনপ্রিয় উপন্যাস এডগার রাইস বারোজের ‘টারজান অব দ্য এপ্স’-এর সম্পর্কেও সমালোচকগণ বলেছেন, টারজানের গল্প হলো মার্কিন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখানো আফ্রিকান বর্বরতা। টারজানের (যে কিনা বানরদের কাছে বড় হয়েছিল) নিজ-সংস্কৃতি রক্ষার্থে কালো মানুষদের অপদস্ত করা বা হত্যা করার মধ্যেও সেই সভ্যতাগর্বী ভাবটিই প্রকাশিত হয়।
পশ্চিমা দুনিয়ার এই একমুখী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বেরিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক আফ্রিকাকে সেলুলয়েডের পর্দায় তুলে ধরলেন দক্ষিণ আফ্রিকান পরিচালক জেকোবাস জোহানেস আইস। সংক্ষেপে জ্যামি আইস। সিনেমার নাম ‘দ্য গডস মাস্ট বি ক্রেজি’।
সিনেমার শুরুই হয় কালাহারি মরুভূমির রুক্ষ সৌন্দর্যের দৃশ্য দিয়ে। হলদেটে তৃণভূমি, তার মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা বাওবাব, অ্যাকাসিয়া গাছ। তার সাথে চলে কথকের বর্ণনা। বছরে ন’মাস এখানে বিরাজ করে শুষ্ক আবহাওয়া। সর্বত্র জলের ধারা শুকিয়ে যায়। তখন এই লোভনীয় ঘাসবন ছেড়ে পালে পালে তৃণভোজীদের দল ধীরে ধীরে অন্যদিকে সরে যেতে থাকে। জেব্রা, উইল্ডবিস্ট, হরিণ, সকলেই চলে যায় এই সুন্দর চারণভূমি ছেড়ে। একমাত্র যারা সারাবছর এই শুকনো জায়গাতেও দিব্যি মানিয়ে নিয়ে বেঁচে থাকে, তারা হলো কালাহারির সান বা বুশম্যান আদিবাসীর মানুষজন।
বুশম্যানদের জীবনযাত্রা বড় সহজ। তারা একটি পরিবার একটি ছোট কুঁড়েঘর বানিয়ে বাস করে। ক্বচিৎ অন্য একটি পৃথক পরিবারের সাথে দেখা হয়। তাদের মধ্যে হিংসা নেই, হানাহানি নেই, লোভ নেই, আইন নেই। জীবনধারণের তীব্র প্রতিকূলতাকে তারা যেন আপন করে নিয়েছে, তাই কোনোকিছুর অভাবকে তারা অভাব বলে মনেই করে না। বরং তারা তাদের ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ, তিনি তাদের এতকিছু দিয়েছেন বলে। আমাদের সভ্যচোখে হয়তো তাদের সামান্য পরিমাণকে নিতান্ত অস্বাভাবিক মনে হবে, কিন্তু তাদের সম্পর্কে এইটেই সবচেয়ে বড় সত্যি, যে তারা নিজেদের জীবনে কাঠ এবং প্রাণীর হাড়ের চেয়ে শক্ত কোনো জিনিস দেখেনি, এমনকি পাথরও নয়।
তাদের শিকার করার মধ্যেও আছে বড় এক পবিত্রতা। তারা গাছের ডালকে ছেঁটে সূচাগ্র করে নেয়, তারপর তার ডগায় বিষ মাখিয়ে কোনো তৃণভোজীকে ঘায়েল করে। তার মৃত্যুর পর শিকারী বুশম্যান মানুষটি হাঁটু গেড়ে বসে মৃত প্রাণীটির আত্মার শান্তি কামনা করে, এবং তাকে যে তার পরিবারের মানুষের খাদ্যের প্রয়োজনে হত্যা করতে হলো, সে কথা জানিয়ে সে মৃত আত্মার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। ‘সভ্য’ মানুষের পশুর কসাইখানা বানানোর পেশাদারিত্বকে যেন বড় লজ্জায় ফেলে দেয় ‘অসভ্য’ বুশম্যানের এই সারল্য।

তারা জল সংগ্রহও করে বিচিত্র উপায়ে। রাতে গাছের পাতা মাটিতে ফেলে রেখে দেয়। রাতে সেই পাতায় শিশির জমা হয়। ওই একফোঁটা শিশিরই তাদের কাছে আশীর্বাদ। এছাড়া কোনো ঘাস বা কোনো গাছের ফাঁকে জল জমা হয়ে থাকে, সেই জ্ঞান তারা আয়ত্ত করেছে সহজাত প্রকৃতি-শিক্ষার মাধ্যমে।
মরুভূমির দৃশ্য থেকে এরপর সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরা চলছে কয়েকশো মাইল দূরের ধাবমান শহুরে জীবনযাত্রার দিকে। যেখানে কেবলই গতি, ঘড়ি ধরে এগনোর প্রতিযোগিতা। এখানে কথকের মুখে শোনা যাচ্ছে একটি কালোত্তীর্ণ সংলাপ-‘সভ্য মানুষ প্রকৃতির সাথে একাত্ম হতে অস্বীকার করে, বরং সে প্রকৃতিকে নিজের মতো করে বদলে নেয়।’ এই দৃশ্যটিতে সভ্যজগতের সীমাবদ্ধতাকে খুব সরাসরি কথকের মুখ দিয়ে বলিয়ে নিচ্ছেন পরিচালক।
সভ্যতা অর্থে শুধুই বড় বড় শহর, রাস্তা, গাড়ির চলাচল, ইলেক্ট্রিক লাইনের জঙ্গল। বড় বড় যন্ত্রপাতির দ্বারা কেবলই নিজের জীবনকে সহজ থেকে সহজতর করে তুলছে শহুরে মানুষ। কিন্তু তার সমস্যা হলো, সে কোথাও থামতে জানে না। ফলে জীবনধারণকে যত সহজ করে তুলতে চায়, ততই জটিলতা বৃদ্ধি পায়। বনবাসী শিশুরা যেখানে অতি অল্পেই শিখে নেয় জীবনধারণের কৌশল, সেখানে সভ্য শিশুদের অন্তত পনেরো বছর আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হয় এই জটিল পৃথিবীতে সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে, বা বলা ভালো, উন্নতির উদ্দেশ্যে। সভ্যজগতের কৃত্রিমতার উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গ এখানে খুব স্পষ্ট।
এই দুই জগতের মধ্যে হঠাৎ একদিন মোলাকাত হয়ে গেল। সৌজন্যে, একটি খালি কোকাকোলার বোতল। একটি টু-সিটার প্লেন থেকে ফেলে দিয়েছিলেন পাইলট। বালির উপর পড়ার ফলে কাঁচটি ভাঙেনি। এমনিতেও প্লেনের আওয়াজকে বুশম্যান আদিবাসীর মানুষজন ভাবে ঈশ্বরের ক্রোধের প্রকাশ হিসেবে। জেট প্লেনের ধোঁয়ার রেখাটিকে তারা ভাবে, ঈশ্বরের এঁকে দেওয়া চিহ্ন। তাই কোকাকোলার বোতলটিকে দেখে তারা ভাবল, উপর থেকে ঈশ্বরই বোধহয় তাদের কাছে উপহার হিসেবে পাঠিয়েছেন। এই সরল বিশ্বাস থেকে একটি সম্পূর্ণ অচেনা দ্রব্যকে ব্যবহার করতে তাদের বাধল না।
আচমকাই তারা আবিষ্কার করল, এই লম্বাটে অদ্ভুতদর্শন জিনিসটির দ্বারা প্রয়োজনীয় অনেক কাজই হতে পারে। নরম কাঠ গুঁড়ো করা, সাপের খোলসকে ঘষে ঘষে মসৃণ করা, কিংবা খাদ্যদ্রব্য বাটা। এছাড়া, নানা বিনোদনমূলক কাজও ঘটছে বস্তুটি ব্যবহার করে। বাচ্চারা সেটিকে নিয়ে লোফালুফি খেলছে, সেটির মধ্যে ফুঁ দিয়ে সুর উৎপন্ন করা যাচ্ছে, আবার নকশা আঁকাও সম্ভব। কিন্তু সমস্যা হলো, এমন জরুরী একটি জিনিস ভগবান কেবল একটিই পাঠালেন।
দেখা যাচ্ছে, কীভাবে একটি জিনিসের প্রয়োজনীয়তা ধীরে ধীরে চাহিদায় পরিণত হচ্ছে। এখান থেকে আসলে তাদের মধ্যে জন্ম নিচ্ছে স্বার্থবোধ, অনর্থক প্রতিযোগিতা এবং সর্বোপরি রেষারেষি। কিন্তু যেহেতু তারা সহজাত ভদ্রলোক, তাই সকলে মিলে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হচ্ছে যে, এই দানটিকে তারা গ্রহণ করবে না। তাদের ধারণা, ঈশ্বর তাদের পরীক্ষা নিচ্ছেন। অবশেষে ঠিক হয়, তাদের নেতা কাই এই লম্বাটে অভিশাপটিকে পৃথিবীর একদম শেষ প্রান্তে গিয়ে নিক্ষেপ করে দিয়ে আসবে।

গল্পের চরিত্র কাই কর্তৃক এই পৃথিবীর শেষ প্রান্ত অন্বেষণের অভিযান শুরু হচ্ছে যখন তখন দুটি সমান্তরাল ঘটনা ঘটছে ওই একই দেশে। দেশটি বতসোয়ানা। দুটি ঘটনাই সভ্যজগতের। এক ঘটনার চরিত্র হচ্ছে একটি গ্রামের নতুন স্কুলশিক্ষিকা কেট থম্পসন, প্রাণীতত্ত্ববিদ অ্যান্ড্রু স্টেইন, স্টেইনের সহকারী এম’পুডি এবং ওয়াইল্ড সাফারি গাইড জ্যাক হাইন্ড। অন্য ঘটনাটিতে রয়েছে দেশের সরকারপক্ষ ও বিদ্রোহী স্যাম বোহার নেতৃত্বাধীন গেরিলাবাহিনী।

নানা ঘটনার পর কাইয়ের সাথে দেখা হয় সভ্য জগতের মানুষের। কাই তাদের কাছে বোতলটি ফিরিয়ে দিতে চায়। তার জীবনে এই প্রথমবার সভ্য মানুষ দেখল, এবং তাদের দেখে তার কুৎসিত বলেই মনে হয়।
সিনেমার একপর্যায়ে দেখা যাচ্ছে, খিদে পাওয়ায় একজন ছাগলপালকের একটি ছাগলকে তার নিজস্ব শিকার পদ্ধতি ব্যবহার করে মেরে ফেলেছে কাই। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসছে আইন রক্ষক। ছাগল মারার অপরাধে জেল হচ্ছে তার। সরল কাইয়ের আসলে ধারণা নেই, এই ছাগলটির মালিক তার ঈশ্বর নন, এর মালিক সভ্যজগতের উর্দিধারীরা।
জেলে কাইকে পোশাক পরে থাকতে হয়, মুক্ত জগতের মানুষ সেখানে আবদ্ধ। স্টেইনের সহকারী এম’পুডি আবার দু’ধরনের জগতের সাথেই সমান পরিচিত। তিনি বুশম্যান ভাষাও জানেন। তার সাহায্য নিয়ে কাইকে আইনমুক্ত করে আনেন স্টেইন। কাই নিযুক্ত হয় স্টেইনের আরেক সহকারী হিসেবে। এর মধ্যেই কেট গ্রামের যে মিশনারি স্কুলটিতে শিক্ষকতা করছিলেন, সেখানে স্যাম বোহার বাহিনী এসে কেট-সহ সকল শিক্ষার্থীকে পণবন্দি করে নিয়ে যায়। উদ্দেশ্য, সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে নিজেদের দাবী আদায় করা।
পাহাড়-ঘেরা জঙ্গলের এক প্রান্তে এসে বাচ্চারা তখন সকলেই প্রায় ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। স্যাম বোহার এই নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান কেট। সকলে খাবার খেতে বসে। পাহাড়ের মাথাতেই এক জায়গায় ফিল্ডওয়ার্ক করছিলেন স্টেইনরা। দুটি ঘটনা-প্রবাহ এই জায়গায় এসে মিলছে তখন। কাইয়ের বুদ্ধিমত্তায় ভর করে স্যাম বোহার বাহিনীকে ঘায়েল করেন স্টেইন ও এম’পুডি। কাইও বিদায় নেয় তাদের কাছ থেকে। অবশেষে সে খুঁজে পায় পৃথিবীর শেষ প্রান্তর। একটি খাদের প্রান্তে এসে পৌঁছায় সে। চারিদিকে সাদা মেঘের ভেলার উপর ছুঁড়ে দেয় বোতলটি। ভারমুক্ত সে, অভিশাপমুক্ত তার পরিবার। আসলে শেষ প্রান্তটি হচ্ছে গ্লাইড নদীখাতের গড’স উইন্ডো ক্লিফ।

‘দ্য গডস মাস্ট বি ক্রেজি’-র পরিবেশনার মেজাজটি হালকা হলেও এখানে এই সভ্য-অসভ্যের দ্বন্দ্বটিকে খুব ক্ষুরধারভাবে দেখাতে পেরেছেন জ্যামি আইস। মনে রাখতে হবে, সিনেমাটি যখন মুক্তি পেয়েছে, অর্থাৎ ১৯৮১ সালে, তখন দক্ষিণ আফ্রিকায় তীব্র বর্ণবৈষম্য বিদ্যমান। কাইয়ের ভূমিকায় যিনি অভিনয় করেছিলেন, তার নাম ছিল কাও কোমা। তিনি নিজে সান আদিবাসীর মানুষ ছিলেন। শোনা যায়, অভিনয়ের পারিশ্রমিক-স্বরূপ প্রথমদিকে পাওয়া তিনশো ডলার স্রেফ হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছিলেন কাও কোমা। কারণ, তাদের সমাজে কাগুজে মুদ্রার কোনো মূল্যই নেই।
সুস্থির আদিবাসী সমাজে যেখানে রঙের কোনো বৈষম্য নেই, যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আমরা-ওরা নেই, সেখানে সভ্য সমাজে বর্ণ সচেতনতা, অসুস্থ প্রতিযোগিতা, আইনের মারপ্যাঁচ, বিদ্রোহের আগুন সবকিছুই কেমন যেন বড় অস্থিরতাকে চিহ্নিত করে। আমাদের দাঁড় করিয়ে দেয় এই প্রশ্নের মুখোমুখি, সভ্য হওয়ার অর্থ কি তাহলে শুধুই বৈষম্য? আসলে মানুষের সভ্যতা তো তার পোশাকে-আশাকে বা জীবনধারণে নয়, সভ্যতার আসল নির্যাস লুকিয়ে আছে তার বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, ব্যবহারে।
শিক্ষা মানে তো কেবল পুঁথিবিদ্যা নয়, শিক্ষা অর্থে জ্ঞানার্জন। আদিবাসী মানুষরা নিজেদের মতো করে শিক্ষিত, জঙ্গলকে তারা অনেক নিখুঁতভাবে চেনে, জানোয়ারের সম্পর্কে তাদের জ্ঞান সভ্য মানুষে পুঁথিপড়া বিদ্যার চেয়ে অনেক বেশি সমৃদ্ধ। সিনেমার একটি দৃশ্যে দেখা যায়, কেট ওয়ার্টহগ (বুনো শুয়োর) বা গণ্ডারের নামই শোনেননি, এবং সেজন্য স্টেইনকে মিছিমিছি সন্দেহ করেন।
ফিল্ডওয়ার্ক করার কারণে স্টেইন সেখানে জঙ্গল নিয়ে অনেক বেশি জ্ঞানী, তাকে আদিবাসীদের সঙ্গে তাদের ভাষায় কথাও বলতে দেখা যায়। কেট গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা করতে যাচ্ছেন, কারণ তিনি শুনেছেন গ্রামের স্কুলগুলোয় শিক্ষকের অভাব। কেটের জ্ঞান অনেকবেশি বইপত্র এবং গণমাধ্যম-নির্ভর। ‘স্টাডিমুজ’ ডেটাবেসে এই চলচ্চিত্রের আলোচনা করতে গিয়ে পশ্চিমা দুনিয়ার এই পুঁথিগত বিদ্যার ক্ষেত্রটিকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে ‘আ ব্রডার ম্যাক্রো ওয়ার্ল্ড’।


স্যাম বোহার চরিত্রটিকে বিপ্লবী চে গেভারার সাথে তুলনা করেছেন সমালোচক গ্রাহাম বডেন। গোটা ছবি জুড়েই দেখা গেছে, গাড়ি এসে ধাক্কা মেরে দিচ্ছে চেকপয়েন্টে, স্টেইনের জিপে দরজা ভাঙা, ব্রেক নেই, সামনের কাচ নেই, এরকম আরও অনেক মজাদার কোলাজ। আসলে আমাদের অতিরিক্ত যন্ত্র-নির্ভরতার অন্তঃসারশূন্যতাকেই যেন দেখাতে চাইছেন জ্যামি।
তবে বডেনের মতে, এই প্রয়াসটি কিন্তু কোনোভাবেই দক্ষিণ আফ্রিকার সমকালীন সময়কে তুলে ধরছে না। বডেনের যুক্তি হল, বর্ণবৈষম্য দূর করতে যে বিশ্ব-রাজনীতির তীব্র প্রভাব পড়েছিল, সেই অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল গণমাধ্যমের অভাবনীয় উন্নতির ফলেই, যা কিনা প্রযুক্তির উন্নতিকেই নির্দেশ করে। তবে বডেন যাই বলুন, ‘কালো মানুষের’ আফ্রিকাকে তাদের চোখ দিয়ে দেখানোর কাজটিতে আইস পুরোপুরি সফল।