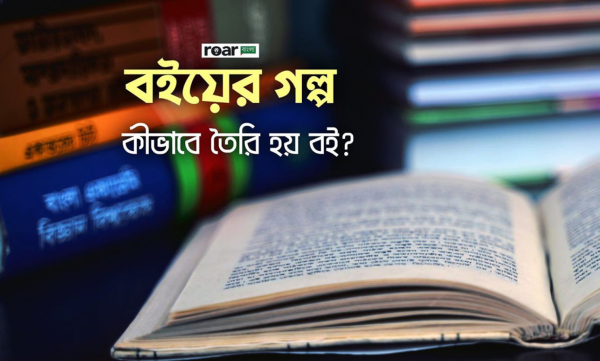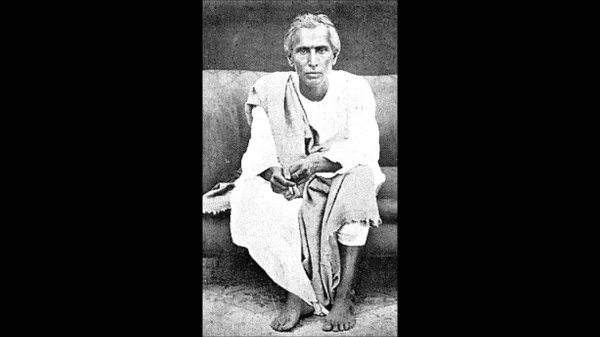বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস নিয়ে কাজ করেছেন এমন লেখকদের সংখ্যা খুব বেশি না হলেও একেবারে হাতে গোনার মতনও নয়। তবে এখানে হাস্যরসের ধরনটা নিয়ে একটুখানি গোল আছে। কোনো কোনো লেখক হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন নিছকই হাস্যরস সৃষ্টির লক্ষ্যে, হাস্যরস সৃষ্টির জন্য তারা সস্তা চটুলতা কিংবা অশ্লীলতার পথ অবলম্বনেও পিছপা হননি।
অন্যদিকে কেউ কেউ এই হাস্যরসকে নিয়ে গেছেন একেবারে শিল্পের পর্যায়ে। এসব হাস্যরসে লেখকেরা শব্দের জাদুকরী খেলায় একদিকে যেমন পাঠককে হাসিয়েছেন, আরেকদিকে তাদের মনোজগতে খুলে দিয়েছেন নতুন দ্বার। শিবরাম চক্রবর্তী এই দলেরই একজন। এপার বাংলা আর ওপার বাংলা মিলিয়ে আজ অব্দি যত হাস্যরস সমৃদ্ধ সাহিত্য রচিত হয়েছে, তার মধ্যে শিবরামের লেখাগুলো এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে।

শিবরামের জন্ম পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায়, ১৯০৩ সালের ১৩ ডিসেম্বর। যদিও তার শৈশব ও কৈশোরের অধিকাংশ সময়ই কেটেছে পাহাড়পুর আর চাঁচলে। শিবরামের মা শিবরাণী দেবী মালদহের চাঁচলের জমিদার পরিবারের মেয়ে ছিলেন। বাবা শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী ছিলেন কিছুটা সন্ন্যাসী প্রকৃতির। প্রায়ই ভবঘুরের মতো নিরুদ্দেশ হয়ে যেতেন। শিবরামও বাবার এই স্বভাবের খানিকটা উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন করেছিলেন। মায়ের মাঝেও ছিলো আধ্যাত্মিকতার প্রচ্ছন্ন ছায়া। পার্থিব জীবনের প্রতি আকর্ষণ শিবরামের মা-বাবা কারোরই তেমন ছিলো না। তাই ছোটবেলা থেকেই বন্ধনহীন মুক্ত পরিবেশে বড় হয়েছিলেন শিবরাম। সুযোগ পেলেই উদ্দেশ্যহীন, গন্তব্যহীন হয়ে ঘরছাড়ার স্বভাবটা তখন থেকেই গড়ে উঠেছিলো। শিবরামের এই স্বভাবের প্রতিফলন আমরা দেখি তার কিশোর উপন্যাস ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’ (১৯৩৭)-তে।
শিবরাম ছিলেন খাপছাড়া আর আজন্ম বৈরাগ্যের সাধনাকারী এক মানুষ। অনেকটাই নিজের খেয়াল-খুশিতে চলতেন। ১৯১৯ সালে মালদহের সিদ্ধেশ্বরী ইনস্টিটিউট থেকে মেট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়ার কথা থাকলেও তা আর হয়ে ওঠেনি। কারণ ওই সময়ে তার দেখা হয় বিপ্লবী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সাথে। চিত্তরঞ্জন দাশ তখন স্ত্রী বাসন্তী দেবীর সাথে চাঁচলে এসেছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের সভা করতে। শিবরাম এতটাই আগ্রহী হলেন যে চিত্তরঞ্জন দাশের সাথে ফিরতি ট্রেনে চেপে বসলেন। স্বপ্ন কলকাতা যাবেন, স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেবেন।

কলকাতায় আসার পর বিপ্লবী বিপিনবিহারী বাবুর পরামর্শে শিবরাম কলকাতার ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন এর অধীনস্থ গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তনে ভর্তি হন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সে সময় সেই বিদ্যায়তনের প্রিন্সিপাল ছিলেন। দেশবন্ধুর সহযোগিতায় শিবরামের ফরবেস ম্যানসনে বিনে পয়সায় থাকা-খাওয়ার এবং নিয়মিত কিছু মাসোহারার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। প্রথম বেশ কিছুদিন ভালো কাটলেও শিবরামের বাউণ্ডুলে স্বভাবের কারণে এই অবস্থা আর বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কিছুদিনের মধ্যেই পড়াশোনা আর মেসের পাট চুকিয়ে তাকে আবারও রাস্তায় নামতে হয়। যদিও পরে দেশবন্ধুর প্রচেষ্টায় এই বিদ্যায়তন থেকেই এন্ট্রান্স পাশ করেন তিনি।
শিবরামের লেখালেখি সম্পর্কে খুব একটা প্রচার প্রসার হয়নি। এর পেছনে লেখকের খামখেয়ালিপনাই অধিকাংশে দায়ী। লেখালেখি সংরক্ষণ বা ছাপার খুব একটা আগ্রহ তার ছিলো না। শিবরামের লেখালেখি বা সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে যতটা জানা যায় তার চেয়েও কম জানা যায় ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে।
ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত অনাড়ম্বর এই মানুষটি লোকচক্ষুর আড়ালেই থাকতে বেশি ভালোবাসতেন। ভালোবাসতেন সাদাসিধে জীবনযাপন। খুব বেশি জামাকাপড় তার ছিলো না। শোনা যায়, এমনও নাকি বহুবার হয়েছে যে, শুধুমাত্র দু’খানা কাপড় ছিলো তার। একটিকে ধোপাবাড়ি দেওয়া হয়েছে বিধায় তাকে কোনো কারণে কাপড় বদল করতে হলে ধোপা বাড়িতে গিয়েই কাপড় বদলে আসতে হয়েছে।
শিবরাম ভালোবাসতেন তিনটি জিনিস। ভোজন, নিদ্রা আর সিনেমা। হাতে তার টাকা থাকতো না কখনোই। শোনা যায়, তিনি নাকি একই ঠিকানায় কাটিয়ে দিয়েছেন জীবনের ৬০টি বছর। শিবরামের নিজের ভাষায়, “মুক্তারামের মেসে, শুক্তারাম খেয়ে, তক্তারামে শুয়ে”। অনেকে বলেন, মুক্তারাম স্ট্রীটের এই বাড়িটিতে তিনি নাকি পাহাড়াদার হিসেবে এসেছিলেন, তারপর আমৃত্যু এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান।
তার ঘরটিও ছিলো দেখবার মতন। আসবাবপত্রের কোনো বালাই না থাকলেও অভাব ছিলোনা পুরনো কাগজ, অগোছালো জঞ্জাল আর আজেবাজে জিনিসের। এ সম্পর্কে বিখ্যাত লেখক শতদল গোস্বামী তার ‘১৩৪, মুক্তারাম স্ট্রীটের সেই রসিক লেখক’ শীর্ষক লেখায় জানান,
“বয়সের ভারে জরাজীর্ণ মেস-বাড়ি। বাড়িটা কবে তৈরি তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। কেউ বলে, মহারানি ভিক্টোরিয়ার মুখে ভাতের দিন, কেউ আবার অত দূর অতীতে যেতে চায় না; বলে, অসম্ভব! মুখে ভাতের দিনে নয়, গায়ে-হলুদের দিন। জরাজীর্ণ রেলিং আর ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে উপরতলায় উঠতে হবে। আহা হা হাঁচবেন না, হাঁচবেন না। শব্দদূষণের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া এক্ষুণি টের পাবেন। চুন-বালি-সুরকির পলকা পলেস্তারা আশীর্বাদের মতো ঝুরঝুর ঝরে পড়বে। এবার ধীরেসুস্থে উপরে উঠুন। ভেজানো দরজা ঠেলা দিন, ঘর। হোম। সুইট হোম। হোম নয়, রুম। শৈলেশ্বরের একক সোনার সংসার!”
শতদল গোস্বামীর সেই লেখা থেকে আরো জানা যায়, শিবরামের ঘরের সমস্ত দেয়াল জুড়ে ছিলো অজস্র আঁকিবুকি। অবশ্য শিবরামের যে চিত্রকলায়ও পারদর্শিতা ছিলো ব্যাপারটি কিন্তু তা নয়। দেয়ালে লেখা ছিলো অসংখ্য লোকের নাম আর তাদের যোগাযোগের ঠিকানা, ফোন নম্বর। নামগুলোর নিচে আবার লাল-নীল কালিতে দাগ দেওয়া। ওই দাগের রং দিয়েই নাকি বুঝতেন কে তার পাওনাদার আর তিনি কার কাছে টাকা পাবেন। খামখেয়ালিতে যদি খাতা হারিয়ে যায়, সেই ভয়েই নাকি এই ব্যবস্থা!
শিবরামের ভোজনরসিকতা নিয়ে খুব মজার কিছু ঘটনা জানা যায়। স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলে সবসময়ই ছিলেন পুলিশের নজরদারিতে। একবার এক পুলিশের দায়িত্ব পড়লো তাকে অনুসরণ করার। পুলিশের অভিযোগ, শিবরামকে ধাওয়া করতে গিয়ে তিনি মুটিয়ে গেছেন। তা কেমন করে হলো এসব? শিবরাম নাকি এখান থেকে ওখানে যান, আর হোটেল বা খাবার দোকান দেখলেই থেমে শিঙাড়া, রসগোল্লা, চপ-কাটলেট মুখরোচক যা পান খেতে বসে যান। এখন শিবরামকে ধাওয়া করতে গিয়ে তার পিছু পিছু হোটেলে গিয়ে তো খালি মুখে বসে থাকা যায় না। কিছু না কিছু অর্ডার করতে হয়। সেই করে খেতে খেতে পুলিশ অফিসার গেলেন মুটিয়ে। পুলিশ অফিসারের আফসোস, শিবরামের মতো লোকের পেছনে লাগার শিক্ষা তাকে পেতে হয়েছে গা ভর্তি মেদের পাহাড় জমিয়ে।

‘যুগান্তর’ পত্রিকার দায়িত্ব নেওয়ার সাথে সাথেই শিবরামের স্বদেশী মনোভাবের প্রতিফলন দেখা গেলো যুগান্তরের পাতায়, কলামে। রাজরোষে পড়তেও সময় লাগলো না। প্রথমে তাকে প্রেসিডেন্সি জেলে কারাবন্দী করা হলেও পরবর্তীতে বদলির আদেশ এলো। এবারের গন্তব্য বহরমপুর জেলখানা। বহরমপুরের জেলখানা একরকমের পাগলা গারদ বলেই শুনেছিলেন শিবরাম। বদলির আদেশ শুনে খানিকটা ভয় পেলেও যখন শুনলেন সেখানে কাজী নজরুল ইসলামের দেখা মিলবে, তখন তার সমস্ত ভয় উবে গেলো।
বহরমপুর গিয়ে শিবরামের মন আনন্দে ভরে গেলো। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর স্বভাবসুলভ চাপল্যে সবাইকে মাতিয়ে রাখেন। আর গান-বাজনা, আবৃত্তি তো আছেই। কিন্তু শিবরামের জন্য আরো একটি বিশেষ আকর্ষণীয় দিক ছিলো। আর তা হলো নজরুলের হাতের রান্না। ছেলেবেলায় নজরুলকে অর্থাভাবে হোটেলে কাজ করতে হয়েছিলো, সেখান থেকেই রান্না শেখা।
তাঁর হাতের অপূর্ব স্বাদের রান্না খেয়ে বহরমপুরের দিনগুলো ভালোই কেটেছিলো শিবরামের। শিবরামের ভাষায়,
“মনে পড়লে এখনও জিভে জল সরে। নিজেকে সজিভ বোধ করি! আর জেলখানার সেই খানা। আহা! আমি তো বহরমপুর জেলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত টিঙটিঙে রোগা ছিলাম। তারপর দুইবেলা কাজীর খানা খেয়ে এমন মোগলাই চেহারা নিয়ে বের হলাম যে আর রোগা হলাম না। জেলখানায় আর জেলের খানায় গড়া এই চেহারা এতটুকু টসকায়নি।”
ভোজন আর নিদ্রা ছাড়া শিবরাম আর যে কাজটি ভালোবাসতেন তা হলো সিনেমা দেখা। পকেটে শেষ টাকাটি থাকা অব্দি নাইট শোতে একটি সিনেমা তার দেখতেই হতো।
খামখেয়ালিপনা, হাস্যরস ছিলো শিবরামের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে। প্রখর বুদ্ধিমত্তা আর ভাষাজ্ঞানের জোরে সেই হাস্যরস ফুটে উঠতো তার লেখাতেও। তবে শিবরামের লেখায় হাস্যরসের আড়ালে থাকতো ঘুণে ধরা সমাজ ব্যবস্থার আসল রূপ, বিপ্লব আর সাধারণ মানুষদের কথা। শিবরামের লেখা শুধুমাত্র ছোটদের জন্যই নয়, বরং সকল বয়সী পাঠকের কাছে এর সমান আদর।
শিবরামের লেখালেখি শুরু হয়েছিলো অনেকটা বিপদে পড়ে। এক কাবুলিওয়ালার কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা ধার নিয়েছিলেন। শর্ত ছিলো সময় মতো সুদের টাকা পরিশোধ করতে না পারলে কাবুলিওয়ালা মেসে এসে হামলা করবে। জাঁদরেল সেই কাবুলিওয়ালার হাত থেকে বাঁচতেই মূলত লেখালেখির শুরু। কেননা এতে করে নিজের পেট চালানো তো যেতোই, উপরন্তু কাবুলিওয়ালার সুদের টাকাও দেওয়া যেতো।
শিবরামের প্রথমদিকের রচনাগুলোতে প্যারডির প্রভাব বেশ লক্ষণীয়। তারপরে ধীরে ধীরে স্বকীয়তা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। ভাবতে অবাক লাগে, ‘ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি’, ‘হাতির সঙ্গে হাতাহাতি’, ‘চটির সঙ্গে চটাচটি’র মতো কথা কিংবা হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধনের মতো চরিত্র যিনি জন্ম দিয়েছেন, তিনিই ‘আজ এবং আগামীকাল’ (১৯২৯), ‘চাকার নীচে’ (১৯৩০), ‘মস্কো বনাম পণ্ডিচেরী’ (১৯৪৩), ‘যখন তারা কথা বলবে’ (১৯৪৯) এর মতো সমাজ ও সময়কে ধারণ করে এমন লেখার জন্ম দিয়েছেন।
এখানে লেখকের ‘মস্কো বনাম পণ্ডিচেরী’ প্রবন্ধের একটি লাইন তুলে ধরা হলো, “ব্রাহ্মণের আদর্শের ক্ষেত্র এতই সংকীর্ণ যে সেখানে কেবল তাদেরই ধরে, ধরিত্রীর সমস্ত মানুষদের সেখানে ঢোকার পথ আর নেই।” এই লাইনটি থেকে শিবরামের চিন্তা সম্পর্কে আঁচ পাওয়া যায়। শিবরামের সৃষ্টিকর্মগুলোর মাঝে ‘ইশ্বর, পৃথিবী, ভালোবাসা’ (১৯৭৪) এক অনন্য স্থান দখল করে আছে। এটি প্রথমে ‘দেশ’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ছাপা হলে তুমুল জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং পরবর্তী তা বই আকারে প্রকাশিত হয়।

নিজের সৃষ্টি দিয়ে মানুষের মন জয় করলেও শিবরামের অহংকার ছিলো না এতটুকুও। প্রচুর লেখা থাকা স্বত্ত্বেও অভাব কখনোই তার পিছু ছাড়েনি। তার সরলতার সুযোগ নিয়ে লোকে তাকে বহুবার ঠকিয়েছে। নিজের প্রচার কখনোই পছন্দ করতেন না। সাহিত্যে অবদানের জন্য বেশ কিছু সম্মানজনক পুরস্কারে ভূষিত হলেও সেগুলোর প্রতি তার বিশেষ কোনো আগ্রহ ছিলো না। বরং ভালোবাসতেন লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতে।
অবশেষে সেই লোকচক্ষুর আড়ালেই ১৯৮০ সালের ২৮ আগস্ট কলকাতার এস এস কে এম হাসপাতালের এক বেডে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন হাসির এই রাজা। মৃত্যুহীন প্রাণ শিবরাম অমর হয়ে থাকবেন তার সৃষ্টির মধ্য দিয়ে।
তথ্যসূত্র:
১. শিবরাম চক্রবর্তী শ্রেষ্ঠ গল্প (সম্পাদনা-আবদুশ শাকুর, প্রকাশক – বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র)
২. ইশ্বর পৃথিবী ভালোবাসা (লেখক – শিবরাম চক্রবর্তী, প্রকাশক – নবপত্র)