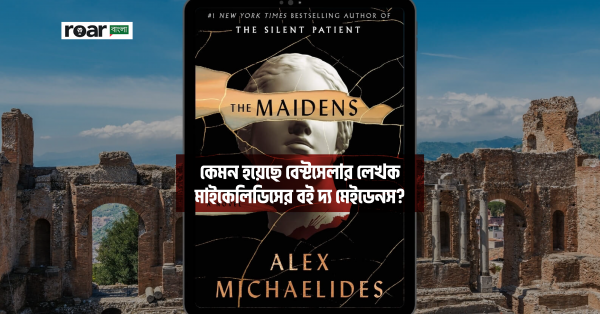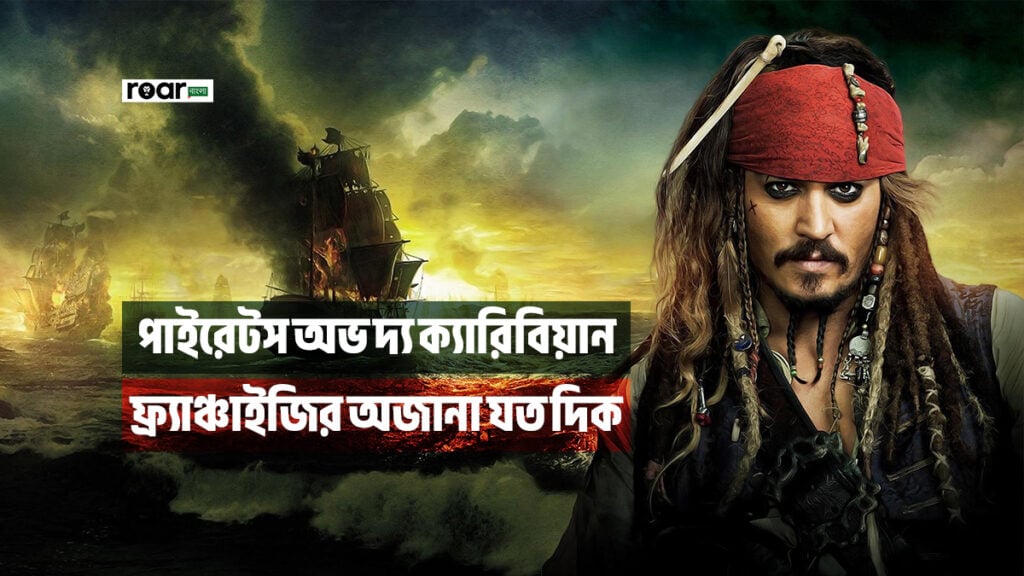.jpg?w=1200)
‘বক্তব্য কথাটিই সাহিত্যগন্ধী। ‘রূপক’ও তাই। আধুনিক কাব্যে এমনকি নাট্যশিল্পের একটি বিশিষ্ট ধারাতেও তাদের প্রয়োগ তার উদাহরণস্বরূপ। চলচ্চিত্রশিল্প তথাকথিত ‘সাহিত্যিক’ উপায় অবলম্বনে নিঃসংকোচ। সে উপায় তির্যক কিংবা সরল যাই হোক।’
ঋত্বিককুমার ঘটকের ‘আফটার-পার্টিশন ট্রিলজি’ বলতে যে তিনটি ছবিকে ধরা হয়, তার দ্বিতীয় ছবিটির মেজাজ বাকি দুটির চেয়ে বেশ অনেকটাই আলাদা। প্রথমটি ‘মেঘে ঢাকা তারা’, মুক্তি পেয়েছিল ১৯৬০ সালে। সে ছবিতে উদ্বাস্তু-শিবিরের জীবন, নীতার যাপনযন্ত্রণা, এবং সর্বোপরি দর্শকের মনে চিরকালীন জায়গা করে নেওয়া ‘দাদা, আমি বাঁচতে চাই’-এর আকুল মায়া-ক্রন্দনের কথকতা ছিল। কিন্তু তার পরের ছবি ‘কোমল গান্ধারে’ই সেই যন্ত্রণাক্লিষ্টতাই ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে, সরাসরি নয়। যাকে ঋত্বিক ‘রূপক’ বলছেন, হয়তো সেভাবেই। সেখানে যন্ত্রণাকে ছাপিয়ে যাওয়ার প্রবণতাও লক্ষণীয়। আবার তৃতীয় ছবি ‘সুবর্ণরেখা’র ক্ষেত্রে সেই যন্ত্রণার করুণঘন প্রত্যাবর্তন।

এই স্বাধীনচেতা মেজাজ, চিন্তাশীলতাই ঋত্বিকের ছবিকে বরাবর নতুন করে সংজ্ঞায়িত করেছে, সেজন্যই এই তিনটি ছবিকে পুরোপুরি ট্রিলজি বলা যুক্তিযুক্ত নয়। এই ব্যাপারে ঋত্বিক নিজেও একটি সাক্ষাৎকারে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন-
‘মেঘে ঢাকা তারা’, ‘কোমল গান্ধার’ এবং ‘সুবর্ণরেখা’-কে কোনো কোনো সমালোচক একটি যোগসূত্রে আবদ্ধ এই যুক্তিতে ‘ট্রিলজি’ বলার চেষ্টা করেছেন কিন্তু এটা ঠিক নয়। আমি যখন যেভাবে চিন্তায় মগ্ন হয়েছি সেভাবে ঘটনাগুলিকে আমি প্রকাশ করেছি। এর মধ্যে কোনো ঘটনা-পারম্পর্য নেই।
‘কোমল গান্ধার’-এর শুরুতেই একটি মুখবন্ধের মাধ্যমে বলা হচ্ছে- “নানা জায়গা থেকে নাটক পাগল ছেলেমেয়েরা এসে জড়ো হয়, একত্রে দল করে, সেই দলের মধ্যে গড়ে ওঠে স্নেহ-ভালবাসা-ঈর্ষা-হিংসায় জড়িয়ে তাদের পরিবার। সাধারণ অর্থে পারিবারিক জীবন তাই এদের নেই। এরকম একটি পরিবারের ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের কথাটুকু মাত্র এ ছবিতে বলার চেষ্টা করা হয়েছে।” ছবির মূল গল্পে প্রবেশের আগেই ছবির বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটি সারবত্তা জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে খুব স্পষ্টভাবে, সরাসরি। ঋত্বিক ঘটকের ছবিকে সাধারণ দর্শক বরাবরই কিঞ্চিৎ দুর্বোধ্য ভেবেছে, কিন্তু মজা এই, ছবির মধ্যে দিয়ে যে বার্তা দিতে চেয়েছেন ঋত্বিক, প্রত্যেকটি ছবিতেই সেই বার্তা এসেছে অত্যন্ত সরাসরি।

মুখবন্ধের পরেই একটি নাট্যাভিনয়ের দ্বিতীয় অংকে আমরা দেখতে পাচ্ছি একজন বৃদ্ধকে, যিনি চিৎকার করে জানতে চান- ‘এমন কোমল দ্যাশটা ছাইড়া, আমার নদী, পদ্মার ইলিশ ছাইড়া, আমি যামু ক্যান?’ উত্তরে তার পুত্রবেশী সহ-অভিনেতা বলে-‘যাইবা খাইবার লাইগা। এই শ্যাষ সুযোগ, এখনও শরনার্থী হও।’ পরিষ্কার বোঝা যায়, নাটকের বিষয় দেশভাগ।
এই দৃশ্যটি দেখতে দেখতে দেশভাগ নিয়ে তৈরি হওয়া সবচেয়ে প্রামাণ্য চলচ্চিত্রটির একটি দৃশ্যের কথা সহজেই মনে পড়ে যায়। নিমাই ঘোষের ‘ছিন্নমূল’ যেখানে কাছের মানুষদের বোঝানো সত্ত্বেও সেই বৃদ্ধা মানুষটি সমানে বলে যান ‘যাম না, যাম না, যাম না আমি’, কারণ তার শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে আর কোথাও যে তার বাড়ি থাকতে পারে, এমনটা তার ভাবনার অতীত। ‘কোমল গান্ধার’-এর বৃদ্ধের পুত্র যেমন তাকে খাবারের সংস্থানের কথা বলে, তেমন বৃদ্ধার প্রিয়জন বলে, ভিটেয় থাকলে শেয়াল-কুকুরে ছিঁড়ে খাবে। ভিটে এমন এক বন্ধন, যে, শত কষ্ট সয়েও সেখানে খুঁটি আঁকড়ে পড়ে থাকতে চায় মানুষ, কিন্তু খাবার-নিরাপত্তার জ্বালায় জর্জরিত হতে হতে বোধহয় একসময় খুঁটি আলগা হয়ে পড়ে।

এই ছবিতে এর পরের ঘটনা-পরম্পরা পুরোটিই অনুষ্ঠিত হতে থাকে নাট্যদলের উত্থান-পতনের ক্যালেইডোস্কোপে। সেই দলের নেতা ভৃগু (অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায়), স্বভাবে স্পষ্টবক্তা, প্রথম দর্শনে তাকে আবেগহীন মনে হয়। আছে শিবনাথ (সতীন্দ্র ভট্টাচার্য), দলে যার জায়গা বলতে গেলে ভৃগুর পরেই, কথায় কথায় খোঁচা দেওয়া তার অভ্যাস। মঞ্চে আলোকসজ্জার দায়িত্ব ঋষির (অনিল চট্টোপাধ্যায়) উপর। ঋষি বোহেমিয়ান, তার পোশাক মলিন। তাকে একপর্যায়ে দেখা যায়, কার্শিয়াঙের পাহাড়ি রাস্তায় ভোরবেলা হাঁটতে হাঁটতে ‘আকাশভরা সূর্যতারা’ গেয়ে চলেছে। এহেন ডোন্ট কেয়ারি মনোভাবের মানুষটিকে ভালবাসে জয়া (চিত্রা সেন), যাকে কিনা নাটক করার জন্য প্রতিদিনই রক্ষণশীল পরিবারের কাছে নির্যাতন সইতে হয়।

ভৃগুর দল আর একদা তাদের দলেরই অভিনেত্রী শান্তার (গীতা দে) নেতৃত্বে কয়েকজনের দল ভেঙে চলে যাওয়ার মধ্যেকার যে টানাপোড়েন, সেখানে হঠাৎ যেন সেতুবন্ধন করতে আসেন নবাগতা অনুসূয়া ভট্টাচার্য (সুপ্রিয়া দেবী), যে কিনা সম্পর্কে আবার শান্তার ভাসুরঝি, এবং শান্তাদের দল ‘দক্ষিণাপথ’-এর সম্পাদিকাও বটে। দুই দলের যৌথ প্রযোজনার উদ্যোগ নিতে গিয়েই প্রত্যেকের চরিত্র-স্ফুরণ ঘটে। প্রত্যেকেই যেন নিজেকে ও তার আশেপাশের সকলকে আবিষ্কার করতে থাকে। প্রসঙ্গত, ছবিতে এই যে নাট্যদলের পরবর্তী প্রযোজনা নিয়ে নিরন্তর পরিশ্রম, উদ্যোগ, আনন্দে গান গাইতে গাইতে বাইরে যাওয়া, কখনও লালগোলা, কখনও কার্শিয়াং, কখনও বোলপুর, ঠিক তার বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে ছিল বাস্তবের শুটিং। টাকার অভাবে বহুবারই মাঝপথে শুটিং বন্ধ করতে হয়েছিল ঋত্বিক ঘটককে।

ছবি এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে আপাত-কঠিন ভৃগু ও কোমলতা-কাঠিন্যের সঠিক মিশ্রণে গড়া অনুসূয়ার সম্পর্কও এগোতে থাকে। তাদের সম্পর্কের মধ্যে বিশেষ ভূমিকা নিয়ে আসে লালগোলার পদ্মার পাড়। যে ভৃগুকে দেখলে বড্ড রুক্ষ মনে হতে থাকে ছবির শুরু থেকেই, সেই ভৃগুই এতদিনকার সমস্ত বেদানাগাথা উজাড় করে দেয় অনুসূয়ার কাছে, এই পদ্মার পাড়ে দাঁড়িয়ে। পড়ন্ত বিকেলে ওপারের ‘দেশে’র কথা বলতে বলতে একে অপরের কাছাকাছি আসে, তারপর একসময় অনুসূয়া ভেঙে পড়ে নিজেকে সামলে নেয়। তাদের বুকের উপর দিয়ে ছুটে চলে কোনও এক অদৃশ্য রেলগাড়ি, পরিত্যক্ত রেললাইনের উপর দিয়ে ছুটে চলা সেই রেলের আওয়াজের সঙ্গে ‘দোহাই আলি’-র সমবেত চিৎকার ওঠে।
এই দৃশ্যটি যেন দেশভাগকে সরাসরি না দেখিয়েও সেই হাহাকারকে আরো মারাত্মক প্রকট আকারে দেখাতে পেরেছে। সেই করুণ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তির দীর্ঘ দেড় দশক পরেও যেন ক্ষত শুকোয় না, তাই বুঝি আপাত শান্ত পরিবেশে দুই নাট্য-কুশলী হঠাৎই নিজেদেরকে অন্যভাবে আবিষ্কার করতে পারে।

অনুসূয়া বলে তার মায়ের কথা, পদ্মাস্নান, দেশের বাড়ির সেই নিশ্চিন্তজীবনের আখ্যান। পরিবর্তে ভৃগু আস্তে আস্তে বলতে থাকে- ‘তুমি সেদিন বললে আমি অকারণ রুক্ষ আর কোনও বন্ধু পাব না, কিন্তু জানো, আমি সবসময় এমন ছিলাম না। এমন একদিন ছিল, যেদিন পদ্মার ওপারে বসে শাঁখ-ঘণ্টার শব্দ ভেসে আসত, আকাশের মেঘগুলো মুহূর্তে মুহূর্তে রং বদলাত। কিন্তু তারপর? এক মুহূর্তে সর্বস্বান্ত হয়ে গেলাম আমরা।’ তারপর কিছু থেমে, ‘বাবা মারা গেলেন ভিখিরির মতো। মা একরকম না খেতে পেয়েই শেষ হয়ে গেলেন চোখের সামনে। মরার ঠিক আগেই বাবা বলেছিলেন, জীবনটাকে আরম্ভ করেছিলাম কী নির্মল ছন্দে, এইভাবে শেষ হয়ে যাওয়াটা কি উচিৎ? সেদিন থেকে আমি কেমন যেন হয়ে গেলাম! কী ভীষণ একা হয়ে গেছি, তুমি জানো না!’ তা শুনে অনুসূয়াও বলে ফেলে-‘ভৃগু, আমিও বড় একা।’

পড়ন্ত গোধূলির ব্যাকড্রপে দুজনের গায়ে কোনো আলো পড়ে না, নদীর হাওয়ায় গাছের পাতার সঙ্গে দুজনের চুলই উড়তে থাকে। ক্যামেরার ফ্রেম কখনো নদীর ধারের দুজনের স্মৃতিমন্থনকে ধরে, আবার পরমুহূর্তেই ক্লোজ-আপে দুজনের মুখের ব্যথাকে তুলে আনে। নদীর ওপারেই ভৃগুদের বাড়ি, এপার থেকে দেখা যেত তা। ভৃগু খোঁজে, আর অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় আর গ্রিসিয়ান মুখভঙ্গিতে যেন ফুটে উঠে সমস্ত হারিয়ে শোক করতে ভুলে যাওয়া এক ক্লিষ্ট মানুষের আর্তি। ‘সে সম্পূর্ণ সুস্থও নয়, সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থও নয়, অবদমিত, কিছুটা বিকারগ্রস্ত।’ ঠিক তার বিপরীতে সুপ্রিয়া দেবীর ভেঙে পড়ার স্বাভাবিক সৌন্দর্যের যোগ্য সঙ্গত।

‘মেঘে ঢাকা তারা’ বা ‘কোমল গান্ধার’, দুটি ছবিতেই সুপ্রিয়া দেবীর স্বাভাবিক সৌন্দর্যকেই পুরোপুরি ব্যবহার করেছেন ঋত্বিক। সুপ্রিয়া দেবীর পরবর্তী বাণিজ্যিক ছবিগুলিতে তার চড়া মেক-আপ বা শরীরী আবেদনকে বেশি ধরতে দেখা গেছে, তাতে তাকে অভিনেত্রী মনে হয়েছে হয়তো, কিন্তু এই দুই ছবিতে তার স্বাভাবিকত্ব তাকে দর্শকের কাছে অনেক বেশি আপন করেছে বলেই মনে হয়।
দুই দলের যৌথ প্রযোজনার ‘শকুন্তলা’ নাটকটি অবশেষে শোয়ের মাঝেই ভেস্তে যায় শান্তাদের প্রতিহিংসা চরিতার্থতার কারণে। মানসিকতার অসুস্থতা, সম্পর্কের টানাপোড়েন, পরস্পরে অবিশ্বাস – এইসব কিছুর মাঝেই সেই নাটকের মধ্যেই তারা ফিরে পায় নিজস্ব সত্তাকে। অনুসূয়া ‘দক্ষিণাপথ’ ছেড়ে চলে আসে ভৃগুর দলে। তাদের নাটক দেখে এক সন্তানহারা বৃদ্ধা তার সন্তানের শেষ চিহ্নটুকু তুলে দিতে এগিয়ে আসেন। ভৃগুকে বলেন, তার আদরের নাটুও খুব ভাল গান গাইত, কিন্তু যুদ্ধের আকাল তাকে টেনে নিয়েছে। ভৃগুর মনে পড়ে যায় নিজের মায়ের অনাহারে মৃত্যু। আশাবাদ, যা ঋত্বিকের ছবিতে কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রমী ছিল, সেই আশাবাদ এই ছবিতে শেষ দৃশ্য পর্যন্ত থাকলেও তার ঠিক সমান্তরালেই চলমান ছিল কাঁটাতার-যন্ত্রণা।

ভৃগুর দলের ভাঙনে যে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও ঈর্ষার অন্ধকার দিকটি দেখালেন পরিচালক, সেখানেও কিন্তু সেই বিভাজন-রাজনীতির স্পষ্ট ছায়া। শিবনাথের ঈর্ষাপরায়ণ রাজনীতির সামনে দাঁড়িয়ে দাপুটে নেতা হওয়া সত্ত্বেও ভৃগু ঠিক কী কারণে দল ধরে রাখতে পারল না, তা বুঝতে খুব বেশি মনস্তত্ত্ব-চর্চার প্রয়োজন হয়ত পড়ে না। কিন্তু এই ভাঙনের মধ্যে দিয়েই ভৃগু আবিষ্কার করে দলের দুই নতুন সদস্যের অনন্যসাধারণ প্রতিভাকে। মঞ্চের রহস্যটা পরিষ্কার হয় তার কাছে– ‘মানুষের নড়াচড়ার ছন্দে, একটা অর্কেষ্ট্রাল কন্ডাকশনের মতো, বহু সুরে, হারমোনি, পলিফোনিক সব প্যাটার্নস, গতি বাড়িয়ে, কমিয়ে, একমুহূর্তের জন্য স্থগিত করে দিয়ে, স্টেজের যে টাওয়ারিং প্যাটার্ন।’ অবনীশের অভিনয় দেখে মনে হয়, প্রকৃত মঞ্চাভিনেতার মতো তিনিও সত্যিই আবার নাটক করার উদ্যম খুঁজে পেয়েছেন।

সঙ্গীত ও শব্দের ব্যবহার, যা ঋত্বিকের ছবির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল, এই ছবিতেও তার কোনও অন্যথা হয়নি। ছবির নামেই ছিল সঙ্গীতের ছোঁয়া (কোমল গান্ধার উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের একটি রাগবিশেষ)। ‘মেঘে ঢাকা তারা’য় প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীত ব্যবহার করেছিলেন তিনি। এই ছবিতেও সেই ধারা অক্ষুণ্ণ রেখে দেন। ‘আকাশভরা সূর্যতারা’ ছাড়া আরও যে রবীন্দ্রসঙ্গীতটি ব্যবহার হয়েছিল, সেটি হল ‘আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে’। দৃশ্যায়নে সাবেকী রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে লোকসঙ্গীত এবং স্ট্রিং ইনস্ট্রুমেন্টকে মিশিয়ে দিয়েছিলেন সুরকার জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র।

পদ্মার পাড়ে নায়ক-নায়িকার দৃশ্যটির সম্পর্কে বলতে গিয়ে চলচ্চিত্র-বিশেষজ্ঞ সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় বলেছেন – ‘যেখানে তিনি দেশমাতৃকাকে, বা দ্বেষ বিষয়ে তার ধারণা উন্মুক্ত করেছেন, সেই বাফার শট, সেখানে সেই ‘দোহাই আলি’, এই ‘দোহাই আলি’ কার? আমরা শুনলেই বুঝতে পারি, যে এ হচ্ছে, পদ্মা নদীর সেই মাঝির, যে একসময় উৎসবের জন্য আল্লাকে স্মরণ করত, আজ চূড়ান্ত বিষাদ মুহূর্তে, শ্মশানযাত্রার মুহূর্তে আর কাকে আবেদন জানাবে?
সেই দরিদ্র, নিরক্ষর, শ্রমজীবী, সে জানাচ্ছে সর্বশক্তিমানকে। ঈশ্বরকে বা আল্লাকে। ঋত্বিক ঘটক ঈশ্বরকে আনেন, আল্লাকে আনেন, এবং তা আনেন অন্তর্ঘাতের জন্য।’ সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের কথার সূত্র ধরে একথা বলাই যায়, বর্তমান সময়ে ভারতের বিশেষ দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলটি ঋত্বিকের ছবিকে যেভাবে ভুল দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখাতে চাইছে, তার বিরুদ্ধে জোরদার অস্ত্র হয়ে উঠবেন স্বয়ং ঋত্বিকই।
এমনকি, বর্তমান বাংলার আরো একটি জ্বলন্ত সমস্যা, যা কিনা শিক্ষকদের ঘিরে কেন্দ্রীভূত, বাংলার সেই শিক্ষক-সমস্যার দীর্ঘ ইতিহাসের শুরু যেখানে, সেই ষাটের দশকের শিক্ষক আন্দোলন সমসাময়িক কোনো জনপ্রিয় শিল্পমাধ্যমে উঠে আসেনি, একমাত্র ‘কোমল গান্ধার’ ছাড়া। আসলে, ঋত্বিক যে সত্যিই মানুষের পেটের জ্বালাটা বুঝতেন। তার ছবি বুঝতে গেলে সেই চিরকালীন খিদের ব্যথাটা বোঝার মানসিকতার বিশেষ প্রয়োজন।
বস্তুত, ‘কোমল গান্ধার’ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ঋত্বিক নিজেই বলে গিয়েছিলেন – ‘এ ছবির দর্শকদের কাছ থেকে একটি এপিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রার্থনীয় – সে দৃষ্টিভঙ্গি এদেশে এখনও একটি প্রাণবন্ত ঐতিহ্যরূপে বিরাজমান।’
[ঋত্বিককুমার ঘটক এর বাকি বই কিনতে ভিজিট করুন এই লিংকে।]