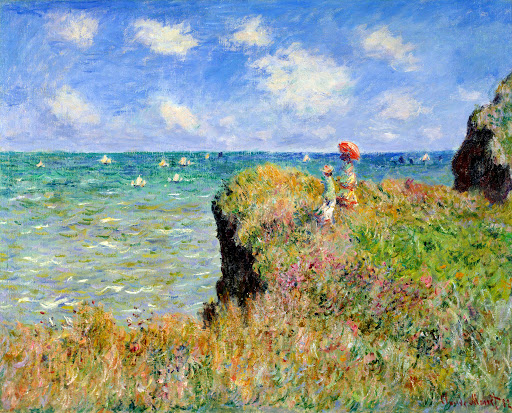১.
১৮৯৮ সালের এক শীতের দিন। উত্তর জার্মানির হামবুর্গের একটি খালের পাড় ধরে রুদ্ধশ্বাসে দৌড়াচ্ছেন গাঁট্টাগোট্টা শরীরের, হ্যান্ডলবার গোঁফধারী এক ব্যক্তি।
তার নাম ফ্রাঞ্জ কার্ল বুহলার।
প্রচণ্ড ভীত-সন্ত্রস্ত তিনি। পালানোর চেষ্টা করছেন রহস্যময় এক গোষ্ঠীর কবল থেকে, যারা বিগত কয়েক মাস ধরে তার জীবনটাকে স্রেফ নরক বানিয়ে ছেড়েছে।
ছুটতে ছুটতেই একটা চিন্তা খেলা করে গেল তার মনে। ভাবলেন, সাঁতরে এই জলাশয় পাড়ি দিতে হবে তাকে। পালাবার আর কোনো পথ নেই।
তাই কৃষ্ণবর্ণ জলে ঝাঁপ দিলেন তিনি। কনকনে ঠান্ডা সেই জল। তাপমাত্রা আরেকটু নিম্নগামী হলেই যা পরিণত হবে বরফে। বছরের এই সময়ে এমনই হয়ে থাকে সাধারণত।
বলাই বাহুল্য, প্রায় হিমশীতল জলে সাঁতরানোর চেষ্টায় খুব একটা সুবিধা করতে পারলেন না তিনি। বেশ অনেকক্ষণ পর আশপাশের মানুষজন মিলে তাকে টেনেহিঁচড়ে তুলল ডাঙায়। তার সারা শরীর তখন জলে সিক্ত, থরথর করে কাঁপছে।
এর ঠিক অব্যবহিত পরেই একটা বিষয় দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল সকলের কাছে: নির্ঘাত কোনো গণ্ডগোল আছে এই মানুষটার মধ্যে।
ধাওয়াকারীদের ভয়ে আতঙ্কিত তিনি। অথচ কোথাও তো তাদের কোনো নাম-নিশানাই চোখে পড়ছে না।
এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, মানুষটা হয় কোনো কারণে বিভ্রান্ত, অথবা বদ্ধ উন্মাদ!
তাই সবাই মিলে জোরজবরদস্তি করে তাকে নিয়ে গেল নিকটস্থ ফ্রেডরিকসবার্গ পাগলাগারদে। হ্যাঁ, এই নামেই জনসাধারণের কাছে পরিচিত ছিল সেই জার্মান সাইকিয়াট্রিক সিস্টেমটি।
এবং সেখানেই, জীবনের পরবর্তী ৪২ বছর কাটান বুহলার। তিনি হলেন সেই লক্ষ লক্ষ রোগীদের একজন, যাদের জীবন কেটেছে ওই পাগলাগারদে, চার-দেয়ালে বন্দি অবস্থায়।
সে জীবন বীভৎস, অমানবিক।

২.
এই অনাকাঙ্ক্ষিত কারাবাস তথা বন্দিদশা বুহলারের জীবনকে বিষিয়ে দিয়েছিল ঠিকই। তবে এর মাধ্যমেই সূচনা ঘটেছিল এক বিস্ময়কর গল্পের, যে গল্পের মুখ্য চরিত্রে ছিলেন তিনি নিজে।
যে গল্পের কথা বলছি তা আমাদেরকে জানায়, শিল্প ঠিক কতটা ঋণী মানসিক অসুস্থতার কাছে। পাশাপাশি, এই গল্পই সংযোগ স্থাপন করে ইতিহাসের সবচেয়ে বিধ্বংসী সাংস্কৃতিক যুদ্ধের সঙ্গে।
৩.
বুহলার ভুগছিলেন সিজোফ্রেনিয়ায়। যখন তাকে এক সাইকিয়াট্রিক ক্লিনিক থেকে আরেক সাইকিয়াট্রিক ক্লিনিকে পাঠানো হচ্ছিল, সেই নিয়ত-পরিবর্তনশীল অসহ্য জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নেয়ার জন্য তিনি এক চমকপ্রদ কৌশল আবিষ্কার করেন। নিজেই নিজেকে শেখাতে শুরু করেন ছবি আঁকা।
চিত্রাঙ্কনে তার হাতেখড়ি হয় চারপাশের মানুষের স্কেচ করে। এছাড়াও প্রাতিষ্ঠানিক জীবনের একঘেয়ে, অহেতুক কর্মকাণ্ডকেও তিনি তার ছবির মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে থাকেন। তারপর একপর্যায়ে তিনি সেলফ-পোর্ট্রেটে মনোনিবেশ করেন, এবং সেখানেও ক্ষান্ত না দিয়ে, ছবিতে জায়গা দিতে থাকেন সাইকোটিক ভিশনে প্রাপ্ত নানা ভয়ঙ্করদর্শন জীবজন্তুকে। সেই তালিকায় স্থান পায় দানব কুকুর থেকে শুরু করে মৃত্যুদেবতা পর্যন্ত।
ডাক্তাররা অবশ্য তার এসব ছবিতে খুব একটা ভ্রুক্ষেপ করেন না। হাজার হোক, একজন ‘পাগল’ আবার শিল্পের কী বোঝে! তাই তো পুরো দুই দশক ধরে তার আঁকা স্কেচ কিংবা ছবিগুলো ফাইলবন্দি অবস্থাতেই পড়ে থাকে। অবশেষে সেগুলোকে নতুন আলোয় দেখার ব্যবস্থা হয় হাইডেলবার্গ থেকে আগত এক গুরুত্বপূর্ণ পরিদর্শকের বদৌলতে।

৪.
হান্স প্রিঞ্জহর্ন ছিলেন একজন বহুগুণে গুণান্বিত ব্যক্তি। একাধারে তিনি ছিলেন একজন চিকিৎসক, শিল্প ইতিহাসবিদ, দুর্ধর্ষ সৈনিক, এবং পেশাদারভাবে প্রশিক্ষিত ব্যারিটন। তবে তার যে কৃতিত্বটি ইতিহাসের পাতায় সমুজ্জ্বল হয়ে আছে, তা হলো হাইডেলবার্গ ইউনিভার্সিটির সাইকিয়াট্রিক ক্লিনিকে করা মানসিকভাবে অসুস্থদের শিল্প নিয়ে গবেষণা।
১৯১৯-২১ সালের মধ্যে তিনি জড়ো করেন বিশ্বের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ সাইকিয়াট্রিক আর্টের সংগ্রহ। শত শত মানসিক রোগীর শত-সহস্র শিল্পকর্মকে একাট্টা করেন তিনি। সেসব শিল্পকর্মের ক্যানভাস হিসেবে এমনকি ব্যবহৃত হয়েছে টয়লেট পেপার, খসে পড়া পলেস্তারা কিংবা খাটের ভাঙা কাঠও।
যেসব মানসিক রোগীর কথা বলছি, তাদের অধিকাংশই ভুগছিলেন সিজোফ্রেনিয়ায়। তাদের উদ্দেশ্য হয়তো শিল্প সৃষ্টি ছিল না। তারা নিছকই নিজেদের অসুস্থ মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন স্কেচ, ভাস্কর্য কিংবা হিজিবিজি লেখার মাধ্যমে। কেউ কেউ আবার বন্দিদশার একাকিত্ব ঘোচাতে, যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবেও রচনা করেছেন অনেক বার্তা।
প্রিঞ্জহর্ন তার কাজ যখন প্রথম শুরু করেন, তখন তার মাথায় শুধু এটুকুই ছিল যে এসব তথাকথিত শিল্পকর্ম হয়তো তাকে রোগীদের চিকিৎসার নতুন কোনো পথ দেখাতে সাহায্য করবে। কিন্তু অচিরেই তিনি উপলব্ধি করেন যে এসব শিল্পকর্মের পূর্বে ‘তথাকথিত’ বিশেষণটি ব্যবহার করা অনুচিত। কেননা এগুলোর প্রকৃতপক্ষেই রয়েছে নিগূঢ় ভাব প্রকাশের ক্ষমতা এবং শিল্প মূল্য।
৫.
দর্শনার্থীরা নানা ধরনের মন্তব্য করেছে এসব শিল্পকর্মের ব্যাপারে। কারো মতে, “এগুলো খুলে দিয়েছে এক ভিন্নধর্মী বাস্তবতার জানালা।” কেউ-বা আবার বলে, “এসব শিল্পকর্ম উদ্ভাসিত হয়েছে মানবাত্মার গভীরতম স্থান থেকে।” এক ভবিষ্যৎ কিউরেটর, যিনি এই সংগ্রহ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পান, লিখেছেন, “এই সংগ্রহ আমাকে টেনে নিয়ে গেছে তাদের ক্ষমতার অভ্যন্তরে; খোলা জায়গা নাড়িয়ে দিয়েছে আমার সুস্থিতিকে, ঝিমুনি ধরিয়েছে আমার মননে।“
এদিকে ১৯২২ সালে প্রিঞ্জহর্ন তার গবেষণালব্ধ ফলাফলের উপর ভিত্তি করে প্রকাশ করেন এই খাতের এক যুগান্তকারী গ্রন্থ, ‘আর্ট্রিস্ট্রি অভ দ্য মেন্টালি ইল’। সেই গ্রন্থ অলঙ্করণে ব্যবহৃত হয় তার সংগ্রহের অসংখ্য ছবি। সেগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হিসেবে বিবেচিত ছবিটির নাম ‘সিজোফ্রেনিক মাস্টার্স’, যার স্রষ্টা বুহলার।
‘আর্ট্রিস্ট্রি’ খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে আভঁ-গার্দদের মাঝে, যারা ওই সময় যুদ্ধের বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতাকে শিল্পে ফুটিয়ে তোলার জন্য উন্মাদনাকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করছিলেন। ফলে প্রিঞ্জহর্নের বইটি তাদের কাছে যেন পরশ পাথর রূপে আবির্ভূত হয়।
ম্যাক্স আর্নস্ট যখন বইটির একটি কপি প্যারিসে নিয়ে গেলেন, তখন সেখানকার নব পরাবাস্তববাদী আন্দোলনের সদস্যদের কাছেও এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে প্রতিভাত হয়। যেসব সদস্যদের কথা বলছি, তাদের মধ্যে আর্নস্ট নিজে তো ছিলেনই, এমনকি ছিলেন সালভাদর ডালিও। এদিকে, পরাবাস্তববাদীদের প্রধান আন্দ্রে ব্রেটনও শেষমেশ লেখেন, “অবশেষে কেউ একজন উন্মাদ শিল্পীদেরকে দিয়েছে তাদের প্রতিভার সমতুল্য একটি উপস্থাপনা।“

৬.
পাগলপনা কখনোই এতটা অস্পষ্টতা, অনিশ্চয়তায় ভরা ছিল না। কিন্তু হাইডেলবার্গে হওয়া গবেষণাকর্মগুলো নিয়ে বিতর্কও নেহাত কম হয়নি। এবং ১৯২০-র দশকের মাঝামাঝি সময়েই, শিল্পের সঙ্গে মানসিক অসুস্থতার সংযোগটি চলে আসে উগ্র-ডান চরমপন্থীদের নজরে।
আডলফ হিটলারও বুহলারের মতোই, ছিলেন একজন স্বশিক্ষিত শিল্পী। তাছাড়া তাকে ১৯২৩ সালে পরীক্ষা করা এক মনোবিদের মতে, তিনি ছিলেন একজন ‘মরবিড সাইকোপ্যাথ’, এবং হিস্টিরিয়াপ্রবণ। ভিয়েনার অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের ভর্তি পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি ওয়াটারকালারে ট্যুরিস্ট পোস্টকার্ড কপি করে জীবিকা নির্বাহ করতে শুরু করেন। ১৯১৪ সালে যখন যুদ্ধ বাধে, তখন তিনি রঙ-তুলি নিয়ে যান রণাঙ্গনে। যুদ্ধ শেষে যখন তিনি রাজনীতিতে নাম লেখান, তখনও সঙ্গী করে নিয়ে যান নিজের গভীর শিল্পানুরাগকে।
শিল্পই তাকে সাহায্য করে এক নাৎসিবাদী নান্দনিকতা নির্মাণ করতে। দলের প্রতীকচিহ্ন, ব্যাজ, ইউনিফর্ম, মঞ্চ ইত্যাদি সব জায়গাতেই তিনি নিজের শিল্পীসত্তার ছাপ রাখেন। শিল্প তাকে আরো দেয় এক উচ্চতর রাজনৈতিক লক্ষ্য। তিনি নিজের বলতেন, “যুদ্ধ তো যাবে-আসবে, কিন্তু হাজার বছর পরেও জার্মানদেরকে বিচার করা হবে তাদের সাংস্কৃতিক অর্জন দিয়ে, ঠিক যেভাবে অতীতের সভ্যতাগুলোকেও বিচার করা হয়েছে অভিন্ন মাপকাঠিতে।“
হিটলার বিশ্বাস করতেন, জার্মান সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করা মানে হলো ‘জাতিগতভাবে বিশুদ্ধ’ জার্মান ভল্ককে সংরক্ষণ করা। জার্মান সংস্কৃতির অবনতি হলো সেই ভল্কেরই অবনতি। এবং যেভাবে সমসাময়িক শিল্প মানসিক অসুস্থতার পথে ধাবিত হচ্ছিল, তা ছিল তার মতে, অবনতিরই নামান্তর।
৭.
হিটলার যে প্রিঞ্জহর্নের বইটি পড়েছিলেন, সেরকম কোনো প্রমাণ মেলেনি। তবে এ-কথা আন্দাজ করাই যায় যে, কোনো সংবাদপত্র বা ম্যাগাজিনের মাধ্যমে হয়তো তিনি ওই বইয়ে বর্ণিত ধারণার ব্যাপারে অবগত হয়েছিলেন। এবং এমনও হতেই পারে যে ওই ধারণাই তার দৃষ্টিভঙ্গিকে কাঠামো প্রদানে প্রভাবক ভূমিকা পালন করেছে।
‘মাইন কাম্ফ’ বইতে তিনি একহাত নেন ‘বোকা’ ও ‘পাজি বদমাশ’দের, যারা তৎকালে চেষ্টা করছিলেন তার নিজের পছন্দের অভিজাত রোমান্টিক চিত্রকরদের ‘স্বাস্থ্যসম্মত শৈল্পিক অনুভূতি’ নস্যাৎ করার।
হিটলারের মতে, আধুনিকতাবাদী শিল্প ছিল একেবারেই ‘অর্থহীন’ ও ‘নির্বোধ’ জিনিস; যা নির্মাণের পেছনে কাজ করছিল ভীত-সন্ত্রস্ত জনগণের সমালোচনাকে নিবৃত্ত করার হীন ষড়যন্ত্র। এদিকে ঘনবাদ (কিউবিজম) ও ডাডাবাদের মতো আন্দোলনগুলো ছিল বদ্ধ উন্মাদ ও অধঃপতিতদের অসুস্থতার বহিঃপ্রকাশ।
সেই ১৯২০ সাল থেকেই পার্টি ম্যানিফেস্টোতে লড়াইয়ের ডাক দেয়া হয় শিল্প ও সাহিত্যে জনজীবনের অধঃপতনের মানসিকতাকে প্রচারের প্রবণতার বিরুদ্ধে। ১৯৩৩ সালের পর ঠিক এই কাজটিই তারা করে।

৮.
১৯৩৭ সালে ‘ডিজেনারেট আর্ট’ শো-টি মঞ্চস্থ করা ছিল গোয়েবলসের বুদ্ধি। এই ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনীতে উপস্থিত হয়েছিল ৩০ লক্ষ দর্শনার্থী, যে রেকর্ড এখন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রয়েছে। তবে এখানে শিল্পকে উদযাপন করা হয়নি, জনসম্মুখে শিল্পের উপহাস করা হয়েছে।
বার্লিনে এই প্রদর্শনীর দ্বিতীয় ধাপ শুরুর আগে হাইডেলবার্গ ক্লিনিক থেকে শতাধিক শিল্পকর্ম নিয়ে আসা হয়, যার অনেকগুলোই ছিল বুহলারের; এবং প্রদর্শনীতে পেশাদার শিল্পকর্মের পাশাপাশি হাইডেলবার্গের সংগ্রহের অনেকগুলোও তোলা হয়।
অফিসিয়াল গাইডবুক অনুযায়ী, এই কাজের পেছনে উদ্দেশ্য ছিল এটাই সবাইকে জানান দেয়া যে আভঁ-গার্দরা ‘উন্মাদ’-এর চেয়েও অনেক বেশি ‘অসুস্থ’। হিটলারের বিবেচনায়, এর উদ্দেশ্য ছিল আঘাত করা সেই ইহুদি-বলশেভিক ষড়যন্ত্রকে, যা চাইছিল জার্মান সংস্কৃতিকে খাটো করতে, এবং তাদের জাতিকে ‘হীনতর রক্ত’ দিয়ে দূষিত করতে। তিনি মনে করতেন, এই সাংস্কৃতিক অধঃপতন হলো বিশ্বকে একটু একটু করে পচিয়ে দেয়া কিংবা জার্মানদের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের গায়ে কালিমা লেপনের পাঁয়তারা।
৯.
এই সমস্যার সমাধান ছিল খুবই সহজ: সাংস্কৃতিক নির্মূলের অভিপ্রায়ে এক নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধ।
তাই জার্মানির জাদুঘর থেকে সরিয়ে ফেলা হয় আধুনিক শিল্প। কিছু বিক্রি করে দেয়া হয়, আর অধিকাংশই স্রেফ ধ্বংস করে ফেলা হয়। ‘অধঃপতিত’ শিল্পীদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়।
তবে হিটলারের সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী শৈল্পিক প্রকল্প, তার জেসামটকুনস্টওয়ার্ক (Gesamtkunstwerk), ছিল স্বয়ং জার্মানদেরই ‘পরিশোধন’ করা।
এ লক্ষ্যেই তিনি ১৯৩৯ সালে আদেশ দেন প্রথম নাৎসি গণহত্যা প্রকল্প, ‘অ্যাকশন টি৪’, যেখানে লক্ষ্য ছিল মানসিকভাবে অসুস্থরা।
১০.
১৯৪০ সালে বুহলার ছিলেন বাদেন ইউর্টেমবার্গে, এমেনডিঙ্গেনের একটি অ্যাসাইলামে। ওই বছরের ৫ মার্চ, একটি ছোট যানবাহনের বহর এসে হাজির হয় প্রতিষ্ঠানটির সামনে। সেগুলোতে ছিল সাধারণ পোশাক পরিহিত এসএস সদস্যরা। তারা জনাপঞ্চাশেক রোগীকে তোলে তাদের বাসে। সেই পঞ্চাশজনের মধ্যে ছিলেন বুহলারও।
এরপর বাসটি নিয়ে যাওয়া হয় সোয়াবিয়ায় অবস্থিত গ্রাফেনেক ক্যাসলে, যেটি বিশেষায়িত ছিল প্রতিবন্ধকতার শিকার ব্যক্তিদের জন্য। সেখানে রোগীদের কাপড় খুলে তাদেরকে ঢুকিয়ে দেয়া হয় একটি গোসলখানায়। কিন্তু আদতে সেটি গোসলখানা ছিল না। সেটি ছিল একটি গ্যাস চেম্বার। সেই গ্যাস চেম্বারে তাদেরকে কার্বন মনোক্সাইড দিয়ে হত্যা করা হয়।
নাৎসিদের ভাষ্যে, এই কার্যক্রমের নাম ছিল ‘ইউথেনেশিয়া’। এবং একেই অনেকে মনে করে হলোকাস্টের অগ্রদূত হিসেবে। কেননা, এই প্রকল্প সফল হওয়ার পর অ্যাকশন টি৪-এর অনেক মানসিকভাবে শক্তিশালী সদস্যকেই নিযুক্ত করা হয় পূর্বাঞ্চলের নানা নিধনশিবিরে।

১১.
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ অবধি হিটলারের বাহিনী কর্তৃক হত্যা করা হয় প্রায় দুই লক্ষ মনোবৈকল্যের শিকার রোগীকে। তাদের মধ্যে ছিলেন প্রিঞ্জহর্নের ৩০ জন শিল্পীও।
অবশ্য যুদ্ধ প্রিঞ্জহর্নের সংগ্রহকে শেষ করে দিতে পারেনি। অলৌকিকভাবে, তার সংগ্রহের অধিকাংশ শিল্পকর্মই বেঁচে যায়, এবং নতুন প্রজন্মের অনেক শিল্পীকে অনুপ্রাণিত করে। তাদের মধ্যে প্রণিধানযোগ্য হলেন আর্ট ব্রুটের (র আর্ট) স্রষ্টা জন ডুবুফে।
বুহলারকে হয়তো হত্যা করা হয়েছে, ঠিক যেভাবে হত্যা করা হয়েছে প্রিঞ্জহর্নের আরো অনেক শিল্পীকে। কিন্তু তবু, বুহলারের সৃষ্টি ও অর্জন টিকে রয়েছে আজও। তার শিল্পকর্ম বিস্তৃত করেছে শিল্প-সংজ্ঞার দিগন্তকে। এবং শিল্পকে কেবল তথাকথিত এলিটদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে, ছড়িয়ে দিয়েছে সর্বসাধারণের মাঝে।
(মূল লেখক চার্লি ইংলিশ। তিনি দ্য গার্ডিয়ানের সাবেক আন্তর্জাতিক সংবাদ প্রধান। তিনি ‘দ্য গ্যালারি অভ মিরাকলস অ্যান্ড ম্যাডনেস’ নামে একটি বই লিখেছেন। এই লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০২১ সালের আগস্টে, দ্য গার্ডিয়ানে।)