
অডস্ এগেনস্ট টুমরো (১৯৫৯)
সময়ের দিক থেকে একটু দেরিতে হলেও ‘অডস্ এগেনস্ট টুমরো’ আক্ষরিক অর্থেই ফিল্ম নোয়াহ। ফিল্ম নোয়াহর বিশেষত্বগুলোকে ধারণ করেছে। এতে ভঙ্গুর আর জটিলতাপূর্ণ নায়ক আছে। ফিল্ম-নোয়াহর অমন ভিন্নধর্মী লাইটিং আছে। ‘কিয়ারস্কিউরো ইফেক্ট’ আছে। স্বাভাবিকের চেয়ে ভিন্ন, ডাচ এংগেলের প্রাধান্য সব শট আছে সিনেমাটোগ্রাফিতে। সর্পিল আকৃতির গল্প আছে। হিরো, ভিলেন, নায়িকা সবারই একটা ধূসর জায়গা আছে। পরিচিতি আর অস্তিত্ব নিয়ে প্রগাঢ় আলাপও আছে। মানে, ফিল্ম-নোয়াহর প্রধান সব বৈশিষ্ট্য এই সিনেমা ধারণ করেছে। তবে এনেছে ভিন্নতা। একজন কৃষ্ণাঙ্গকে প্রধান তিনটি চরিত্রের একটি হিসেবে দাঁড় করিয়ে এই জনরায় নতুন এক মাত্রা যোগ করেছে অডস্ এগেনস্ট টুমরো।
মূলত একটি ব্যাংক চুরিকে কেন্দ্র করেই সিনেমার গল্প। সম্পূর্ণভাবে বিরুদ্ধ রেখার তিনজন, নিজেদের ব্যর্থতার সকল গ্লানি মুছতে নানা দ্বন্দ্ব আর মতভেদের পরো একত্রিত হয় চুরির পরিকল্পনায়। একজন সাবেক পুলিশ অফিসার, অপরাধ তদন্তকারীদের সহযোগিতা করার ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানানোয় যার ক্যারিয়ার অকালেই ধসে যায়। একজন; বদমেজাজি, বর্ণবাদী, অবসরপ্রাপ্ত মিলিটারি। এবং একজন নাইটক্লাবের জুয়াড়ি, যার দেনা জমেছে গলা সমান।
সাবেক পুলিশ অফিসারই এই ব্যাংক চুরির পরিকল্পনাকারী। সে-ই বাকি দুজনকে তার এই পরিকল্পায় অংশীদার হিসেবে চায়। যথারীতি প্রথমেই তারা দুজন কাজটি করতে তুমুল অনীহা প্রকাশ করে। তার উপর একজন বর্ণবাদী, আরেকজন কৃষ্ণাঙ্গ- তাই স্বভাবতই তাদের মাঝে রয়েছে চাপা আক্রোশ। কিন্তু চাহিদার কাছে নতি স্বীকার করে যোগ তাদের দিতেই হয়। একসাথে কাজ করতে সম্মতি জানালেও ভেতরের ক্ষোভটা দমেনি একবিন্দু। বর্ণ বিভেদ নিয়ে এই ক্ষোভই শেষ পর্যন্ত তাদের সফল চুরির পরিকল্পনার ছক উল্টে দেয়।

হলিউড তখন নিয়ন্ত্রিত হতো ‘হেইস কোড’ দ্বারা। ‘৩০, ‘৪০ এবং ‘৫০-এর দশকেও বেশ কিছুটা সময় ধরে এই হেইস কোডের নিয়মাবলী সচল ছিল। এই হেইস কোড সিনেমায় কী কী দেখানো যাবে এবং যাবে না- সেটার উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত। উদাহারণস্বরূপ বলা যায় সিনেমায় তখন কোনোভাবেই অপশক্তিকে জয়ী দেখানো যেত না। সবসময় হিরোরই জয় হতে হবে। তারপর, ভিন্ন বর্ণের মাঝে সম্পর্ক দেখানোর অনুমোদন ছিল না। শ্বেতাঙ্গ দাসত্ব দেখানোর নীতি ছিল না। কিন্তু কালো বর্ণের ক্ষেত্রে দাস দেখালে আবার সমস্যা নেই। কারণ, তাদের তো সমাজ দাস হিসেবেই দেখতো। তাই সেই ট্যাবুকে তখন ভাঙার চেষ্টা করা হতো না। বা করতো না প্রোডাকশন কোম্পানিগুলো। দর্শক যদি ক্ষেপে যায়, তবে ব্যবসার কী হবে- সেই জায়গা থেকে। তো সেই হেইস কোডের কারণেই তখনকার আমেরিকান সিনেমায় কৃষ্ণাঙ্গ অভিনেতাদের প্রধানত ছোট, অগুরুত্বপূর্ণ এবং গৎবাধা কিছু চরিত্রে নির্বাচন করা হতো। মোটামুটি পঞ্চাশের দশকের মাঝ থেকে কিংবা শেষের ভাগ থেকে এই নিয়ম ভাঙার একটা বিপ্লবী চেতনার উদ্ভব ঘটে।
কারণ, সিনেমা যে শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয়। নন্দনতত্ত্ব দেখানোর প্রয়োজনীয়তা তো আছে। তবে সমাজকে দেখানোর, প্রতিবাদ করার দরকারটা আরো বেশি আছে। কারণ, এটা যে শিল্পমাধ্যম। আমেরিকান সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তন ঘটে সিনেমার এই দিকগুলোর। শুধু কৃষ্ণাঙ্গ চরিত্রকে প্রধান চরিত্রে নির্বাচনের দিকটিই নয়, গোটা হেইস কোডের কঠোরতাই তখন ভেঙে পড়তে শুরু করে। এবং সেই পরিবর্তনের চিত্রকে ধারণ করে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিনেমা হয়ে উঠেছে অডস্ এগেনস্ট টুমরো।

অডস্ এগেনস্ট টুমরো তার কৃষ্ণাঙ্গ চরিত্রকে যথেষ্ট একাগ্রতা এবং সহমর্মিতা দিয়েই চিত্রিত করে। সিনেমার কেন্দ্রে একটি কৃষ্ণাঙ্গ চরিত্র রাখার সমস্ত সুযোগই এই সিনেমা ব্যবহার করেছে এবং সব কয়টি ফায়দা লুটেছে। দুটো চরিত্র একে অপরকে হেয় করছে, নিন্দা জানাচ্ছে, সুযোগ পেলেই মুষ্টিযুদ্ধে জড়াচ্ছে- দুটি চরিত্রের মধ্যকার দ্বন্দ্ব প্রতিষ্ঠা করতে এই ধরনের সাধারণ অলংকারসমূহ ব্যবহার না করে অডস্ এগেনস্ট টুমরো ব্যবহার করেছে বর্ণ বিভেদ হতে দুটি চরিত্রের মধ্যকার সৃষ্ট উত্তেজনা। এবং বলাই বাহুল্য, একটি ড্রামাটিক ডিভাইস হিসেবে সিনেমার গোটা ন্যারেটিভে এই বর্ণবিদ্বেষের উত্তেজনা আরো সফলভাবে কাজ করেছে। এ কাজে সাধুবাদ প্রাপ্য সিনেমার চিত্রনাট্যকার আব্রাহাম পলনস্কির। নীতিগত দিক থেকে যিনি ছিলেন একজন সমাজতন্ত্রী। বর্ণবিদ্বেষের মুখোমুখি হতে বাধ্য করেছেন তিনি দর্শককে। চরিত্রগুলোতে দিয়েছেন তিনি যথাযথ প্রগাঢ়তা।
চরিত্রগুলোর ব্যক্তিগত জীবন এবং তাদের চারপাশের সমাজব্যবস্থার চিত্রের অভ্যন্তরে যাওয়ার মধ্য দিয়ে ক্রাইম সিনেমার গড়পড়তা সীমানা হতে আলাদা রেখায় অবস্থান করছে অডস্ এগেনস্ট টুমরো। প্রধান তিনটি চরিত্রই সমাজের প্রান্তিক অবস্থাকে সম্মুখে আনে। তবে তিনটি চরিত্রের মাঝে সর্বাপেক্ষা মজার চরিত্র হলো বর্ণবিদ্বেষী স্লেটার। কর্কশ ভাব এবং সৌজন্যের এক অদ্ভুত বৈপরীত্য বহন করে সে। সাথে রবার্ট রায়ানের নিখুঁত অভিনয় আরো উপভোগ্য এবং স্মরণীয় করে তোলে চরিত্রটিকে। শুধু রবার্ট রায়ানই নয়, হেনরি বেলাফন্তে, এড বেগলি, শেলি উইন্টার্স, গ্লোরিয়া গ্রাহাম- প্রত্যেকের অভিনয়শৈলী পূর্ণতা দিয়েছে চরিত্রগুলোয় এবং সতেজ করেছে সিনেমাকে। বুদ্ধিদীপ্ত একঝাঁক অভিনেতা/অভিনেত্রী পাওয়ার সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে। সাথে অন্যান্য গ্রেট নোয়াহ সিনেমার মতোই ছোট ছোট চরিত্রগুলোকেও প্রভাববিস্তারকারী হিসেবে তুলে ধরতে পেরেছে এই সিনেমা।

পরিচালক রবার্ট ওয়াইজ ‘দ্য সাউন্ড অভ মিউজিক’ (১৯৬৫), ‘দ্য হন্টিং’ (১৯৬৩), ‘ওয়েস্ট সাইড স্টোরি’ (১৯৬১), ‘দ্য সেট আপ’ (১৯৪৯)-এর মতো অসাধারণ সব সিনেমা নির্মাণ করেছেন। বিভিন্ন জনরাতেই ক্লাসিক সব সিনেমা উপহার দিয়েছেন। তার সিনেমাগুলো কোনোটা ডকুমেন্টারি না। তবে যখন তিনি রিয়ালিজমকে ধরতে চাইতেন, সিনেম্যাটিক জেল্লাকে অনেকখানি সরিয়েই ডকুর রিয়ালিজমটা তিনি ধরতে চাইতেন যা তার এই সিনেমাতেও আছে। গল্পবয়ানের ক্ষেত্রে এমন চমৎকার ‘লুসিডিটি’ খুব কম ফিল্মমেকারের মধ্যেই পাওয়া যাবে। এটা তার সবচেয়ে দক্ষ দিক। তবে তার মূল কুশলতা ফিল্ম-নোয়াহ জনরাতেই। এবং অডস্ এগেনস্ট টুমরোর বহিঃঅঙ্গে পুরোপুরিই জড়িয়ে আছে ফিল্ম-নোয়াহর ছাপ।
আলো-ছায়ার ব্যঞ্জনা তৈরিতে কিয়ারস্কিউরো লাইটিংয়ের সুনির্দিষ্ট ব্যবহার, চকচকে সাদা-কালো সিনেমাটোগ্রাফি, ডীপ ফোকাস, আয়নায় প্রতিবিম্ব পড়ছে এমন শটের ব্যবহার, অন-লোকেশন শ্যুটিং, বুদ্ধিদীপ্ত এবং স্টাইলিস্টিক সব সংলাপ, উদ্ভাবনী ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল যেগুলো প্রকৃতির দিক থেকে জার্মান এক্সপ্রেশনিজমের অনুপ্রেরণা বহন করে, হোটেল রুম, বার- এমন জায়গাগুলোতে ধারণকৃত দৃশ্যের আধিক্য, অপরাধ বিষয়ক গল্প এবং পৌরুষবোধে ভারী চরিত্র, সর্বোপরি ফিল্ম নোয়াহর সবকটি উপাদানকে নিখুঁত উপায়ে কার্যকর করেছে এই সিনেমা। অধিকন্তু, জন লুইসের আবহসঙ্গীত গা-ছমছমে অনুভূতি জাগায় এবং পাশাপাশি, সিনেমার দৃঢ় প্রকৃতিকে আরো বলিয়ান করে।

অডস্ এগেনস্ট টুমরোর সৌন্দর্যের বড় রহস্য নিহিত এর বিবরণের ধারা এবং নিখুঁত সেটপিসের উপর। সূক্ষ্ম প্রভেদকেও গুরুত্ব দেওয়াই বোধকরি সেই রহস্যের মূল কারণ। আর, বিষয়ের দিক হতে গুরুত্ব তো বহন করছেই এই সিনেমা। শৈল্পিক আঙ্গিকের দিক থেকে যতটা বিমুগ্ধকারী, প্রতিবাদী বক্তব্যের দিক থেকে ততটাই সাহসী।



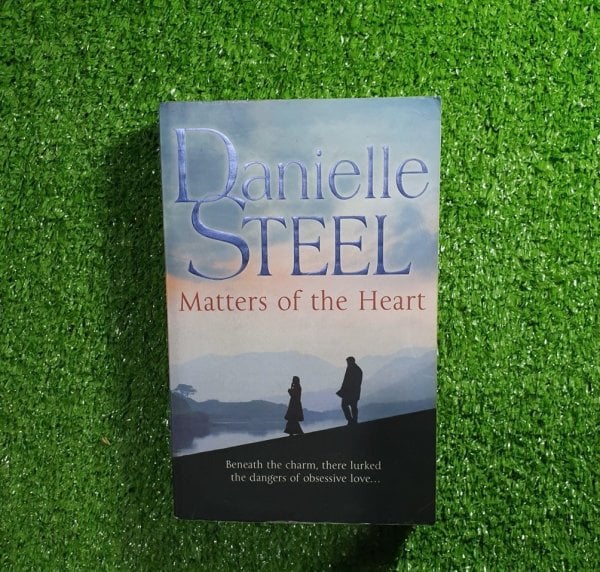

.jpg?w=600)

