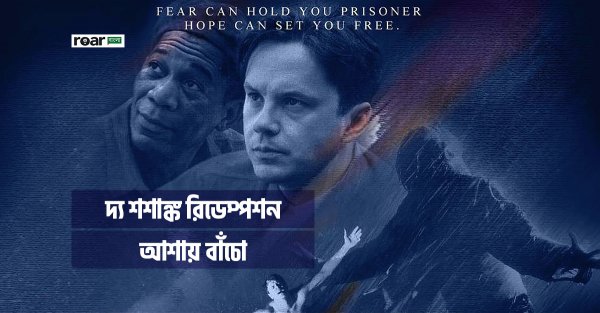ব্লাড অ্যালকোহল কনসেন্ট্রেশন বা সংক্ষেপে ব্যাক লেভেল হলো, মানবদেহের যে পরিমাণ রক্ত অ্যালকোহল দ্বারা ঘনীভূত থাকে। এই লেভেল অনুযায়ী মানবদেহের প্রতি ১০০ মিলিলিটার রক্তপ্রবাহে থাকে ০.০৫ শতাংশ অ্যালকোহল। এ তত্ত্ব প্রদান করেন মনোবিজ্ঞানী ফিন স্কারদেরুদ। তার মতে, রক্তে অ্যালকোহলের পরিমাণ যদি এই নির্দিষ্ট পরিমাণ ধরে রাখা যায়, তাহলে কাজের সাধারণ গতি আরো বৃদ্ধি পাবে। মানসিক স্বাস্থ্য ত্বরান্বিত হবে। সবকিছুতে থাকবে প্রাণোচ্ছলতা। একথার পিঠেই জুড়ে দেওয়া যায় বিখ্যাত উপন্যাস ‘আ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস’-এ লেখা আর্নেস্ট হেমিংওয়ে’র একটি লাইন,
“ওয়াইন হলো চমৎকার জিনিস। একেবারে ঐশ্বর্যমণ্ডিত। এটি মুছে দিতে পারে তোমার সাথে ঘটে যাওয়া সকল খারাপ ঘটনা।”
হেমিংওয়ে যে অতিরিক্ত মদ্যপান করতেন, তা তো জানবেন তার ভক্তকূল। তাই এ সিনেমাতেও তাকে স্মরণ করা হয় বিশেষভাবে। কারণ মদই যে এই সিনেমার প্রাণকেন্দ্র!
সে-যোগ ব্যতিরেকে এই সিনেমার প্রারম্ভিক দৃশ্যটিও যদি দেখা হয় যেখানে, কলেজপড়ুয়া সকল ছাত্রছাত্রীরা বিয়ারের কেইস হাতে নিয়ে দৌড়ানোর আর পান করার এক ঐতিহ্যবাহী প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করেছে। বিয়ার খেতে খেতে তাদের উল্লাস, উদযাপনে মুখরিত সবকিছু। তারপরই হঠাৎ করে সব কোলাহল থেমে যায়। ব্ল্যাক স্ক্রিনে ভেসে বেড়ায় টাইটেল আর ব্যাকগ্রাউন্ডে গ্লাসে মদ ঢালার শব্দ। এই গোটা দৃশ্যটিই সিনেমার কেন্দ্রের বিষয়টিকে গভীরভাবে অঙ্গীভূত করে, যেমন করে রক্তপ্রবাহে মিশে থাকে ০.০৫ শতাংশ অ্যালকোহল।
সিনেমার মুখপাত্ররা সকলেই শিক্ষক। কেউ ইতিহাসের, কেউ মনোবিজ্ঞানের, কেউ গানের আর কেউ ক্রীড়ার। তাদেরই গল্প ‘অ্যানাদার রাউন্ড’। প্রথম দৃশ্যের তারুণ্যের জোয়ার মূলত পরের দৃশ্যে এই মুখপাত্রদের মধ্যবয়সের নির্জীবতার সাথে বৈপরীত্য আনে উপস্থাপনের জন্যই। এদের মুখখানার দিকে তাকালে মনে হয়, জীবনের সকল রস যেন যুবক বয়সেই নিঃশেষিত হয়েছে। জীবনটা টেনে নিতে হবে বলেই টেনে নেওয়া, এমনটাই ভাব। তাদের সকল কাজের মধ্যেই মিশে আছে নিরানন্দ অনুভূতি, যা প্রকটভাবে ধরা পড়ে মার্টিনের ক্ষেত্রে। সে এ সিনেমার ‘বিগ শট’। এ দোলাচলে দুলছে যখন জীবন, তখন বাতাসটার বিপরীতমুখী আভাস প্রথম পাওয়া যায় নিকোলাইয়ের ৪০তম জন্মদিন উদযাপনের আসরে।

Image Source: Nordisk Film
উদযাপনে ‘উদ’ আর কই, কোনোভাবে যাপনই সার। সে রাতেই মনোবিজ্ঞানের শিক্ষক বন্ধুর হাত ধরে ফিন স্কারদেরুদের সেই থিওরির কথা উঠে এল। সব হারানো মানুষ যেমন খড়কুটো আঁকড়ে বাঁচতে চায়, তেমনি চল্লিশে পা দেওয়া এই চার বন্ধুও তাদের একঘেয়ে জীবনের অবসাদ দূর করতে ভাবল, ওই তত্ত্ব একবার অ্যাপ্লাই করে দেখতে ক্ষতি কি! ব্যস, পরদিনই বসে গেল চারজনে।
কিছুটা তত্ত্ব, বাকিটা ইন্টারনেট ঘেঁটে দাঁড় করানো হাইপোথিসিস। দুয়ে মিলে দাঁড়ালো এক সুডো-সায়েন্টিফিক তত্ত্ব। তারা সারাদিনেই বিরতি দিয়ে দিয়ে পান করে রক্তে অ্যালকোহলের লেভেল ০.০৫ শতাংশ ধরে রাখবে। সারাদিনে হবে এমন, তবে রাত্রি ৮টা হলেই ও-জিনিস ছুঁলে পাপ আর শাপ দুটোই লাগবে। দেখা যাক না, সবকিছুতে একটা প্রাণোচ্ছলতা আসে কি না।
হ্যা, সত্যিই এসেছে। মার্টিন, যার কিনা ইতিহাস পড়ানোতে নেই বিন্দুমাত্র মনোযোগ, এই নিরীক্ষার পরদিনই তার মাঝে হারানো তেজ ফিরল যেন। সে হাসছে, দেহটাকে নাড়ছে দ্রুত, ছাত্রছাত্রীদের করছে অবাক। ইতিহাসের পাঠ দিচ্ছে হেমিংওয়ে, ক্লিনটন, চার্চিলদের মদপ্রীতির উদাহারণ দিয়ে! সংসারজীবনে আগের মতো আবার খেয়ালী হয়েছে। স্ত্রী, সন্তানদের নিয়ে ট্যুর দিতে চাইছে! বয়স যেন তার, উল্টোরথে কুড়ি ছুঁয়েছে।
বাকিদেরও ফলাফল কান অব্দি পৌঁছানো হাসি। কারো আঙুল কিবোর্ডে উড়ে চলেছে, কেউ খেলার মাঠে একাই দাপিয়ে বেড়ানোর শক্তি ফিরে পেয়েছে। থিওরি তাদের ক্ষেত্রে সত্য প্রমাণিত হলো। কিন্তু তার স্থায়িত্বকাল? কোনোকিছুই যে চিরকালের নয়। শীঘ্রই বদলাবে চাল। ভাঙছে কার ঘর? মদ পান করা যায়, কিন্তু সমস্যা তো পান করা যায় না। ক্ষণিকের ভুলে থাকা যে সমাধান নয়। বাস্তবের ঘা’টা যে মর্মান্তিকই হয়।
অ্যানাদার রাউন্ডের পরিচালক থমাস ভিন্টারবার্গ হলেন ডেনমার্কের ‘ডগমি ৯৫’ ফিল্মমেকিং মুভমেন্টের নেপথ্যের প্রধান ব্যক্তিত্ব। তিনি আর লার্স ভন ত্রিয়ার মিলেই ৯৫ সালে শুরু করেন এই মুভমেন্ট। তৈরি করেন সব নিয়মাবলী এবং এই মুভমেন্টের লক্ষ্য। ভিজ্যুয়াল ইফেক্টস, চটকদার এবং ব্যয়বহুল প্রযুক্তি বাদ দিয়ে ডেনমার্কের সিনেমাকে একদম ‘বিশুদ্ধ’ রূপ দেওয়ার লক্ষ্যেই এ আন্দোলনের সৃষ্টি। রিয়েল লোকেশন, হ্যান্ডহেল্ড ক্যামেরা, প্রপ্স বর্জন, ন্যাচারাল লাইট; সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত ছিল এ আন্দোলনের নিয়মাবলীতে। ২০০৫ অব্দি ছিল এর স্থায়িত্বকাল।
আন্দোলনের দুই প্রবাদপুরুষ ভিন্টারবার্গ এবং ভন ত্রিয়ার নানান নিরীক্ষা চালালেও ডগমি ৯৫-এর মূল লক্ষ্য, সিনেমাকে তার বিশুদ্ধ রূপ ফিরিয়ে দেওয়া, তা থেকে পিছু হটেননি। নিয়মগুলোকে নানাভাবে ব্যবহার করেছেন এবং করছেন তারা। এ সিনেমায় এসেও তা লক্ষণীয়। মূলত এ জায়গায় আসতেই একটু অতীতকে সাথে রাখা বা ইতিহাসের শেকড়ে যাওয়া।
‘অ্যানাদার রাউন্ড’ পরিচালকের সবচেয়ে ‘পার্সোনাল’ সিনেমা। কারণ, এ সিনেমার সাথে যে জড়িয়ে আছে ভিন্টারবার্গের জীবনের সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা। সিনেমার একটি চরিত্রে অভিনয় করার কথা ছিল তার মেয়ে ইডার। চিত্রনাট্য দারুণ পছন্দ হয়েছিল মেয়ের। বাবার উদ্যমটাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল মেয়ের আগ্রহ। কিন্তু সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায় ১৯ বছর বয়সী ইডা। মারাত্মক জখম তার সাবেক স্ত্রী। অপরদিক থেকে আসা গাড়ির ড্রাইভারের ফোনালাপে মগ্ন হয়ে অসতর্ক চালনায় ঝরে যায় এই তাজা প্রাণ। তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে যায় এ সিনেমা নিয়ে শ্যুটে যাবার পরিকল্পনা। কিন্তু মেয়ের স্মৃতি আর উচ্ছ্বাস রক্ষার্থেই মাঠে গড়ায় ‘অ্যানাদার রাউন্ড’।
চিত্রনাট্য হয়ে ওঠে আরো নাটকীয়। এবং সিনেমার সূক্ষ্মটোনে পরিচালকের ব্যক্তিজীবন থেকেই আসা একটা বিষাদের সুর সবসময় বেজে যায়। চার বন্ধু যখন বিচ্ছিন্নভাবে নিজেদের রোজকার জীবনের সাথে তাল মেলায়, তখন সেখানে জড়িয়ে থাকা মলিনতা, হতাশা যেন সেই বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই আরো অভিঘাতী হয়ে ওঠে।

Image Source: Nordisk Film
ভিন্টারবার্গের এ সিনেমায় সচরাচরের তুলনায় তিন অঙ্কের উপস্থিতিটা খুব স্পষ্ট হয়ে নজরে আসে। প্রথম অঙ্ক চার বন্ধুর নিরীক্ষা এবং সফলতায় সকলের দিলখোলা উচ্ছ্বাস আর কমনীয় মুহূর্ত দিয়ে ভরা। দ্বিতীয় অঙ্ক এই মদ পানের লেভেল ০.১ শতাংশে নিয়ে যাওয়ার ফলে পরিবর্তিত পরিস্থিতির চিত্রবর্ণনা। এবং এরপর আসে শেষ অঙ্ক, যেখানে আছে ঝড়; বিষাদ এবং জীবনের অমসৃণ পথকে চিনে নিয়ে আপন করার গল্প। তিনটি অঙ্কেই ভিন্টারবার্গের টাচটা সূক্ষ্ম, সংবেদী এবং অভিনেতাদের পরিচালনার মাঝে নিহিত। প্রত্যেকের সুদক্ষ অভিনয়, ভিন্টারবার্গ আর লিন্ডহোমের তেরছা রসবোধ আর নিগূঢ় শোকের এ চিত্রনাট্যে জীবন দিয়েছে।
হাসি থেকে কান্নার, গোটা আবেগের গ্যামাটটাই অভিনেতারা সম্পন্ন করেছেন। অবশ্যই কথা আসবে, ম্যাডস মিকেলসেনের। এর আগে ‘দ্য হান্ট’ (২০১২) সিনেমায় এ অভিনেতা আর পরিচালকের অনবদ্য জুটি দর্শক দেখেছে। মিকেলসেনের অভিনয় এ সিনেমায় রীতিমতো দুর্দমনীয়। তার শরীরি অভিনয়ই একটা আলাদা শক্তি এনে দেয় চরিত্রটির মাঝে। অনেকটা ব্যালে নৃত্য আর রক গানে উন্মত্ত হবার মাঝামাঝি পর্যায়ে দুলে চলে তার শরীর, যার ফলে গোটা পরিবেশটাই আলাদাভাবে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। তার বলার ভঙ্গীতে মিশে আছে সম্মোহনী ক্ষমতা। তাই আশপাশের সবকিছু আরেকটু বেশি মনোযোগী হয়।

Image Source: Nordisk Film
সিনেমার কেন্দ্রবিন্দু অ্যালকোহল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হলেও, ন্যারেটিভ কিন্তু ওটা দ্বারা চালিত হয়নি। ন্যারেটিভ চালিত হয়েছে চার বন্ধুর ক্রাইসিস দ্বারাই। কোনো অবস্থাতেই মদ কোনোকিছুর সমাধান হতে পারে না। এটা হলো অ্যানাদার রাউন্ডের বক্তব্যের জায়গা, যেখানে পৌঁছাতে নীতিকথার প্রপাত ঝরাতে হয়নি। এবং এ জায়গাতেই এ সিনেমার সবচেয়ে বড় সাহস লুকিয়ে আছে। গড়পড়তা নৈতিক শিক্ষায় যেমন ভারি এই সিনেমা হয়নি, তেমনি মদ্যপানকে গ্লোরিফাই করারও চেষ্টা করেনি। এটা অনুসন্ধান চালিয়েছে মদ্যপানের পেছনের কারণে। চালিয়েছে মানুষের প্রকৃতিতে, যেমনটা পরিচালকের বাকি সিনেমাগুলোও করে থাকে।
আর তেমনটি করতে গিয়ে সঠিক ঘটনাদির সঠিক ভিজ্যুয়াল ভাষাটাই দাঁড় করিয়েছে এনাদার রাউন্ড। ওয়ার্ম লাইট ব্যবহার করে মদপানের পর চরিত্রদের আশপাশটা যেমন উজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে, অন্তত চরিত্রদের মনস্তত্ত্বে তা-ই ঘটছে, সেটি প্রকাশ করা হয়েছে। আবার সেই লাইটিং সেটআপে পিওভি শট নিয়ে মদ্যপানের পর চরিত্রদের পরিবর্তনটা একদম দৃঢ়চেতাভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ক্লোজআপ শটগুলোতে ক্যামেরা স্থির না রেখে ম্যাডস মিকেলসেনের নেচে নেচে চলার মতো ভাইবটাও ক্যামেরায় রাখা হয়েছে। এতে করে চরিত্রদের অবস্থা অনুযায়ী ক্লোজ-আপগুলো হয়ে উঠেছে অমোঘ। সম্পাদনায় একটা ফ্লারিশ’নেস জড়িয়ে ছিল গোটা সময়টাতেই। বলতে হয়, ভিন্টারবার্গের ফিল্মমেকিং এখানে একইসাথে শৈল্পিক এবং জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

Image Source: Nordisk Film
‘অ্যানাদার রাউন্ড’ কোনো সাবধানী সাইনবোর্ড বা ঈশপের গল্প নয়। ‘অ্যানাদার রাউন্ড’ হলো একটা ব্যক্তিগত সফর, যাতে আছে হতাশা; যাতে আছে আনন্দ; যাতে আছে বিষাদ এবং শেষ দৃশ্য অনুযায়ী, যাতে আছে ঘুরে দাঁড়াবার মন্ত্র।