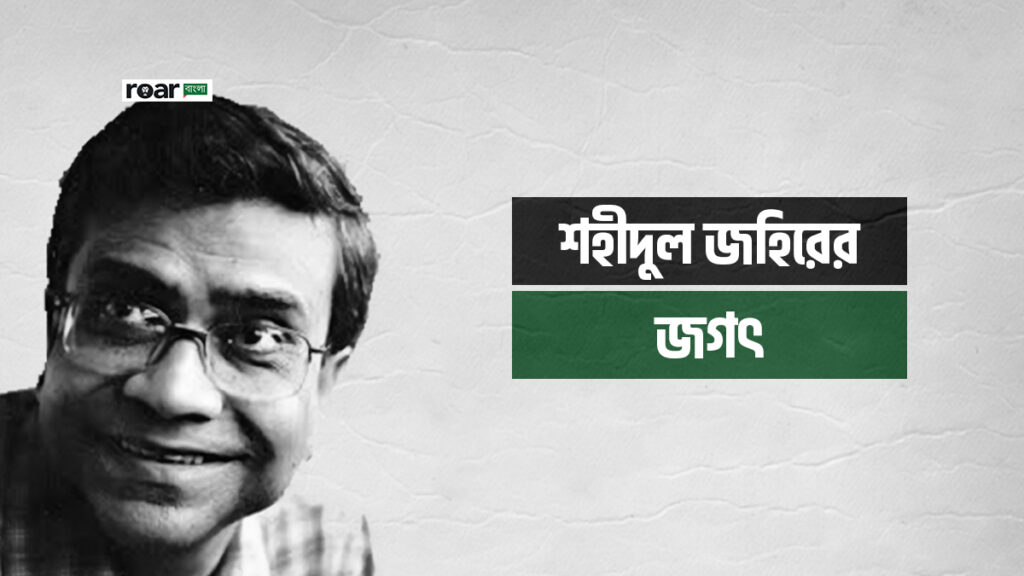‘Wars, conflict- it’s all business. One murder makes a villain, millions a hero. Numbers sanctify, my good fellow!’
মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার ঠিক আগে সেলে আগত সাংবাদিককে তৎকালীন বিশ্ব-রাজনীতির স্বরূপটি এই সামান্য কয়েকটা কথায় খুব সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দেয় আসামী অঁরি ভের্দু।
স্থায়ী চাকরি খুইয়ে প্রতিবন্ধী স্ত্রী ও পুত্রের ভরণপোষণের জন্য সে বাধ্য হয়েই বেছে নিয়েছিল এক জঘন্য অপরাধের পেশা। বিত্তবান বিধবা মহিলাদের ঠকিয়ে বিয়ে করার পর তাদের হত্যা করে সমস্ত অর্থ আত্মসাৎ করত সে। তারপর যুদ্ধের প্রাক্কালে অর্থনীতিতে ধস নামলে নিজেকেই ধরিয়ে দেয় রাষ্ট্রের কাছে।
মৃত্যুদণ্ডের সাজা ঘোষণা তাকে খুব একটা বিচলিত করেনি। ভের্দু মেনে নিয়েছিল তার অপরাধ। কিন্তু এজলাসে দাঁড়িয়ে এই ভের্দুই হাসতে হাসতে বলে যায়, সমকালীন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে যেখানে রাষ্ট্রনায়করাই হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী, সেখানে সে তো নেহাতই ছেলেমানুষ।
চার্লি চ্যাপলিনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি ‘মসিয়েঁ ভের্দু’র একদম শেষ পর্বে মুখ্য ভিলেন চরিত্রটির এমন অ্যান্টি-হিরোর পর্যায়ে উত্তরণেই যেন লুকিয়ে ছিল চ্যাপলিনের নিজস্ব সমাজচেতনার মূল সুর।

ভের্দুর কাহিনীর সময়কাল ছিল তিরিশের দশকের মাঝামাঝি সময়। অর্থাৎ, বিশ্বযুদ্ধ তখনও শুরু হয়নি, কিন্তু তার জ্বলন্ত ম্যাগমার আঁচ টের পাওয়া যাচ্ছে ব্যাপক অর্থে।
হিটলার-মুসোলিনি-ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিবাদী আস্ফালন সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে শক্তিধর ব্রিটিশ ও ফরাসি সাম্রাজ্য। যাদের ঔপনিবেশিক শোষণ একসময় নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে নব-আবিষ্কৃত ভূখণ্ডের বহু জাতিকে, তারাই এরপর মানবতা-রক্ষার দোহাই দিয়ে হিটলারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামবে। এবং ঠিক এখানেই চ্যাপলিনের মুখ দিয়ে বলা ভের্দুর কালজয়ী সংলাপটির যথার্থতা খুব সহজেই অনুধাবন করা যায়।
নায়ক কে, আর খলনায়কই বা কে, যুদ্ধের সময়ে দাঁড়িয়ে এ কথা একবাক্যে বলা একপ্রকার একমুখিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। ‘সেভিং প্রাইভেট রায়ান’ বানানোর সময়ে পরিচালক স্টিফেন স্পিলবার্গ বলেছিলেন, পৃথিবীর গত একশো বছরের ইতিহাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো ভয়ঙ্কর অথচ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আর ঘটেনি। আসলে, একাধিক পরস্পর-বিরোধী দিকগুলোই তো চালিত করে যুদ্ধ-রাজনীতির গতিপ্রকৃতিকে।
জয়ী পক্ষের দৃষ্টিকোণ থেকে খলনায়ক অবশ্যই অ্যাডলফ হিটলার। মানবিকতার প্রেক্ষিতেও বারো বছরের শাসনকালে অন্তত দু’কোটি মানুষকে নির্বিচারে হত্যার দায় তিনি এড়াতে পারেন না কোনোভাবেই।
কিন্তু এই দুই দৃষ্টিভঙ্গিকে সরিয়ে রেখে আমরা যদি শুধুমাত্র নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে কেবল মানুষ হিটলারকে বিচার করতে বসি, তাহলে তাকে কীরূপে পেতে পারি? একজন নিষ্ঠুর মানুষের মনেও কি সংবেদনশীলতা, ভালোবাসা এসব সূক্ষ্ম অনুভূতি বিচরণ করে, নাকি তার সমস্তটাই এক শীতল কাঠিন্যে আচ্ছাদিত?
২০০৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত জার্মান চিত্র-পরিচালক অলিভার হার্শবিগেলের ‘দের উন্টারগাং’ বা ‘দ্য ডাউনফল’ ছবির দৃশ্যায়ণ যেন এই অমোঘ প্রশ্নেরই পরিচায়ক।
জার্মান সাংবাদিক ও লেখক জোয়াকিম ফেস্টের লেখা ‘ইনসাইড হিটলার’স বাঙ্কার: দ্য লাস্ট ডেজ অফ দ্য থার্ড রাইখ’ এবং খোদ হিটলারের শেষ ব্যক্তিগত মহিলা সচিব ট্রডল জুঙ্গের স্মৃতিকথা ‘আন্টিল দ্য ফাইনাল আওয়ার’, এই দুটি বইয়ের উপর ভিত্তি করে বানানো হয়েছিল সিনেমাটি।

ছবির শুরু হচ্ছে ১৯৪২ এর নভেম্বরের কনকনে শীতের রাতে পূর্ব প্রাশিয়ার জঙ্গলে হিটলারের সদর দপ্তর উলফ’স লেয়ারে। পাঁচজন আগত তরুণীর মধ্যে থেকে ট্রডল হাম্পসকে (পরে এসএস অফিসার হ্যান্স হার্ম্যান জুঙ্গেকে বিয়ে করার পর নামের পাশে জুঙ্গে পদবী বসে) নিজের সচিব নির্বাচিত করলেন স্বয়ং ফ্যুয়েরার।
তিনিও হিটলারের প্রিয় শহর মিউনিখের বাসিন্দা শুনে হিটলার উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। টাইপিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে হিটলার তাকে সচিব হিসাবে নির্বাচিত করলেন।
ছবির দৃশ্য এরপরেই এগিয়ে আসছে আরও আড়াই বছর। ১৯৪৫ সালের ২০শে এপ্রিল। সেদিনই ছাপ্পান্ন পূর্ণ করছেন হিটলার। মিত্রবাহিনীর হানায় প্রায় বিধ্বস্ত হয়ে গেছে বার্লিন। যখন তখন অতর্কিতে বোমাবর্ষণ করছে বোমারু বিমান। খবর এসেছে, বার্লিন সিটি সেন্টার থেকে রাশিয়ান সেনাবাহিনী আর মাত্র ১২ কিলোমিটার দূরে।
এই খবর জেনে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন ফ্যুয়েরার। অকারণে তীব্র গালিগালাজ করছেন কার্ল কোলার-সহ অন্যান্য নাৎসি উচ্চপদস্থ অফিসারদের। জন্মদিনের আনন্দ তো দূর, যে জার্মানিকে খুব অল্প দিনের মধ্যেই বিশ্বশ্রেষ্ঠ করে তুলবেন বলে ভেবেছিলেন, সেই জার্মানিরই ধ্বংসের নিয়তি আসন্ন দেখে তখন দিশেহারা পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম নিষ্ঠুর একনায়কটি। বাঙ্কারে থাকা সমস্ত মানুষই তখন আতঙ্কের প্রহর গুনছে।

এসএস সুপ্রিম কম্যান্ডার হেইনরিখ হিমলার (উলরিখ নোথেন), তার ডেপুটি কম্যান্ডার হার্ম্যান ফেগেলিন (থমাস ত্রেৎশম্যান) সকলেই তখন বার্লিন ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবছেন। তাদের ইচ্ছে, হিটলারও তাদের সঙ্গে একমত হোন।
মিত্রবাহিনীর সঙ্গে সমঝোতার রাজনীতিই যে এখন একমাত্র বাঁচার উপায়, সেকথা হিটলারকে বললে তিনি সাফ জানিয়ে দেন, রাজনীতিটা আর তার করার ইচ্ছা নেই। তাদের যদি রাজনীতি করতেই হয়, তবে তা যেন তার মৃত্যুর পর তারা করে। জীবন থাকতেও শত্রুর সঙ্গে সমঝোতায় আসার কথা ভাবতে পারেন না ফ্যুয়েরার।
একের পর এক মন্ত্রী অফিসাররা বার্লিন ছেড়ে চলে যাচ্ছে, ফ্যুয়েরার বুঝছেন তিনি ক্রমশ একা হয়ে পড়ছেন। কিন্তু, চূড়ান্ত পরাজয়ের মুখে দাঁড়িয়েও তার ঐ চিরকালীন অহংকারটি বজায় ছিল পুরোমাত্রায়। সিনেমার পরতে পরতে হিটলারের মানসিক অস্থিরতার দৃশ্যগুলো খুব নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন পরিচালক।
‘জিতব নাহয় মরব’ এমন নাছোড় মনোভাবের আড়ালে পুরোদস্তুর ভেঙে পড়া এক দোর্দণ্ডপ্রতাপের শেষ মুহূর্তের পরিস্ফুটনে যেন কর্মফলের অমোঘ নিয়তিই মূর্ত হয়ে ওঠে।
নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার মরিয়া চেষ্টায় তখন চূড়ান্ত খামখেয়ালিপনা শুরু করেছেন অ্যাডলফ হিটলার। মিত্রশক্তির হাতে পড়ার আগে নাৎসি জার্মানির সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো ধ্বংস করে ফেলার নির্দেশ দিলেন অস্ত্র ও সম্পদমন্ত্রী অ্যালবার্ট স্পিয়ারকে (হেইনো ফার্শ)।
কিন্তু এই কাজ করলে অসংখ্য সাধারণ জার্মান মানুষের মৃত্যু হতে পারে একথা হিটলারকে স্পিয়ার বললে হিটলার বর্বরের মতো জবাব দেন, দুর্বল মানুষদের মরাই ভাল!
রাশিয়ানদের আক্রমণে এসএস বাহিনী তখন কোণঠাসা, এমন অবস্থাতেও কম্যান্ডার ফেলিক্স স্টেইনারকে হিটলার নির্দেশ দিলেন পাল্টা-আক্রমণের। কিন্তু আবেগ এক দিকে, আর যৌক্তিক বাস্তবতা অন্যদিকে। হিটলারের নির্দেশ অমান্য করে বার্লিন ছেড়ে চলে গেলেন অ্যালবার্ট স্পিয়ার। স্টেইনারের বাহিনীরও পতন ঘটল রাশিয়ানদের হাতে। ক্ষমতাগর্বী হিটলার অবশ্য এই কাজকে বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছুই ভাবলেন না।

প্রোপাগান্ডা মন্ত্রী হার্ম্যান গোরিং (মাথিয়াস নাদিংগার) সর্বময় নেতৃত্ব দাবী করলে তাকে সমস্ত দায়িত্ব থেকে সরিয়ে হত্যার আদেশ দিলেন হিটলার। হিমলার মিত্রপক্ষের সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা করলে তাকেও ঐ একই শাস্তি দেওয়ার নির্দেশ এল ফ্যুয়েরারের কাছ থেকে।
গোরিং-হিমলাররা বেঁচে গেলেও বাঁচলেন না ফেগেলিন। হিমলারের সঙ্গে ‘ষড়যন্ত্রে’র অপরাধে তাকে গুলি করে মারা হলো। ফেগেলিন সম্পর্কে ছিলেন হিটলারের প্রেমিকা ইভা ব্রাউনের (জুলিয়েন কোহ্লার) বোন মার্গারেটের স্বামী। ইভার অনুরোধেও একবিন্দু টলল না মৃত্যুদণ্ডের আদেশ। আসলে, সমস্ত কাছের মানুষকেই তখন শত্রু বলে মনে হচ্ছে ফ্যুয়েরারের।

কিন্তু আবার একই সময়ে সচিব ট্রডল জুঙ্গে বা পোষা জার্মান শেফার্ড ব্লন্ডির প্রতি হিটলারের স্নেহপরায়ণতা এক অদ্ভুত বৈপরীত্যের জন্ম দেয়। ট্রডল পরবর্তীকালে সাক্ষাৎকার ও স্মৃতিকথায় বলেছিলেন, নাৎসিদের ঘৃণ্য বাস্তব সম্পর্কে তিনি তেমন অবগত ছিলেন না। তার কাজ ছিল টাইপিস্টের। হিটলারের পিতৃতুল্য ব্যবহার ও ক্যারিশমা তাকে মানুষটির প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু আসল সত্য ঘটনা জানলে তিনি কখনোই হিটলারের জন্য কাজ করতে যেতেন না!
কিন্তু যে ‘ঘৃণ্য বাস্তবে’র সঙ্গে তখন সমস্ত বিশ্বই ওয়াকিবহাল, খোদ হিটলারের কর্মী হয়ে ট্রডল একথা জানতেন না, এমনটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবে তার কথায় হিটলারের সম্পর্কে এই ধারণা খুব স্পষ্ট হয় যে, খর্বকায় মাছি গোঁফ-ধারী মানুষটি সকলের কাছে নৃশংসতার নামান্তর হয়ে দেখা দেননি।

হিটলারের এমন একগুঁয়েমির সামনে দাঁড়িয়ে তার পারিষদবর্গও তখন দিশেহারা। হিমলার-স্পিয়ারের মতো অনেকেই পালিয়ে গিয়েছিলেন বার্লিন ছেড়ে। নিজের পরিবারের কথা ভেবে তাদের নিয়ে পালাতে চেয়েছিলেন এসএস বাহিনীর ডাক্তার আর্ন্সট-রবার্ট গ্রাউইৎজও (ক্রিশ্চিয়ান হোনিং)। কিন্তু হিটলার তাকে সেই অনুমতি দেননি।
রুশদের হাতে ধরা পড়লে চরম লাঞ্ছনা অপেক্ষা করছে, জানতেন তিনি। ব্যাবেলসবার্গে নিজের বাড়িতে এক রবিবারে পরিবারের সকলের সঙ্গে নৈশভোজে বসেছিলেন তিনি। পরিবারের কেউ তখনও জানে না, কী পরিকল্পনা করেছেন গৃহকর্তা। কিছুক্ষণ পরেই তীব্র বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল গ্রাউইৎজ ম্যানসন। অন্ধ জাতীয়তাবাদ বোধহয় এমনই দুঃসহ ঘটনার জন্ম দিয়ে যায়, বারবার।

নাৎসি পার্টির আরও একজন ডাক্তার আর্ন্সট-গুন্টার শেঙ্ক অবশ্য পালাতে চাননি আহত সৈনিক ও শহরবাসীর কথা ভেবে। তবে জাতিপ্রেম অন্ধত্বের সবচেয়ে করুণ আখ্যানটি লিখে গিয়েছিল গোয়েবেলস পরিবার। হিটলারের খাস অনুচরদের একজন ছিলেন জোসেফ গোয়েবেলস (উলরিখ ম্যাথেস)। স্বামীর মতোই স্ত্রী মাগদাও হিটলার তথা নাৎসিবাদের পরম ভক্ত। পরাজয় নিশ্চিত জেনে সর্বহারা হিটলার যখন আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন, তাকে অনুসরণ করতে চাইলেন গোয়েবেলসরাও। এমনকি মৃত্যুর আগে নিজেদের ছয় সন্তানকেও হত্যা করার পরিকল্পনা নিলেন তারা।

ছবিতে একপর্যায়ে দেখা যায়, হ্যামবার্গ চলে যাওয়ার আগে অ্যালবার্ট স্পিয়ার যখন মাগদা গোয়েবেলসের সঙ্গে দেখা করতে আসেন, তখন এই প্রাণঘাতী পরিকল্পনা থেকে অন্তত ছোট বাচ্চাগুলোকে রেহাই দেওয়ার জন্য মাগদাকে অনুরোধ করেন। মাগদা তাকে বলেন, যেখানে ন্যাশনাল সোশ্যালিজমই আর থাকবে না, সেখানে বাচ্চাদের আর কোনো ভবিষ্যৎ নেই!
অন্ধ জাতিপ্রেম কোন পর্যায়ে গেলে এক মায়ের কাছে সন্তানের চেয়েও বড় হয়ে ওঠে জাত্যাভিমান, তা বোধহয় এই একটি দৃশ্যেই জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যায়।
এবং শেষপর্যন্ত, ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ছয় সন্তানকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়ার পর তাদের মুখে যখন এক এক করে সায়ানাইড ক্যাপসুল তুলে দিচ্ছেন মাগদা, তখন বিরাজ করছে এক অদ্ভুত শান্তি! ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে তাদের বাবা জোসেফ। সিনেমার সবচেয়ে করুণ অধ্যায়টি রচিত হয়ে যায় মাগদার ভূমিকায় করিন্না হারফশের কুশলী অভিনয়ের মুন্সিয়ানায়।

হিটলারের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন স্যুইস অভিনেতা ব্রুনো গাঞ্জ। ৫৬ বছর বয়সী হিটলারের চরিত্রায়ণে ৬৩ বছর বয়সী ব্রুনোকে একটু বেশিই বয়স্ক দেখিয়েছিল। তবে সেই খামতি ঢেকে দিয়েছিলেন অনবদ্য অভিনয়ে।
চরিত্রটি নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলতে প্রচুর পড়াশোনা করেছিলেন স্যুইস তারকা। হিটলারের অসহায় ক্রোধ, দুঃখ, পরাজয়ের গ্লানি, ভঙ্গুর অভিব্যক্তির নিখুঁত পরিস্ফুটন করেছিলেন ব্রুনো।
ওদিকে যুদ্ধের পরিস্থিতিতে চোখে-মুখে সদা-আতঙ্কের ছাপ নিয়ে ঘুরে বেড়ানো এক যুবতীর ভূমিকায় দারুণভাবে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিলেন ট্রডল জুঙ্গের ভূমিকায় অভিনয় করা আলেকজান্দ্রা মারিয়া লারাও।

মুক্তির পর ছবিতে হিটলারের চিত্রায়ণ নিয়ে তীব্র বিতর্ক হয়েছিল খোদ জার্মানিতেই। ‘দ্য ব্লিড’, ‘দের স্পাইগেল’, ‘দের ট্যাগেসস্পাইগেল’, ‘ডাই ট্যাগেসজেইতুং’-এর মতো প্রথম সারির সংবাদপত্রে তীব্র সমালোচিত হন ছবির নির্মাতারা।
নিউ ইয়র্ক টাইমসের চলচ্চিত্র-সমালোচক অ্যান্টনি অলিভার স্কট লিখেছেন, হিটলার এবং গোয়েবেলস ছাড়া অন্যান্য নাৎসি অফিসারদেরও তেমন নিষ্ঠুরভাবে দেখানো হয়নি ছবিতে। বিশেষত, জেনারেল উইলহেল্ম মঙ্কে বা প্রফেসর শেঙ্ককে যেভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে, তা যেন খানিক সহানুভূতি আদায়ের জন্যই, এমনটাই মনে করেছেন বর্তমান প্রজন্মের জার্মান দর্শকগণ, যারা নিজেদের দেশের এই অন্ধকার অধ্যায়টিকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করে থাকেন।
‘দ্য ডাউনফল’-এর আগে হিটলারের শেষ ক’টা দিন নিয়ে যেসব ছবি বানানো হয়েছিল, যেমন ব্রিটেন-ইতালির যৌথ প্রযোজনায় ১৯৭৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘হিটলার: দ্য লাস্ট টেন ডেজ’ বা ১৯৮১ সালে মার্কিন টেলিভিশনের জন্য বানানো ছবি ‘দ্য বাঙ্কার’ যেখানে হিটলারের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন প্রখ্যাত অভিনেতা অ্যান্টনি হপকিন্স, সেই ছবিগুলির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পুরোপুরিই বিজয়ী পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি। সেখানে হিটলারকে অমানবিক হিসাবে দেখানোটাই দস্তুর। কিন্তু ‘দ্য ডাউনফল’ সার্বিকভাবেই জার্মানে বানানো ছবি।

এখানে অতি সচেতনভাবে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে হিটলারকে দেখানোর ব্যাপারে এই ছবির চিত্রনাট্যকার ও প্রযোজক বার্ন্ড এইশিংগার বলেছিলেন, নাৎসি যুগ যারা প্রত্যক্ষ করেছেন, তাদের মধ্যে স্পষ্টত দুটো ভাগ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এক দল মনে করত, হিটলার চরম ভুল ছিলেন, আরেক দল একদম উল্টো, তারা বরং সময়ে সময়ে যারা নাৎসিবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন, তাদের বিশ্বাসঘাতক ছাড়া আর কিছু মনে করত না।
ঠিক তার পরের প্রজন্ম অর্থাৎ যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে যাদের জন্ম, তাদের মধ্যে এই পর্ব সম্পর্কে লজ্জাবোধ তো আছেই, কিন্তু সেই সঙ্গে তারা অনেকটা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই যুগকে বর্ণনা করতে আগ্রহী। কারণ এই দ্বিতীয় প্রজন্মে যারা জন্মেছে, তারা যুদ্ধের ইতিহাসের সঙ্গে ওয়াকিবহাল হয়েছে একদম যাকে বলে ফার্স্ট-হ্যান্ড অভিজ্ঞতা শুনে। বার্ন্ড এইশিংগার সেই প্রজন্মটিরই প্রতিনিধি।
এইশিংগারের বাবা ডাক্তার ছিলেন, রাশিয়ান ফ্রন্টে টানা চারবছর তাকে থাকতে হয়েছিল। সেই দুর্বিষহ অভিজ্ঞতা বারবার ভুলতে চাইতেন তিনি। এইশিংগার তাই চিত্রনাট্যে যেমন নিজের দেশের মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়ার মাধ্যমে হিটলারের অযোগ্যতা দেখিয়েছেন, তেমনই মানুষ হিটলারের কিছু মানবিক দিকও দেখিয়েছেন।

ওই দু’কোটি মৃত্যুর কথা মাথায় রেখেও হিটলার মানেই সে একেবারে মনুষ্যত্বহীন, এমন মানসিকতা পোষণ করলে এই ছবির আসল সারমর্মটাই বোঝা কঠিন হয়ে ওঠে। আবার হিটলার মহান, এমনটা বোঝানোও এই ছবির উদ্দেশ্য ছিল না। তাকে একজন পথভ্রষ্ট, বিকারগ্রস্ত মানুষ হিসাবে দেখাই বরং এখানে সমীচীন।
এই প্রসঙ্গে পুলিৎজার পুরস্কার-জয়ী চলচ্চিত্র সমালোচক রজার এবার্ট একটি চমৎকার উপসংহার টেনেছিলেন তার লেখায়। তার সেই উদ্ধৃতিটি দিয়েই শেষ করছি-
Admiration I did not feel. Sympathy I felt in the sense that I would feel it for a rabid dog, while accepting it must be destroyed. … All we can learn from a film like this is that millions of people can be led, and millions more killed, by madness leashed to racism and the barbaric instincts of tribalism.