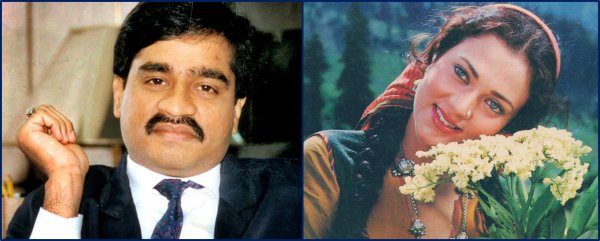‘স্ক্রিম অব ফিয়ার’ মুক্তির সময় ‘টেস্ট অব ফিয়ার’ নামেও মুক্তি পেয়েছিল। নামের মতোই সুস্বাদু এই সিনেমা! আর কেন, সেটা আলোচনাতেই জানা যাবে। গল্পটা এমন: বন্ধুর আত্মহত্যার পর নিঃসঙ্গতা থেকে বাঁচতে প্রায় ১০ বছর বাদে বাবার ঘরে ফেরার সিদ্ধান্ত নেয় মেয়ে। মায়ের কাছেই বড় হয়েছিল, ইতালিতে। মায়ের মারা যাওয়ার পর ফ্রান্সে আর ফেরেনি। বাবার দ্বিতীয় বিয়ের আক্ষেপ থেকেই অবশ্য এমনটা করা। এবার যা ফিরল, কিন্তু বাবার দেখা পেলো না। সৎমা জানালো, কাজের সূত্রে কয়েকদিন বাবার দেখা মিলবে না। সৎমায়ের মিষ্টি কথায় মন ভোলে না মেয়ের। তার অতি আদরকে সে সন্দেহের চোখে দেখে।
ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জানান দেয়, কোনো ভয়ানক গড়বড় আছে। এরই মধ্যে গেস্ট হাউজে সে দেখতে পায় বাবাকে। বরাবর বলতে গেলে, তার বাবার লাশ দেখতে পায়। তাকে বলা হয় যে তার মতিভ্রম হয়েছে। কিন্তু একাধিকবার এমন হলো। বাবার গাড়ির ড্রাইভারই একমাত্র মেয়ের এই মতিভ্রম, আসলে সত্যিই কোনো অর্থ রাখে বলে বিশ্বাস করলো, এবং পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিলো। কিন্তু গল্প যতই এগোচ্ছে, সেই প্রতিশ্রুতিতে ততই চিড় ধরছে। মেয়ে এবার নিশ্চিত, আসলেই কোনো রহস্য আছে তার বাবা আর এই সৎমাকে ঘিরে, যার সবটা ড্রাইভার জানে। তবে, তার রহস্যের কথা কে জানে বা জানবে?

‘স্ক্রিম অব ফিয়ার’ হ্যামার ফিল্ম প্রোডাকশনের সিনেমা। সেটা টেনে আনার কারণ হলো পঞ্চাশের দশকের মধ্যভাগ থেকে ষাটের দশকের মধ্যভাগ অব্দি ব্রিটিশ এই প্রোডাকশন হাউজের জনপ্রিয়তা ছিল আকাশছোঁয়া। তখনকার হরর সিনেমার মার্কেটে ছিল হ্যামার ফিল্মের তুমুল আধিপত্য। তারা যাত্রা তো শুরু করে ত্রিশের দশকের মধ্যভাগ থেকে। কিন্তু জনপ্রিয়তা পায় পঞ্চাশের মধ্যভাগে।
হরর জনরায় ভিড়বার পরই আসলে এই প্রোডাকশন কোম্পানি নবজন্ম লাভ করে। এবং এর পেছনে বড় অবদান টেরেন্স ফিশার, রয় ওয়ার্ড বেকার পরিচালকদ্বয়ের। এত বাক্যব্যয় আসলে অহেতুক মনে হবে অনেকের কাছে। কিন্তু এই সিনেমা হলো হ্যামার ফিল্ম প্রোডাকশনের জন্য একটা ‘চেঞ্জ অব পেস’। আর কেন তা, সেটা অনুসন্ধান করতে গেলেই ওই বাক্যগুলোতে হেতু যুক্ত হবে। সাধারণত, হ্যামারের সিনেমাগুলো আবহের দিক থেকে খুবই কড়া হয়। গথিক সেটিং বেছে নেয় তাই। সাথে শকিং উপাদান আর ক্যাম্পি ভাইবও থাকে একেবারে মূলধারার দর্শকদের ধরতে।
এই ‘টেস্ট অব ফিয়ার’ হ্যামার ফিল্মের সচরাচর গথিক হরর সেটিংয়ের মধ্যেই সাইকোলজিক্যাল থ্রিলারের পরত যোগ করে। এবং সেটা ড্রামা আর জটিলতা দুটোকে প্রাধান্য দিয়েই। অন্যান্য সিনেমার মতো উপর্যুপরি শকিং উপাদানেও ভর করে,নি কিংবা অমন ক্যাম্পি হররও হয়নি। বরং, টান টান উত্তেজনার থ্রিলার হয়েছে। হিচককের ‘সাইকো’, ‘ভার্টিগো’; ওদিকেরই মাইকেল পাওয়েলের ‘পিপিং টম’; আবার একই বছরে জ্যাক ক্লেটনের ‘দ্য ইনোসেন্টস’ সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার জনরাকে সমৃদ্ধ করেছে। তাই সেসবের দেখাদেখি হ্যামার ফিল্ম প্রোডাকশন তাদের বি-মুভি বাজেট আর গথিক সেটিংয়ের মাঝেই আনলো এই সিনেমা।
জটিল এবং জিলাপির মতো প্যাঁচানো গল্প তো রইলই। আর সেটাকে চিত্রনাট্যে রূপান্তর করার দায়িত্ব পড়লো এমন জনরার জন্য সেই সময়কার আদর্শ ব্রিটিশ চিত্রনাট্যকার জিমি স্যাংস্টারের উপর। এই সময়ে এসে গল্পের নানা বাঁক গড়পড়তা ঠেকলেও জিমির সংলাপে একটা ধার আর ধাঁধা আছে, যেটা এখনও দ্বন্দ্ব তৈরি করতে পারে দর্শকমনে।

সেই দ্বন্দ্ব অভিঘাতী করতে আছে সকলের দক্ষ অভিনয়। সকলের চরিত্রেই একটা রহস্য জড়িয়ে আছে। আর সেটাকে বিশ্বাসযোগ্য করতে তাদের বাচিক অভিনয়ই যথেষ্ট। কেন্দ্রীয় চরিত্রে সুজান স্ট্রাসবার্গের ধূর্ততাই বাকি সবকিছুকে হার মানায়। এছাড়া, ক্রিস্টোফার লীর অসামান্য অভিনয় তো রইলোই। এই সিনেমা কাগজে-কলমে যতটা, তার চেয়েও দ্বিগুণ চমকপ্রদ হয়ে উঠেছে এর ভিজ্যুয়াল ভাষার কারণে। মেয়ের প্রত্যাবর্তন এবং ড্রাইভারকে নিয়ে নদীতীরে বসে থাকার দৃশ্যগুলোতে ইংমার বার্গম্যানের ‘সামার ইন্টারল্যুড’ সিনেমার পরিচিত আবহ ভেসে ভেসে আসছিল অবশ্য। আলো-ছায়ার তারতম্যে আছে ভীষণ পরিমিতিবোধ।
ডগলাস স্লকম্বের ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট সিনেমাটোগ্রাফি ভীষণ তীক্ষ্ণ। সুজান স্ট্রাসবার্গ হুইলচেয়ারে বসে তাকিয়ে আছেন জানালা দিয়ে সামনের পুলের পানির দিকে। সেখান থেকে তার মুখের ক্লোজ আপ এবং সেখানে ডিজলভ ব্যবহার করে পুলের পানিতে তার মুখটা প্রতিবিম্বিত করার দৃশ্যে ডিজলভের সম্মোহনীয় ব্যবহার করা হয়েছে রীতিমতো। আর হবে না-ই বা কেন? ডগলাস স্লকম্ব যে ব্রিটিশ সিনেমার অন্যতম দক্ষ সিনেমাটোগ্রাফার! বিশেষ করে, জনরা সিনেমাতে। পরবর্তীতে ‘ইন্ডিয়ানা জোনস’ সিরিজের প্রথম দুটো সিনেমার সিনেমাটোগ্রাফি করে হলিউডেও যথেষ্ট নামডাক করেছিলেন।

আলো-ছায়ার সুষম বণ্টন আর মোহনীয় ডিজলভ ব্যবহারর পাশাপাশি সিন ব্লকিংয়ে চরিত্রগুলোকে সঠিক জায়গায় অবস্থান দিয়ে এক ত্রিমাত্রিক জগত তৈরি করা হয়েছে। শেষের দৃশ্যে লো-অ্যাঙ্গেল ব্যবহার করে ত্রিভুজাকৃতির ব্লকিংয়েই সেই জিনিস আবার ধরা দেয়। এক ব্যতিক্রম রসবোধের পরিচয়ও তখন পাওয়া যায়। সিনেমার গথিক আবহ অনুযায়ী আবহসঙ্গীতের ব্যবহারও হয়েছে নিখুঁত। পুলের সেই দৃশ্যই আবার দেখা যাক, ড্রাইভারের কথায় নিশ্চিত হবার পর সুজানের চেহারায় নেমে আসে বিষাদ। তার মুখের ক্লোজ আপ নিয়ে তা প্রকাশ না করে আবহসঙ্গীতেই তা বলে দেওয়া হয়। কিন্তু পরক্ষণেই চারপাশের বাতি নিভে যাওয়ায় সুজানের মাঝে যে ভয়ের সঞ্চার হয়, তা-ও কোনো ক্লোজ আপ ছাড়াই শুধুমাত্র আবহসঙ্গীত দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এখানে মুহূর্তের মাঝেই আবহসঙ্গীতের সুর বদলের কাজটি হয়েছে অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং চমকপ্রদ।
পরিচালক হিসেবে এই সিনেমায় ছিলেন সেথ হল্ট। ষাটের দশকে সুপরিচিত ছিলেন তিনি, তার রহস্যময় আবহ তৈরি করায় আর অভিভূত করা ভিজ্যুয়াল ভাষার জন্য। যার প্রমাণ ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। তবে এই সিনেমায় সেথ হল্টের মূল কাজ ছিল দর্শককে ম্যানুপুলেট করতে পারায়। এবং তিনি দক্ষতার সাথেই সেই কাজ করেছেন। মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব আর ভয় স্পর্শনীয় হয়ে উঠেছে তার পরিচালনার গুণে। পরিচালনায় তার গুরুগম্ভীর ভাব এমন গল্পের জন্য যথোপযুক্ত। এবং এই সিনেমার পরে ১৯৬৫ সালে আসা ‘দ্য ন্যানি’ সিনেমাও তার পরিচালিত সিনেমাগুলোর মাঝে অন্যতম ভালো সিনেমা। ‘দ্য ন্যানি’তেও সেথ হল্ট সাইকোলজিক্যাল আবহ তৈরি করেই সাসপেন্স আরো ঘন হয়ে উঠতে দিয়েছেন। ওটাও হ্যামার প্রোডাকশনের সিনেমা। এবং চিত্রনাট্য জিমি স্যাংস্টারেরই লেখা। তাই অমন করে চরিত্রে ফোকাস থাকতে পেরেছে সিনেমাটি, এবং হরর থেকে বেরিয়েও ভালো থ্রিলার হয়ে উঠেছে হ্যামারের জন্য। সেথ হল্টের এই দুটো সিনেমা তাই পাশাপাশি রাখলে বেশ কিছু কমন ব্যাপার আর ন্যারেটিভ থ্রেড চোখে পড়বে।

‘স্ক্রিম অব ফিয়ার’-এর নাম এই জনরার পরিচিত ক্লাসিকগুলোর পাশে হয়তো বসবে না, অতটুকু তার আওতায়ও না। তবে অবশ্যই হ্যামার ফিল্ম প্রোডাকশনের জন্য ক্লাসিক, এবং দর্শককে এখনও আকৃষ্ট করার আর অনুমানের ধাঁধায় ফেলে দেওয়ার ক্ষমতা এতে আছে। পুরো সময় রহস্য আর উত্তেজনায় বেধে রাখবার মতো উপাদানও এতে আছে।