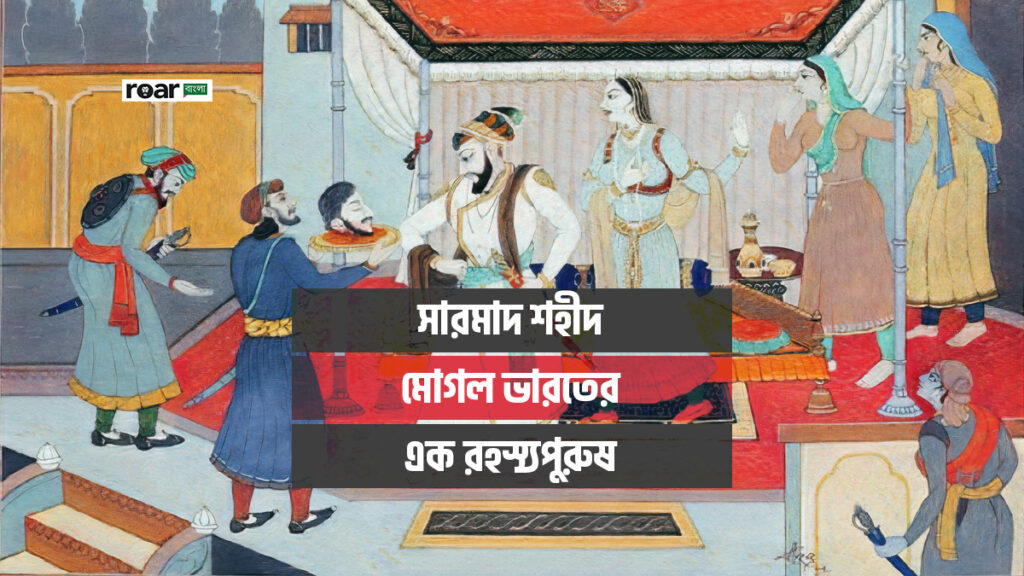.jpg?w=1200)
ধরুন,একটি বাগানে অনেক রকমের ফুলগাছ আছে, কিন্তু সঠিক পরিচর্যা নেই। আরেকটি বাগানে গুটিকয়েক ফুলগাছ আছে, কিন্তু বাগানের মালিক তার নিয়মিত পরিচর্যা করছে। আমাদের কাছে কোন বাগানটিকে সুন্দর লাগবে? অবশ্যই দ্বিতীয় বাগানটি। কারণ, প্রথম বাগানটির হরেক রকম ফুল গাছ থাকা সত্ত্বেও যত্নের অভাবে তা সেভাবে কারোর নজর কাড়বে না।
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টপাধ্যায়ও তেমনি একজন ব্যক্তি, যার নাম আম-বাঙালি পাঠকদের কাছে সেভাবে পরিচিত নয়। শুধু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বললে কয়জন চেনে তাকে? কিন্তু যদি বলি সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অগ্রজ হলেন এই সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তাহলে কিন্তু আমরা অনেকেই কিছুটা হলেও ঠাওর করতে পারি তিনি কে।
সঞ্জীবের ছিল প্রতিভার অমিত তেজ, কিন্তু যা ছিল না- তা হলো উদ্যম! শুধু প্রতিভা থাকলেই হয় না; সেই প্রতিভাকে যথাযথ ব্যবহার করতে হয়, হতে হয় অধ্যবসায়ী। বলা বাহুল্য, তেমনটা ছিলেন না সঞ্জীব। তিনি ছিলেন কিছুটা আয়েশি গোছের মানুষ; ছকে বাঁধা জীবনে যাকে বাঁধা যেত না।

জন্ম ও পরিচয়
১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে চব্বিশ পরগণা জেলার কাঁটালপাড়া গ্রামে যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও দুর্গাদেবী চট্টোপাধ্যায়ের ঘর আলো করে জন্ম নেন সঞ্জীব। বাবা ছিলেন বর্ধমান জেলার ডেপুটি কালেক্টর। অনুজ ও কিংবদন্তি বাঙালি সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে সঞ্জীব ছিলেন বছর চারেকের বড়।
শিক্ষা
মেধার কমতি ছিল না। কিন্তু জোর খাটানো যেত না তার ওপর। নেহায়েত নিজের মর্জি সায় দিলেই পড়তেন। পরীক্ষা পালানো, আর পরীক্ষায় যদি বসেও ফেল করা ছিল স্বভাবগত। তার বেশি টান ছিল মূলত দাবা খেলায়।
যা-ই হোক, পরীক্ষা সংক্রান্ত নানা জটিলতার কারণে শেষ পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া শেষ করতে পারেননি তিনি। তার বাবা তাই তাকে সাথে করে বর্ধমানে নিয়ে গেলেন। সেখানে একটি কেরানির চাকরি পান সঞ্জীবচন্দ্র।
অভিজাত পরিবারের সন্তান হয়েও এই ‘সামান্য’ কেরানির চাকরি করতে তার বাঁধল না একবারের জন্যও। তিনি হাসিমুখেই তা মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু মেনে নিতে পারছিলেন না ছোট ভাই বঙ্কিমচন্দ্র।
তখন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে নতুন আইনের ক্লাস শুরু হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র তার অগ্রজকে (সঞ্জীবচন্দ্র) নিয়ে আইনের ক্লাসে ভর্তি হয়ে গেলেন।
সেই বঙ্কিমচন্দ্র পড়া শেষ না করেই চাকরিতে ঢুকে গেলেও সঞ্জীব কিন্তু রয়ে গেলেন। কিন্তু তাতেও বিশেষ লাভ হলো না। কারণ পরীক্ষায় যথারীতি অকৃতকার্যই হলেন তিনি!
কর্মজীবন
জীবনযাপনেও কোনো গোছ ছিল না তার। মধ্যবিত্ত পরিবারের আত্ম-প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তিনি কখনো ছিলেন না। কী করে নিজেকে দাঁড় করানো যায়, তা নিয়ে না ভেবে বরং কোন কাজটি করলে আনন্দ পাবেন- সেটিই তার কাছে গুরুত্ব পেত।
আর তাই আইনের পরীক্ষায় ফেল করে তিনি বাগান করার প্রতি মনোযোগী হলেন। বেশ আনন্দেই তার দিন কাটছিল ফুলের বাগানের সাথে। এই সুখে সাধলেন তার বাবা, সন্তানের এই কাজ মোটেও ভালো লাগেনি তার।
তখন ইনকাম ট্যাক্সের জন্য জেলায় জেলায় নতুন আসসের নিয়োগ চলছিল। পিতা যাদবচন্দ্র কোনোরূপ দেরি না করেই তার উদাসী ছেলেকে সেখানে ঢুকিয়ে দিলেন। মাইনে ছিল আড়াইশ’ টাকা।
কয়েকবছর এই চাকরি করলেনও তিনি। কিন্তু ভাগ্য সহায় হলো না তার। বিলুপ্ত হয়ে গেল পদটি। যদিও তাতে তার তেমন কিছু যায় আসছিল না। কারণ তার মনকে টানছিল কেবলই সেই পুষ্পের উদ্যানটি। তাই তিনি সেখান থেকে ফিরে এসে দ্বিগুণ উদ্যমে বাগানের কাজ করতে থাকলেন।
কিন্তু এবার যেন সমস্যা একটু বেড়েই বসল। তার বড় ভাই শ্যামচরণ পিতা যাদবচন্দ্রের নিকট বাগানের স্থলে একটি শিবমন্দির করার ইচ্ছে পোষণ করলেন। বড় ভাইয়ের ইচ্ছে অনুযায়ী, সেখানে ফুলের বাগান ভেঙে মন্দিরই স্থাপিত হলো।
কে জানে, হয়তো এই ঘটনার দুঃখ-কষ্টেই সঞ্জীব জ্বলে উঠলেন। লিখে ফেললেন ‘Bengal Ryots’!

সেই সময়ের হাইকোর্টের জজদের হাতে হাতে ঘুরতো ইংরেজিতে লেখা এই বইটি। এটি লেখার জন্যই সম্ভবত তিনি জীবনের সব থেকে বেশি পরিশ্রম করেছিলেন। প্রতিদিন কাঁটালপাড়া থেকে দশটার সময় ট্রেনে করে এসে কলকাতায় আসতেন। প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে আবার সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে লেখা নিয়ে বসতেন। অবশ্য তার এই কঠিন এবং স্বভাবের বিরুদ্ধে বিস্ময়কর পরিশ্রমের উপযুক্ত প্রতিদানই পেয়েছিলেন তিনি।
বড় বড় সাহেব মহলে হুলস্থূল পড়ে গিয়েছিল এই বইটি প্রকাশ হওয়ার পর। রাজস্ব বোর্ডের চ্যাপমান সাহেব এই বইয়ের একটি ইতিবাচক সমালোচনা লিখেছিলেন। অনেক সাহেব বলেছিলেন, ইংরেজরাও নাকি এরকম বই লিখতে পারবে না! এমনকি হাইকোর্টের জজেরাও রায়ের জন্য এই বই পড়া শুরু করে দিয়েছিলেন।
লেফটেন্যান্ট গভর্নর সাহেব তার এই বই পড়ে তাকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ উপহারস্বরূপ দিয়ে দিলেন। কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন এ চাকরি তার থাকবে না। তিনি বঙ্কিমকে বললেন,
ইহাতে পরীক্ষা দিতে হয়। আমি কখন পরীক্ষা দিতে পারি না। সুতরাং এ চাকরি আমার থাকবেনা।
হলোও তাই। তিনি পরীক্ষায় ফেল-ই করলেন! তবে এই ফেলের পেছনে কতটা তার দোষ ছিল, আর কতটা ভাগ্যের- তা পরিষ্কার করে বলা যায় না। অনেকে বলেন, শত্রুতা করেই নাকি তাকে ফেল করানো হয়েছিল!
চাকরি ফেরত পাবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন তিনি। কিন্তু সেই চাকরি আর ফেরত পাননি তিনি। পেলেন অন্য একটি চাকরি। বারাসাতে সাব-রেজিস্ট্রারের কাজ। পরে অবশ্য বদলি নিয়ে হুগলিতে আসেন তিনি।
সেখানে বেশ সুখেই দিন কাটছিল তার। বাড়ি থেকেই অফিসে কাজ করতে যেতে পারতেন। কিন্তু এই সুখও স্থায়ী হলো না বেশিদিন। বেতন কমানোর কথা শুনে তিনি বর্ধমানে চলে এলেন।
আর সেই বর্ধমানেই মূলত বাংলা সাহিত্যের সাথে তার প্রকাশ্য সম্বন্ধ শুরু হয়! বাংলা সাহিত্যের প্রতি ছোটবেলা থেকেই তিনি অনুরক্ত ছিলেন। কিশোর বয়সে দুইটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন, যা ব্যাপক সমাদৃত হয়েছিল।
বঙ্গদর্শন
বঙ্গদর্শন পত্রিকাটির নাম শুনলেই আমাদের সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের কথাই মনে পড়ে। কিন্তু অনেকেই জানেন না যে, বঙ্গদর্শন-এর সাথে আরেকটি নাম জড়িত আছে, তা হলো- সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭৫ সালে এই পত্রিকাটি বন্ধ করে দিলে তার অনুরোধেই বঙ্গদর্শন আবার চালু হয়। সেটির সাথে যারা বঙ্গদর্শন কিনতে পারবে না বা যাদের জন্য উপযোগী নয়, তাদের জন্য প্রকাশিত হতো ভ্রমর নামে একটি পত্রিকাও।
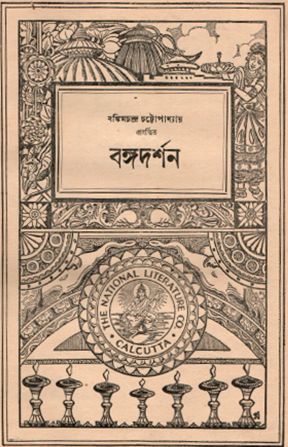
কিন্তু স্বভাবের বাইরে গিয়ে তো আর কিছু হয় না। তেমনটাই হলো এখানে। খুব বেশিদিন মন টিকলো না সঞ্জীবের। ভ্রমর ও বঙ্গদর্শন দুটোই বন্ধ হয়ে গেলো। এক বছর বন্ধ থাকলে তিনি বঙ্কিমের নিকট এর স্বত্বাধিকার চান। ১৮৭৭-১৮৮২ সাল পর্যন্ত ছয় বছর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সঞ্জীব। সেখানে তার জালপ্রতাপচাঁদ, পালামৌ, বৈজিক্তত্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।
পালামৌ
সঞ্জীবচন্দ্রের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বিখ্যাত বই পালামৌ। এটি মূলত একটি ভ্রমণকাহিনী । কিন্তু বইটি পাঠককে যেভাবে গল্পের মধ্যে ডুবিয়ে রাখে, তাতে তা তুমুল কোনো প্রেমের উপন্যাসকেও হার মানায়!
পালামৌ অঞ্চলটির একেবারে জীবন্ত দৃশ্য তুলে ধরেছেন তিনি এখানে। এত নিখুঁত, নিপুণতার সাথে এত প্রাণবন্ত বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, তা পাঠককে নিমিষেই যেন সেখানে নিয়ে যেতে পারবে। “বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে” প্রবাদটি এখান থেকেই এসেছে।
পালামৌ নিয়ে চন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে,
উপন্যাস না হইয়াও পালামৌ উৎকৃষ্ট উপন্যাসের ন্যায় মিষ্ট বোধ হয়। পালামৌ এর ন্যায় ভ্রমণসাহিত্য বাংলা সাহিত্যে আর নেই। আমি জানি উহার সকল কথাই প্রকৃত, কোনো ঘটনাই কল্পিত নয়। কিন্তু মিষ্টিটা মনোহরিত্তে উহা সুরচিত উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত ও সমতুল্য।
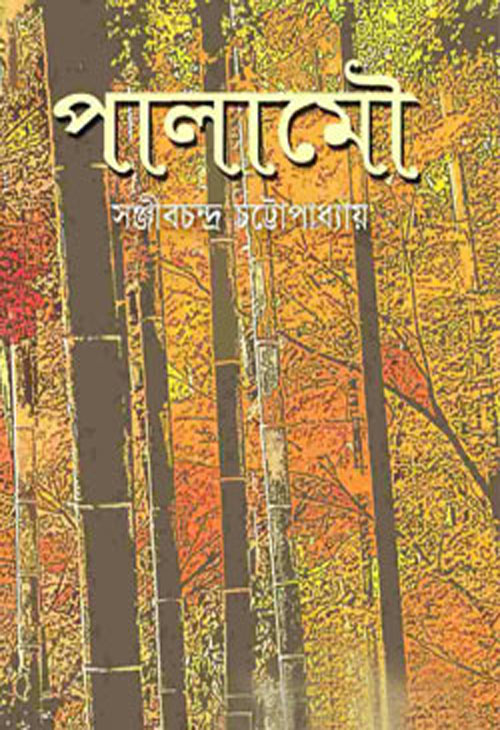
এছাড়াও তার অন্যান্য বই হলো-
- মাধবী লতা
- কণ্ঠমালা
- জাল প্রতাপচাঁদ
- রামেশ্বরের অদৃষ্ট
- যাত্রা সমালোচনা
- Bengal Ryots ( the rights and liabilities)
- দামিনী
- বাল্যবিবাহ
- সৎকার
বহুদর্শী, বুদ্ধিদীপ্ত মন, বাস্তবকে খুঁটিয়ে দেখার দৃষ্টি আছে- এমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের পক্ষে সাহিত্যে প্রবেশ স্বাভাবিক ও অনিবার্যই মনে হয়। তার লেখনভঙ্গি, দৃষ্টিভঙ্গি সবকিছুর মাঝেই স্বাতন্ত্র্যর ঠাসবুনোট লক্ষণীয়।
নিজস্ব নন্দনবোধের কারণে সৌন্দর্যের সংজ্ঞাও তার কাছে অন্যরকম। তার কাছে সৌন্দর্য ভূতের মতো! ভূত যেমন স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বিভিন্ন রুপ নিতে পারে, সৌন্দর্যের সংজ্ঞাও তার কাছে সেরকম। তার চোখে সৌন্দর্যও বিভিন্ন রূপ নেয় পাত্রভেদে। তিনি বলেন-
রূপ এক, তবে পাত্র ভেদ। আমি পাত্র দেখিয়া ভুলি না; দেহ দেখিয়া ভুলি না; ভুলি কেবল রূপে। সে রূপ লতায় থাক কিংবা যুবতীতে থাক, আমার মনের চক্ষে তাহার কোনো প্রভেদ দেখিনা। অনেকের এই প্রকার রুচিবিকার আছে। যাহারা বলেন, যুবতীর দেহ দেখিয়া ভুলিয়াছেন, তাহাদের কথা মিথ্যা। (পালামৌ, চতুর্থ অংশ, বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১২৮৮)
তার দেখার চোখও ছিলো সকলের থেকে আলাদা। সবকিছু খুঁটিয়ে এবং নিখুঁতভাবে দেখতে ভালোবাসতেন তিনি।
তিনি যাইতে যাইতে প্রায়ই দাঁড়ান, একটি গাছ দেখিবার জন্য, একটি লতা দেখিবার জন্য, একটি ঘাস দেখিবার জন্য, একটি ফুল দেখিবার জন্য, প্রায়ই দাঁড়ান। কখনো বা পথ ছাড়িয়া একটু এদিক ওদিকেও যেতেন। এইরূপে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এদিক সেদিক করিয়া, এটি সেটি দেখিতে দেখিতে যাইতে তিনি বড়ই ভালোবাসিতেন। (সঞ্জীবনী সুধা, পৃষ্ঠা ১৯)
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম মূলত সঞ্জীবনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বাংলা সাহিত্যে তার অবদান স্বীকৃতিযোগ্য হলেও যোগ্যতা অনুযায়ী সম্মান পাননি তিনি। আর এজন্য হয়তো তার উদাসী, আনমনা স্বভাব-ই দায়ী। তাকে নিয়ে তার অনুজ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এমনটাই লিখে গেছেন,
প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই জীবিতকালে আপন আপন কৃতকার্যের পুরস্কারপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অনেকের ভাগ্যে তাহা ঘটে না। যাহাদের কার্য দেশ ও কালের উপযোগী নহে, বরং তাহারা অগ্রগামী, তাহাদের ভাগ্যে ঘটে না। যাহারা লোকরঞ্জন অপেক্ষা জনহিতকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন, তাহাদের ভাগ্যেও ঘটেনা। যাহাদের প্রতিভার এক অংশ উজ্জল, অপর অংশ ম্লান, কখনো ভস্মাচ্ছন্ন, কখনো প্রদীপ্ত- তাহাদের ভাগ্যেও ঘটে না।
কেননা অন্ধকার ঘাটিয়া দীপ্তির প্রকাশ পাইতে দিন লাগে। ইহার মধ্যে কোন কারণে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাহার জীবিতকালে বাংলা সাহিত্যসভায় তাহার উপযুক্ত আসনপ্রাপ্ত হয়েন নাই, তাহা এ জীবনী পাঠে পাঠক বুঝিতে পারেন। কিন্তু তিনি যে এ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে আপনার উপযুক্ত আসনপ্রাপ্ত হয়েন নাই, তাহা যিনিই তাহার গ্রন্থগুলো যত্ন সহকারে পাঠ করিবেন, তিনি স্বীকার করিবেন।
বঙ্কিম এবং সঞ্জীব ছিলেন একেবারে বিপরীত স্বভাবের দুজন মানুষ। তার ব্যবহারে সর্বদা আলিঙ্গনের হাত বাড়ানো থাকত। মানুষকে আপন করে নেওয়ার অসাধারণ ক্ষমতা ছিলো তার। আনন্দ-হাসিতে ভরপুর করে রাখতেন সবসময়। গল্প করতে তিনি যেমন ভালবাসতেন, তেমনি তার মুখে গল্প শুনতেও ভীষণ ভালোবাসতেন শ্রোতারা।
তার লেখার হাতের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল; তিনি যেভাবে খোশ-গল্প করতে পারতেন সেভাবে লিখতেও পারতেন। মুখের কথায় যেরূপ মুগ্ধতা, রস দিয়ে কথা বলতেন, ঠিক তেমনি করে সব রস ঢেলে দিতে পারতেন তার লেখায়। কিন্তু উদাস সঞ্জীবের লেখালেখি ছিল বেশ হেলাফেলার। তিনি যা পারতেন, তার ভেতরে যতটুকু ছিল, তার পুরোটুকু ঢেলে দিতেও বোধহয় তিনি আলসেমি করে গেছেন!
স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তার প্রসঙ্গে লিখে গেছিলেন,
তাহার প্রতিভার ঐশ্বর্য ছিল, কিন্তু গৃহীপনা ছিল না… তাহার মধ্যে যে পরিমাণ ক্ষমতা ছিল, সে পরিমাণ উদ্যম ছিল না!
১৮৮৯ সালে প্রবল জ্বরে এই গুণী তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। উদারাত্মা সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জীবনের অনেকটা সময়ই কাটিয়েছেন ধার দেনায়। দেনার দায়ে বাড়ি হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পালিয়ে বেড়াতেন অনেক সময়। আর সেই দেনার ভার গিয়ে পড়ত ছোটভাই বঙ্কিমের ওপর। এতে অনেক তিরস্কারও শুনতে হতো তাকে। এতোটা নির্বিকার না হয়ে একটু মনোযোগ দিলে হয়তো আজ তিনিও ছোটভাইয়ের মতো বাংলা সাহিত্যে একটি শক্ত জায়গা দখল করে নিতে পারতেন। আবার কে জানে, হয়তো তার তেমন কোনো অভিলাষ আদৌ কখনো ছিল না!