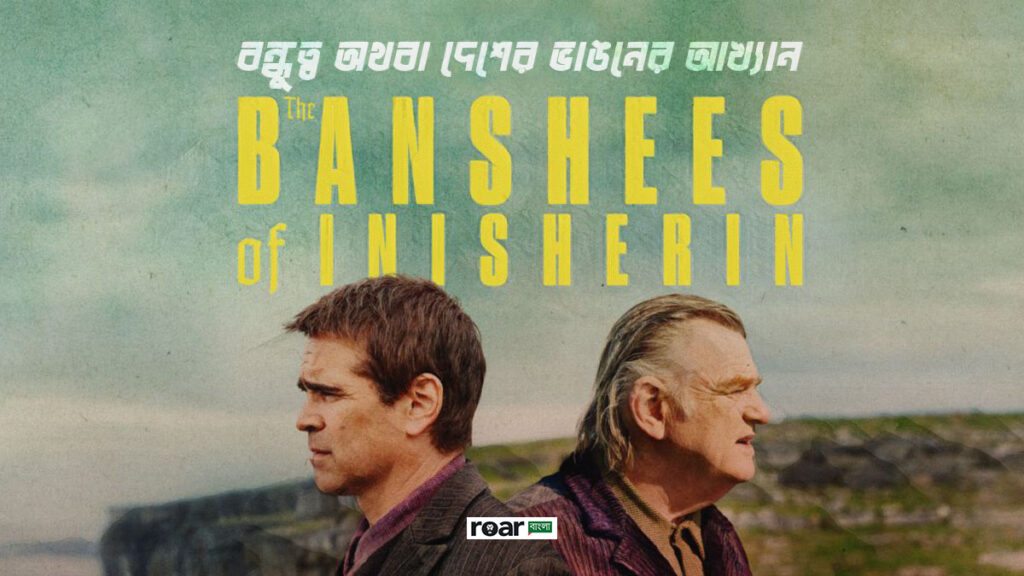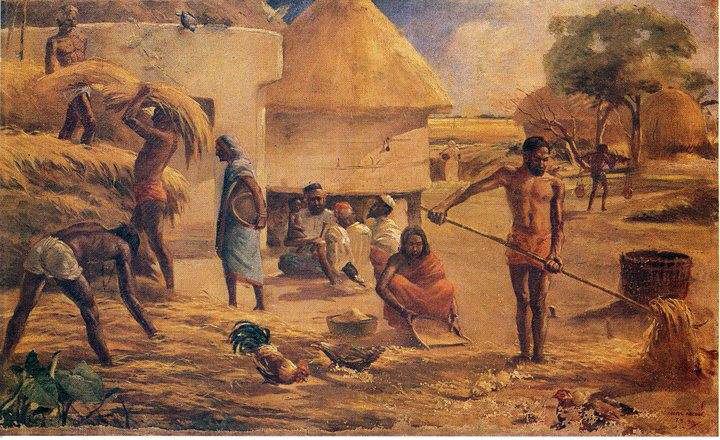
আত্মজীবনী কি জীবনের তাবৎ যাপনপ্রণালীর সমূহ যোগ–বিয়োগের খোলা পাতা? নাকি সত্যকথন নামক মোড়কের আড়ালে স্বীয় কীর্তিধ্বজাবাহী কোনো কাহিনি–আখ্যান? আমাদের মগজের নিরবচ্ছিন্ন ক্রিয়াকাণ্ডে তাবৎ লজ্জার–অপমানের কাহিনি সঙ্গোপনে ঢাকা থাকে। তাকে আত্মজীবনীতে অকপটে উগরে দেওয়া আদৌ সহজ নয়। নিজের সঙ্গে এই আড়াল প্রতিটি লেখকের মজ্জাগত। ‘আমিত্ব’কে বিসর্জন দিয়ে নির্মোহ দৃষ্টিতে পাঠকের সামনে নিজেকে ও সমসময়কে উপস্থাপিত করাই রুচিবান লেখকের লক্ষণ। আসলে আপন সারল্য ও সত্যবদ্ধতায় সমসাময়িক জন, সমাজ, দেশ, কালকে বিবৃত করার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠে একটি প্রকৃত আত্মজীবনীর প্রতিটি পর্ব। জসীম উদদীনের ‘জীবন কথা’ তেমনই এক সহজিয়া সুরে গাঁথা আত্মমালিকা।
একজন কবি, যিনি এই মাটির পৃথিবীর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন সারাটা জীবন, যার সৃষ্টি ও ভাবনায় সোঁদা মাটির গন্ধ বহতা নদীর মতো, তিনি শেষজীবনে লেখা তার আত্মজীবনীতেও ফুটিয়ে তুলেছেন অনাবিল সারল্য আর প্রিয় মানুষের সুখ–দুঃখের সহজিয়া সুর। চুয়াত্তর বছর বয়স্ক কবি রোগশয্যায় শুয়ে লিখতে শুরু করলেন তার শৈশব আর কৈশোরের সোনাঝরা মুহূর্ত, তার ব্যথাময় জীবনের কথা।
নিজেকে খনন করে স্নিগ্ধ প্রসন্নতায় বিনি সুতোর মালা গাঁথলেন জসীম উদদীন, তার আত্মজীবনী ‘জীবন কথা’–য়। বিগত দিনের সেই কথা তার মনে কল্পনার জাল বোনে, দুঃখের দিনে শোনায় সান্তনার বাণী। মায়াবী শব্দের নিটোল মায়ায় তার এই গ্রন্থে জসীম উদদীন প্রকৃতির পটে আপন মনে ছবি আঁকেন। সেই ছবিতে বাহ্যিক কোনও আড়ম্বর নেই, নেই জটিল কোনও তর্কের আভাষও। যেন স্বতোৎসারিত আলো এসে আলোকিত করছে, ধুয়ো দিচ্ছে অপাপবিদ্ধ জীবনের বৃত্তান্ত।

আগেই বলেছি, জসীম উদদীন তার লেখার মধ্যে দিয়ে ছবি আঁকেন পাঠকের মনে। সে ছবি রং–রূপ–রসে এমনই হৃদয়গ্রাহী যে পাঠক নিজের অজান্তেই প্রবেশ করেন সেখানে, কাঁদেন – হাসেন আর সহজিয়া শব্দমাধুর্যে অনাবিল আনন্দে ভরে উঠে তার মন। মাত্র ১১০ পৃষ্ঠার (প্রথম প্রকাশ , ২২ শ্রাবণ, ১৩৭৮ প্রকাশক , গ্রন্থপ্রকাশ, ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা–১২) এই জীবন কথায় কবির অসাধারণ গদ্যশৈলীর ছাপ সুস্পষ্ট। তার জীবনের একটা পর্বের এই কাহিনি তার অন্যতম সেরা রচনা, এক আকর গ্রন্থ।
কবির এই অপূর্ব স্মৃতিকথাটি যখন ‘চিত্রালী’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল তখন এক পাঠক তা পড়ে লিখেছিলেন, ‘জসীম উদদীনের ‘জীবনকথা’ পড়িতেছি, না মায়ের হাতের পিঠা খাইতেছি’। প্রকৃত অর্থেই এ-লেখায় দৃশ্য বোনেন কবি। ভোর রাতে তার বাজানের (পিতার) নামাজের সুর, আতসীর মালা পরা ফকিরের সুর করে ইউসুফ–জুলেখার পুঁথি পড়া, আকাশে ঝড়ের দাপাদাপি, রঙিন শাড়ি পরা কিশোরী জানকীর রূপের আলোয় ঝলমল করে উঠা আঙিনা— এ সবই লেখকের মনের নাট্যমঞ্চে এসে অনাবিল প্রসন্নতায় খেলা করে। এর মধ্যে কোথাও কোনো চাতুর্য নেই, বরং আছে সামান্য বস্তুকে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে আলোকোজ্জ্বল করে দেখানোর অবিশ্বাস্য দক্ষতা।

জসীম উদদীনের ‘জীবন কথা’র পাতায় পাতায়ও কাব্যধর্মিতার সুস্পষ্ট ছাপ। এক আশ্চর্য নির্মাণকৌশলে তার নিরাভরণ গদ্য ও সংলাপ কবিতা হয়ে ওঠে। এই বৃদ্ধ বয়সেও তার চোখে বাল্যের বিস্ময়। আর সেই বিস্ময় আর জিজ্ঞাসায় অবলীলায় মিশে যায় লোকজ শব্দ ও চরিত্র। কোনো ঘোরানো–প্যাঁচানো সংলাপ নয়, তুলির একটানে ছবি আঁকার মতো তিনি সহজ গদ্যে ফুটিয়ে তোলেন ছবি—
কুঁচের ফল ডালে ডালে পাকিয়া রাঙা টুকটুকে হইয়া হাসিতেছে। এ যেন বনরানীর সিঁদুরের ঝাঁপি। হিজল গাছের তলা দিয়া যখন পথ, তখন ত সেখান হইতে যাইতেই ইচ্ছা করে না। রাশি রাশি হিজল ফুল মাটিতে পড়িয়া সমস্ত বনভূমিকে যেন আলতা পরাইয়া দিয়াছে। …মাঠের পর আবার বন। মামাবাড়ি আর কতদূর—ওই ত সামনে দেখা যায় মুরালদহ। আহা কি মিষ্টি এ গ্রামের নাম। জাঙলা ভরিয়া লাউ–কুমড়ার জালি বাতাসে দোলা দিতেছে। কনে–সাজানী সীমলতার জাঙলায় কী রঙ, এ বাড়ির বউ বুঝি তার নীলাম্বরী শাড়িখানি মেলিয়া ধরিয়াছে এই জাঙলার উপর। ও বাড়ির গাছে আম পাকিয়া পাকিয়া রাঙা হইয়া আছে। সেই আমের মত রাঙা টুকটুকে বউটি বাঁশের কোটা দিয়া আম পাড়িতেছে। ও বাড়ির গাছে হাজার হাজার কাঁঠাল ধরিয়াছে। এ যেন ওদের ছেলেমেয়েগুলি গাছের ডালে ডালে ঝুলিতেছে।…
জসীম উদদীন গদ্য লিখেছেন সাধু ভাষায়৷ কিন্তু তার সাধু–গদ্যে সংস্কৃত শব্দের কোনও বাহুল্য নেই। বরং তাতে মিশেছে আঞ্চলিক বাকরীতি। আর তাই ‘জাঙলা’, ‘কোটা’ প্রভৃতি শব্দ অনায়াসে চলে এসেছে তার লেখায়। তার ফলে ছন্দপতন তো ঘটেইনি বরং আরো শ্রুতিমধুর, আরো ঝরঝরে হয়েছে সে গদ্য। সাধু রীতিতে লেখা গদ্যসম্ভার পড়ে জসীম উদদীনের হয়তো মনে হয়েছিল— বাংলা গদ্য ক্রমশ হয়ে উঠছে কৃত্রিম; এবং জনজীবন থেকে তা দূরে সরে যাচ্ছে। আর হয়তো সেজন্যই তার হাত দিয়ে বেরিয়ে এল তার নিজস্ব ধাঁচ, যার মধ্যে মাটির কাছাকাছি অবস্থানকারী প্রান্তিক মানুষের সহজ কথ্যরীতি আর আঞ্চলিক বাকরীতির সার্থক প্রয়োগ ঘটল। ‘ভাষার ভবিষ্যৎ’ গ্রন্থে প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন, ‘ভাষা মানুষের মুখ থেকে কলমের মুখে আসে। কলমের মুখ থেকে মানুষের মুখে নয়।’ প্রমথ চৌধুরীর এই বক্তব্যের সার্থক রূপায়ণ আমরা দেখি জসীম উদদীনের লেখায়।

‘জীবনকথা’ গ্রন্থটি কয়েকটি পর্বে ভাগ করেছেন লেখক। তারপর সেই বিষয়গুলো আপন ঢঙে পাঠকের সামনে ছবির মতো তুলে ধরেছেন। লেখা শুরু করেছেন এভাবে— “আজ রোগশয্যায় বসিয়া কতজনের কথাই মনে পড়িতেছে। সুদীর্ঘ জীবনের পথে কতজনই আসিল আবার চলিয়া গেল।” আর লেখার শেষ চরণে তার প্রিয় মেজদি আর সেজদির জন্য আকুল কবি লিখলেন, “আজও দুর্গাপূজার ঢোলের শব্দ শুনিলে আমার সেজদি ও মেজদিকে আমি মানসচক্ষে দেখিতে পাই। কপালে কাচপোকার ফোঁটা, মাথায় সুন্দর সিন্দুরের শোভা আর আলতায় রঞ্জিত রাঙা টুকটুকে পা দু’খানি। আর কি জীবনে তাঁহাদের সঙ্গে দেখা হইবে? সেই স্নেহভরা ভাই ডাকটি শুনিবার জন্য আজও আমার মন আকুলি–বিকুলি করে।”
প্রথম অধ্যায়ে তার বাজানের (পিতা) কথা, তাদের বাড়ির চারপাশের দৃশ্য, তার পিতার দারিদ্র, পিতার শিক্ষা, নামমাত্র বেতনে শিক্ষকতা, গ্রামীণ আচার–অনুষ্ঠান, শিশু জসীম উদদীনের বাল্যের দুষ্টুমি, সারা গ্রাম টো টো করে ঘুরে বেড়ানো, চাচাতো ভাই নেহাজদ্দিনের সঙ্গে নানান অ্যাডভেঞ্চার, স্কুল পালিয়ে আখের ক্ষেতের মধ্যে চুপটি করে বসে থাকা, ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ এসেছে। ছোটোবেলায় এক কাকচরিত ব্রাহ্মণ গ্রামে গ্রামে হাত দেখে বেড়াতেন। তার ভারি ন্যাওটা ছিলেন বালক জসীম। তিনিও জসীম উদদীনকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। বালক জসীম নিজে পরিচর্যা করে সুন্দর একটা বাগান করেছিলেন বাড়িতে। তা দেখতে এসে ওই ব্রাহ্মণ তো ভারি খুশি। জসীম উদদীন লিখেছেন,
পাতাবাহারের গাছগুলি দেখিয়া তিনি বড়ই খুশী হইলেন। আমাকে কানে কানে বলিয়া দিলেন, এই গাছগুলির কাছে আসিয়া তুমি মনে মনে বলিবে, এই পাতাবাহারের মত সুন্দর একটি বউ যেন আমার হয়। এরপর এই পাতাবাহারের গাছে পানি দিতে আসিয়া কেমন যেন লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিতাম। হয়তো মনে মনে দুই একবার বলিতামও, গাছ, তোমার মতো সুন্দর বউ যেন আমার হয়।
জসীম উদদীনের লেখায় আমরা জানতে পারি, দু’খানা খড়ের ঘরে তারা বাস করতেন। নলখাগড়ার বেড়া আর চাটাইয়ের ঝাঁপ লাগানো সেই বাড়ির উত্তর দিকে ঘন বিজে–কলার বাগান। কিন্তু অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা তার পিতা আনসারউদ্দীনের ছিল না। চরম দারিদ্রে তার ছেলেবেলা যে অতিবাহিত হয়েছে, সে-বৃত্তান্ত তিনি লিখেছেন এ-গ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে। তার মা রাঙাছুটু–র নিদারুণ কষ্টের কথা লিখেছেন জসীম। যদিও প্রথম অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন, “আমাদের উঠানে বারো মাসে বারো ফসল আসিয়া রঙের আর শব্দের বিচিত্র খেলা খেলিত।”
জসীম উদদীনের বাবা নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে পড়াশুনা করেছিলেন। ঘরের কাজ ফেলে তিনি স্কুলে যেতেন বলে তার পিতা জমিরউদ্দীন মোল্যা খুব রাগ করতেন। এমনকি কটু গালমন্দও করতেন। আসলে এ তো দরিদ্র ভারতবর্ষের চিরাচরিত দিনলিপি। এই জেটগতির যুগেও তা থেকে আমরা পরিত্রাণ পাইনি আজও জসীম উদদীনের পিতা অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন। তার পরনে থাকত ধুতি–পাঞ্জাবি, মাথায় টুপি এবং কাঁধে ‘একপাটা’ নামক পাতলা কাপড়। দেশে তখন ওহাবী আন্দোলনের জের থামেনি। হাজী শরিয়তুল্লার পুত্র দুদু মিঞা তখন সুবে বাংলার খলিফা। তিনি খবর পেলেন আনসারউদ্দীন ‘নাছেরা’ ইংরেজের ভাষা শিখছেন স্কুলে। জামাতপন্থী লোকদের কাছে এর চেয়ে বড় অপরাধ আর কিছু নেই। ফলে অচিরেই ইংরেজি পড়া তাকে ছাড়তে হল। জসীম উদদীন তাই আক্ষেপ করে লিখেছেন, ‘বাজান যদি ইংরেজী স্কুলে পড়িতেন তবে ডেপুটি হইতে পারিতেন, উকিল হইতে পারিতেন। আমাদের ছোট্ট সংসারে কোনো প্রকারের অর্থকষ্ট থাকিত না।’ কিছু কূপমণ্ডুক মানুষের জন্য, ধর্মনেতার জন্য সাধারণ মানুষকে কতই না কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়।
ফরিদপুর হিতৈষী এম. ই. স্কুলের শিক্ষক ছিলেন জসীমের পিতা। দুজন শিক্ষক। ছাত্রছাত্রীদের কাছে থেকে বেতন উঠত মাসে তিন–চার টাকা। তাই নিয়েই তারা প্রসন্ন থাকতেন। আসলে শিক্ষকতাকে তিনি জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ওই স্কুলেই পড়তেন বালক জসীম। সঙ্গী তার চাচাতো ভাই নেহাজউদ্দীন। স্কুলের ওই সামান্য বেতনে সংসার চলত না বলে জসীমের পিতাকে নানা উঞ্ছবৃত্তিও করতে হতো। গ্রাম্য চাষীদের বিবাহ পড়িয়ে তিনি দু–তিন টাকা রোজগার করতেন। কখনও কখনও মৃতের জানাজা (গোরস্থানে গিয়ে কবর দেওয়ার আগে মৃত ব্যক্তির জন্য প্রার্থনাসূচক নামাজ) পড়িয়ে কাঁসার থালা বা ঘটিও পেতেন তিনি। এভাবেই শৈশব কেটেছে জসীম উদদীনের।
তখন আশ্বিন–কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন গাস্বী উৎসব হতো। হিন্দু–মুসলমান দুই ধর্মের মানুষই এই উৎসব পালন করতো। জসীম উদদীন লিখেছেন, “আশ্বিনে রান্দে কার্ত্তিকে খায়, যে বর মাঙে সে বর পায়।…আমরা ছেলেবেলায় সারা বৎসর এই গাস্বীর দিনটির প্রতি চাহিয়া থাকিতাম।” তখনকার দিনে হিন্দু–মুসলমান মিলিতভাবে এমন আরো অনেক লোকাচার পালন করতেন। পাড়ায় পাড়ায় বসতো জারি গান, গাজীর গান আর কেচ্ছা গানের আসর। আর সে সব আসরে জসীম উদদীনের অনিবার্য উপস্থিতি। তার শৈশবের চঞ্চলতার নিদর্শন দিতে গিয়ে জসীম উদদীন লিখেছেন—
আমাকে কাপড় পরানো এক মুস্কিলের ব্যাপার ছিল। বহু বয়স পর্যন্ত আমি লেংটা ছিলাম। গ্রাম সম্পর্কে আমার এক দাদী আমার মাজায় ব্যাঙ বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। তাহাতেও আমাকে কেহ কাপড় পরাইতে পারে নাই। ভাবী এখনও আমাকে ঠাট্টা করিয়া বলেন, ‘ক্লাস থ্রি–তে যখন তুমি পড় তখনও দেখিয়াছি স্কুল হইতে আসিয়া ওই পথের মধ্যে তুমি পরনের কাপড়খানি মাথায় বাঁধিয়া বাড়ি ঢুকিতে।’ জামাকাপড় পরা আমার কাছে একটি শাস্তির মতো মনে হইত।
গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে ছেলেবেলার নানা ঘটনা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন জসীম উদদীন। বাবুই বাসার বর্ণনা, বাড়ির সামনের ছোট্ট নদীতে সাঁতারের বর্ণনা, হৈলডুবি, ঝাপড়ি প্রভৃতি খেলার কথা ও প্রকৃতির বর্ণনায় জসীম উদদীন অকৃপণ। কোনও অন্তর্দৃষ্টি নয়, আপন হৃদয়ে ধারণ করা নানাবিধ শব্দ ও চরিত্র নানা ব্যঞ্জনায় ঐশ্বর্য হয়ে ফুটে উঠেছে তার এই আত্মকথায়।
‘আমার মা’ অধ্যায়ে মা রাঙাছুটুর কষ্ট ও দারিদ্রের কথা, তাম্বুলখানা গ্রামে তার নানাবাড়ির (দাদামশায় দাদুর বাড়ি) কথা ব্যক্ত করেছেন জসীম। এই তাম্বুলখানা গ্রামে ১৯০৪ সালের ১ জানুয়ারি (মতান্তরে ১৯০৩) জন্মগ্রহণ করেছিলেন কবি। সে গ্রামের চারপাশে বিজাবন জঙ্গল। সেখানে বন্যজন্তু প্রচুর পরিমাণেই ছিল। তার নানা অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ ছিলেন। একমাত্র কন্যা রাঙাছুটুর বাড়ি তিনি সময় পেলেই আসতেন।
নানা যখনই আমাদের বাড়ি আসিতেন, হয়ত নারকোলের লাড়ু, খই–এর মওয়া অথবা কদমা বাতাসা লইয়া আসিতেন। তারপর দু’একদিন থাকিয়া চলিয়া যাইতেন। যাইবার সময় মা কাঁদিয়া ফেলিতেন। কোঁচার খোঁটে চোখ মুছিতে মুছিতে তিনি মাঠের পথ ধরিতেন।
সংসারের দারিদ্রের কথা লিখতে গিয়ে তিনি এ অধ্যায়ে অনেক আক্ষেপও করেছেন। এমনকি শিশু জসীম উদদীনের মনে হত, ‘আমার বাজান যদি মাষ্টার না হইয়া কৃষাণ হইতেন, আলিমদ্দি, বাহাদুর খাঁর মত খেজুরের গাছ কাটিয়া রস বাহির করিয়া আনিতেন, কত মজা করিয়া খাইতে পারিতাম।…এই মন্দভাগ্যের জন্য মাঝে মাঝে আমি কাঁদিয়া ফেলিতাম।’ এমন একটি সংসারকে দশভূজা হয়ে আগলে রাখতেন রাঙাছুটু। ছেলের গায়ে তিনি দারিদ্রের আঁচ লাগতে দিতে চাইতেন না। তার মায়ের পিঠা তৈরির বর্ণনা দিতে গিয়ে জসীম লিখেছেন—
…এইসব কাজ মা কত পরিপাটি করিয়া করিতেন। মা যেন তার স্নেহের সন্তানের জন্য একটি মহাকাব্য রচনা করিতেছিলেন।… কত যত্ন লইয়া, কত মমতা লইয়া, কত আয়াস আরাম ত্যাগ করিয়া তার সৃষ্টিকার্যে মশগুল রহিতেন। …দ্বিতীয় পিঠাটি খোলায় দিয়া মা মিঞাভাইকে ডাকিতেন। কি মিষ্টি করিয়াই ডাকিতেন, মাফি আয়রে পিঠা হইয়াছে। দ্বিতীয় পিঠাটি নামাইয়া ভাঙিয়া মা আমাদিগকে খাইতে দিতেন। পিঠা বানাইতে বানাইতে বারবার আমাদের মুখের দিকে চাহিতেন। মায়ের মুখে চোখে কি অপূর্ব তৃপ্তি!
আমাদের গরীবের সংসার। ঘি, ময়দা, ছানা দিয়া জৌলুস পিঠা তৈরী করিবার উপকরণ মায়ের ছিল না। চাউলের গুঁড়া আর গুড় এই মাত্র মায়ের সম্পদ। তাই দিয়া তিনি আমাদের জন্য অমৃত পরিবেশনের চিন্তা করিতেন।
‘আমার মায়ের সংসার’ পর্বে পোয়াতি মায়ের আঁতুরঘরের বর্ণনা অধিক প্রাধান্য পেয়েছে। তাদের সংসারে তারা ক’জন ছাড়া আর কেউ ছিল না। ফলে সব কাজ তার মা–কেই করতে হতো। এখানে একটি তথ্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বহু পরিবারেই আঁতুরঘর অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়— জানালাহীন, বদ্ধ, আলোবাতাস সেখানে ঢোকে না বললেই চলে। এই স্বাস্থ্য সচেতনতার যুগে কিছুদিন আগেও গ্রামবাংলার আশি শতাংশ বাড়িতে ওই রকম অস্বাস্থ্যকর ঘরে মায়েরা অশিক্ষিত ধাই–এর তত্ত্বাবধানে সন্তানের জন্ম দিতেন। বলা ভালো, দিতে বাধ্য হতেন। কিন্তু জসীম উদদীন লিখেছেন, ‘আমাদের মুসলমান পাড়ায় কিন্তু সবচাইতে ভাল ঘরখানাই পোয়াতী মায়েদের জন্য রাখা হইত।’

‘জীবনকথা’–র সবচেয়ে উজ্জ্বল, আনন্দ আর বিষাদের বর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত অধ্যায় ‘রাঙাছুটুর বাপের বাড়ি’। এই পর্বে নকশী কাঁথার মতো দৃশ্য বুনেছেন কবি। আসলে ‘জীবন কথা’য় যত না প্রাধান্য পেয়েছে তার (জসীম উদদীনের) কথা, তার চেয়ে অনেক অনেকগুণ বেশি গুরুত্ব পেয়েছে তার মায়ের কথা এবং প্রকৃতির বর্ণনা। রাঙাছুটুর বাপের বাড়ির গ্রাম তাম্বুলখানার সঙ্গে জসীম উদদীনের পিতার গ্রাম গোবিন্দপুরের দূরত্ব ছিল আট–নয় মাইল। মায়ের বাপের বাড়ি যাওয়ার সময় স্বভাবতই ছোট্ট জসীম তার সঙ্গী হতেন। অজ গ্রামের মুসলিম বাড়ির বউ কোথাও যাওয়ার সময় যেভাবে বাহনটিকে শাড়ি দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়, তেমনিভাবেই তার মা–ও বাপের বাড়ি যেতেন পাল্কি ধরনের বাঁশের ঢুলিতে। মামাবাড়ির এই যাত্রাপথের বর্ণনা জসীম উদদীন যেভাবে দিয়েছেন তেমনটি লিখতে পারলে যেকোনো লেখকই শ্লাঘা বোধ করবেন।
১. একটা দুইটা তিনটা পানের বর। চারিদিকের পাটখড়ির বেড়া। তারই ফাঁকে ফাঁকে সবুজ পাতা মেলিয়া পান গাছগুলি দেখা যায়। যেন কতগুলি শ্যামল রঙের গ্রাম্য মেয়ে সরু পাটখড়ির চিকের আড়াল হইতে উঁকি দিতেছে।
২. গোবিন্দপুরের গ্রাম ছাড়াইয়া শোভারামপুরের গ্রাম। মধ্যে ছোট গাঙ, বাঁশের সাঁকোতে সেই গাঙ পার হইয়া নদীর তীর দিয়া পথ। গাঙ তো নয়, পল্লীবাসীদের খেলাইবার একটি ঝুমঝুমি। …দল বাঁধিয়া বধূরা নদীতে জল লইতে আসে। নদীর ঘাটে বসিয়া কেহ স্নান করে, কেহ কাপড় ধোয়, সখীতে সখীতে হাসাহাসি করিয়া এ ওর গায়ে কলসীশুদ্ধ পানি ঢালিয়া দেয়। …সব বধূরা হাসিয়া খুন হয়। নদীও যেন ওদেরই মত হাসিমুখরা মেয়ে। তাই ওদের বুকে পাইয়া আপনার জলধারা নাচাইয়া কূলে কূলে ঢেউ তুলিয়া ওদের ক্ষণিকের ক্রীড়া কৌতুককে আরও সুন্দর করিয়া তোলে।

এ গ্রন্থে জসীম উদদীন যেন এক রূপমুগ্ধ পর্যটক। কখনো উপমা–উৎপ্রেক্ষা, কখনো রূপক, কখনোবা লোকজ ও ধন্যাত্মক শব্দে নান্দনিক পটভূমি রচনা করেন তিনি। প্রকৃতি ও নারী যেন একাকার হয়ে উঠে এ লেখায়। ছায়া সুনিবিড় শান্ত প্রিয় গ্রামগুলি আশ্চর্য এক মায়ায় জীবন্ত হয়ে ওঠে, যেখানে গাছে গাছে বাবুই বাসা, তিরতিরে স্বচ্ছ জলের ছোট্ট নদী, মাঠে মাঠে শস্যের সাত রঙা ক্যানভাস, পাখির হরেক রকম বিচিত্র সুরের ডাক। বাপের বাড়িতে বিবাহিত মেয়েরা বাবা–মা–পাড়াপড়শির কাছে আমৃত্যু ছোট্ট আদুরে মেয়ে। রাঙাছুটুও বাপের বাড়ি গিয়ে তেমনটি হয়ে ওঠতেন। তাতে বালক জসীমউদ্দীন বড়ই বিস্মিত হতেন—
কত রকমের খাবার করিয়া রাখিয়াছেন নানী। তিলে–পাটালি…ঢ্যাপের মোয়া, নারকেলের লাড়ু, ঘরের গরুর ঘন–আওটা দুধ, পাকা সিন্দুরে–গাছের আমের গোলা। নানী মার মুখে তুলিয়া দিতে যান। মা আমাকে দেখিয়া লজ্জা পান। নানীর হাতখানা আমার মুখের দিকে বাঁকাইয়া ধরেন। মা যেন আজ এতটুকু হইয়া গিয়াছেন। আমার চাইতেও ছোট। ছোট বলিয়াই কি এত আদর করিতে হয়?
এই অধ্যায়ে এসেছে তার মায়ের সখিদের কথা, রাঙাছুটুকে নিয়ে তাদের আনন্দময় আড্ডার পর্ব, একসঙ্গে সবাই মিলে তেল–সিন্দুর পরার কথা (তখনকার দিনে মুসলমান মহিলারা সিঁদুর পরতেন কোনো কোনো অঞ্চলে), তাম্বুলখানার বিখ্যাত পানের কথা, তার নানার মৃত্যুদৃশ্য, বাপের বাড়ি থেকে তার মায়ের ঘরে ফেরার মুহূর্তের বিষাদময় দৃশ্যের কথা, প্রভৃতি। আর এই বিদায়দৃশ্যের বর্ণনা লেখকের লেখায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে—
দেখিতে দেখিতে নানাবাড়ি ভরিয়া গেল। গরীবুল্লা মাতবরের বউ তার মেয়েকে লইয়া আসিল। ফেলি আসিল, আছিরণ আসিল। মিঞাজানের বউ, মোকিমের বউ, তাহেরের মা, পাড়ার সমস্ত মেয়ে আসিয়া নানীর বাড়িতে ভাঙিয়া পড়িল। আজ রাঙাছুটু বাপের বাড়ি হইতে শ্বশুরবাড়ি যাইবে। এ যে বাঙালী জীবনের যুগ যুগান্তরের বিয়োগান্তক ঘটনা।…কাঁদিতে কাঁদিতে মা নানার হাট হইতে আনিয়া নেওয়া নতুন কাপড়খানা পরিলেন। কপালে সিঁদুর দিয়া চোখে কাজল পরিয়া মা যখন দাঁড়াইলেন, মাকে বিসর্জনের প্রতিমার মতো দেখাইতেছিল।
সমাজের নাক উঁচু মানুষের চোখে যাদের প্রান্তিক অবস্থান, সেই তথাকথিত নিম্নবর্গের মানুষেরা জসীম উদদীনের লেখায় বারবারই উঠে এসেছে। জসীম উদদীনের সঙ্গে আজীবন তাদের আত্মিক বন্ধন। মনীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ওরফে মনাদা জসীমউদ্দীন–জীবনকথার অন্যতম এক চরিত্র। খুবই মজার মানুষ ছিলেন তিনি। পদ্মার ভাঙনে যখন গ্রামের পর গ্রাম তলিয়ে যাচ্ছে জলের তলায়, গরীব মানুষেরা ভিটেমাটি হারিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে পড়ছে, সেই করুণ দৃশ্য সহ্য হলো না মনাদা এবং জসীম উদদীনের। দুস্থদের সাহায্য করার জন্য তারা এলাকার স্কুলছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করলেন। ত্রাণকার্যে পাশে পেলেন ভূতপূর্ব কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট অম্বিকাচরণ মজুমদারের পুত্র কিরণ মজুমদারকে। মাঝপথে বাগড়া দিলেন ফরিদপুরের প্রসিদ্ধ উকিল বাবু পূর্ণচন্দ্র মৈত্র এবং মথুরানাথ মৈত্র। তাদের আশঙ্কা ছাত্রদের যদি কোনো বিপদ হয়। কৌশলে বেনামী পত্র লিখে মনাদা ও জসীম তাদের ওই আপত্তি প্রত্যাহার করাতে বাধ্য করালেন। ফল হল এই যে, শত শত ছাত্র গ্রামবাসীদের সাহায্যের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল। এই মনাদাকে নিয়েই কৈশোরে একটি পত্রিকা (ঊষা) প্রকাশের আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেলেছিলেন জসীমউদ্দীন। কিন্তু শেষমুহূর্তে অর্থের অভাবে ‘ঊষা’ প্রকাশের আলো দেখেনি।
জীবন কথা–র শেষ পর্বে আমরা মেজদি ও সেজদির কথা জানতে পারি। এরা দু’জনে ছিলেন জসীমউদ্দীনের বন্ধু ধীরেনের দুই দিদি। এদের অকৃত্রিম স্নেহ ও ভালোবাসায় সঞ্জীবিত হয়েছিলেন জসীম উদদীন। বিশেষত, সেজদি ছিলেন তার সবচেয়ে প্রিয়জন। এই দিদির জন্য জীবন পর্যন্ত দিতে কুণ্ঠিত হতেন না তিনি। সেজদি নানাভাবে জসীম উদদীনকে সাহায্য করতেন। নদীতে বাড়ি ভেঙে গেলে জসীম–এর পিতা প্রায় নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন। তখন এই সেজদি জসীমকে বই–খাতা–পত্র কিনে দিতেন। তাকে ডাকতেন ‘সাধু’ বলে। সেজদির টাইফয়েড হলে বরফের দরকার পড়ল। কাছেপিঠে পাওয়া যায় না। যেতে হবে রাজবাড়ি। জসীম উদদীন বরফ নিয়ে অম্বিকাপুর স্টেশনে নেমে ওই আধমনি বরফ মাথায় নিয়ে ঘেমে–ভিজে সেজদির বাড়িতে পৌঁছোলেন। রাস্তায় বারবার প্রার্থনা করতে করতে এলেন, “খোদা আমার সেজদিকে ভাল করিয়া দাও।” সেজদির স্বামী গণেশচন্দ্র ঘোষাল সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। জসীম উদদীন লিখছেন, “তিনিও সেজদির মত আমার লেখার খুব অনুরাগী ছিলেন।…সেকালের লেখা আমার বহু কবিতায় তাঁহার সংশোধনের ছাপ আছে।”
জসীম উদদীনের এই গ্রন্থে সততই উৎসারিত হয়েছে আলো। সর্বদা আধুনিক কথ্যরীতির দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি এ গ্রন্থের ভাষাকে করেছেন শ্রুতিমধুর। শব্দসন্ধানী স্রষ্টা হয়ে তিনি শৈশব ও কৈশোরের অতলে প্রবেশ করে নিপুণ ডুবুরির মতো তুলে এনেছেন আপন জীবনদর্শনের নান্দনিক রূপ। তবে তার জীবনের বাল্য ও কৈশোরের পুঙ্খানুপুঙ্খ ঘটনার উল্লেখ এ গ্রন্থে নেই। সেই সময়কালের সামাজিক ও রাজনৈতিক পালাবদলের কোনো উল্লেখও নেই এ গ্রন্থে। জীবন কথা লিখতে গিয়ে এই বিষয়গুলির ক্ষেত্রে আশ্চর্যরকম নীরব থেকেছেন তিনি। সম্ভবত রূপতাপস জসীম উদদীন ডায়েরি লিখতে চাননি। তার জীবন কথা জানার জন্য ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উন্মুখ হবে— এমন ধারণা আদৌ পোষণ করতেন না হয়তো। তাই নিজের প্রতি এতখানি নিরাসক্ত থাকতে পেরেছেন তিনি।
পরিশেষে শুধু এটুটুই বলি, এক নির্ভেজাল আনন্দ সাগরে ডুব দেওয়ার জন্য আসুন পাঠক, আবারও জসীম উদদীনের ‘জীবন কথা’ নিয়ে পড়তে বসে যাই।