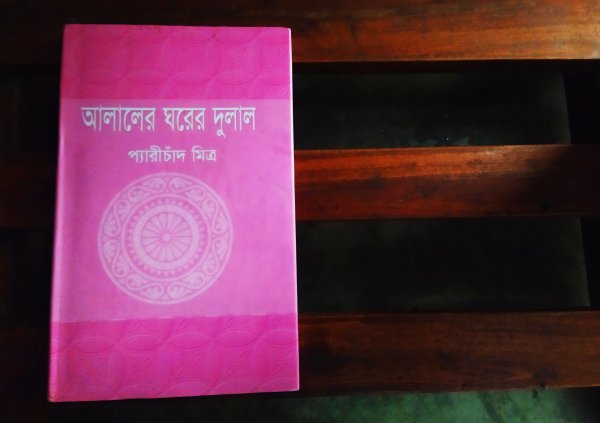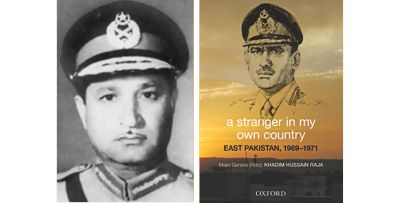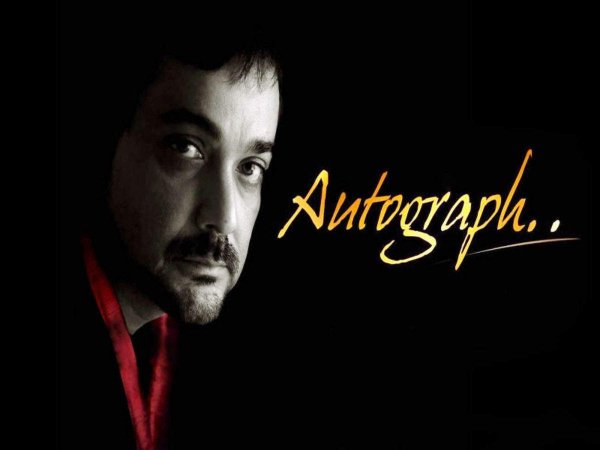“আমি ভেবেছিলাম, আমাদের ঘরটা বানাব গাছের একদম উপরে, প্রকাণ্ড শাখায়। পাখিদের মতো উড়ে যাব পাহাড়ে।”
কেন্দ্রীয় চরিত্রের এই সংলাপের পরপরই কালো পর্দা কেটে গিয়ে দেখা মেলে মেঘের। মেঘ কেটে দেখা যায় নিচের ওই শহর। হিটলার এসেছেন সে শহরে। হিটলারের ওই প্লেন থেকেই ‘বার্ডস আই ভিউ’ শটে শহরটা দেখছিল দর্শক। নিচের সেই শহরের আকাশে, বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে হিটলারের স্তুতি। সারিবদ্ধ মানুষ তাকে স্বাগত জানাচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কাল তখন। ১৯৩৯ সাল। অস্ট্রিয়াতে হিটলারের আগমনের সেই নিউজরিল মন্তাজ শেষে দর্শককে নিয়ে যাওয়া হয় অস্ট্রিয়ার এক গ্রামে। নদীর পাশে; পাহাড়ের উপরে এক শান্ত গ্রাম, যেন পৃথিবীতে থাকা এক টুকরো স্বর্গ। সেই কথাটাকে আক্ষরিক রূপ দিতেই যেন শুরুর ওই শটটা।
ওয়াইড শটে চোখে পড়ে বিস্তীর্ণ ফসলি জমি। ওদিকে ডিপ ফোকাসে দেখা যায়, দূরের ওই পাহাড়চূড়া; চার্চের উঁচু স্তম্ভ। ধানগাছ কাটতে দেখা যায় সিনেমার কেন্দ্রীয় চরিত্র ফ্রাঞ্জকে। ওদিকে তার জীবনসঙ্গিনী ফ্রাঞ্জিস্কা শান দিচ্ছে কাস্তেতে। তাদের প্রথম দেখা হওয়া থেকে সংসারজীবন- সংক্ষেপে পুরোটাই ভয়েসওভারে বলতে থাকে ফ্রাঞ্জিস্কা। মোটরসাইকেলে চড়ে এসেছিল সেদিন ফ্রাঞ্জ। পরনে তার সবচেয়ে দামী স্যুটটা। ফ্রাঞ্জিস্কা পরেছিল সবচেয়ে পছন্দের নীল জামাটা। তাকে দেখে ফ্রাঞ্জের সেই হাসিতেই বুঝে গিয়েছিল, এই যুবক তারই।
জীবন তখন ছিল সহজ, সাধারণ। তারা একসাথে ঘর বাঁধল উপত্যকায় এসে, যেখানে কোনো সমস্যাই তাদের ছুঁতে পারবে না। মেঘের উপরে তাদের বাস, ফ্রাঞ্জিস্কা বলতে থাকল। কোল জুড়ে এল দুটো পরী। ধান চাষ করেই তাদের জীবন সুন্দরভাবে চলে যেত। ধান মাড়াইয়ের পর আগাছা দিয়ে তারা দু’জনে মাতত খুনসুটিতে।

Image Source: Foxlight
তারপর তো ফ্রাঞ্জ চলে গেল যুদ্ধে। যেতে বাধ্য হলো আসলে। ফ্রাঞ্জিস্কা চিঠিতে জানাচ্ছিল, বাছুরগুলোর দেখাশোনার কাজে তাকে খুব প্রয়োজন এখানে। ওদিকে যুদ্ধের মঞ্চে বসে ফ্রাঞ্জ প্রত্যুত্তরে লিখছিল,
“কী হয়েছে আমাদের দেশটার, যাকে আমরা ভালোবাসতাম?”
ফ্রাঞ্জের এ প্রশ্ন থেকেই তার দর্শন বোঝা যায়। যুদ্ধ তার কাছে বিজয় কিংবা শান্তি ছিনিয়ে আনার কোনো অস্ত্র নয়। বরঞ্চ ক্যান্সারের মতো একটা মরণব্যাধি। তাইতো সে ফেরত আসে ময়দান থেকে। ফ্রাঞ্জের বন্ধু যখন বলছিল, “আমরা ভেবেছিলাম শান্তি আসবে। কিন্তু যুদ্ধ চলছে তো চলছেই। জানি না কেন।” ফ্রাঞ্জ তখন পাল্টা প্রশ্ন করে, “যে কারণটার জন্য আমরা লড়ছি, তুমি কি বিশ্বাস করো সেই কারণটায়?” উত্তর আসে, “না”।
মেয়র যুক্তি দেয়, হিটলার আসার আগে এই পুরো দেশটাই ধসে যাওয়ার পর্যায়ে ছিল। আরেকটা ব্যাবিলন হওয়ার দ্বারপ্রান্তে ছিল। তারা বেঁচে তো ছিল, কিন্তু জীবনটা হারিয়েছিল। হিটলার সে অবস্থা থেকে পরিত্রাণকারী হয়ে এসেছে। তাদের মতাদর্শের জায়গাটা সম্পর্কেও দর্শক তখন জানতে পারে। কিন্তু ফ্রাঞ্জ জানে, এসবের কোনো অর্থ নেই। যুদ্ধের কারণে মারা পড়ছে অসহায় মানুষ। অন্য দেশের ক্ষতি করে, দুর্বলের উপর অত্যাচার চালানোই হচ্ছে যুদ্ধের কাজ। ধর্মযাজকরা যুদ্ধসেনাদের হিরো বলছে, ফেরেশতা বলছে। অথচ হিরো তো তারাই, যারা নিজেদের ঘরবাড়ি, সম্বল বাঁচানোর জন্য শেষ অব্দি লড়াই করে। ফ্রাঞ্জ বলছিল সেসব চার্চের ফাদারকে। কিন্তু ফাদার উল্টো তাকে যুদ্ধ ছেড়ে আসার পরিণতি ভাবতে বলে ভয় দেখায়। এটাই ছিল তখনকার বাস্তব পরিস্থিতি।
ধর্মযাজকের কাজ যেখানে শান্তির কথা বলা, শাপমোচনের উপায় দেখানো; সেখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে অনেক যাজক পরোক্ষভাবে ছিলেন হিটলারের নাৎ্সি বাহিনীর সহযোগী। ফ্রাঞ্জের যুদ্ধ ছেড়ে আসাটাকে গোটা গ্রাম দেখে গর্হিত অপরাধ হিসেবে। মেয়রের সেই মতাদর্শ থেকেই গোটা গ্রামের মানুষদের নৈতিক অবস্থানটা বোঝা যায়। হিটলার তাদের সেভাবেই বুঝিয়েছিলেন। সে কারণেই ফ্রাঞ্জের প্রতি গ্রামের সবার ওমন সরু দৃষ্টিভঙ্গি স্বাভাবিকই। তার এবং তার পরিবারের প্রতি সবার মনোভাব অন্যরকম হয়ে যায়। অনেকটা একঘরে করে রাখার মতো অবস্থা হয়।
এরপর ফ্রাঞ্জকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় দ্রোহের অপরাধে। মাসের পর মাস আটকে রাখা হয়। স্ত্রী-সন্তানদের গোটা সমাজ কোণঠাসা করে রাখে। এরপর রচিত হলো এক করুণ, ছুরির ফলার মতো তীক্ষ্ণ হয়ে হৃদয়ে গেঁথে যাওয়া দৃশ্যপট। কিন্তু তারপরও ফ্রাঞ্জ তার বিশ্বাসে অটল আর সেই অটলতার দেনা শোধের পরিমাণও যে হয়ে এল অনেক বেশি আর ভারী!

Image Source: Foxlight
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎ্সি বাহিনীর হয়ে যুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানানো এক অস্ট্রিয়ান লোকের সত্য ঘটনাবলি অবলম্বনেই নির্মিত ‘আ হিডেন লাইফ’ সিনেমাটি, যা দিয়ে বেশ কয়েকবছর আবারো নিজের ক্ষমতার জায়গাটি নিশ্চিত করলেন মাস্টার পরিচালক টেরেন্স মালিক। যুদ্ধবিরোধী বক্তব্যের দিক থেকে এই সিনেমা পাশাপাশি বসবে তার আরেক গ্রেট সিনেমা ‘দ্য থিন রেড লাইন’-এর। আর তার ভিজ্যুয়াল কাব্যিকতা এবার হয়ে উঠেছে মহাকাব্যিক। মালিকের ক্যারিয়ার গ্রাফটা তার সিনেমাগুলোর প্রকৃতির মতোই, নিরীক্ষাধর্মী। ‘ব্যাডল্যান্ডস’ এবং ‘ডেইজ অভ হেভেন’-এর মতো দুটো সিনেমা উপহার দেওয়ার পর প্রায় ২০ বছর অদৃশ্যই ছিলেন একপ্রকার, ৯৮-এর দ্য থিন রেড লাইনের আগে।
মাস্টারফুল কাজ ‘দ্য ট্রি অভ লাইফ’ (২০১১)-এর পর আরো গোটা তিনেক সিনেমা (‘টু দ্য ওয়ান্ডার’, ‘নাইট অফ কাপস’, ‘সং টু সং’) বানালেও, সেগুলো ঠিক ‘মালিকীয়’ সিনেমা হয়ে উঠেনি। অবাক করার মতো সুন্দর ভিজ্যুয়াল ভাষা থাকলেও ন্যারেটিভে অতি-নিরীক্ষা প্রবণতা কাজগুলোকে অসংসক্ত এবং বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। তবে ‘আ হিডেন লাইফ’ দিয়ে মালিক তার পরিচিত ন্যারেটিভেই ফিরেছেন। পূর্ববর্তী সিনেমাগুলো বিচারে, লিনিয়ার ন্যারেটিভেই এগিয়েছে এই সিনেমা। সেইসাথে, দৈর্ঘ্যের বিচারে এটি তার সবচেয়ে দীর্ঘ সিনেমা। সেল্ফ-ইন্ডালজেন্স তো যুক্ত আছেই এই দৈর্ঘ্যে, তবে তারচেয়েও বেশি যেটা প্রতিভাসিত হয়, তা হলো; মালিক সিনেমাটির প্রধান চরিত্রের বন্দীদশা এবং তার ন্যায়বিচারের দীর্ঘসূত্রিতাকে দর্শকমনে গভীরভাবে জায়গা দিতেই কাজটি করেছেন।
ভয়েসওভার ন্যারেশান মালিকের সিনেমার অন্যতম প্রধান একটি অনুষঙ্গ। শান্ত, ধীর; একরকম একটা সুরে চরিত্ররা গল্প বলতে থাকে, যা দর্শককে নিবিষ্ট করে ফেলে সিনেমার সাথে। একইসাথে দর্শকের অনুভূতির সাথে অন্তরঙ্গ, কিন্তু পরিচালকের পরিচালনার রীতিতে মহাকাব্যিক হওয়ার একটা বৈপরীত্য তার সিনেমাগুলোয় পেলবতা যোগ করে, যার খাঁটি গন্ধটা আবার অনেকদিন পর এই সিনেমায় পাওয়া গেল। দার্শনিকতা এবং আধ্যাত্মিকতার বিচারে তার সিনেমাগুলো যে প্রগাঢ়তা বহন করে, তা বোধকরি নতুন করে বলার প্রয়োজন রাখে না। এ কারণে মালিকের সিনেমা ‘পূর্ণভাবে’ উপলব্ধি করতে দর্শককে দর্শন সম্পর্কে জ্ঞাত থাকতে হবে এবং চিন্তাচেতনায় গভীর হতে হবে।
ফেরা যাক, তার সিনেমার দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক তত্ত্বে। দু’টি দিক তার এই সিনেমায় ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে প্রধান চরিত্রের গঠনে এবং মালিকের নিজের অদৃশ্য উপস্থিতিতে। আ হিডেন লাইফে নৈতিকতা নিয়ে দ্বন্দ্বের প্রশ্নটা অনেক প্রচলিত সিনেমার উপায়ে আরোপিত হয়ে আসেনি। পরিস্থিতি এবং চরিত্রদের অবস্থানই আপনা-আপনি সেইসব প্রশ্ন দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আর তা অমোঘ হয়েছে সকলের শক্তিশালী অভিনয়ে। কিংবদন্তী মিকায়েল নিকভিস্ট এবং ব্রুনো গাঞ্জের শেষ সিনেমা এটি। ওদিকে শান্তিবাদী এবং বিশ্বাসী ফ্রাঞ্জ চরিত্রে অগাস্ট ডিয়েল চরিত্রটির অন্তর্দৃষ্টিকে পুরোপুরি মেলে ধরেছেন তার অভিনয়ে।

Image Source: Foxlight
যুদ্ধের আসল প্রকৃতি এবং এর অর্থহীনতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে এ সিনেমা ভয় পায়নি। পৃথিবী নামক গ্রহে মানুষের অস্তিত্ব নিয়েও কারণ খুঁজতে চেয়েছে। কারো বিশ্বাসে আঘাত হানার যে চিরন্তন রীতি মানব প্রকৃতিতে দেখা যায়, তার কারণ যাচাই করতে চেয়েছে এই সিনেমা। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে পিছু হটলে তা কাপুরুষতা বলে গণ্য হবে কি না, সে প্রশ্নও তুলেছে এই সিনেমা এবং তলিয়ে দেখতে চেয়েছে এমন পরিস্থিতিতে মানুষ কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায়। সিনেমার একটি চরিত্রের মুখে শোনা যায়,
“ন্যায়বিচার চেয়ে আক্রমণের শিকার হওয়ার চাইতে, অবিচার মেনে নিয়ে একা একা ভোগাটাই শ্রেয়।”
এ কথাতেই সিনেমার মূল বিষয় লুকিয়ে আছে। এ কথার জের ধরেই উত্থাপিত হয় উক্ত প্রশ্নগুলো। ওভাবেই স্পষ্ট হয় সিনেমার দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক কোণ, যেদিক থেকে ধরা পড়ে সিনেমার অন্তরঙ্গ প্রকৃতি। আর মহাকাব্যিকতা তো রয়েছে সর্বোপরি সেটিংয়ে। সেইসাথে, চিত্রনাট্যের যথেষ্ট ডিটেল বা বিবরণের জায়গাটি এবং চরিত্রদের আঙ্গিক গঠন অনুভূতিটাকে আরো পোক্ত করেছে।
মালিকের সিনেমা গল্পসর্বস্ব তো নয়ই, বাগ্মিতাও নেই। সেটা ঠিক এই অর্থে যে, সংলাপ কম। প্রয়োজনের বেশি একটা কথাও নেই। তাই বলে কি তার সিনেমা বড় অংশে নির্বাক? মোটেও তা নয়। তার সিনেমা সর্বক্ষণই কথা বলে, তবে সেটা ভিজ্যুয়ালে। নিখুঁত আর অনিন্দ্যসুন্দর প্রতিটি ইমেজারিই কথা বলে, চরিত্রদের বলতে হয় না। বিষাদকেও যে এতটা স্নিগ্ধ, মন ভেজানো রূপে ধরা যায়, আ হিডেন লাইফের ইমেজারিই তার প্রমাণ। তাইতো তার অতি-নিরীক্ষামূলক কাজগুলোও আর যা-ই হোক, একেকটা ভিজ্যুয়াল কবিতা হয়ে উঠতে ভুলেনি।
তবে কেউ কেউ খানিক হতাশ হবেন সিনেমাটোগ্রাফিতে ইমানুয়েল লুবেস্কির নাম না দেখে, যিনি ২০০০ পরবর্তী মালিকের সবক’টি (ছয়টি) সিনেমার সিনেমাটোগ্রাফার ছিলেন। কিন্তু ইয়র্গ উইডমারকে নিয়ে টেরি মালিক যেই ওয়াইডস্ক্রিন ভিজ্যুয়াল প্রতিষ্ঠা করেছেন, লুবেস্কির অভাববোধ অনেকাংশেই কম হবে। শটগুলো যতটা ওয়াইডে নেওয়া সম্ভব, ততটা নিতে ১২ মি.মি.তেই বেশিরভাগ অংশের শ্যুট করা হয়েছে। আর লং লেন্স হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে ১৬ মি.মি.। ওয়াইডস্ক্রিন হওয়া সত্ত্বেও অভিনেতাদের ক্লোজ আপ’টা পাওয়া গেছে লেন্সের ফোকাল লেন্থের কারণে।

Image Source: Foxlight
ক্যামেরার পজিশন অবশ্য স্ট্যাটিক রাখেননি মালিক, প্রধান চরিত্রের নিজের বিশ্বাসের উপর আঘাত আর যুদ্ধের পরিস্থিতি নিয়ে তার উদ্বেগ প্রকাশ করতে। তবে মুভমেন্ট খুবই ফ্লুইড, তার বাকি কাজগুলোর মতো। শটের কম্পোজিশন সচরাচরের মতোই চিত্রকলার অনুরূপ। সম্মোহনী ডিসলভ তো আছেই। সফট লাইটিং চোখটাকে শান্তিতে ভেজায় যেমন, তেমনি জেলে বন্দী অবস্থায় লো-কি লাইটে করা দৃশ্যগুলো হাঁসফাঁস জাগায় সেগুলোর নির্মমতা দিয়ে। যুদ্ধের ভয়াবহতার বেশিরভাগটা অফস্ক্রিনে থাকা সত্ত্বেও সেটা অনুভূত হয়েছে জেমস নিওটনের বিষণ্ণ আবহসঙ্গীতে। ভয়ের অনুভূতি জাগিয়েছে। সেটা যেন স্ক্রিনের এক কোণে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। ইমেজারি আর আবহসঙ্গীতের এই দ্বন্দ্ব মালিক তার প্রথম সিনেমা থেকেই রেখেছেন। অভিভূতকারী ইমেজারির সাথে হৃদয়ে হাহাকার তোলার মতো সঙ্গীত। এই দ্বান্দ্বিকতা তার সিনেমার প্রকৃতিকে করে আরো জটিল।
তবে আ হিডেন লাইফে দ্বান্দ্বিকতা আরো অভিঘাতী হয়ে ধরা দিয়েছে ভিজ্যুয়ালের সাথে বিষয়ের প্রসঙ্গে। ওই দ্বান্দ্বিকতাই এই সিনেমাকে করেছে স্বকীয়। প্রকৃতির নৈসর্গিক সৌন্দর্যকে তো তিনি বরাবরই ধরেন। তবে, দ্য থিন রেড লাইনের পর আরো একবার ধরলেন যুদ্ধের ভীতিতে। এবং তা দিয়ে মালিক প্রতীয়মান করে তুলতে চেয়েছেন, মানুষ নামক প্রাণীর এত ভয়াবহতার মুখেও কীভাবে প্রকৃতি তার সৌন্দর্য নীরবে বিলায়? এই প্রাণীর দ্বারা তার বিনাশ জেনেও কেন প্রকৃতি হাসিমুখে তার অনাবিল সৌন্দর্য নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে? তা দিয়েই মালিক মানুষের শেকড়জাত স্বভাবকে পর্যবেক্ষণ করেছেন।

Image Source: Foxlight
আ হিডেন লাইফ ২০১৯-এর অন্যতম স্বকীয় এবং টেরেন্স মালিকের শ্রেষ্ঠ কাজগুলোর একটি হয়েই শুধু রয়ে যায়নি, সবদিক বিবেচনায় তার ক্যারিয়ারের রেট্রোস্পেক্টিভ হিসেবে কাজ করেছে, যেমনটা একই বছরে স্করসেজির ‘দ্য আইরিশম্যান এবং টারান্টিনোর ‘ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন হলিউড’ও করেছে। ফ্রাঞ্জ চরিত্রটি দিয়ে বিশ্ব জুড়ে চলা মানবতার উপর সংঘাত এবং মানুষের দুর্দশাকে সার্বজনীন স্কেলে উপস্থাপন করেছে।
তবে কি এই ধরণীতে ভুগতে থাকাটাই মানুষের একমাত্র পরিণতি? কেন তবে তার, পৃথিবীতে আসা? আরো বহু প্রশ্নের উত্থাপন মালিক করেছেন, কিন্তু উত্তর দেননি সবের। দিতে চাননি। কারণটাও জানিয়ে দিয়েছেন। সঠিক সময়েই উত্তর আপনা-আপনি মিলবে। সিনেমায় প্রশ্নগুলো উত্থাপিত হয়েছে দর্শকের আত্মদর্শনকে জাগাতে, তাই স্বভাবতই উত্তর খোঁজার প্রক্রিয়াও হবে তেমন। স্বীয় অভিজ্ঞতাই হয়তো মিলিয়ে দেবে সব উত্তর, নাহয় অপেক্ষা অন্তহীনের।