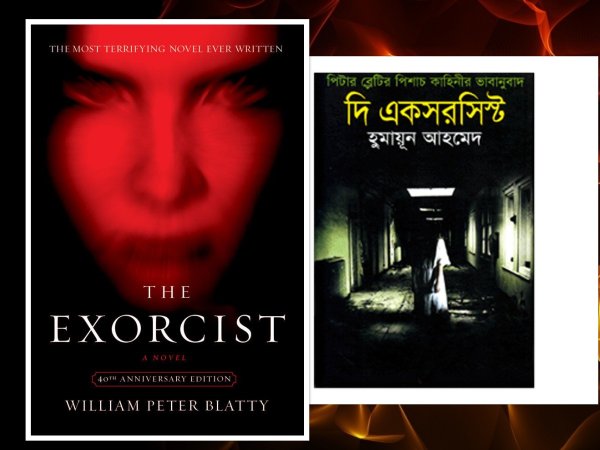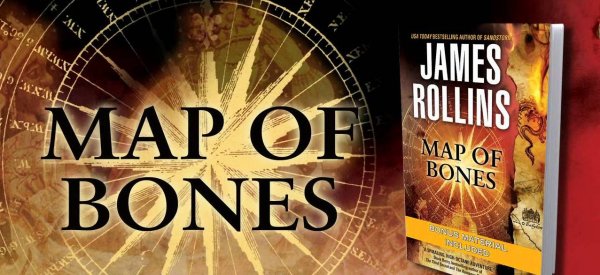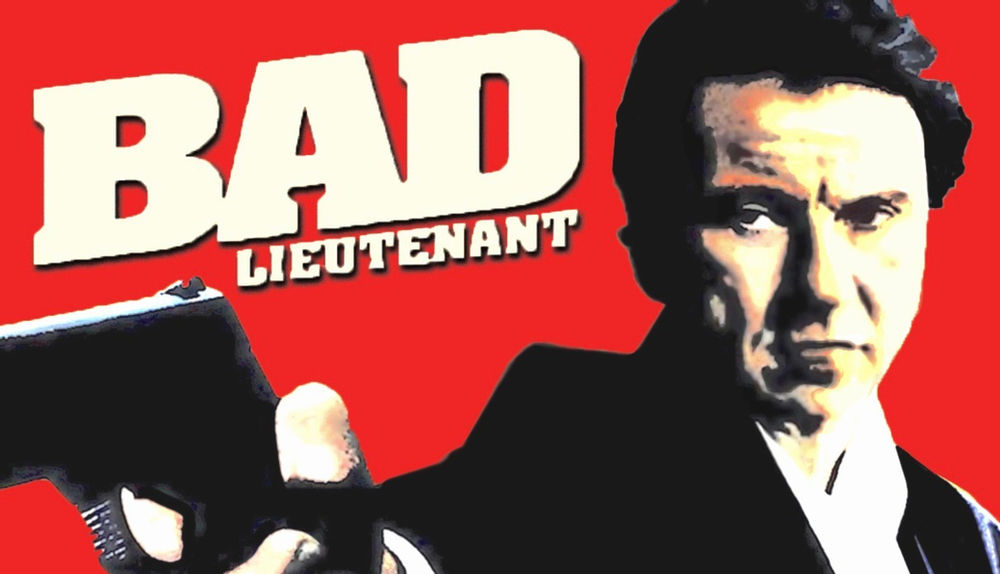
আবেল ফেরারা, খ্যাপাটে এবং একজন প্রথিতযশা ইন্ডি-ফিল্মমেকার। গোটা ক্যারিয়ারেই যিনি ইন্ডি কাজ করে গেছেন। তাকে বিশেষায়িত করা হয় ‘প্রভোকেটিভ অঁতর’ বলে। আবার কুখ্যাত ফিল্মমেকার হিসেবেও তিনি পরিচিত। সেটার কারণ অবশ্য তার সিনেমার বিষয়াদি। নিও-নোয়াহ্’র সেটিংয়ে মেট্রোপলিসের নানান নোংরা কানাগলি, অপরাধ, মাদক, যৌনতার গল্প বলেন তিনি। সেই ‘ড্রিলার কিলার’ (১৯৭৯)-এর হিপি জীবনযাপনের মধ্য দিয়েই তার এসব নিগূঢ় বিষয়াদি তিনি উপস্থাপন করা শুরু করেছিলেন, যা পাওয়া যায় এই ‘ব্যাড ল্যুটেন্যান্ট’ (১৯৯২) এ। ‘কিং অভ নিউ ইয়র্ক’ (১৯৯০) আর এই সিনেমা দিয়েই ফেরারা ৯০ দশকের আমেরিকার ইন্ডি-সিনেমার দৃশ্যপটে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একজন নির্মাতা হয়ে উঠেছেন। এই ‘ব্যাড ল্যুটেন্যান্ট’ ইন্ডি-মুভমেন্টের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং ফেরারার নিজের ক্যারিয়ারেরও অন্যতম সেরা সিনেমা।
সিনেমার বিষয়বস্তু, নাম থেকেই আন্দাজ করা যায়। হ্যাঁ, একজন ল্যুটেন্যান্ট, যার নৈতিকতার কোনো মাপকাঠি নেই, তাকে নিয়েই এই সিনেমা। তার নাম নেই, ওই পদবীই আছে শুধু। এবং সিনেমা এগোতে এগোতে বোঝা যায়, নামটা আসলে প্রয়োজনীয় না। সিনেমার প্রারম্ভিক দৃশ্য থেকেই দর্শক তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা পায়।
নাম ক্রেডিটের সাথে সাথে দুটো কণ্ঠ শোনা যায়। আমেরিকান বেইজবল টিম ‘মেটস’ এবং ‘দ্য ডজারস’-এর বাজি লাগায় একজন। উত্তেজিত কণ্ঠস্বর তার। বাজি হারতে যাচ্ছে। সেই সিনেমার ল্যুটেন্যান্ট চরিত্রটি। এই তর্কাতর্কির মাঝে তার দুই ছেলে গাড়িতে উঠল। স্কুলে নামিয়ে দিয়েই ওখানেই গাড়ি স্থির রেখে কোকেইনে টান দিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিল। রেডিওতে তখন খেলার টানটান উত্তেজনা পর্ব।
এবং হেরে গেল ল্যুটেন্যান্টের বাজি ধরা টিম। ক্ষোভ প্রকাশ করতে পিস্তল বের করে গাড়ির রেডিওটাই উড়িয়ে দিল। এমনই খ্যাপাটে উন্মাদ সে। এরপর সেখান থেকে একটা ক্রাইম সিনে গেল। খুন হয়েছে। গাড়ির চালকের আসনে খুন হয়ে পড়ে থাকা মেয়েটার লাশ দেখার সময় লিউটেন্যান্টের একটা বিকৃত দৃষ্টির আভাস ওই দৃশ্যটায় পাওয়া যায়। সেখান থেকে সে গেল ফের বাজি ধরা নিয়ে কথা বলতে। তারপর স্থানীয় গুন্ডাদের কাছ থেকে ড্রাগ কিনতে। পতিতার কাছেও যায়। হোটেল রুমে নেশায় আর মদে সে তখন চুর।
পতিতার কাছে যতটা না সে যৌন ক্ষুধা মেটাতে যায়, তারচেয়েও বেশি হয়তো নারীর স্পর্শ পেতে। নেশায় এতটাই বুঁদ সে, যে গ্লাসটাও সোজাসুজি ধরতে পারছিল না। নগ্নাবস্থায় হাত দুটো দু’পাশে ছড়িয়ে ক্রাইস্টের ভঙ্গীতে অদ্ভুত স্বরে কঁকিয়ে উঠল সে। যেন সমস্ত শরীরের বেদনার শাব্দিক রূপ ওই কঁকিয়ে ওঠাটা। এই রূপক সিকুয়েন্সটা হয়তো তার নিজস্ব সত্ত্বাকে হারিয়ে ফেলার বেদনাটাই প্রকাশ করছে।

Image Source: Aries Films
কিন্তু ওই শোকে সে বেশিক্ষণ থাকে না। কিছুক্ষণ বাদেই আবার ডুবে যায় কোকেইনের নেশায়। সুপারশপ থেকে টাকা চুরি করা দুই চোরকে ধরে টাকাটা নিজের পকেটে ঢুকিয়ে তাদের খেদিয়ে দেয়। এভাবেই তার চলে। মদ, নেশা, বাজি, দুর্নীতি। সিনেমার প্রথম ২০/২৫ মিনিটে তার এই অন্ধকারে পড়ে থাকা জীবনটাকেই দেখানো হয়। সেভাবে এতে গল্প নেই। গোটা সিনেমাটাই যে একটা চরিত্রনির্ভর ড্রামা।
বলা যায়, যতটা না গল্পের বাঁক, তারচেয়েও বেশি চরিত্রের জীবনে একটা মোড় আনতে, সিনেমায় আসে চার্চের নানকে দুই যুবকের ধর্ষণের ঘটনাটি। কেইসটা তার হাতে আসে। সে দুই ধর্ষকের পরিচিতি জানতে চায়। কিন্তু নান তাকে বলে, “আমি তাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।” একথা সে কিছুতেই মানতে পারে না। এমন ঘৃণ্য অপরাধ করেও কেন পার পাবে ওই দুই অপরাধী? নান তার কথায় কোনোভাবেই প্রভাবিত হয় না। বরঞ্চ, নানকে বোঝাতে গিয়ে সে নিজেই তার বিশ্বাস নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে যায়। আটকে যায় পাপবোধের যন্ত্রণায়।
মার্টিন স্করসেসি ৮৮ সনে বানিয়েছিলেন ‘দ্য লাস্ট টেম্পটেশন অভ ক্রাইস্ট’। আর এই ‘ব্যাড ল্যুটেন্যান্ট’কে বলতে হয় আবেল ফেরারার নিজের একটা সংস্করণ, ওই সিনেমার। (স্করসেসি অবশ্য এই সিনেমাকে ৯০ দশকের অন্যতম সেরা সিনেমা হিসেবে সম্মানিত করেছেন।) এখানে ওই পথভ্রষ্ট ল্যুটেন্যান্টের মধ্য দিয়েই তিনি ক্রাইস্টের কষ্টের সুরটা এনেছেন। প্রশ্ন ছুঁড়েছেন ক্ষমার প্রকৃতি নিয়ে; কতটুকু করলে(?) আর কতটা চরম অব্দি(?) ক্ষমা করা যায়। ল্যুটেন্যান্ট যখন পুরোপুরি হতাশ হয়ে মেঝেতে লুটিয়ে কঁকাতে থাকে বিরামহীন, তখন তার সামনে উদয় হওয়া রক্তাক্ত ক্রাইস্টকে দেখে সে ক্ষিপ্ত প্রশ্ন করে,
“এতদিন যখন অপরাধ করে বেড়াচ্ছিলাম তখন তুমি কোথায় ছিলে? কী করছিলে?”
জো লুন্ডের সাথে একত্র হয়ে লেখা, ফেরারার এই চিত্রনাট্য শুধু প্রধান চরিত্রটির নৈতিক সমস্যাকেই না, তার আধ্যাত্মিক দ্বন্দ্বকেও উপস্থাপন করে। এবং সেটাই মূলে প্রোথিত থাকা বিষয়। লিউটেন্যান্ট অবিশ্বাসী নয়। তার গাড়ির রিয়ারভিউ মিররের উপর ঝোলানো ক্রুশকাঠি দেখেই সেটা জানতে পারা যায়। কিন্তু সে গভীরভাবে ক্যাথলিকও না। অপরাধ আর নেশার এই উন্মত্ত জীবন তার ক্যাথলিক বিশ্বাসের সাথে দ্বন্দ্ব স্থাপন করে, যে দ্বন্দ্বের মাঝে সে নিজের আত্মাটাকেই হারিয়ে ফেলেছে। মূলত তার অস্তিত্ববাদী চেতনাকে জাগিয়ে তুলতেই গল্পে নানের প্রবেশ। নানের উপস্থিতি তার হাড় জিরজিরে অস্তিত্বে সন্দেহের কাঁপন ধরায়। তার পাপগুলো, পাপ জেনেও সে এতদিন করে এসেছিল।
কিন্তু এমন ঘৃণ্য অপরাধের শিকার হয়েও নানের ক্ষমা করতে পারার দৃঢ়তা তাকে জ্বালায় ভেতরে। সেটা হয়তো তার অবদমিত করে রাখা বিবেকটাকে জাগিয়ে তুলতে চাইছে। ক্ষমা তো সে নিজেকেও করেনি। তাই নানের এই ক্ষমার বিষয়টি সে মেনে নিতে পারে না। তার অস্তিত্ব সংকট তখন আরো অভিঘাতী হয়ে ওঠে। কোনোরকম সংঘাত ছাড়া ক্ষমা যে তার দুনিয়ায় নেই, এই শহরের কানাগলিগুলোতে নেই। তাইতো সে ভুলতে বসেছিল, ক্ষমা আত্মার মুক্তির একমাত্র পথ। নানের কথা তার মরচে পড়া বিশ্বাস নাড়িয়ে দেওয়ার পর তাই সে ক্রাইস্টকে দেখে। ক্ষমার একটা রূপ হিসেবে। তাইতো আত্মদংশনে, বেদনায় ওভাবে লুটিয়ে পড়ে কঁকাতে থাকে ব্যাড ল্যুটেন্যান্ট।

Image Source: Aries Films
তবে ব্যাড ল্যুটেন্যান্টের এতকিছু অধরা রয়ে যেত, যদি প্রধান চরিত্রটিতে হার্ভি কাইটেল না থাকত। নামের সাথে ‘ওয়ান অভ দ্য গ্রেটেস্ট মেথড অ্যাক্টরস’ উপাধিই সেসবের ব্যাখ্যা করে। স্করসেসি, রিডলি স্কট, টারান্টিনো, থিও আগেলোপুলোস, পাওলো সরেন্টিনো, আবেল ফেরারা, জেইন ক্যাম্পিয়ন-সহ অনেক গ্রেট ফিল্মমেকারের সাথেই তাই তার কাজ করা হয়েছে। আবেল ফেরারা যে নিখুঁত কাস্টিংই বাছাই করেছেন এ চরিত্রে, তা বলাই বাহুল্য। ল্যুটেন্যান্ট চরিত্রটা যেন চরিত্র নয়, কাইটেলের ভেতরকার সত্ত্বা।
লুটিয়ে পড়ে যখন সে আর্তনাদ করে, তখন যেন নিজের বেদনাকেই প্রকাশ করছে। আত্মার ওই কেটে যাওয়া সুরের ক্ষতই তাই তার চোখেমুখে স্পষ্ট। ল্যুটেন্যান্টের হারানো অস্তিত্ব নয়, নিজের অস্তিত্বকেই যেন খোঁজার উন্মাদ চেষ্টা চলাচ্ছে সে, ক্যারিয়ারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই চরিত্রে আর চরিত্রাভিনয়ে।
সিনেমার তৃতীয় অঙ্কের শেষভাগে লুটিয়ে পড়ার সেই দৃশ্যটার কথাই যদি কেউ ধরে, যেটা এক টেকে নেওয়া, ওখানে কোনো অভিনয় ছিল না। একজনের বিশ্বাসের দ্বন্দ্বের, তার ভেঙে পড়ার একটা বাস্তবিক দৃশ্য ছিল। একদম বাস্তব একটা মুহূর্ত, ঈশ্বরের সামনে তার সৃষ্টির ক্ষোভ প্রকাশের, অভিযোগের, যেটা বড়জোর আড়াল থেকে কেউ ক্যামেরাবন্দী করেছে। সিনেমার প্রয়োজনে ওই কান্না নয়, বরং কান্নাকে ক্যামেরায় ধরার প্রয়োজনেই ওটা সিনেমা। ফ্রাঁসোয়া ক্রুফো যেমন বলেছিলেন,
“ক্যামেরা বাস্তবকে ধরতে যতটা নৃশংস হতে পারে, যতটা চরমে পৌঁছাতে পারে আর কিছুই তা পারে না।”
আবার ইংমার বার্গম্যান যেমন বলেছিলেন,
“আমার কাছে মানুষের মুখই হলো সিনেমার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্ট।”
কারণ ওই মুখ দিয়েই ভেতরকার সবকিছুর প্রকাশ ঘটে। এই দুটো কথারই একটা অভিঘাতী রূপ, ব্যাড ল্যুটেন্যান্ট। মুখ তো হার্ভি কাইটেলের আছেই, সেইসাথে ক্যামেরায় অমোঘ ভাষা তৈরি করার পেছনে আছে ফেরারার ক্ষিপ্র পরিচালনা।

Image Source: Aries Films
ফেরারা তার অন্ধকারাচ্ছন্ন নাগরিক সেটিংয়ে, নিও-নোয়াহ্ ইমেজারিতে একদম ‘র’ ভাবটাই তুলে এনেছেন। রিয়েল লোকেশনে শ্যুট করেছেন, ক্যামেরায় জরাজীর্ণতাকে ধরতে। হ্যান্ডহেল্ড ক্যামেরায় শ্যুট করেছেন, ডকুমেন্টারির মতো করে উপস্থাপনে। কারণ এতে ফেরারার ওই জগতের, তার বিষয়াদির বিশ্বাসযোগ্যতা আরো বাড়বে। ইমেজারিগুলোকে স্ট্যাটিক, ফ্ল্যাট রেখেছেন সে কারণে। আর গ্রেইনি লুক দিয়েছেন, যাতে নিউ ইয়র্কের এসব রাস্তা আর মোড়গুলোর নোংরা রূপটা বাস্তবিক আকারেই ক্যামেরায় তোলা যায়।
ক্যামেরাকে বেশিরভাগ সময়ে চরিত্রদের মুখের কাছাকাছি থাকতে দিয়েছেন। ফেরারা হয়তো ওই মুখের দিকে ক্যামেরা তাক করে ভেতরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জানার চেষ্টা করছিলেন। অবজেক্টিভ ডিটেলগুলোকে যেভাবে ভিজ্যুয়ালে তুলে ধরেছেন, তাতে ডকুমেন্টারির ভাবটা আরো প্রগাঢ় হয়েছে। কাইটেলের, দুই তরুণীর গাড়ি থামিয়ে তাদের যৌন হেনস্তা করার দৃশ্যটা দেখা যাক। পুলিশ পরিচয় দিয়ে তাদের ভয় দেখিয়ে বাধ্য করে যৌন উত্তেজনা জাগাতে তার মাঝে। তারপর তাদের সামনেই হস্তমৈথুন করে। এই গোটা দৃশ্যটা তো স্বাভাবিক চোখেই প্রচণ্ড অস্বস্তিদায়ক। তার উপর ফেরারার ‘র’ ভাবটার কারণে আরো অস্বস্তি জাগায়। বারবার এদিক-ওদিক নড়াচড়া করতে বাধ্য করে।

Image Source: Aries Films
আবেল ফেরারা যে একজন ভিশনারি ফিল্মমেকার; অঁতর, তাতে সন্দেহ নেই। এবং এই অব্দি এসে, সেই সন্দেহ পোষণ করার কথাও না। ৮০’তে রিভেঞ্জ ড্রামা, এক্সপ্লয়টেশন সিনেমা (‘মিস ৪৫’, ‘চায়না গার্ল’, ‘ফিয়ার সিটি’) বানিয়েছেন, সেখানেও তার শৈল্পিক উৎকর্ষের জায়গাটি ছিল। আর ৯০ দশকে ইন্ডি মুভমেন্টে ভিড়ে তো পুরোপুরি তার শৈল্পিক ভিশনটাকেই ব্যবহার করেছেন। আর্টহাউজ, আভা-গার্দ এপ্রোচের সাথে ‘বি-মুভি’র অলংকারের মিশেলটা তাকে আরো স্বকীয় করে তুলেছে। ‘প্রভোকেটিভ অঁতর’ তো সেকারণেই তাকে বলা হয়। ‘ব্যাড ল্যুটেন্যান্ট’ সেই কথার একটা বড় দলিল। তাই এর নামটা সবসময় জ্বলজ্বলে হয়ে থাকবে। সকল সীমা অতিক্রম করে বাস্তবকে ধরতে, বিশ্বাস; পাপবোধ; ক্ষমার ব্যবচ্ছেদ করতে অবাধ্য হয়ে এগিয়ে যে গেছে এই সিনেমা।