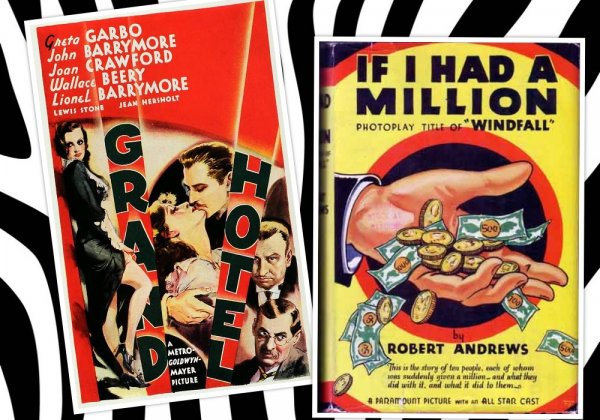এমন অনেক সিনেমা আছে, যেগুলো তাদের সূক্ষ্ম বক্তব্য দ্বারা কিংবা কোনো নিজস্ব দর্শন দ্বারা দর্শকদের মাঝে চিন্তার উদ্রেক ঘটায়, অনেকরকম বোধের সন্নিবেশ ঘটায়। মোটাদাগে এ ধরনের কিংবা এমন অনুভূতি জাগানো সিনেমাগুলোকে ‘ভালো সিনেমা’ হিসেবে অভিহিত করা হয়। তবে সিনেমা কীভাবে ভালো কিংবা খারাপ হয়, সে প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা এ লেখার উদ্দেশ্য নয়। বিষয়টা টানা হচ্ছে অন্য কারণে। এমন বেশকিছু সিনেমা থাকে, যেগুলো দর্শকের মাঝে অনেক অনেক ভাবনার সমাবেশ তো ঘটায়, কিন্তু সেই ভাবনাগুলোকে কিংবা ভাবনা থেকে দাঁড় করানো অনুভূতিগুলোকে সংঘবদ্ধ কিংবা কংক্রিট উপায়ে প্রকাশ করা যায় না। মাঝখানে তৈরি হয়ে যায় অনেক বাগাড়ম্বরতা। এই সিনেমাগুলোকে ভালো/খারাপের বহুল ব্যবহৃত মাপকাঠি দিয়ে বিচার করা যায় না। সিনেমাগুলো তার ব্যাপ্তিকালের গোটা সময়টাতেই চলচ্চিত্রের ভাষা, আঙ্গিক নিয়ে নিরীক্ষা করে। বক্তব্য প্রদানের উপায় নিয়ে নিরীক্ষা করে। তাই সেই সকল সিনেমাকে বিচার করার মাপকাঠিও হতে হয় ভিন্ন।
এ ধরনের সিনেমাগুলো পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে দর্শকের সবকিছু উপলব্ধির চেষ্টাতে নয়, বরং অনুভূত করার চেষ্টায়। কারণ, শিল্পের সবটা বোঝা দুঃসাধ্য যে কারো পক্ষেই। নানাজন একটা শিল্প বা শিল্পকর্মকে নানাভাবে দেখবে, মত প্রকাশ করবে; ওতেই তার মাহাত্ম্য। শিল্পকে বোঝার চেষ্টাতে নয়, তার সাথে নিজেকে সংযুক্ত করার চেষ্টাতেই আসল সার্থকতা। তো সেইসকল সিনেমার কথাতেই বলি, ওমন একটি সিনেমা হলো আজকের আলোচ্য ‘আই অ্যাম থিংকিং অভ এন্ডিং থিংস’ (২০২০)। আবার শিল্পের ওই প্রকৃতিতেই বলি, ওমন একটি শিল্পকর্ম হলো, এই সিনেমা। তাই শুরুর এই বিবৃতিটুকু অবান্তর নয়, বরঞ্চ এই সিনেমার প্রকৃতিটাই ঠিক করা হচ্ছিল অংশটায়।
“আই অ্যাম থিংকিং অভ এন্ডিং থিংস”, সিনেমার প্রারম্ভিক দৃশ্যে অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র লুসি ঠিক এই সংলাপটি দিয়েই তার নাটকীয় মনোলগ শুরু করে। ভয়েসওভারে তার মনোলগ চলতে থাকে আর পর্দায় দর্শক একটি জনহীন ঘরের বিভিন্ন রুমের মন্তাজ শট দেখতে পায়। ধীরে ধীরে লুসিকে দেখতে পাওয়া যায় রাস্তায়। লুসি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে তার প্রেমিক জ্যাকের জন্য। জ্যাকের মা-বাবার সাথে দেখা করতে যাবে আজ।

Image Source: Netflix
জ্যাকের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে এখন আর সুনিশ্চিত নয় সে। আপাতদৃষ্টিতে, সব ঠিক। জ্যাক আদর্শ একজন প্রেমিক। কিন্তু লুসির মনে হতে থাকে, কোথাও যেন একটা বিশাল ফাঁপা অংশ পড়ে রয়েছে উন্মোচনের অপেক্ষায়। গোটা জার্নিতে লুসি সেটা ক্রমাগত ভাবতে থাকে। আর কিছুক্ষণ পরপরই তার দীর্ঘ মনোলগে একটাই লাইন ঘুরেফিরে আসে, “আমি সবকিছু শেষ করার কথা ভাবছি।” কী শেষ করার কথা ভাবছে লুসি? সম্পর্ক? ওটুকু তো অনেকটা দিনের আলোর মতো স্বচ্ছ, আবহাওয়া যত খারাপই হোক না কেন এই জার্নিতে। কিন্তু শুধু সম্পর্ক নিয়েই লুসি ভাবছে না; ভাবছে আরো অনেককিছু নিয়ে। তারা দু’জনেই যথেষ্ট বুদ্ধিমান। নানান দর্শন আর ভারি সব রেফারেন্সের আদানপ্রদান হয় তাদের মধ্যে, পথ চলতে চলতে।
উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা নিয়ে কথামালার আদানপ্রদান হয়। ‘আ উইমেন আন্ডার ইনফ্লুয়েন্স’, গ্রেট এই সিনেমাটি নিয়ে সমালোচক পওলিন কায়েলের লেখা রিভিউর একটা অংশ নিয়ে বেশ বড়সড় আলোচনা হয়; যে শ্রদ্ধাঞ্জলি পরের এক দৃশ্যে জ্যাকের রুমে রাখা পওলিন কায়েলের একটি বই দিয়ে দেওয়া হয়। টলস্টয়, ডেভিড ফস্টার ওয়ালেস, ওয়াল্ডো এমারসনের দর্শন নিয়ে আলোচনা হয়। লুসি আবার ‘বোনডগ’ নামের একটি কবিতাও আবৃত্তি করে শোনায় জ্যাককে, যা শুনে জ্যাক বলে, কবিতাটা যেন তাকেই নিয়ে লিখেছে লুসি। তারা এক বিষয় থেকে আরেক বিষয়ে ঘুরে বেড়ায়। কথা বলে অস্কার নিয়েও। সম্পর্কের গতিরেখা যে বদলে যাচ্ছে, সেটাকে ঢাকতেই লুসির সাতপাঁচ কথা। আর জ্যাক চাচ্ছে বিরক্তিকর নীরবতাকে নীরবেই রাখতে। কিন্তু আদতে লুসির এই কথাগুলো সাতপাঁচ নয়। এই সবগুলো রেফারেন্সই পাজল মেলানোর একেকটা ছোট অংশ হয়ে উঠে পরবর্তীতে।
ফের গল্পে ফেরা যাক। তো, একটা সময় তারা পৌঁছে যায় জ্যাকের মা-বাবার বাড়িতে। সিনেমার গল্প যেন ঢুকে গেল তার দ্বিতীয় অংকে। বৈরী আবহাওয়া, জনশূন্য খামারবাড়ি, বুড়োবুড়ির অদ্ভুত আচরণ; হরর সিনেমার জন্য এ যেন একেবারে আদর্শ সেটআপ। হ্যাঁ, সেই আবহটা এ সিনেমায় আছে। কিন্তু উদ্দেশ্য ভিন্ন যোজন যোজন ফারাক মেনে। ডিনার টেবিলে সবাই একসাথে খেতে বসেছে। অসংলগ্ন সব কথায় আর জোরপূর্বক হাসির চেষ্টায় গোটা পরিবেশটা একপ্রকার থমথমে হয়ে ওঠে। কিন্তু চেপে বসে এই থমথমে ভাবের ভেতরে বাস করা অদ্ভুত প্রকৃতিটা। ডেভিড লিঞ্চের সিনেমার সুররিয়াল আবহের আঁচ পাওয়া যায়।
এই ডিনার টেবিল থেকে তো সবে শুরু। এর পরপরই একে একে বদলে যেতে থাকে দৃশ্যপট। পরিবর্তন দেখা দেয় চরিত্রদের মাঝে, যেন অনেক সময়কালের মাঝে সংঘর্ষ বাঁধে। কিন্তু এসবে নির্বিকার থাকে লুসি! সব যেন স্বাভাবিক। এ পর্যায়ে দর্শকের মনের সন্দেহটা গাঢ় হয় আরো। লুসি আর জ্যাক বেরিয়ে ফিরতি পথ ধরে। কিন্তু জ্যাক গাড়ি ঘুরিয়ে চলতে শুরু করে তার ছেলেবেলার স্কুলে। পরাবাস্তবতার দুর্বোধ্য ধাঁধার পথ যে সবে শুরু দর্শকের জন্য।

Image Source: Netflix
পৃষ্ঠতলে একটি সাইকোলজিক্যাল ড্রামা আর হরর আবহের সিনেমা এটি, যার গল্পধারণায় বোঝা যায়, বেশ বাঁকানো আর অদ্ভুত এর প্রকৃতি। সিনেমার চিত্রনাট্যকার এবং পরিচালক চার্লি কফম্যানের সাথে পরিচিত দর্শকমাত্রই বুঝে নেবে, পৃষ্ঠতল নিয়ে জলঘোলা কখনো তিনি করেন না। এর নিচেই বরঞ্চ তাঁর সব কাজ। পরিচিতি জটিলতা, মৃত্যু এবং বার্ধক্যের প্রতি ভয়, যোগাযোগহীনতা, জীবনের অর্থ, মানবিকতা; এসব গূঢ় বিষয়াদি নিয়েই তার কাজ। তবে সোজাসাপটা বয়ানভঙ্গিতে এসকল বিষয় ধরেন না তিনি। ফিল্মমেকিং এবং রাইটিংয়ের প্রচলিত নীতিগুলো ভাঙেন নিজের মতো করে। ধরেন মেটাফিজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কে। কোনো নির্দিষ্ট জনরায় তাই তার কাজকে ধরা যায় না। ‘প্রচন্ড সুররিয়ালিস্টিক’ এ বিশেষণেই একটা ছায়াতলে চার্লি কফম্যানের কাজগুলোকে জড়ো করে রাখা যায়।
সেই ‘বিয়িং জন মালকোভিচ’ (১৯৯৯), যেটির চিত্রনাট্য লিখেছিলেন, থেকেই তার অসীম ভাবনার জগতে একটু একটু করে প্রবেশ করিয়েছেন দর্শককে। কখনো অন্য কারো মস্তিষ্কে বাস, কিংবা কখনো মস্তিষ্ক থেকে কাউকে মোছার চেষ্টা (ইটার্নাল সানশাইন অভ দ্য স্পটলেস মাইন্ড); রীতিমতো গোটা গ্যামাট’টাই পূর্ণ করেছেন কফম্যান। চেতনার মধ্যে তৈরি হওয়া একটা ব্ল্যাকহোলের ভেতর দিয়ে সবসময় ছুটে বেড়ায় তার চরিত্রগুলো। নিজের লেখা চিত্রনাট্যে ‘সিনেকডোকি নিউ ইয়র্ক’ (২০০৮) দিয়ে পরিচালনায় এলেন যখন, তখনো করলেন সেই কাজটাই। সেখানে তার চিন্তাভাবনাগুলোর শৈল্পিক উপস্থাপন যেন একেকটা বাস্তববাদী জীবন হয়ে উঠল, যা মিশে গেছে পরাবাস্তবিক এক জগতে।
তার পরিচালনার দ্বিতীয় সিনেমা ‘অ্যানোমালিসা’ (২০১৫), যেটি তিনি লিখেছেনও, সেই সিনেমার সাথে তৃতীয় এই সিনেমার একটা গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্য রয়েছে। সেই সিনেমা, কোনো ব্যক্তির চোখ দিয়ে যে জগতটা দেখা হচ্ছে, তার কি আদৌ কোনো অস্তিত্ব আছে, নাকি পুরোটাই মস্তিষ্কে তৈরি বিভ্রম (?)- সে প্রশ্ন উত্থাপন করে। এটিই আরেকটু জটিল আকারে উঠে এসেছে এই সিনেমায়। একদম শুরুর দিকে জ্যাক, লুসিকে একটা কথা বলে এমন; “এই কথাটা নিজেকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া ভালো যে, মাথার ভেতর যে জগতটা, তার থেকে বাইরের জগত অনেক বেশি বড়।” এবং সিনেমার শেষে গিয়ে এই কথাটাকেই কফম্যান একটা প্রশ্ন আকারে দাঁড় করান। সিনেমায় যে জগতে কফম্যান দর্শকদের নিয়ে যান, সেটা কারো মাথার ভেতর ছাড়া বাস্তবেও কতটুকু অস্তিত্ব ধারণ করে, সে নিশ্চয়তার প্রশ্নে তিনি ঘোরপাক খাওয়ান দর্শকদের।
চার্লি কফম্যানের এবারের এই অদ্ভুত গল্প আর চরিত্ররা পুরোপুরি তার মাথার ভেতরের কোটি কোটি নিউরন থেকে জন্মায়নি, বরং গল্প আর চরিত্ররা ভিতটা পেয়েছে ইয়ান রিডের একই নামের উপন্যাস থেকে। ওই অতটুকুই। শুধু পৃষ্ঠতলটাই নিয়েছেন। এবং পূর্বেই যেমনটা উল্লেখ করা হয়েছে এই লেখায়, পৃষ্ঠতলে কখনোই বেঁধে রাখা যায় না চার্লি কফম্যানকে। গোটা সিনেমাটা তিনি সাজিয়েছেন রূপকের ছড়াছড়িতে তৈরি হওয়া একটা গোলকধাঁধা হিসেবে, উপন্যাসে ইয়ান রিড সেটি পাঠকদের জন্য সমাধান করে দিলেও, সিনেমায় কফম্যান সেখানে ব্যবহার করেছেন অস্পষ্টতা।
অনেক অনেক দরজা খোলার চাবি একটাই। একটা খুললেই সব খুলে যাবে, কিন্তু নির্ধারণ করতে হবে দর্শককে, সেই একটা কোনটা (?)। পরাবাস্তবিক জগত আর সেই জগতের চরিত্র সব, যাদের কথাবার্তায় জড়িয়ে আছে খোদ কফম্যানের একদম নিজস্ব দর্শন। কফম্যান ভালোবাসার ভঙ্গুর প্রকৃতি নিয়ে লিখেছেন এখানে, আবার লিখেছেন সেটা না থাকার হাহাকার নিয়েও। লিখেছেন স্মৃতিকাতরতা, একাকিত্বের গ্লানি নিয়ে। লিখেছেন অস্তিত্ব বিনাশের ভয় নিয়ে। জ্যাকের ছেলেবেলার সেই ঘরটাই যেন এই গোলকধাঁধার চাবি। সমস্ত রেফারেন্স ছড়িয়ে আছে ওখানেই। তার রুমের সেসব রেফারেন্সে ভর করে তার চিন্তাধারার গভীরে উঁকি মেরে দেখলে সবকিছু শেষ করার দড়িটা খুঁজে পেতে কষ্ট হলেও, সবকিছু শুরুর হদিস পাওয়া যাবে।

Image Source: Netflix
সিনেমার এই দ্ব্যর্থবোধক প্রকৃতিকে পর্দায় তুলে আনার জন্য নিখুঁত ভিজ্যুয়াল ভাষাটাই তৈরি করেছেন কফম্যান, সিনেমাটোগ্রাফার লুকাস জ্যালকে সাথে নিয়ে। একাডেমি অ্যাসপেক্ট রেশিও’তে শ্যুট করেছেন, যাতে করে দর্শককে চরিত্রদের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের জগতটায় বেঁধে ফেলা যায় এবং জটিলতায় ভারি তাদের সেই জগতে একটা দমবন্ধ অনুভূতি তৈরি করা যায়। বরফাচ্ছন্ন ল্যান্ডস্কেপ শটগুলো অনেকটা সম্মোহিত অবস্থায় নিয়ে যায়। একাডেমি রেশিওতে শ্যুট করায় দর্শকের জন্য সুবিধাটি হয়েছে সিনেমার ভিজ্যুয়াল ডিটেল বুঝতে পারায়। ইমেজারিগুলোতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ডিটেল কফম্যান রাখেননি, যেহেতু জায়গা ধরাবাঁধা। তাই সচেতন দর্শক প্রতিটি ডিটেল অনুসরণ করে বুঝে উঠতে পারবে, পর্দায় কী চলছে।
এই নিখুঁত সুররিয়াল ইমেজারিগুলোর চাপা ভয় জাগানিয়া হয়ে ওঠায় ভূমিকা রেখেছে আবহসঙ্গীতও। তাইতো গাড়ির উইন্ডশিল্ডের সেই সাধারণ শব্দটাও ক্রমাগত ব্যাকগ্রাউন্ডে চলতে থাকায় গুমোট পরিস্থিতি আরো গমগমে হয়ে উঠেছে। রবার্ট ফ্রাজেনের সম্পাদনা আলাদা করে উল্লেখ্য হওয়ার দাবি রাখে। খুবই সূক্ষ্ম তার সম্পাদনা, যার চমৎকার প্রমাণটা পাওয়া যায় ডিনার টেবিলের সেই দৃশ্যের পর। একের পর এক ক্রমাগত যেভাবে দৃশ্যপট বদলেছে, সেভাবে কাটগুলোকে এতটাই সংহতিপূর্ণ আর তড়িৎ উপায়ে জোড়া লাগানো হয়েছে যে বিসদৃশ করাটা কঠিন হয়ে ওঠে। এছাড়া প্রোডাকশন ডিজাইনও হয়েছে বেশ দৃষ্টিনন্দন।
তবে সুররিয়ালিজমে ঠাসা এ সিনেমায় মানবিক আবেদনটা অনুনাদী হয়ে উঠেছে মূলত চরিত্রদের অভিনয়ে। জ্যাক, সচরাচরের মতোই খুবই বুদ্ধিমান এবং একইসাথে অসহায় একটি কফম্যানিয় চরিত্র। এ চরিত্রে জেস প্লেমনস হৃদয় নিংড়ানোর মতো অভিনয় করেছেন। জ্যাক চরিত্রটি অন্তর্মুখী। সে চরিত্রের হতাশা, বিষাদ, আকুলতা সবই তার অভিনয়ে জীবন্ত রূপ পেয়েছে। দর্শকের আকর্ষণ মূলত কেড়ে নেবে জেসি বাকলির ‘প্রেমিকা’ চরিত্রটি। কারণ গল্পের মতোই অদ্ভুত আর ধাঁধাপূর্ণ চরিত্র এটি। এই একটা চরিত্রকেই অনেকগুলো নতুন আঙ্গিক থেকে দর্শক আবিষ্কার করবে। এবং প্রতিটিতেই ভুলত্রুটি ছাড়া দক্ষতার সাথে অভিনয় করে গেছেন বাকলি।

Image Source: Netflix
সিনেমার শেষ অংকই বলে দেয়, কেন এই কাজটি চার্লি কফম্যানের সর্বাপেক্ষা জটিল কাজ। তার কাজের নিয়মিত দর্শকও ভিড়মি খাবেন শেষ অংকের সুররিয়াল জার্নির অংশ হতে গিয়ে। গোটা সিনেমাটাই একটা ‘ফিভার ড্রিম’ যেন। সবকিছু কেটে গেলেও ঝাঁকুনি দিয়ে জ্বরটা তখনো নামে না। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে সবকিছু জোড়া লাগানোর চেষ্টা করা হলেও, খুব একটা ফলপ্রসূ তা হবে না। বিমূঢ় করে রেখে যাবে এই সিনেমা এবং সেটাকেই পাওনা হিসেবে টুকে রাখা উচিত। বারবার দেখা হলে, বারবারই নতুন ধাঁধার সামনে ফেলে দেবে এই সিনেমা। শিল্প তার রূপে চোখ ভরাবে, কিন্তু রহস্য জানাবে না। ওটাই শিল্পের সার্থকতা। আর এভাবেই একটি বিমূর্ত শিল্প হয়ে উঠেছে ‘আই অ্যাম থিংকিং অভ এন্ডিং থিংস’।