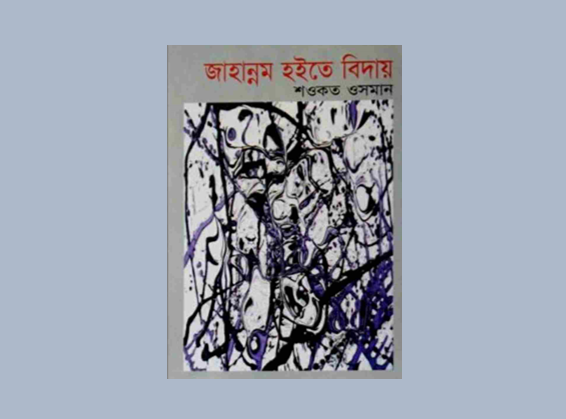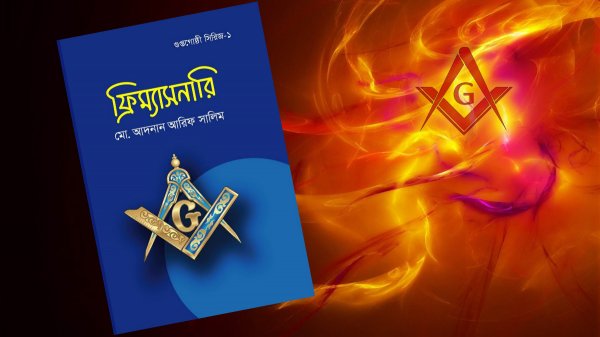মার্ভিন লেরয়, ৩০ দশকের হলিউডের অন্যতম প্রথিতযশা পরিচালক ছিলেন। ওয়ার্নার ব্রাদার্স স্টুডিওর তখনকার অন্যতম লাভবান পরিচালকদের একজন ছিলেন তিনি। স্টুডিওর জন্য, সোনার ডিম পাড়া হাঁস। কারণ তার সিনেমাগুলো লগ্নির টাকা দ্বিগুণ বা কয়েকগুণ করে যেমন তুলে আনতো, তেমনি সমালোচকমহলে হতো প্রশংসিতও। ফিল্মমেকিংয়ে সত্যিকারের সৎ শ্রমটাই যে দিতেন। ড্রামা, মেলোড্রামা, ক্রাইম, মিউজিক্যাল, ওয়ার, এডভেঞ্চার; সব জনরাতেই নিজের বৈচিত্র্যতা আর নৈপুণ্যতা প্রদর্শন করেছেন লেরয়। প্রলিফিক ক্যারিয়ার তার। আর তখনকার স্টুডিও সিস্টেমের যাঁতাকলে সেই কাজ তো ছিল আরো চ্যালেঞ্জিং। যাক সেসব। তবে, সিনেমার নির্বাক থেকে সবাক হবার এই ৩০ দশকে পরবর্তীর যেই ক্লাসিক হলিউড ন্যারেটিভ গড়ে উঠছিল কিংবা একটা রূপরেখা দাঁড়াচ্ছিল, লেরয়ের সিনেমাগুলোর ভিন্ন ভিন্ন নন্দন সেক্ষেত্রে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ‘৩৯-এর দিকে অবশ্য ওয়ার্নার ছেড়ে এমজিএম স্টুডিওতে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু ক্যারিয়ারের সর্বাপেক্ষা ভালো কিংবা শ্রেষ্ঠ কাজগুলো ওয়ার্নার ব্রাদার্সে থাকাকালীন বানিয়েছিলেন। তো মার্ভিন লেরয়ের বর্ণাঢ্য সিনেক্যারিয়ার হতে, তার পরিচালিত অন্যতম মহতি ৫ সিনেমা নিয়েই এবারের আলোচনা।
গোল্ড ডিগার্স অফ ১৯৩৩
‘গোল্ড ডিগার্স অফ ১৯৩৩’ মিউজিক্যাল সিনেমা প্রধানত। ১৯১৯ এবং ১৯২০ সালে মঞ্চায়িত হওয়া একই নামের ব্রডওয়ে প্লে’টাই সিনেমার উপকরণের মূল যোগান। ২৮২ পারফরম্যান্সের বিরাট প্লে ছিল সেটা। ১৯২৩ সালেই প্লে’র উপর ভিত্তি করে একটা সাইলেন্ট সিনেমা বানানো হয়েছিল। আবার ‘২৮/’২৯ সালের দিকে সিনেমা যখন সবাক হলো, তখনো একবার বানানো হয়েছিল (১৯২৯ এ)। সফলও ছিল। তবে শৈল্পিকতার বিচারে ১৯৩৩ সালের ভার্সনটি যেই উচ্চতায় পৌঁছেছে, ওইটুকুতে আসেনি বাকি দুটো। তাইতো মার্ভিন লেরয়ের ভার্সন আজও ‘ক্লাসিক’ হিসেবে বিবেচিত। ২০০৩ সালে আমেরিকান ‘ন্যাশনাল ফিল্ম রেজিস্ট্রি’ তাই সংরক্ষণের জন্যও নির্বাচন করেছে।
সিনেমার নামের সেই গোল্ড ডিগারস্’রা ৪ জন, মঞ্চ অভিনেত্রী। পলি, ক্যারল, ট্রিক্সি, ফেই। এদের মধ্যে পলি হলো থিয়েটারের একটা স্টক ক্যারেক্টার, ‘আনজেনিউ’ বলা হয়। দেখতে যে হবে, খুবই আদরমাখা, ইনোসেন্ট। চোখের সরলতা দিয়ে সে দর্শক মাত করবে। তার চোখ একটুখানি চিকচিক করে উঠলে, ঠোঁট কেঁপে উঠলে একটা তীব্র হাহাকারের মোচড় উঠবে দর্শকমনে। তারপর ক্যারল হলো টর্চ সিংগার। মানে বিরহভরা গানের গায়িকা। হারিয়ে যাওয়া ভালোবাসার বিষাদে ডুবে থাকবে যেই গায়কি এবং লিরিক। ট্রিক্সি হলো কমেডিয়ান। আর ফে’র কাজ রূপের ছটায় দর্শকের চোখ ধাঁধানো। এই নিয়ে গোটা দল। থাকেও তারা একই ফ্ল্যাটে। তাদের গ্ল্যামারের পাশে যেই ফ্ল্যাটের অবস্থা নিতান্তই হতদরিদ্রের ঘরের মতো। জীর্ণশীর্ণ ঘর। কোনরকম জীবনকে যাপন আর বড় অভিনেত্রী হবার স্বপ্ন দেখা এই আরকি। তাদের প্রযোজকেরও দৈন্যদশা। প্রারম্ভিক দৃশ্যেই দেখা যায়, তাদের প্রযোজক ধার না মেটাতে পারাতে মঞ্চের সকল কস্টিউম, জিনিসপত্র পুলিশের লোকবল এসে উঠিয়ে নিয়ে যায়।

Image Source- Warner Bros.
তবে প্রযোজক থেমে নাই। নতুন এক প্লে’র চিন্তা তার মাথায় ভর করেছে। ‘গ্রেট ডিপ্রেশন এরা’র প্রেক্ষাপটে রোমান্টিক, কমেডিক, ট্র্যাজিক এক প্লে। কিন্তু টাকা ঢালবে কে! এমন সময় পাশের ঘরে বেজে উঠে পিয়ানোর সুর সাথে এক শক্তিশালী কণ্ঠ। পলি ঢেকে এনে পরিচয় করিয়ে দেয় সেই ছোকরাকে। ব্র্যাড নাম। প্রযোজক বার্নি তার প্লে’র মিউজিসিয়ানও ঠিক করে ফেলেছেন, শুধু টাকাটা ছাড়া। এগিয়ে আসে ব্র্যাড, সবাই ভাবে ঠাট্টা। যদি সত্যিই থাকে তার কাছে ১৫ হাজার ডলার, তবে থাকবে কেন ৪ ডলারের এই সস্তা ঘরে? তবে টাকাটা ব্র্যাড ঠিকই আনে। শো হয় হিট। শেষ মুহূর্তে ব্র্যাডকে বাধ্য হয়ে পর্দার সামনেই আসতে হয়। ছবি ছাপে পত্রিকায়। পলির সাথে হয় মন দেওয়া-নেওয়া। আর তখনই আসে বাঁধা। পত্রিকার ছবি হাজির করে ব্র্যাডের বড় ভাইকে। ধনী জার্মান পরিবার তারা। ছোটভাই আটকেছে নটী বিনোদিনীর রূপেতে, ছাড়াতে তো হবেই। কিন্তু তার আগে বড়ভাই নিজেই এক হাস্যকর নাটকের অংশ হয়ে পড়েন অজান্তে।
‘গোল্ড ডিগারস্ অফ ১৯৩৩’ প্রি-কোড সিনেমা। মানে তখনকার হলিউডে, স্টুডিও কর্তৃক আরোপিত ‘হেইস কোড’ প্রচলিত হবার আগের সিনেমা। তাই সেই সম্বন্ধীয় কিছু সুবিধা তো পেয়েছেই এই সিনেমা। তখনকার আমেরিকান সিনেমার নিয়মটাই ছিল, দর্শকের মনের উপর খুব বেশি চাপ না দিয়ে, বিনোদিত করা। তাইতো গোটা ২০ দশকে সাইলেন্ট কমেডির ওরকম প্রভাব। অবশ্য চ্যাপলিন, বাস্টার কিটন, লুবিচের মতো মহতীরা কমেডির ভেতর দিয়েই সূক্ষ্মভাবে কত কি বক্তব্য আনতেন! সেই কথা খাটে এই সিনেমার ক্ষেত্রেও। গল্পটা দেখলেই বোঝা যায়; কমেডি, ক্লাসিক মেলোড্রামা আর সঙ্গীতের মিশেলে একদম খাঁটি সরলরৈখিক গল্প। তবে হাস্যরসের মেজাজেই মিউজিক্যালের ভেতর দিয়ে তৎকালীন ‘ডিপ্রেশন এরা’র জটিলতাকে এড্রেস করা হয়েছে।
সাথে ধনিকসম্প্রদায়ের নাকউঁচু স্বভাবটা তো উপরেই আছে। এবং আজকের এই সময়ে নারীর ক্ষমতায়ন যতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে চলচ্চিত্র মাধ্যমেও, সেই দশকেই এই সিনেমা শো গার্লদের প্রতি সমাজের গণ্যমাণ্য লোকেদের যেই তেরছা দৃষ্টি, খারিজ করার স্বভাবটা; সেটাকে তুলে ধরে, সেটার প্রেক্ষিতে নিজেদের সম্মানটাকে দৃঢ়তার সাথে বহন করার দিকটাকেই সংরক্ষণ করেছে। তাছাড়া, চিত্রনাট্যের আরো বেশকিছু উপাদান আজকের এই সময়ের মাপকাঠিতে অতি সাধারণ মনে হলেও, এর উইটিনেস বা সরসতার প্রশংসা করতেই হয়। হাস্যরসের সংলাপগুলো এত ক্ষুরধার যে, ভেতর থেকে হাসিটা স্বাভাবিকভাবেই আসে। আর সাদাকালো হলেও চরিত্রগুলো কি রঙিন। ডিক পাওয়েল, রুবি কিলার, ওয়ারেন উইলিয়ামদের মতো কুশলী অভিনয়শিল্পীরা তো আছেনই।
মার্ভিন লেরয় অবশ্যই একজন টেকনিক্যাল পরিচালক। ৩০ দশকেও তার নন্দনতত্ত্বে স্টাইলিস্টিক উপাদানের কমতি ছিল না। এই মিউজিক্যালে সেগুলো তো আরো স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। তার; ডিসলভ, ফেইড ইন/ফেইড আউটের টেকনিকে সিনেমাটিক ভ্যালুটা পুরোপুরিই যুক্ত থাকে। এই সিনেমার মিউজিক্যাল সিকুয়েন্সগুলো পরিচালনা করেছেন আবার বাসবি বার্কেলি। লেরয় ক্যারিয়ার শুরুই করেছিলেন থিয়েট্রিক্যাল জনরা ‘ভডেভিল’ দিয়ে। তাই কোরিওগ্রাফির গুরুত্ব তিনি ভালো করেই জানেন। একারণেই মিউজিক্যাল সিকুয়েন্সে বার্কেলিকে দায়িত্ব দিয়েছেন। আর বার্কেলির মিউজিক্যাল প্রোডাকশন চোখ ধাঁধানো অভিজ্ঞতা দেয়, এখানেও দিয়েছে। সুবিশাল এবং ডিটেলে ভরা সেট সাজান তিনি। তার মিউজিক্যালের ব্লকিংগুলোই হয় অন্যরকম। স্বকীয়।

Image Source- Warner Bros.
জটিল সব জ্যামিতিক কোণ ধরে ব্লকিংটা সাজান। ক্যামেরায় টিল্ট অ্যাঙ্গেল ব্যবহার করেন। প্রচুর পরিমাণে ব্যাকগ্রাউন্ড ড্যান্সার থাকে। আর তার জ্যামিতিক প্যাটার্নটাকে দক্ষতার সাথে দেখাতে সিমেট্রিক্যাল শট রাখেন। এই সিনেমার শেষের দীর্ঘ ‘প্যাটিং ইন দ্য ডার্ক’ মিউজিক্যাল সিকুয়েন্সটাই এক অনবদ্য উদাহরণ তার স্টাইলের ক্ষেত্রে। এত সুবিশাল আর জৌলুসে ভরা আয়োজন যে এত এত সময় পরে এসে দেখেও চোখ ভরে যায়। মুখ দিয়ে স্তুতিবাক্য বের হয় অনায়াসেই। ‘ক্লাসিক’ ট্যাগটা সারা গায়েই যে সেঁটে আছে তাই।
লিটল সিজার ১৯৩১
ওয়ার্নার ব্রাদার্স থেকে লেরয়ের প্রথম সিনেমাই হলো, ‘লিটল সিজার’। লেরয়ের প্রথম ক্লাসিক সিনেমা। ক্যারিয়ারও লঞ্চ করেছিল এই সিনেমা। সিনেমাটার প্রভাব কিন্তু আরো বেশি। চলচ্চিত্র ইতিহাসে ‘লিটল সিজার’ই প্রথম গ্যাংস্টারধর্মী সিনেমা। ‘৩১ সালে প্রথম এই সিনেমা দিয়েই চলচ্চিত্র ইতিহাসে আরেকটি নতুন এবং দাপুটে জনরার উৎপত্তি হয়। একই বছরেই, কিছু মাস পরে ওয়ার্নার স্টুডিও হতে আরেকটি গ্যাংস্টার সিনেমা মুক্তি পায়, ‘দ্য পাবলিক এনিমি’। এই দুই সিনেমাই রাতারাতি এডওয়ার্ড জি. রবিনসন আর জেমস কাগনিকে পর্দার ‘আইকন’ বানিয়েছিল। পরের বছরই আসলো হাওয়ার্ড হ্যকসের গ্রেট সিনেমা ‘স্কারফেইস’। সাথে পল মুনির জাদুকরী অভিনয়। এই ৩ সিনেমাই গোটা জনরাটা দাঁড় করিয়ে ফেললো। আর এই ৩’টা সিনেমাই ‘হেইস কোড’ আরোপিত হতে শুরু করার আগে।
৩ জন হিংস্র অপরাধীর খুব তাড়াতাড়িই ত্রাস ছড়িয়ে ক্ষমতার শীর্ষে উঠা, আবার ততোধিক তাড়াতাড়ি ভূপতিত হবার আখ্যানই এই ৩ সিনেমা। তারা খলনায়ক/মাফিয়া/গ্যাংস্টার হলেও, তাদের কারিশমা দর্শককে আকৃষ্ট করতো। আর তার পেছনে সবচেয়ে বড়ো একটা কারণ হলো, তখন চলছিলই ডিপ্রেশন এরা। তাই এইসব যুবকদের ওই হিংস্রতা, ক্ষোভ, আক্রোশ কোথা হতে জন্ম নিচ্ছে সেটা দর্শক বুঝতো। পরবর্তীতে ‘হেইস কোড’ চালু হয়ে তো ক্লাইম্যাক্সে তাদের মানে গ্যাংস্টারদের বন্দুকের গুলিতে ঝাঁঝরা বানানোর মহৎ উদ্দেশ্য হাতে নেয়! তাদেরকে দেখানো হতো, সমাজ থেকে বিচ্যুত কোন সোশিওপ্যাথ চরিত্র হিসেবে।
তো, ডব্লিউ.আর. বার্নেটের উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত ‘লিটল সিজার’ এক পাতি মাস্তানের গল্প বলা থেকে শুরু হয়। পাতি হলেও তার স্বপ্ন অনেক বড়। তারউপর বয়স হাঁটুতে, রক্ত মাথাতে আর উত্তেজনা সারা শরীর জুড়ে। তাই যা হয়, শীঘ্রই জড়িয়ে পড়ে গ্যাং অপরাধে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর দুঃসাহসে ভর করে তড়িৎ ‘বস’ আসনটাই পাওয়া হয়। কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষাই তো শেষ অব্দি বিপদ ডেকে আনে। অন্তত তেমনটাই হয় এসব ক্ষেত্রে। রক্ত গরম হওয়ায়, কৌশলী আর হয়ে উঠা হয় না সবার। তাই পতনও হয় তেমনি শীঘ্রই। সিজারেরও হয়েছে।

Image Source- Warner Bros.
‘লিটল সিজার’ (১৯৩১) যেটা করেছে; এই চলমান ইমেজের চলমানতায় গ্যাংস্টার গল্প যেমন করে উপস্থাপিত হবে, তার একটা রূপরেখা তৈরি করে দিয়ে গেছে। এই জনরার অলংকারগুলোর ব্যবহারটা দেখিয়েছে। এরপর আজ এত বছর ধরে ভাঙাগড়া, অলংকারের নতুন ব্যবহার পদ্ধতি, বদল, যোগবিয়োগ/গুণভাগ সবই হয়েছে। তবে ক্লাসিক অনুষঙ্গ ধরে রেখে। সময়ের হিসেবে এই সিনেমা কিন্তু খুব সাহসীও ছিল। না, ভায়োলেন্স বা হিংস্রতা প্রদর্শনে নয় (এই কাজটা অবশ্য পরের বছরের ‘স্কারফেইস’ করেছিল)। ওটা ছিল অনেকটুকুই শব্দগত ভায়োলেন্স। মূল সাহসিকতা দেখিয়েছে এডওয়ার্ড জি. রবিনসনের করা সিজার চরিত্রটার রূপায়নে। সোশিওপ্যাথি তো ছিলই। সাথে সূক্ষ্মভাবে ‘সমকামী’ স্বভাবটাকে এনেছে এই চরিত্রে। বুঝতে পারার মতোই স্পষ্ট।
তবে কখনোই স্থূল বর্ণনায় নয়। বন্ধুকে, বন্ধুর প্রেমিকার সাথে নাচতে দেখে সিজারের রেগে যাওয়া, হিংসা করাতেই তার যৌনাকাঙ্ক্ষার যেই প্রকৃতি, সেটার খন্ডন। তার পতন হবার আগে, আরো একাধিক দৃশ্যেই তার চলাফেরায় আর হাত দিয়ে আরেকজনের চোয়াল স্পর্শ করার সময়কার অভিব্যক্তিতেই এই প্রকৃতিটা সুস্পষ্টরূপে সামনে আসে। আর এই প্রকৃতির কারণেই সিনেমার চিত্রনাট্য, সিজারের মনস্তত্ত্ব এবং আগ্রাসী স্বভাবকে আরো অভিঘাত ও দ্বন্দ্বে পূর্ণ উপায়ে বিশ্লেষণ করেছে। এবং চরিত্রটা রূপায়নে অনন্য এক মাত্রা দিয়েছেন রবিনসন সাহেব। সে কি অভিনয়! আগ্রাসী ভঙ্গীতে যখন সংলাপ প্রদান করছিলেন, যেন আগুন ঝরছিল অভিনয়ে। দৈত্যের মতো শক্তি যেন ওই ছোট্ট দেহের মতো ফুঁসে উঠছিল। অভিনয়ের সংবেদনশীলতা-তেই চরিত্রটাকে ‘এপিক’ স্ট্যাটাস দিয়েছেন এডওয়ার্ড জি. রবিনসন।

Image Source- Warner Bros.
আর লেরয়ের কুশলী পরিচালনা, এমন অভিনয়; এমন রূপায়ন; এমন গঠনবিন্যাসকে আরো সমুন্নত করেছে। রুক্ষতা আর উত্তেজনাকে বাড়তে দিয়েছেন অকপটে। ডিপ্রেশন এরার প্যারালালটা একদম শুদ্ধভাবে তার কাজে রাখেন, লেরয়। ভিজুয়াল স্টাইলের দিক থেকে অবশ্যই তিনি ইকোনমিক। তার ব্লকিংয়ের সেন্স আর শট কম্পোজ করার ধারাটা, সেই কথাকেই প্রতিফলিত করে। সময় অনুযায়ী ‘লিটল সিজার’-এর সাউন্ড ডিজাইনিংও খুব কার্যকর ভূমিকা রাখে ভায়োলেন্সের অনুভূতিটা দর্শকমনে জাগাতে।
পূর্বেই যেমনটা বলা হয়েছে; ‘লিটল সিজার’ (১৯৩১) গ্যাংস্টার জনরার রূপরেখা প্রণয়ন করেছে, সেকারণেই আমেরিকান ‘ন্যাশনাল ফিল্ম রেজিস্ট্রি’তে এর নাম অন্তর্ভুক্ত হবার পাশাপাশি, আমেরিকান ফিল্ম ইন্সটিটিউটের শ্রেষ্ঠ ১০ গ্যাংস্টার সিনেমারও একটি এই সিনেমা।