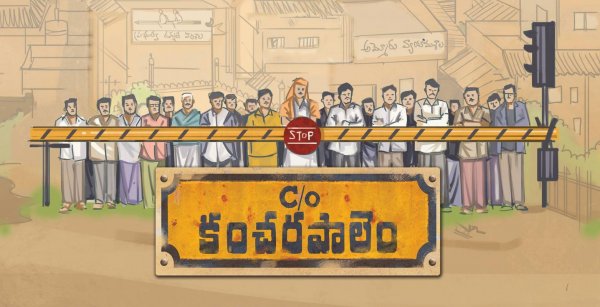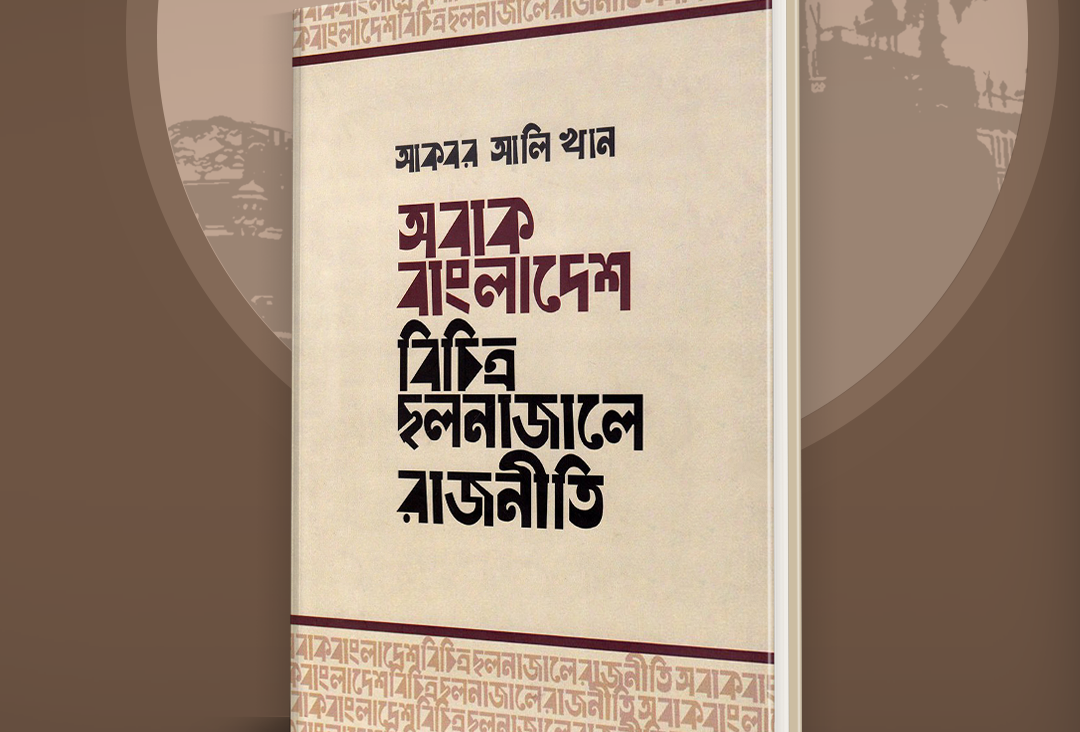
বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে লেখা গবেষণাধর্মী কিন্তু সহজবোধ্য এবং জনপাঠ্য একটি বই এটি। বইটিতে রাজনৈতিক সমস্যা যেমন আলোচনা করা হয়েছে, তার সাথে ঐসব সমস্যা সমাধানের সুন্দর দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে গণতন্ত্রকে সকল সমস্যা সমাধানের একরকম হাতিয়ার হিসেবেই উপস্থাপন করেছেন লেখক।
এদিক থেকে ৬ খণ্ড এবং পনেরটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই বিশালদেহী বইটি যেকোনো রাজনৈতিক জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিকে আকর্ষণ করবে এবং এ বিষয়ে নতুন জ্ঞান সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে লেখক আকবর আলী খান আশাবাদ ব্যাক্ত করেন।
শুরুতেই লেখক অকপটে স্বীকার করেছেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তার আনুষ্ঠানিক কোনো জ্ঞান নেই। জ্ঞানস্পৃহার জায়গা থেকে তিনি এই গ্রন্থ রচনায় প্রলুদ্ধ হননি। বরং নিখাদ একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দেশের প্রতি ভালোবাসার টানে রাজনৈতিক সমস্যাগুলো বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন।
এখানে উল্ল্যেখ্য, মুুক্তিযুদ্ধকালীন হবিগঞ্জ মহকুমার প্রশাসক হিসেবে তিনি অর্থ, খাদ্য ও অস্ত্র দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছিলেন। আর একাডেমিক জগতে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে অনার্স ও মাস্টার্স এবং কানাডার কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে পিএইচডি অর্জন করেন।

১ম অধ্যায়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে ‘রহস্যঘেরা প্রহেলিকাচ্ছন্ন হেঁয়ালি’ বলে সম্বোধন করা হয়েছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও নৈরাজ্যের ইতিহাস অনেক পুরনো। খালিমপুর তাম্রলিপিতে সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর সময়টাকে মাৎস্যন্যায় আখ্যা দেয়া হয়েছে।
ব্রিটিশ আমল, পাকিস্তান আমল এবং এমনকি স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশেরও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিদ্যমান রয়েছে। বর্তমানে হরতাল রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির একটি প্রধান উপাদান।
এর কারণ হিসেবে বাংলাদেশে সামাজিক পুঁজির অভাব, মুরব্বি-মক্কেল সম্পর্ক, ভৌগোলিক সীমানা, বংশভিত্তিক রাজনীতি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, কয়েদিদের উভয়-সংকট ইত্যাদি পরিভাষা উল্লেখ করা যায়। এখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সামাজিক পুঁজি বাড়াতে হবে। সেই সাথে গণতন্ত্রকে কার্যকর করতে হবে।
তারপরে ২য় খণ্ডে সংবিধানের ৮ম অনুচ্ছেদে বর্ণিত রাষ্ট্রীয় মূলনীতিসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তার আগে প্রস্তাবনায় দেখা যায়, পাকিস্তান সৃষ্টি ছিল একটা কাকতালীয় ব্যাপার। এতে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর দূরদর্শিতার চেয়ে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের স্ত্রী এডউইনার ভূমিকাটাই বেশি।
লাহোর প্রস্তাবে একাধিক রাষ্ট্রের উল্লেখ ছিল। কিন্তু পাকিস্তান প্রস্তাবের নামে একটি রাষ্ট্র হওয়া ছিল ইতিহাসের মূলধারা থেকে বিচ্যূতি। বাংলাদেশ রাষ্ট্র আবির্ভাবের মাধ্যমে ইতিহাসের সংশোধন হয়েছে।
১৯৭২ সালের সংবিধানে থাকা ‘বাঙালি জাতীয়তাবাদ’কে ১৯৭৮ সালে পুনঃস্থাপন করা হয় ‘বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ’-এর মাধ্যমে। বাঙালি জাতীয়তাবাদ ভাষাভিত্তিক।
ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা জাতীয়তাবোধই বাংলাদেশের স্বাজাত্যবোধ ও সর্বোপরি স্বাধীনতার অনুপ্রেরণার মূল আধার বাঙালি জাতীয়তাবাদ সমর্থকদের মতে।
অপরপক্ষে, বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ ভূ-খণ্ডভিত্তিক। এ মতবাদে বিশ্বাসীরা যুক্তি দেখান যে, বাংলাদেশের সবাই একই ভাষাভাষী নন, পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু-অধ্যুষিত সাংস্কৃতিক বলয় থেকে মুসলিম-অধ্যুষিত বাংলাদেশ পৃথক ও স্বতন্ত্র।
এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদ ভারত বা পাকিস্তানের চেয়ে শক্তিশালী। কারণ, ৯৮.৭% বাংলাদেশি অভিন্ন। ৯০% মুসলমান এবং ৯৮% লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে। সুতরাং ভারত বা চীনের আধিপত্য থাকলেও তার দ্বারা বাঙালির জাতি-ভাঙনের সম্ভাবনা কম।
ধর্মনিরপেক্ষতা সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষার জন্য সংবিধানে সন্নিবেশিত করা হয়। ১৯৭৬ সালে ভারতের সংবিধানের ৪২ নম্বর সংশোধনীতে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঘোষণা করা হয়।

কিন্তু ভারতেই সংখ্যালঘুরা প্রতিনিয়ত সাম্প্রদায়িক হামলার শিকার হচ্ছেন। বাংলাদেশেও মাঝে মাঝে এ ধরনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দেয়। এজন্য গণতান্ত্রিক পরমতসহিষ্ণুতার প্রয়োজন রয়েছে বলে লেখক অভিমত প্রকাশ করেন।
আন্তঃসাম্প্রদায়িক সহিষ্ণুতা রক্ষার জন্য ধর্মনিরপেক্ষতার প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি আন্তঃগোত্রীয় সদ্ভাব বজায় রাখার জন্যও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রয়োজন রয়েছে। তাছাড়া, সমাজতন্ত্র রাষ্ট্রীয় মূলনীতির একটি। যদিও সমাজতন্ত্র কীভাবে অর্জিত হবে, তার কোনো তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সংবিধানে দেওয়া হয়নি।
সমাজতন্ত্রের মূল স্বপ্ন ছিল অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং সর্বহারা শ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন। এদিক বিবেচনায় লেখক সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য অর্জনের জন্য তিনটি পরামর্শ দিয়েছেন- ১) মৌলিক চাহিদা পূরণ, ২) বেকারত্ব কমানো ও ৩) আর্থিক অসাম্য হ্রাস।
বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হলো গণতন্ত্র, যা স্বাধীনতা অর্জনেরও মূলমন্ত্র ছিল। সমাজতন্ত্রের পতনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের আধিপত্য শুরু হয়। বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র বিকশিত হয়। কিন্তু বাংলাদেশের গণতন্ত্র পাশ্চাত্য থেকে আসেনি। বাংলাদেশে গণতন্ত্র চর্চার ইতিহাস অনেক পুরনো।
৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় গোপাল নামে এক ব্যক্তি গণতান্ত্রিকভাবে জনসমর্থনে মাধ্যমে রাজা নির্বাচিত হন। কিন্তু বাংলাদেশে গণতন্ত্র বারবার বিপন্ন হয়েছে সামরিক সরকার বা কায়েমী স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী দ্বারা। বর্তমানে কর্তৃত্ববাদী বা অনুদার গণতন্ত্র চলছে।
এমনকি গণতন্ত্র বাদ দিয়ে ‘উন্নয়ন’কে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। অর্থনৈতিক অগ্রগতিও অর্জিত হয়েছে অনেক। কর্তৃত্ববাদী শাসন থাকা সত্ত্বেও চীন ও ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি লক্ষণীয়। কিন্তু এই অগ্রগতি টেকসই হবে না, যেমনটা হয়েছে আর্জেন্টিনার ক্ষেত্রে, আরো অবনতি ঘটেছে তাদের।
অমর্ত্য সেন বলেছেন, গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা বাড়ায়। কারণ, গণতন্ত্র না থাকলে জবাবদিহিতা থাকে না, যা দুর্নীতি বৃদ্ধিতে সহায়ক।
৩য় খণ্ডে রাষ্ট্র পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, অর্থাৎ নির্বাহী বিভাগ, জাতীয় সংসদ, বিচার বিভাগ, আমলাতন্ত্র ও শাসন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রিকরণ সম্পর্কে আলোচনা দেখা যায়। মন্ত্রিপরিষদশাসিত শাসন ব্যবস্থায় সংবিধানে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে অনেক সীমিত করা হয়েছে।
সংবিধানের ৪৮(৩) অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ ছাড়া অন্য সকল কাজ প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে সম্পন্ন করবেন। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে ক্ষমতা বাড়ালে রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতিও নিয়োগ করতে পারেন প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়া।
অপরদিকে প্রধানমন্ত্রী অন্যান্য মন্ত্রীর মতো ‘মন্ত্রী’ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ক্ষমতা মন্ত্রীদের থেকে অনেক অনেক ওপরে। বাংলাদেশের সংবিধানে ৫৫(১) ও ৫৫(৩) অনুচ্ছেদে প্রধানমন্ত্রীকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তাতে মন্ত্রিপরিষদশাসিত শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রী-শাসিত সরকার ব্যবস্থা চালু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীই ঠিক করেন কে মন্ত্রী হবে, আর কে বাদ যাবে।
৫৫(৩) অনুচ্ছেদ অনুসারে মন্ত্রিসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকে। কিন্তু সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অনুসারে কোনো সাংসদ তার দলের বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারেন না। অন্যথায় তার আসন হারাবেন!

সংসদ হলো প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের ভিত্তি। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশেও পাশ্চাত্যের অনুকরণে সংসদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বটে, তবে তাদের অনুরুপ কার্যকারিতা নেই। লেখক একে ‘আইসোমরপিক মিমিক্রি’ নামে এক পরিভাষা দিয়ে ব্যাখ্যা করেন।
সংসদের ভূমিকা চারটি- নির্বাহী বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ, আইন প্রণয়ন, বাজেট অনুমোদন ও জনগণের দাবি-দাওয়া পূরণ। বাংলাদেশের সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিপন্থী।
সংসদের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য লেখক এই অনুচ্ছেদ বিলুপ্তির পক্ষে মত দেন। বাজেট অনুমোদন ও আইন প্রণয়নে আরো বেশি সময় দেওয়া দরকার বলে লেখক মনে করেন। এছাড়া, ব্যবসায়ী সাংসদের সংখ্যা বাংলাদেশে যে হারে বাড়ছে তা দেশের জন্য অশুভ লক্ষণ।
বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে বলেন, যেকোনো মামলা মিথ্যা দিয়ে শুরু হয় আর মিথ্যা দিয়ে শেষ করতে হয়।
বিচারপতিদের অভিশংসনের ক্ষমতা জাতীয় সংসদের হাতে দেওয়ার মাধ্যমে বিচারবিভাগের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করা হয়। বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতা লক্ষণীয়। একটি দেওয়ানী মামলা নিষ্পত্তি হতে বাংলাদেশের আদালতে ৩৩ বছর লাগে। সাবেক প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার মতে, আদালতগুলোতে ৩০ লাখ মামলা বিচারাধীন।
বাংলাদেশে প্রচলিত বর্তমান আমলাতন্ত্র ব্রিটিশ আমলে প্রবর্তিত হয়েছিল। আমলাতন্ত্রে অনেক সমস্যা বিদ্যমান, যেমন- নিয়োগ দুর্নীতি, অনুপযুক্ত পরীক্ষাব্যবস্থা, কোটা পদ্ধতি, প্রশাসনের রাজনীতিকরণ ইত্যাদি। এ কারণে, আমলাতন্ত্রে গ্রেশাম বিধির মতো ব্যামো চলছে। গ্রেশাম বিধি বলতে খারাপ মুদ্রা ভাল মুদ্রাকে তাড়িয়ে দেয়। একইভাবে প্রশাসনেও ভাল মানুষগুলোকে তাড়িয়ে দুর্নীতিবাজ মানুষগুলো আসন গ্রহণ করেছে।
৩য় খণ্ডের শেষে অর্থাৎ ১০ম অধ্যায়ে এসে ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণের কথা বলেছেন লেখক। এক্ষেত্রে কুমিল্লা ও ফরিদপুরসহ বর্তমানের আটটি বিভাগ মিলে ১০টি প্রদেশ এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় জেলা পরিষদ গঠন করার প্রস্তাব দেন।
এতে কেন্দ্রের ক্ষমতা হ্রাস পায়। নাগরিকরা অধিক সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ভোগ করতে পারে। নাগরিক ও প্রশাসনের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। এটাকে Double Devolution বা Double Democratization বলা হয়েছে। প্রদেশ সৃষ্টির পরে বিচ্ছিন্নতাবাদের আশঙ্কাও একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের।
১৮৮৫ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত মোট ১১টি সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক নির্বাচন হয় বাংলাদেশ অঞ্চলে। এগুলো হলো- ১৮৮৫, ১৯১৯, ১৯৩৫, ১৯৪৬, ১৯৫৪, ১৯৭০, ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ ও ২০০৮। সুতরাং ভোট জালিয়াতি থেকে রক্ষার জন্য লেখক আনুপাতিক হারে নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করার প্রস্তাব দেন।
এতে সমস্যা হচ্ছে জনগণের সাথে জনপ্রতিনিধির সম্পর্ক থাকে না। সেদিক বিবেচনায় মিশ্র আনুপাতিক হারে নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করার পরামর্শ দেন, যেখানে দুটি কক্ষ থাকবে। নিম্ন কক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠ পদ্ধতিতে এবং উচ্চকক্ষ আনুপাতিক হারে নির্বাচন ব্যবস্থায় চালিত হবে। আর নির্বাচনকালীন সরকার, অর্থাৎ নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন পরিচালনাকারী কর্মকর্তাদের নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে হবে।
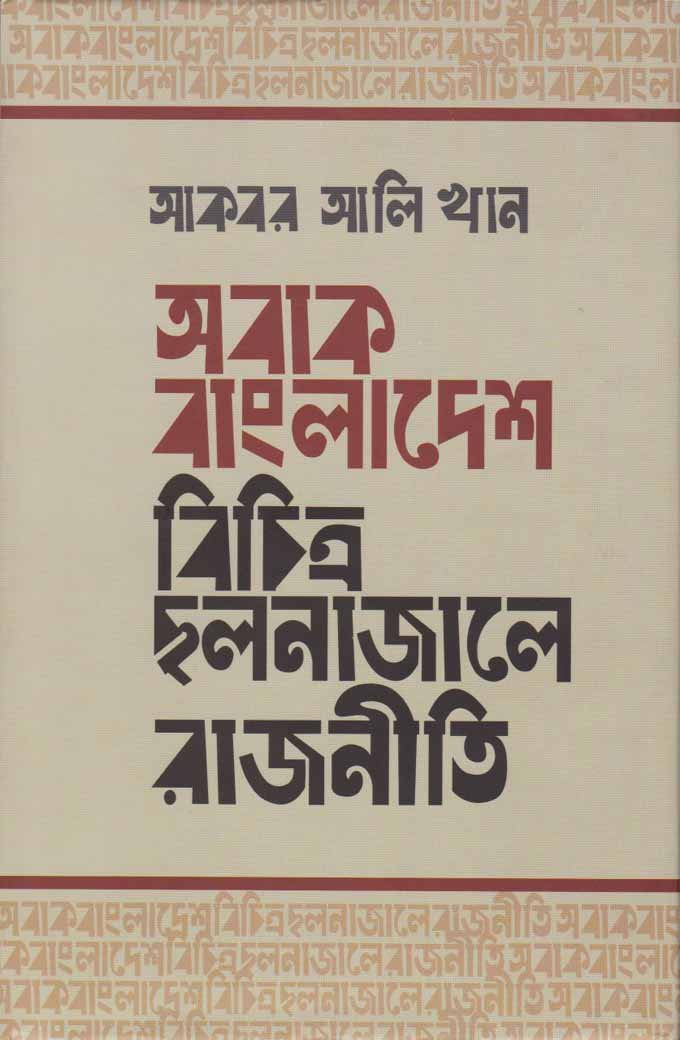
৫ম খণ্ডে রাজনৈতিক দল ও সিভিল সমাজ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। গণতন্ত্রের জন্য রাজনৈতিক দল অপরিহার্য। বাংলাদেশে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল ৪১টি। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দল, মুরব্বি-মক্কেল সম্পর্ক, ব্যক্তিস্বার্থে রাজনীতি, অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের ঘাটতি ইত্যাদি বিদ্যমান রয়েছে। বংশভিত্তিক সংঘাতের রাজনীতি বাংলাদেশে প্রকট। পরমতসহিষ্ণুতা নেই বললেই চলে।
বাংলাদেশে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সিভিল সমাজের ভূমিকার অতীত ইতিহাস অনেক উজ্জ্বল। যদিও বর্তমানে তারা ব্যর্থ। কারণ, মতাদর্শগত ভিন্নতার কারণে তাদের ঐক্যে ফাটল ধরেছে। তাদের আদর্শের রাজনৈতিক দলকে প্রমোট করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে।
মূলত সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ব্যক্তির অধিকার রক্ষার জন্য। পরিবার, রাষ্ট্র ও বাজারের বাইরে ক্রীড়া, বিতর্ক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, পেশাভিত্তিক ও বেসরকারী সংগঠনগুলো সিভিল সমাজের অন্তর্ভূক্ত।
শেষ অধ্যায়ে গিয়ে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও রাজনৈতিক অপসংস্কৃতি থেকে উত্তরণের সন্ধান দেওয়ার চেষ্টা করেন। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখার জন্য আইনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। হরতালের পরিবর্তে গণভোট চালু করা যায়। প্রশাসনের বিকেন্দ্রিকরণের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা হ্রাস করতে হবে।
বইয়ের নাম: অবাক বাংলাদেশ: বিচিত্র ছলনাজালে রাজনীতি || লেখক: আকবর আলি খান
প্রকাশক: প্রথমা || অনলাইন প্রাপ্তিস্থান: রকমারি.কম

.jpeg?w=600)