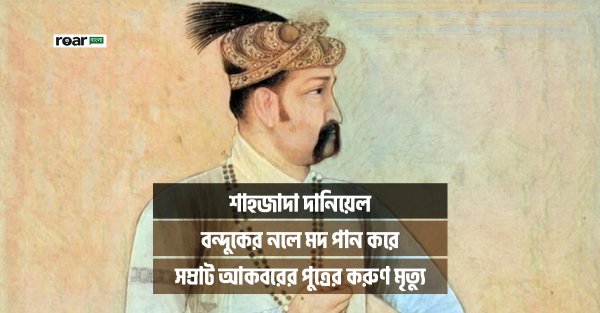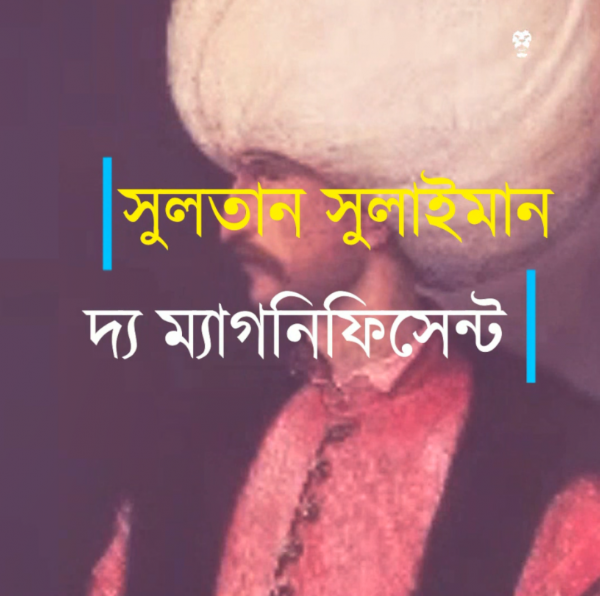অ্যাডলফ হিটলার এবং তার নাৎসি বাহিনী নিয়ে যে কতশত বই রচনা হলো, ব্লগ লেখা হলো কিংবা সিনেমা-ডকুমেন্টরি বানানো হলো, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। যুদ্ধে জয়ের জন্য নাৎসি বাহিনী যে কতসব বিচিত্র কাজকারবার করেছে এককালে, তা ভাবলেও অবাক হতে হয়। আর এ পরিকল্পনা কেবল যুদ্ধের মাঝে সীমাবদ্ধ ছিলো না, বরঞ্চ যুদ্ধ ছাড়িয়ে আরো সুদূরপ্রসারী ছিলো তাদের বিচিত্র সব প্রজেক্ট। তেমনি পাঁচটি পরিকল্পনা, যেগুলো ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়ে গিয়েছিলো, সেসব নিয়েই আমাদের আজকের এ আয়োজন।
অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা
নাৎসি বাহিনীর উচ্চপদস্থ অনেক কর্মকর্তাই জড়িত ছিলেন নানা গুপ্ত সংঘের সাথে। অনেকে তাদের সামরিক বাহিনীর সফলতার জন্য সেসব লোকদের শরণাপন্ন হতেন। এদের মাঝে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন ভিলহেল্ম উলফ, লুডভিগ স্ত্রানিয়াক এবং ভিলহেল্ম গুতবেরলেত। তাদের তিনজনের ছিলো তিন রকমের অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা।

Source: joakimolofsson.deviantart.com
ভিলহেল্ম উলফ ছিলেন একজন জ্যোতিষী। তাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো ইতালীয় একনায়ক বেনিতো মুসোলিনিকে খুঁজে বের করার জন্য, যিনি তখন প্রতিপক্ষের হাতে বন্দী ছিলেন। বলা হয়, তাকে দেয়া কাজটি নাকি আধ্যাত্মিক ক্ষমতাবলে ঠিকমতোই সম্পন্ন করেছিলেন তিনি।
লুডভিগ স্ত্রানিয়াক পেশায় ছিলেন একজন স্থপতি। নরওয়ের জলসীমার কাছে গোপন মিশনে থাকা জার্মান ব্যাটলশিপ দ্য প্রিন্স ইউজেনের অবস্থান সঠিকভাবেই তিনি অনুমান করেছিলেন।
এই তিনজনের মাঝে সবচেয়ে বেশি ভয়াবহ ছিলেন ভিলহেল্ম গুতবেরলেত, পেশায় যিনি ছিলেন একজন চিকিৎসক। হিটলারের একেবারে শুরুর দিককার অনুসারীদের মাঝে তিনি ছিলেন একজন। গুতবেরলেতের ব্যাপারে বলা হয়, তিনি নাকি ইহুদীদের অস্তিত্ব অনুধাবন করতে পারতেন; এমনকি যদি সেই লোকটি কোনো ভিড়ের মাঝেও থাকতো, তবুও তার সেই ‘কাজ’ কিংবা ‘ক্ষমতা’র পথে সেটা কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াত না! এজন্যই হিটলার তার উপর নির্ভরশীল ছিলেন। তার কাজ ছিলো অনেকটা বর্ণ বিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে।
চকলেটের আড়ালে লুকনো ড্রাগ
ব্লিৎজ্ক্রিগ হলো একধরনের যুদ্ধ কৌশল, যেখানে ঝড়ের বেগে প্রতিপক্ষের উপর শক্তিশালী আঘাত হানা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুর দিকে জার্মান বাহিনীর সফলতার অন্যতম কারণ ছিলো এই ব্লিৎজ্ক্রিগ। আর এই ব্লিৎজ্ক্রিগের সফলতার পেছনে কাজ করা বিভিন্ন বিষয়ের মাঝে অন্যতম ছিলো ড্রাগ।
জার্মান মেথ নামে পরিচিত পার্ভিটিনের প্রভাব দেশটির বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপর প্রথমে পরীক্ষা করে দেখা হয়। সেখান থেকে সন্তোষজনক ফলাফল পেলে এরপর নাৎসি বাহিনী তাদের প্রত্যেক সৈন্যের জন্য এ ড্রাগটি সরবরাহের নির্দেশ দেয়। এ ড্রাগের প্রভাবে সেনারা ক্লান্তিহীনভাবে দীর্ঘ সময় একটানা কাজ করে যেতে পারতো। পাশাপাশি মানসিকতার পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন বড় ধরনের ঝুঁকি নিতেও তারা পিছপা হতো না, যা কিনা স্বাভাবিক অবস্থায় অনেকে না-ও করতে পারতো। পরবর্তী সময়ে স্বাদ বৃদ্ধির জন্য ড্রাগটির চারদিকে চকলেট বা ক্যান্ডির আস্তরণ দেয়া হতো।

Source: medium.com
পার্ভিটিন জার্মান সেনাদের সাময়িক সফলতা এনে দিলেও এর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ছিলো ভয়াবহ। অনেক সেনাই এতে ধীরে ধীরে আসক্ত হয়ে পড়ে। এ আসক্তি থেকে তারা মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান শুরু করে দেয়। নিদ্রাহীনতার সমস্যা কাটাতে তারা আফিমযুক্ত মাদক সেবন শুরু করে দেয়, যা তাদের চোখে ঘুমের পরশ বুলিয়ে দিতো।
মিত্র বাহিনীকে ঠেকাতে ১৯৪৪ সাল নাগাদ নাৎসি বাহিনী আরো ভয়াবহ মাত্রার ড্রাগের দিকে ঝুঁকে পড়ে। পার্ভিটিন, মরফিন আর কোকেন মিশিয়ে তারা তৈরি করেছিলো D-IX নামে আরেকটি ড্রাগ। সেই ড্রাগের জন্য গিনিপিগ বানানো হয়েছিলো জেলখানার বন্দীদের। পরীক্ষার ফলাফল ছিলো আশাতীত। ড্রাগটি ব্যবহারের পর বন্দীরা অতিমানবীয় শক্তি ও সহনক্ষমতা দেখিয়েছিলো। মিত্র বাহিনী যদি জার্মানিতে সফলতা না পেতো, তাহলে যে দেশটিতে এর উৎপাদন বেশ ভালোভাবেই শুরু হতো, তা বোধহয় আর না বললেও চলে।
প্রজেক্ট অ্যাঙ্গোরা
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পগুলোতে বন্দীদের উপর কত রকম ভয়াবহ নির্যাতন চালানো হয়েছে, তা অনেকেরই জানা। সেখানে তারা যেন মানুষ ছিলো না, ছিলো গিনিপিগ। তাদের সাথে নাৎসি বাহিনীর সৈন্যদের ব্যবহার, সরবরাহকৃত খাদ্যের অপ্রতুলতা, অত্যাচার, বিভিন্ন গবেষণাতে তাদের ব্যবহারের ইতিহাসগুলো পড়লে এটা ভাবতে বাধ্য হবে যে কেউই।
আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো, যখন মানবতা সেখানে ধুলোয় লুটিয়ে পড়ছিলো, তখনও পশুর প্রতি নাৎসি বাহিনীর মমতা ছিলো দেখার মতো। সেখানে ভূমিকা পাল্টে গিয়েছিলো; মানুষ যেন হয়ে গিয়েছিলো পশু, আর পশু হয়েছিলো মানুষের মতোই মর্যাদাসম্পন্ন! বলা হচ্ছিলো প্রজেক্ট অ্যাঙ্গোরার কথা। হাইনরিখ হিমলারের নির্দেশে এসএস-এর অধীনে হাজার হাজার বন্দীকে নিয়োজিত করা হয়েছিলো বৃহদাকার অ্যাঙ্গোরা খরগোশ পরিচর্যার কাজে। বড়সড় এ খরগোশগুলোকে পরিচর্যার পেছনেও অবশ্য সামরিক বাহিনীর সাথে সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্য ছিলো। এ খরগোশগুলোর পশম সংগ্রহ করে পরবর্তীতে সামরিক বাহিনীর সদস্যদের কোটে ব্যবহার করা হতো। পাশাপাশি অনেক অফিসার শখের বশে সেসব খরগোশ পালতেনও।

Source: popsugar.com
কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পগুলোতে খরগোশগুলো কেমন রাজকীয় হালে আর মানুষেরা অতটা অবর্ণনীয় অবস্থায় দিনাতিপাত করতো, তা ভাবলেও আশ্চর্য হতে হয়। অনাহারে-অর্ধাহারে থেকে যখন বন্দীরা মৃত্যুবরণ করতো, তখন খরগোশগুলোর খাদ্য তালিকায় স্থান পেত নানা পুষ্টিকর খাবার-দাবার। কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের এক কমান্ড্যান্টও তেমনটাই বলেছিলেন, “এসএস যে অ্যাঙ্গোরা খরগোশগুলো পোষা প্রাণী হিসেবে পালতো, মথসেনের (একটি কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প) সবচেয়ে ভালো খাবারদাবার পাওয়া জীব ছিলো সেগুলোই।”
বিলুপ্ত প্রাণীর পুনরাগমন
জুলিয়াস সিজারের (১০০-৪৪ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) বর্ণনায় অরক নামে চতুষ্পদী এক প্রাণীর কথা জানা যায়, যেগুলো হাজার বছর আগে এ পৃথিবীর বুকে বিচরণ করতো। প্রাণীগুলোকে হাতির চেয়ে আকারে কিছুটা ছোট এবং বেশ উগ্র মেজাজী বলে উল্লেখ করেছিলেন সিজার। ইউরোপ জুড়ে বিচরণ ছিলো তাদের। শিকারী ও যোদ্ধারা তাদের সাহস ও বীরত্বের প্রমাণ রাখতে প্রায় সময়ই বদমেজাজি এ প্রাণীগুলোকে শিকার করতো। সব মিলিয়ে তৎকালে বেশ জনপ্রিয় ছিলো এ অরক।
ওদিকে নাৎসি বাহিনীর লক্ষ্যও ছিলো মর্যাদাপূর্ণ আর্য জাতির প্রতিষ্ঠা। সেই জাতির জন্য অরককে তারা বেশ গুরুত্বপূর্ণ এক প্রাণী হিসেবে বিবেচনা করলো। অর্থাৎ আর্য জাতির মানবসমাজে বিচরণ করা পশুগুলোর মধ্যে থাকবে অরকও। কিন্তু ঝামেলা বাধলো অন্য জায়গায়। অরক ততদিনে বিলুপ্ত প্রাণীর খাতায় নাম লিখিয়ে ফেলেছে! হারিয়ে যাওয়া অরককে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব পড়লো জীববিজ্ঞানী দুই ভাইয়ের উপর, নাম তাদের লুৎয্ হেক ও হাইঞ্জ হেক। নাৎসি বাহিনীর পক্ষ থেকে তাদেরকে সকল রকমের সাহায্য-সহযোগিতা দেয়া হয়েছিলো।

Source: theguardian.com
বেশ কয়েকবার চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন হেক ভ্রাতৃদ্বয়, তবু হাল ছাড়েন নি তারা। শেষ পর্যন্ত জেনেটিক্যালি পারফেক্ট অরকের জন্ম দিতে তারা সক্ষম হন ঠিকই, তবে রয়ে যায় একটি ‘কিন্তু’! সেটা কী? আগে যে অরক ইউরোপে চড়ে বেড়াতো সেগুলো যেমন ছিলো লম্বা, তেমনই ছিলো শক্তিশালী। ওদিকে হেক ভ্রাতৃদ্বয়ের হাত ধরে আসা অরক আকারে ছোট হবার পাশাপাশি শারীরিকভাবেও অতটা পেশীবহুল দেহের অধিকারী ছিলো না। দুই ভাইয়ের নামানুসারে এগুলোকে ‘হেক ক্যাটল’ নামে ডাকা হতো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এসব অরকের অধিকাংশই মারা যায়। বেঁচে থাকা অরকগুলোর স্থান হয় বেলজিয়ামে। ২০০৯ সালে সেসব অরকের এক ডজনের কাছাকাছি বংশধরকে যুক্তরাজ্যের ডেনভারের একটি খামারে স্থানান্তরিত করা হয়েছিলো।
প্রজেক্ট লেবেন্সবর্ন
‘বিশুদ্ধ জার্মান’ জাতি গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে ১৯৩৫ সালের ১২ ডিসেম্বর জার্মানিতে যাত্রা শুরু করে ‘লেবেন্সবর্ন’ নামের একটি প্রজেক্ট, যার অর্থ ‘জীবনের ঝর্নাধারা’। ১৯৩৯ সালের হিসেব মতে সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত এ সংগঠনটির সদস্য সংখ্যা ছিলো আট হাজারের এর কাছাকাছি। এখানে অংশ নেয়ার সবচেয়ে বড় শর্ত ছিলো স্বামী ও স্ত্রী উভয়কেই ‘জাতিগতভাবে বিশুদ্ধ’ হতে হবে।

Source: hubpages.com
প্রথমেই আসা যাক সেই শিশুদের বাবাদের কথায়। বিয়ে করতে এসএস অফিসারদের রাষ্ট্রের অনুমতি নেয়া ছিলো বাধ্যতামূলক। আর সেই সাথে এটাও নিশ্চিত করা লাগতো যে, তার স্ত্রী একজন বিশুদ্ধ জার্মান। লেবেন্সবর্ন প্রোগ্রামে আসা অবিবাহিত নারীদের শয্যাসঙ্গী হতো বিভিন্ন বিবাহিত এসএস অফিসার। তবে এটি ছিল বেশ গোপনীয় একটি প্রোগ্রাম। তাই এখানে অংশ নেয়া প্রত্যেক পুরুষেরই পরিচয় গোপন রাখা হয়, একই কথা নারীদের বেলাতেও প্রযোজ্য।
যেসব নারী এখানে অংশগ্রহণ করতে চাইতেন, তাদেরকে অবশ্যই সোনালী চুল ও নীল চোখের অধিকারিণী হওয়া লাগতো, বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ দিতে হতো যে তার মাঝে বংশগতভাবে কোনো রোগ এসে বাসা বাধে নি। সেই সাথে একেবারে প্রপিতামহ পর্যন্ত বংশতালিকা দিয়ে দায়িত্বরত কর্মকর্তাদের বোঝাতে হতো- তিনি একজন বিশুদ্ধ আর্য।
১৯৪৫ সালে বন্ধ হবার আগপর্যন্ত আনুমানিক ৮,০০০ শিশুর জন্ম হয়েছিলো শুধুমাত্র জার্মান লেবেন্সবর্ন কার্যালয়গুলোতেই। অবিবাহিতা নারীরা তাদের বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের ফলে জন্মানো সন্তানদের সেখানে রেখে গেলে সেই নিষ্পাপ, অবুঝ শিশুগুলোর লালনপালনের দায়িত্ব নিতো সেখানকার ডাক্তার-নার্সরাই। কিছুটা বড় হলে তাদের অনেককেই ধনী নাৎসি পরিবারগুলোর কাছে দিয়ে দেয়া হতো পালক সন্তান হিসেবে।