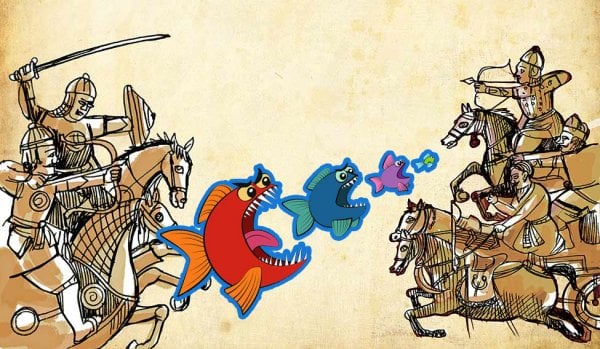এই মুহূর্তে পৃথিবীর সবচেয়ে বিচ্ছিন্ন দেশ কোনটি? নিঃসন্দেহে ২৫ মিলিয়ন জনসংখ্যার উত্তর কোরিয়া। তারা ঠিক কতটা বিচ্ছিন্ন তা ব্যাখ্যা করতে খুব বেশি শব্দ ব্যয় করা লাগবে না। সামান্য একটি গল্প থেকেই বিষয়টি প্রমাণ করে দেয়া যাবে।
২০১০ সালে উত্তর কোরিয়া ভ্রমণে গিয়েছিলেন বিবিসির দুজন সাংবাদিক। তারা পিয়ংইয়ং ইউনিভার্সিটির বিদেশী ভাষা শিক্ষা বিভাগে গিয়ে সেখানকার শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, “তোমরা এত ভালো ইংরেজি বলা কোত্থেকে শিখলে?”
এক তরুণ শিক্ষার্থী উত্তরে বলেছিল, “আমাদের মহান নেতার কারণে। এখানে আমরা অসাধারণ সব ইংরেজি ও আমেরিকান চলচ্চিত্র দেখার সুযোগ পাই। যেমন, দ্য সাউন্ড অভ মিউজিক।”
এরপর যখন ওই তরুণের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, মহান নেতা বাদে আর কোন কোন বিশ্বনেতাদেরকে সে পছন্দ করে, তখন তার ত্বরিৎ উত্তর ছিল, “স্তালিন ও মাও সেতুঙ!”
তবে বিস্ময়কর হলেও সত্য, ওই বিভাগের কোনো শিক্ষার্থীই কোনোদিন নেলসন ম্যান্ডেলার নাম শোনেনি।

অবশ্য প্রতি বছর হাজার তিনেকের মতো উত্তর কোরিয়ান নেলসন ম্যান্ডেলা এবং অন্যান্য বিশ্বনেতাদের নাম জানার সুযোগ পায়, যখন তারা নিজ দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ায় পাড়ি জমায়।
দক্ষিণ কোরিয়ায় পা রাখার পর প্রথমেই তাদের যে অনুভূতিটি হয়, তা হলো: “এ কী রে বাবা, কোনো ভিনগ্রহে চলে এলাম নাকি!”
দক্ষিণ কোরিয়ার জীবনাচরণ দেখে তাদের এমনটি মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কারণ সেখানকার প্রতিটি মানুষের হাতে হাতে মোবাইল ফোন। এই ছোট যন্ত্রটি দিয়েই তারা সুপারমার্কেটে কেনাকাটার পর বিল মেটানো থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সব কাজ করে ফেলতে পারে। এই দেশে রয়েছে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট, যা পৃথিবীর অন্য আর সব দেশের চেয়ে বেশি দ্রুত গতিসম্পন্ন। এই ইন্টারনেটের বদৌলতে তারা মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বের প্রায় যেকোনো প্রান্তের (উত্তর কোরিয়া বাদে) মানুষের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে, যেকোনো তথ্য জেনে নিতে পারে।
এই বিষয়গুলো দেখে উত্তর কোরিয়া থেকে পালিয়ে আসা মানুষগুলো চমৎকৃত ও অভিভূত হয়। নিজ দেশে তো তারা কোনোদিন ইন্টারনেট চালানোর সুযোগ পায়নি। বিশ্বের অন্য কোনো দেশের মানুষের সাথে কথা বলার তো প্রশ্নই আসে না। এসব অধিকার সংরক্ষিত কেবল পিয়ংইয়ং শহরের নির্দিষ্ট কিছু অভিজাত শ্রেণীর নাগরিকের জন্য।
দক্ষিণ কোরিয়ায় আগমনের পর প্রথম কয়েক মাস তাই তাদের কাটে বিশেষায়িত সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে, যেখানে তাদেরকে দেয়া হয় একবিংশ শতকের জীবনধারার সাথে খাপ খাইয়ে নেবার শিক্ষা।
কথায় আছে, তুমি যে খাবারের স্বাদ কোনোদিন চেখে দেখোনি, সে খাবারের জন্য তোমার জিভ কখনো লকলক করবে না। উত্তর কোরিয়ার সাধারণ মানুষের কাছে ইন্টারনেটও ঠিক সেরকমই একটি খাবার, যেটির প্রতি তাদের মনে কখনো আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয় না। বরং তারা সন্তুষ্ট রয়েছে বিশেষ এক ধরনের ইন্টারনাল ইন্ট্রানেট ব্যবস্থা নিয়েই।

বিবিসির সাংবাদিক পিয়ংইয়ং ইউনিভার্সিটির এক পোস্টগ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থীর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, সে কীভাবে তার রিসার্চ পেপারের সাথে লন্ডন কিংবা লস অ্যাঞ্জেলেসে অবস্থানরত একই বিষয়ের শিক্ষার্থীদের রিসার্চ পেপারের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে দেখে। উত্তরে শিক্ষার্থীটি বলেছিল, সে তা করে না, কারণ সে সুযোগই তার নেই। কিন্তু শেষে সে এ-ও বলেছিল, “এতে আমাদের কোনো সমস্যা হয় না। আমাদের যা যা জানার প্রয়োজন তার সবই আমাদের মহান নেতা ইন্ট্রানেট সিস্টেমে মজুদ রেখেছেন।”
তার মানে হলো, একজন গবেষণা পর্যায়ের শিক্ষার্থীর কী কী জানা প্রয়োজন, তা তার দেশের নীতিনির্ধারকরা ইতিমধ্যেই জেনে বসে আছেন!
দেশটির মানুষ যে কেবল ইন্টারনেটের স্বাদ থেকে বঞ্চিত, তা ভাবলে ভুল করবেন। বিনোদন কিংবা তথ্য আহরণের প্রধান মাধ্যম যে টেলিভিশন, সেখানেও তারা নিজেদের মনমতো কিছু দেখতে পারে না। বাধ্য হয় কেবল সেসব অনুষ্ঠান দেখতে, যেগুলো দেখতে তাদের মহান নেতারা তাদেরকে বাধ্য করেন।
টেলিভিশন চ্যানেলগুলো সবই রাষ্ট্রায়ত্ত, যেখানে দেখানো হয় দেশটির তিন মহান নেতার গুণকীর্তন, সেনাবাহিনীর জয়গান, এবং কীভাবে পারমাণবিক অস্ত্রের সুবাদে তারা হয়ে উঠেছে বিশ্বের অন্যতম পরাক্রমশালী রাষ্ট্র তার বিস্তারিত বিবরণ। বাইরের পৃথিবী কীভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, এবং সে তুলনায় তারা ঠিক কতটা পিছিয়ে আছে, তা আঁচ করার ন্যূনতম সুযোগটুকুও তাদেরকে দেয়া হয় না।

সম্প্রতি নাস ডেইলি উত্তর কোরিয়াকে নিয়ে প্রকাশ করেছে একটি ভিডিও, যেখানে দেশটিকে আখ্যায়িত করা হয়েছে “বিশ্বের বিষণ্নতম দেশ” হিসেবে। পাশাপাশি এ-ও বলা হয়েছে, “উত্তর কোরিয়া কোনো কৌতুক নয়। এটি বিচ্ছিন্ন, এটি ভয়ংকর, এটি কঠোর।”
সেই ভিডিওতে আমরা দেখেছি, উত্তর কোরিয়া নামক দেশটি কেমন পৃথিবীর বাইরে অন্য আরেকটি দেশ, যেখানে সাধারণ মানুষের জীবনকে প্রতি পদে পদে নিয়ন্ত্রণ করে ইউনিফর্ম পরিহিত সেনা সদস্যরা। কুরআন, বাইবেল কিংবা অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থ বহনের সুযোগ নেই সেখানে। কারণ ধর্মপালন দেশটিতে নিষিদ্ধ। এছাড়াও নিষিদ্ধ রাজনৈতিক কিংবা স্পর্শকাতর কোনো তথ্য সাথে নিয়ে ঘোরাফেরাও।
মোদ্দা কথা, এটি এমন একটি দেশ যেখানে সাধারণ মানুষ শাসকগোষ্ঠীর হাতের খেলনা পুতুল। শাসকগোষ্ঠী যেভাবে তাদেরকে চালাবে, সেভাবেই তাদেরকে চলতে হবে।
স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে, কেন উত্তর কোরিয়া এমন বিচ্ছিন্ন একটি দেশ। এবং জেনে অবাক হবেন, এমন আত্ম-বিচ্ছিন্নতার পেছনে রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস। যার সূত্রপাত বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে কোরিয়ান পেনিনসুলা ভেঙে কোরিয়া দুভাগে বিভক্ত হওয়ারও অনেক আগে থেকে।
চতুর্দশ থেকে বিংশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত অবিভক্ত কোরিয়াকে শাসন করত চোসন রাজবংশ, যারা দেশটিকে বাকি বিশ্বের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। এর পেছনে প্রধানত দুটি কারণ ছিল। প্রথমত, দেশটিকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। দ্বিতীয়ত, কনফুসিয়ান সংস্কৃতির সুবাদে নিজেদেরকে অন্যদের থেকে অনেক বড় মনে করা। তবে একেবারেই কারো সাথে যোগাযোগ না রাখলে তো আর টিকে থাকা সম্ভব নয়, তাই চোসন শাসকরা সীমিত পরিসরে মৈত্রী বজায় রেখেছিলেন চীন ও জাপানের সাথে।
এবং মজার ব্যাপার হলো, একই সময়কালে জাপান ও চীনও কিন্তু আত্ম-বিচ্ছিন্নতার এই নীতি গ্রহণ করেছিল। তবে কোরিয়ার বিশেষত্ব এই যে, অন্য দুই দেশের চেয়ে তাদের বিচ্ছিন্নতা অনেক বেশি দীর্ঘমেয়াদী ছিল।

উনবিংশ শতকে প্রথম পশ্চিমা শক্তিরা কোরিয়ার ডাকনাম দেয় হারমিট কিংডম (নির্জনবাসী সাম্রাজ্য)। কেননা তারা যখন বাণিজ্যের নাম করে এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঢুকে পড়ছিল এবং একে একে সেসব অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করছিল, তখনো কোরিয়া নিজেদেরকে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন রেখেছিল।
কিন্তু সবকিছুরই তো একটি সমাপ্তি রয়েছে। তেমনই কোরিয়ার আত্ম-বিচ্ছিন্নতার মেয়াদও একদিন ফুরিয়ে যায়। ১৯১০ সালে দেশটি চলে যায় জাপানের দখলে। তবে জাপানও খুব বেশিদিন ধরে রাখতে পারেনি কোরিয়ার নিয়ন্ত্রণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যখন তাদের নির্মম পরাজয় হয়, তখন কোরিয়া চলে যায় যুদ্ধজয়ীদের নিয়ন্ত্রণে।
যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য ছিল তারা পুরো কোরিয়াই দখল করে নেবে। কিন্তু তা হতে দেয়নি সোভিয়েত ইউনিয়ন। তারাও দাবি করে বসে কোরিয়ার ভাগ। তখন দ্বিখণ্ডিত করা হয় কোরিয়াকে। ৩৮তম সমান্তরাল রেখার মাধ্যমে নির্ধারিত হয় দুই কোরিয়ার সীমান্তরেখা। সীমান্তের উত্তরাংশের দখল পায় সোভিয়েত ইউনিয়ন। সেটিকে নিজেদের সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে দীক্ষিত করে তারা। আর দক্ষিণ অংশ নেয় পুঁজিবাদী যুক্তরাষ্ট্র। উত্তর কোরিয়ার রাজধানী করা হয় পিয়ংইয়ংকে, আর দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউল।
তবে এটি হওয়ার কথা ছিল একটি সাময়িক ব্যবস্থা। পাঁচ বছরের মধ্যে পুনরায় কোরিয়াকে স্বাধীন করে দেবার শর্তে ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরে মস্কো সম্মেলনে একটি ট্রাস্টিশিপও গঠন করেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও ব্রিটেন।
বলাই বাহুল্য, যে সমঝোতায় পৌঁছানোর কথা ছিল যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের, শেষ পর্যন্ত তাতে তারা পৌঁছায়নি। ফলে দুই কোরিয়ায় উদ্ভব ঘটে দুটি পৃথক সরকারের। জোসেফ স্তালিন উত্তর কোরিয়ার নেতা হিসেবে ক্ষমতায় বসান কিম ইল সাংকে। ৫০ বছরেরও বেশি সময় শাসন করেন তিনি। এরপর তার জায়গায় দেশটির শাসন ক্ষমতায় বসেন কিম জং ইল। এবং বর্তমানে দেশটির সুপ্রিম লিডার হিসেবে রয়েছেন তার পুত্র কিম জং উন।
বিশ্বব্যাপী যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে যখন চলছে স্নায়ুযুদ্ধের উত্তেজতা ও দ্বন্দ্ব, তারই ভেতর ১৯৫০ সালে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া, যা ইতিহাসের পাতায় কোরীয় যুদ্ধ হিসেবে পরিচিত। এ যুদ্ধে দুই কোরিয়া পাশে পায় তাদের নিজ নিজ মিত্রশক্তিকে।
কোরীয় যুদ্ধ ছিল এককথায় ভয়াবহ। আমেরিকানরা উত্তর কোরিয়ায় যে বোমা হামলা চালিয়েছিল, তারপর সেখানকার রাজধানীতে আর মাত্র একটি দালান বেঁচে ছিল। অবশেষে ১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে কোরীয় যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে এ যুদ্ধের অবসান ঘটে বটে, কিন্তু দুই কোরিয়ার মধ্যে চলমান দ্বন্দ্বের কোনো অবসান তাতে ঘটেনি, বরং সে দ্বন্দ্ব আজও অব্যহত রয়েছে।

১৯৫০-এর দশকে কোরীয় যুদ্ধের অবসানের পর থেকেই উত্তর কোরিয়া এক ভঙ্গুর মানসিকতার মধ্য দিয়ে যেতে থাকে। সব সময় তাদের মনে উৎকণ্ঠা, এই বুঝি আবার শত্রুপক্ষ তাদের দখল নিয়ে নিল। আর ঠিক এই কারণেই কিম ইল সাং একটি আত্ম-বিচ্ছিন্নতা দর্শনের অনুসারী হন, যেটিকে কোরীয় ভাষায় বলা হয় “জুশে”। এমনকি আজও দেশটির আনুষ্ঠানিক দর্শন হিসেবে বিবেচিত হয় এই জুশে।
এই দর্শন অনুযায়ী কিম ইল সাং রাষ্ট্র পরিচালনার তিনটি মূলনীতি দাঁড় করান: রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরশীলতা, এবং সামরিক স্বায়ত্তশাসন। এবং এই রাজনৈতিক অবস্থান উত্তর কোরিয়াকে পরিণত করেছে একটি সত্যিকারের হারমিট কিংডমে। কেননা তারা শুধু সম্ভাব্য শত্রু রাষ্ট্রগুলোর সাথেই নিজেদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেনি, বরং প্রায় একই রকম দূরত্ব বজায় রেখেছে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাথেও।
অবশ্য চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে সীমিত যোগাযোগ ছিল বটে উত্তর কোরিয়ার। কিন্তু চীন যখন পশ্চিমা বিশ্ব, বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের উন্নতি ঘটায়, এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যায়, তখন আরো বেশি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তারা।
গত শতকের শেষ দশকের শেষ ভাগে এসে দক্ষিণ কোরিয়া ও পশ্চিমা বিশ্বের সাথে উত্তর কোরিয়ারও সম্পর্কের উন্নতির একটি ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু সে ইঙ্গিত পুরোপুরি বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্বেই ভেঙ্গেচুরে তছনছ হয়ে যায়, যখন ২০০২ সালে জর্জ ডব্লিউ বুশ দেশটিকে অন্তর্ভুক্ত করেন অ্যাক্সিস অভ ইভিল বা দুষ্টচক্রের।
ওই একই বছর পিয়ংইয়ং থেকে অপসারণ করা হয় আন্তর্জাতিক পরমাণু পরিদর্শকদের। পরের বছর উত্তর কোরিয়া পরমাণু অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ চুক্তি থেকে নিজেদের নাম প্রত্যাহার করে নেয়, এবং জানায় যে তাদের কাছে পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে।

পারমাণবিক অস্ত্রের মালিকানার স্বীকারোক্তি ছিল উত্তর কোরিয়ার আত্ম-বিচ্ছিন্নতার কফিনে শেষ পেরেক। ২০০৯ সালে তারা পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা চালায়। এরপর থেকে তারা নিজেদেরকে আরো বেশি বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে থাকে বহির্বিশ্বের কাছ থেকে। বিশেষত কিম জং উনের শাসনামলে এই বিচ্ছিন্নতা আরো প্রকট রূপ ধারণ করেছে।
আত্ম-বিচ্ছিন্ন অবস্থায় উত্তর কোরিয়ার মানুষ যে খুব ভালো আছে তা-ও কিন্তু নয়। ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক সব ধরনের মানবাধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। সেখানে গণমাধ্যমের নেই কোনো স্বাধীনতা। নেই মতপ্রকাশের স্বাধীনতা। সাধারণ মানুষেরা চরম অপুষ্টির শিকার হচ্ছে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অপরাধে (যেমন কেউ যদি দক্ষিণ কোরিয়ার ডিভিডি দেখে) মানুষকে জেলবন্দি করা হচ্ছে। নারীরা চরম শারীরিক, মানসিক ও যৌন নিগ্রহের শিকার হচ্ছে। মানুষের উপর বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক শ্রমের নীতি চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। এমনকি রেহাই পাচ্ছে না বিদেশীরাও। পর্যটকরা দেশটিতে বেড়াতে গিয়ে নিয়মিতই অপদস্থ হচ্ছে, অনেককে আটক করেও ফেলা হচ্ছে।
ইতিহাসের চমৎকার সব বিষয়ে রোর বাংলায় লিখতে আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন এই লিঙ্কেঃ roar.media/contribute/