
১৬৮৫ সাল। ইংল্যান্ডের সিংহাসনে তখন রাজা দ্বিতীয় জেমস। রাজনৈতিক বিভিন্ন ইস্যুতে সংসদের সাথে বিরোধে জড়িয়ে পড়েন রাজা দ্বিতীয় জেমস, বিরোধ ছিল ধর্মীয় আচরণের ভিন্নতা নিয়েও। রাজা নিজের শাসনকে সুসংহত করতে প্রথা ভেঙে দ্বিতীয় মেরির বদলে সিংহাসনের উত্তরাধিকার করেন তরুণ জেমস ফ্রেন্ডিস এডওয়ার্ড স্টুয়ার্ডকে, তৎকালীন কার্যকর সংসদকে ভেঙে দিয়ে উদ্যোগ নেন নিজের পছন্দকে আইনসভা গঠনের।
রাজা আর আইনসভার এই সংকটের মধ্যেই ইংল্যান্ডে আক্রমণ করে হল্যান্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়াম, যাতে প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিল পরিবর্তনকামীদের। শাসনক্ষমতা পরিবর্তিত হওয়ার সাথে সাথে রাজা তৃতীয় উইলিয়ান ও রানী দ্বিতীয় মেরির কাছ থেকে আইনসভা বিভিন্ন সংস্কার নিয়ে দেনদরবার শুরু করে। ১৬৮৯ সালের সংস্কারে রাজার কাছ থেকে পাওয়া যায় নিয়মিত সংসদ অধিবেশন বসানোর অনুমতি, রাজা প্রতিশ্রুতি দেন সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনেরও। মত প্রকাশের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, চিহ্নিত করার সাথে সাথে সীমিত করা হয় রাজার ক্ষমতাকে। যদিও এই রাজনৈতিক সংকটকালীন সময়ে স্কটল্যান্ড আর আয়ারল্যান্ডে ভয়াবহ সহিংসতা হয়, তথাপি এই সময়কে ইংল্যান্ডে চিহ্নিত করা হয় ‘গৌরবময় বিপ্লব’ হিসেবে।
এই বিপ্লবের পরে ইংল্যান্ডে রাজা আর কখনোই সুযোগ পাননি চূড়ান্ত কর্তৃত্ববাদ চর্চার, কাজের জন্য রাজাকে দায়বদ্ধ থাকতে হয়েছে আইনসভার কাছে। রাজার অসীম ক্ষমতাকে সীমিত করে আইনসভার মাধ্যমে জনগণের স্বাধীনতা আর সার্বভীমত্বের চর্চার এই উদাহরণ পরবর্তীতে ভূমিকা রেখেছে আধুনিক গণতন্ত্রের বিবর্তনে, ভূমিকা রেখেছে সাংবিধানিক শাসনতন্ত্রের আন্দোলনের প্রেরণা হিসেবে।

আটলান্টিক রেভ্যলুশনের মাধ্যমে শুরু হওয়া আধুনিক গণতন্ত্রের বিবর্তনের তৃতীয় ঢেউ হিসেবে অধাপক সেভা গুনিস্কায় চিহ্নিত করেছেন প্রথম সাংবিধানিক শাসনতন্ত্রের আন্দোলনকে। ২০১৮ সালে প্রকাশিত ‘‘ডেমোক্রেটিক ওয়েভস ইন হিস্ট্রিকাল পার্সপেকটিভ’’ আর্টিকেলে অধ্যাপক সেভা এই তৃতীয় ঢেউয়ে অন্তর্ভুক্ত করেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের দাবিতে সংগ্রামগুলোকে, রাজার অসীম ক্ষমতার বিপরীতে দাঁড়িয়ে আইনসভার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার দাবিগুলোকে। অন্তর্ভুক্ত করেছেন অটোমান সাম্রাজ্য থেকে গ্রিকদের দশকব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রামকেও।
প্রথম সাংবিধানিক শাসনতন্ত্রের আন্দোলন
উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই ফ্রান্সে উত্থান ঘটে সমরনায়ক নেপোলিয়ন বেনোপার্টের, যার উত্থানের প্রভাব পড়ে পুরো ইউরোপে। নেপোলিয়নের আক্রমণে ইউরোপে রাজনৈতিক সংকটের শুরু হয় পর্তুগালকে দিয়ে, চার বছরের মধ্যে তিনবার পর্তুগালকে আক্রমণ করে নেপোলিয়নের সেনাবাহিনী। ফরাসি আক্রমণের মুখে পর্তুগালের রাজা আশ্রয় নেন ব্রাজিলে, ইউনাইটেড কিংডম অব পর্তুগাল, ব্রাজিল এন্ড আলগার্ভেস এর রাজধানী করা হয় ব্রাজিলের রিও ডি জেরিনোকে। ১৮১৫ সালে ফ্রান্সে নেপোলিয়নের পতন হলে রাজনৈতিক সংকটের একটা ধাপ শেষ হয় পর্তুগালের, রাজা সিদ্ধান্ত নেন ব্রাজিলকে থেকেই সাম্রাজ্য পরিচালনার, পর্তুগালে রিজেন্ট হিসেবে নিযুক্ত করেন ব্রিটিশ প্রতিনিধিকে। পর্তুগালের সেনাবাহিনীর একটা অংশ মেনে নেয়নি পর্তুগালকে ব্রাজিলের উপনিবেশ হিসেবে আচরণের এই সিদ্ধান্ত, গোপনে গোপনে চলতে থাকে বিপ্লবের প্রস্তুতি।

১৮১৭ সালে এই পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যায়, মৃত্যুদন্ড হয় বিপ্লবের পরিকল্পনার সাথে যুক্ত ডজনখানেক সামরিক কর্মকর্তার। ব্রিটিশ রিজেন্টের মাধ্যমে দেশপ্রেমিক সৈন্যদের মৃত্যুদন্ডের ক্ষোভ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে দেশব্যাপী, পর্তুগালে বিভিন্ন স্থানে সামরিক বাহিনীও বিদ্রোহ করা শুরু করে। রাজা দ্রুত পর্তুগাল থেকে ফিরে আসেন। বিদ্রোহীদের দাবিতে শাসনব্যবস্থার কাঠামোর ব্যাপারে নির্বাচন হয়, ফলাফলের সাথে একমত হয়ে রাজা মেনে সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের দাবি।
এরপরও রাজা তার ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা করেছেন, আইনসভার কার্যক্রমে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করেছেন, পর্তুগালকে ঠেলে দিয়েছেন সংঘাতের দিকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর সিকিতে এই বিপ্লব সাংবিধানিক শাসনতন্ত্রের পথ দেখায় পর্তুগালকে। নেপোলিয়নের সেনাবাহিনীর আক্রমণের কারণে কিংডম অব পর্তুগালের রাজধানী ব্রাজিলের রিও ডি জেনেইরোতে স্থানান্তরিত হওয়ারে প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে, বিপ্লবকালে প্রথমে পর্তুগাল স্বাধীনতা ঘোষণা করে ব্রাজিলের কাছ থেকে, পরবর্তীতে ব্রাজিলকে আবার উপনিবেশ করতে চাইলে পর্তুগালের কাছ থেকে ব্রাজিলের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন পর্তুগালের রাজপুত্র পেদ্রো। ১৮২৫ সালে পর্তুগালের রাজা স্বীকৃতি দেন ব্রাজিলের স্বাধীনতার।

পর্তুগালকে যখন নেপোলিয়নের সেনাবাহিনী প্রথম আক্রমণ করে, তখন জাতীয় নিরাপত্তাকে প্রাধান্য দিয়ে ফ্রান্সের সাথে চুক্তি করেন স্পেনের রাজা। চুক্তি থাকার পরও, ‘চিরস্থায়ী জাতীয় স্বার্থকে’ কেন্দ্র করেই পর্তুগাল আক্রমণের সফলতার পরপরই স্পেনে আক্রমণ করে নেপোলিয়নের সেনাবাহিনী। যুদ্ধে স্পেন পরাজিত হয়, বন্দী হন স্পেনের রাজা সপ্তম ফার্দিনান্দ। এর ফলে স্পেন বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়, বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে সহিংসতা। এর মধ্যেই ফ্রান্সের বিরুদ্ধে স্পেনের বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধযুদ্ধ চলতে থাকে, যুদ্ধপদ্ধতিতে প্রথমবারের মতো উত্থান ঘটে গেরিলাযুদ্ধের। রাজনৈতিক সংকটের মধ্যেই ১৮১২ সালে স্পেনে আইনসভার মাধ্যমে একটি সংবিধান তৈরি করা হয়, সীমিত করা হয় রাজার ক্ষমতাকে, বৃদ্ধি করা হয় আইনসভার ক্ষমতা।
নেপোলিয়নের পতনের পর ফ্রান্সের বন্দিত্ব থেকে স্পেনে ফিরে আসেন রাজা সপ্তম ফার্দিনান্দ, প্রবল বিরোধিতার মুখেও বাতিল করেন সংবিধান, পুরোপুরি ফিরে যান রাজতন্ত্রে। উদারপন্থীদের বিপ্লব চলতে থাকে, চলতে থাকে সাংবিধানিক শাসনতন্ত্রের দাবিতে আন্দোলন। ১৮২০ সালের এক ক্যু এর মাধ্যমে স্পেন পুনরায় ফিরে যায় সাংবিধানিক রাজতন্ত্রে, নিশ্চিত করা হয় আইনসভার প্রাধান্য।

পর্তুগাল আর স্পেনের শাসনকাঠামোর পরিবর্তনের দাবিতে বিপ্লবের ছোঁয়া লাগে ইউরোপের আরেক দেশ ইতালিতেও, শুরু হয় সাংবিধানিক শাসনের দাবিতে বিপ্লব। বিপ্লবের শুরু হয় ইতালির দ্বীপরাজ্য সিসিলিতে, সামরিক বাহিনী কমান্ডার গাগ্লিলমো পেপের নেতৃত্বে। দ্রুতই এই সংস্কারের দাবি ছড়িয়ে পড়ে ইতালির অন্যান্য অংশে, সফল অভ্যুত্থান হয় নাপলিসে। বিপ্লবের সাথে যুক্ত হয় পাইডমন্ট, লুম্বারডি, পার্মার মতো অঞ্চলগুলো, যুক্ত হয় মডেরা, প্যাপেল স্টেটের মতো অঞ্চলগুলোও। গণদাবির মুখে ১৮২০ সালে ইতালিতে গঠিত হয় নতুন একটি আইনসভা, সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে শুরু হয় সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের।
ইউরোপের আরেক দেশ গ্রিসের সংগ্রামটা ছিলো সম্পূর্ণ অন্যরকম। ১৪৫৩ সালে অটোমান সাম্রাজ্যের কাছে স্বাধীনতা হারানোর পর থেকে গ্রিকরা বহুবার চেষ্টা করেছে স্বাধীনতা ফিরে পেতে, ব্যর্থ হয়েছে প্রতিবারই। স্বাধীনতার দূর্বার আকাঙ্ক্ষাকে সঙ্গী করেই ১৮১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীনতাকামী গ্রিকদের গোপন সংগঠন, ফিলিকি ইটেরিয়া। ৬ মার্চ, ১৮২১ সালে শুরু হয় তাদের বিদ্রোহ, আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষিত হয় ২১ মার্চ। দান্যুবাইনে ছড়িয়ে পড়া এই বিদ্রোহ স্থানীয়ভাবে অটোমানরা দমন করলেও দ্রুতই তা ছড়িয়ে পড়ে পুরো গ্রিসজুড়ে।
প্রায় এক দশকব্যাপী যুদ্ধে গ্রিকদের পাশে এসে দাঁড়ায় রাশিয়ান সাম্রাজ্য, গ্রেট ব্রিটেন আর ফ্রান্সের সাথে গ্রিকদের সহযোগিতা করে অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তিগুলোও। গ্রিকদের কাছে নৌযুদ্ধে পরাজিত হয়ে অটোমান সাম্রাজ্য সাহায্য চায় মিশরের রাজার কাছে, অটোমানদের পাশে দাঁড়ায় আলজেরিয়াও, সৈন্য আসে ত্রিপোলিতানিয়া থেকেও। শুরুতে মিশরের রাজপুত্রের নেতৃত্বে আসা সাহায্যকারী বাহিনী সাফল্য লাভ করলেও দ্রুতই অটোমানরা নিয়ন্ত্রণ হারাতে থাকে গ্রিসের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। এই যুদ্ধের সাথে অটোমানদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয় রাশিয়ানরাও, প্রযুক্তি আর রুশ রণকৌশলের বিপক্ষে বছরব্যাপী এই যুদ্ধ অটোমানদের পিছিয়ে দেয় গ্রিসের বিভিন্ন ফ্রন্টে। সবকিছু মিলিয়েই, প্রায় চারশ বছর উপনিবেশ থাকার পরে অটোমানদের বিপক্ষে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে গ্রিকরা, মুক্ত হয় উপনিবেশ শাসন থেকে, লাভ করে স্বাধীনতা।
আধুনিক গণতন্ত্রের তৃতীয় ঢেউ
সাম্রাজ্যবাদের যুগ থেকে আধুনিক গণতন্ত্রে বিবর্তনের প্রক্রিয়াটি হয়েছে উপনিবেশগুলো স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে, হয়েছে রাজার অসীম ক্ষমতাকে সংবিধানের মাধ্যমে নির্দিষ্ট, চিহ্নিত ও সীমিত করার মধ্য দিয়ে। আধুনিক গণতন্ত্রের বিবর্তনের প্রথম ঢেউয়ে ছিল এই জাতিরাষ্ট্রের উত্থানের প্রক্রিয়া, ছিল ইউরোপীয় উপনিবেশ থেকে লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলনেও। এই প্রক্রিয়া ধারাবাহিকভাবে বজায় থেকেছে তৃতীয় ঢেউয়েও, ইউরোপীয় দেশগুলোর প্রথম সংবিধানিক শাসনতন্ত্রের আন্দোলনের সময়েও।
প্রথমত, নগররাষ্ট্র এবং সাম্রাজ্যবাদের যুগে রাজাকে দেখা হতো ঐশ্বরিক প্রতিনিধি হিসেবে, রাজারা ছিলেন আইনের উর্ধ্বে, শাসনকাঠামোতে চর্চা করতেন অসীম ক্ষমতা। ইংল্যান্ডে ম্যাগনাকার্টা চুক্তির মাধ্যমে প্রথমবারের মতো রাজাকে আইনের অধীনে আনা হয়, যার পূর্ণতা পায় গৌরবময় বিপ্লবের সময়ে এসে। পর্তুগাল, স্পেন, ইতালির মতো দেশগুলোতে রাজারা অসীম ক্ষমতা ভোগ করার সুযোগ পেয়েছেন উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত, রাজাদের ক্ষমতা ছিল দায়বদ্ধতা আর জবাবদিহিতার উর্ধ্বে। আধুনিক গণতন্ত্রের বিবর্তনকালে এই অঞ্চলগুলোতে রাজার এই অসীম ক্ষমতাকে দায়বদ্ধ করার চেষ্টা হয় সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের মাধ্যমে, জবাবদিহিতার আওতায় আনা হয় আইনসভা তৈরির মাধ্যমে। বন্ধ হয় রাজাকে ঐশ্বরিক প্রতিনিধি হিসেবে দেখার প্রবণতা।

দ্বিতীয়ত, রাজতন্ত্রে রাজা অসীম ক্ষমতা একাই চর্চার সুযোগ থাকলেও, রাজা এই অসীম ক্ষমতা চর্চা করেন তার আশেপাশে থাকা কিছু স্বার্থগোষ্ঠীর মাধ্যমে। রাজার ক্ষমতার অংশ হওয়ার সাথে সাথে এই স্বার্থগোষ্ঠী নিয়ন্ত্রণ নেওয়া শুরু করে অর্থের বড় অংশের, চর্চা করে রাজনৈতিক ক্ষমতা, গ্রহণ করে সামাজিকভাবে মর্যাদাপূর্ণ স্থান। এই স্বার্থগোষ্ঠীর কার্যক্রমে রাষ্ট্রের অধিকাংশ সম্পদের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় তাদের হাতে, চালু হয় কতিপয়তন্ত্র। ইউরোপের যেসব দেশে লিবারেল অংশ শাসনতন্ত্র সংশোধনের আন্দোলনে সফল হয়েছে, সেসব দেশে স্পষ্ট চেষ্টা ছিল কতিপয়তন্ত্রের কাঠামো থেকে বেরিয়ে আসার। সংবিধানগুলোতে এই অভিজাত শ্রেণিকে দেওয়া হয়নি কোনো বিশেষ সুবিধা, আইনসভাতেও তাদের জন্য ছিল না কোনো সংরক্ষিত আসন। রাজাকে এই অভিজাত শ্রেণীর পরামর্শ গ্রহণের পরিবর্তে আইনসভার পরামর্শ গ্রহণের কাঠামো তৈরি হয়, সংবিধানের মাধ্যমে।
সংবিধানে মাধ্যমে সীমিত করা হয় রাজ্যের ক্ষমতাচর্চার সুযোগকেও, কমে যায় রাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান হিসেবে চার্চের আবির্ভাবের সুযোগও। বিচারব্যবস্থাকে নিয়ে আসা হয় রাষ্ট্রকাঠামোর অধীনে, ফলে কমে চার্চের অর্থনৈতিক আয়ও।
তৃতীয়ত, দীর্ঘকাল রাজতন্ত্রের অধীনে থাকা ইউরোপীয় দেশগুলোর রাজারা গণতান্ত্রিক বিবর্তনের সাথে খুব একটা সহযোগিতামূলক আচরণ করেননি, আইনসভাকে দিতে চাননি ক্ষমতার ভাগ। ফলে, রাজারা যখনই সুযোগ পেয়েছেন, রাজনৈতিক সংঘাতের সুযোগে সংবিধানকে স্থগিত করেছেন, ভেঙে দিয়েছেন আইনসভাকে, বাধা দিয়েছেন তাদের নিয়মিত সভায়। এরপরও আধুনিক গণতন্ত্রের পথে, সাংবিধানিক শাসনতন্ত্রের পথে, সমাজের রক্ষণশীল কাঠামোর বিপরীতে সংস্কারমূলক পদক্ষেপের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন শাসনব্যবস্থার বিবর্তনে রাখে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, গণতান্ত্রিক বিবর্তনের আবেদন ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তে।
চতুর্থত, সাম্রাজ্যবাদের যুগ থেকে আধুনিক গণতন্ত্রের যুগে যাত্রার অন্যতম নিয়ামক হয়েছে অষ্টাদশ আর উনবিংশ শতাব্দীতে স্বাধীনতা পাওয়া দেশগুলো। ভাষা, ধর্ম, জাতিগত পরিচয়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি হওয়া জাতীয়তাবাদ উপনিবেশ শাসনে থাকা বিভিন্ন রাজ্যগুলোকে স্বাধীন হওয়ার প্রেরণা জোগায়, স্বাধীনতা আর নাগরিক অধিকারের ধারণা থেকে শাসনব্যবস্থা হিসেবে রাজতন্ত্রের জায়গায় প্রতিস্থাপিত হয় গণতন্ত্র। দীর্ঘ চারশো বছরের অটোমান উপনিবেশ শাসনের পরে গ্রিকদের স্বাধীনতা অর্জন অন্যান্য উপনিবেশের স্বাধীনতার মতো সুগম করে আধুনিক গণতন্ত্রের সম্প্রসারণমূলক বিবর্তনের পথ।

সাংবিধানিক শাসনতন্ত্রের আন্দোলন রাজার ক্ষমতাকে সীমিত করতে পারলেও, আইনসভার প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারলেও, রেনেসাঁর ধারণায় প্রভাবিত হয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতা আর নাগরিক অধিকারের দাবিতে অগ্রসর হতে পারলেও, এই শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলে তৈরি হওয়া সংবিধানগুলো অর্থনৈতিক পিরামিডে নিচুস্তরে থাকা অংশের অধিকার নিশ্চিতে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেনি, পদক্ষেপ নেয়নি সমাজে বিরাজমান বৈষম্য দূরীকরণেও। অর্থাৎ আটলান্টিক রেভ্যলুশন, লাতিন আমেরিকার স্বাধীনতার পর্ব পেরিয়ে তৃতীয় পর্বে এসেও রাজনৈতিকভাবে গণতন্ত্র পূর্ণাঙ্গ কাঠামোগত রূপ ধারণ করতে পারেনি, রেনেসাঁর ধারণাগুলো বারবার হোঁচট খেয়েছে সমাজের রক্ষণশীল কাঠামোর কাছে।

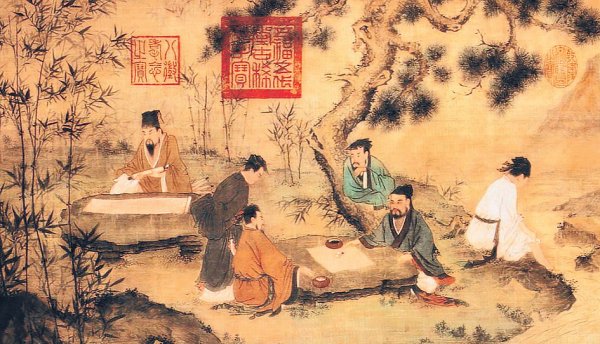




.jpeg?w=600)

