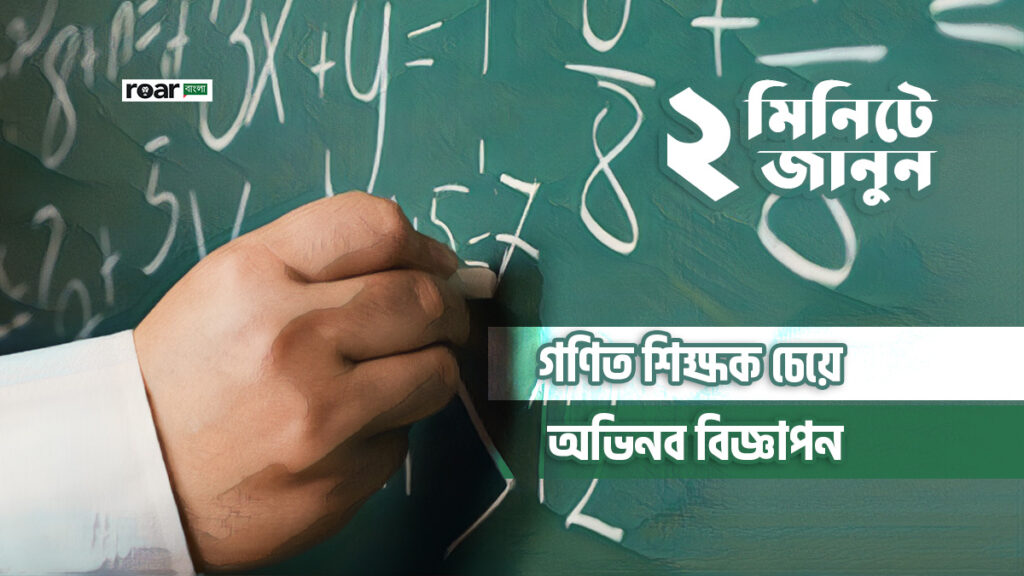.jpeg?w=1200)
সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তুরস্কের ওপর, বা আরো স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, তুর্কি প্রতিরক্ষা খাতের ওপর, অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। মার্কিন ফেডারেল আইন ‘Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act’–এর (CAATSA) আওতাধীনে তুর্কি ‘প্রেসিডেন্সি অফ ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রিজ’ ও সংশ্লিষ্ট কতিপয় ব্যক্তির ওপর এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, যেসব রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূরাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী (যেমন: রাশিয়া, ইরান, উত্তর কোরিয়া প্রভৃতি), সেসব রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই সাধারণত এই আইন ব্যবহার করে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। কিন্তু তুরস্ক (অন্তত আপাতদৃষ্টিতে) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূরাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী তো নয়ই, বরং দেশটি যুক্তরাষ্ট্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত মিত্র এবং মার্কিন–নেতৃত্বাধীন ‘উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা’র (North Atlantic Treaty Organization, ‘NATO’) অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। তাহলে যুক্তরাষ্ট্র কেন তার ‘মিত্র’ রাষ্ট্রের সঙ্গে ‘শত্রু’ রাষ্ট্রের মতো আচরণ করছে?
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা অবশ্য লর্ড পামারস্টোনের সেই অমোঘ বাণীর প্রতি আস্থাশীল – আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কোনো স্থায়ী মিত্র বা স্থায়ী শত্রু নেই, কেবল রয়েছে স্থায়ী স্বার্থ। কিন্তু এই ‘বাস্তববাদী’ প্যারাডাইম আপাতত দূরে সরিয়ে রাখা যাক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাষ্য অনুযায়ী, তুরস্ক মার্কিন সতর্কবাণী উপেক্ষা করে ন্যাটো জোটের শত্রুরাষ্ট্র রাশিয়ার কাছ থেকে ‘এস–৪০০ ত্রিউম্ফ’ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ক্রয় করেছে এবং নিজস্ব সশস্ত্রবাহিনীতে সিস্টেমটিকে অঙ্গীভূত করার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। মার্কিন সরকারের ভাষ্য অনুযায়ী, ‘এস–৪০০’ ক্ষেপণাস্ত্র ন্যাটোর সামরিক সরঞ্জামসমূহের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ক্ষেপণাস্ত্রটির রাডার অত্যাধুনিক মার্কিন–নির্মিত ‘এফ–৩৫’ যুদ্ধবিমানের তথ্য সংগ্রহ করে রুশদের কাছে পৌঁছে দেবে এবং এর ফলে ভবিষ্যতে মার্কিন সৈন্য ও সামরিক প্রযুক্তি রুশ হুমকির সম্মুখীন হবে। তদুপরি, তুরস্ক রাশিয়ার কাছ থেকে এই সিস্টেমটি ক্রয় করার ফলে রাশিয়া কয়েক বিলিয়ন ডলার লাভ করেছে এবং এর ফলে রুশদের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। এজন্য যুক্তরাষ্ট্র তুরস্কের ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে ‘বাধ্য হয়েছে’।
তুরস্ক কোন ধরনের পদক্ষেপ নিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেবে– সেটিও মার্কিন সরকার স্পষ্ট করেছে। তুরস্ক যদি ক্রয়কৃত ‘এস–৪০০’ ব্যাটারিগুলো পরিত্যাগ করে, বা অপর কোনো পক্ষের কাছে বিক্রি করে দেয়, বা সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় করে রাখে, এবং একই সময়ে যদি রাশিয়ার কাছ থেকে নতুন কোনো ভারী অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় না করে, তাহলে তুরস্কের ওপরে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়া হবে। অবশ্য, ইতিপূর্বে ‘এস–৪০০’ ক্রয়ের কারণে যুক্তরাষ্ট্র তুরস্ককে আরো একটি ‘শাস্তি’ প্রদান করেছে, আর সেটি হলো– মার্কিন ‘এফ–৩৫’ স্টেলথ যুদ্ধবিমান তৈরির যৌথ প্রকল্প থেকে তুরস্ককে বহিষ্কার করা হয়েছে।

কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তিধারায় ও কর্মকাণ্ডে বেশ কিছু ফাঁক রয়েছে।
প্রথমত, তুরস্ক ১৯৮০–এর দশক থেকেই উচ্চ প্রযুক্তির ও কার্যকরী এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম সংগ্রহ করার চেষ্টা করে আসছে, এবং তারা মূলত মার্কিন–নির্মিত অস্ত্র ক্রয় করতেই ইচ্ছুক ছিল। দীর্ঘদিন যাবৎ তুরস্ক মার্কিন–নির্মিত ‘প্যাট্রিয়ট’ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ক্রয় করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু মার্কিনিরা তুরস্কের কাছে এই সিস্টেম বিক্রি করতে রাজি হয়নি। ২০১৬ সালে তুরস্কে সংঘটিত ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানের (যেটির প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন ছিল বলে তুর্কি সরকার সন্দেহ করে) সময় এয়ার ডিফেন্সের ক্ষেত্রে তুরস্কের দুর্বলতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এসময় অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত বৈমানিকরা তুরস্কের রাষ্ট্রপতি ভবনের ওপর যুদ্ধবিমান থেকে বোমাবর্ষণ করে, কিন্তু এর বিরুদ্ধে কোনো কার্যকরী প্রতিরক্ষা গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি।
ফলে একপ্রকার বাধ্য হয়েই তুরস্ককে এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ক্রয়ের জন্য বিকল্প উৎসের দিকে ঝুঁকে পড়তে হয়েছে। ২০১৭ সালে তুরস্ক রাশিয়ার কাছ থেকে ‘এস–৪০০’ ক্ষেপণাস্ত্র ক্রয়ের জন্য ২.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এরপর থেকে মার্কিনিরা তুরস্ককে এই চুক্তি বাতিল করার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে শুরু করে, কিন্তু তুরস্ক মার্কিন চাপ উপেক্ষা করে। চুক্তি অনুযায়ী ২০১৯ সালের জুলাইয়ে রাশিয়া তুরস্ককে ‘এস–৪০০’ সরবরাহ করে, যার ফলশ্রুতিতে তুরস্ককে ‘এফ–৩৫’ প্রকল্প থেকে বের করে দেয়া হয়। এরপর ২০২০ সালের মার্চে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তুরস্ককে প্রস্তাব করে যে, তুরস্ক এস–৪০০ সিস্টেম পরিত্যাগ করলে যুক্তরাষ্ট্র তুরস্কের কাছে প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র বিক্রি করবে।
কিন্তু এই প্রস্তাব তুরস্কের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, এক ব্যাটারি এস–৪০০ সিস্টেমের মূল্য যেখানে প্রায় ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, সেখানে এক ব্যাটারি প্যাট্রিয়ট সিস্টেমের মূল্য প্রায় ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, অর্থাৎ রুশ সিস্টেমের প্রায় দ্বিগুণ! তদুপরি, প্যাট্রিয়টের তুলনায় এস–৪০০ একই সময়ে তিনগুণ বেশি লক্ষ্যবস্তুকে প্রতিহত করতে পারে, এবং প্যাট্রিয়টের তুলনায় এস–৪০০ এর পাল্লা পাঁচগুণ বেশি। এস–৪০০ সিস্টেমকে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে ব্যবহারের পাশাপাশি ‘নো ফ্লাই জোন’ সৃষ্টি এবং স্বল্প পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপনাস্ত্র হিসেবেও ব্যবহার করা সম্ভব। অর্থাৎ, এস–৪০০ প্যাট্রিয়টের তুলনায় আর্থিকভাবে সাশ্রয়ী, প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত এবং এর ব্যবহারও বহুবিধ। ফলে মার্কিন প্রস্তাব তুরস্কের জন্য মোটেই আকর্ষণীয় নয়।

অর্থাৎ, তুরস্ক যে রুশ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ক্রয় করেছে, সেটার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব নীতিই বহুলাংশে দায়ী।
দ্বিতীয়ত, মার্কিন সরকারের দাবি অনুযায়ী, এস–৪০০ সিস্টেমে ব্যবহৃত রাডারের মাধ্যমে মার্কিন এফ–৩৫ যুদ্ধবিমানের তথ্য রাশিয়ার কাছে পাচার হয়ে যাবে। কিন্তু কীভাবে এটি ঘটতে পারে, সেটি মার্কিন কর্মকর্তারা স্পষ্টভাবে বলেন নি। বিশ্লেষকরাও এই বিষয়টি নিয়ে একমত নন। কারো মতে, সত্যিই এস–৪০০ সিস্টেমের রাডার এফ–৩৫ এর তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে। আবার কারো কারো মতে, এটি আদৌ সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে একটি বিষয় উল্লেখ্য, এস–৪০০ সিস্টেম এখন পর্যন্ত কোনো যুদ্ধবিমানের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয় নি। সুতরাং, এই বিষয়ে স্পষ্ট কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া, রুশরা তুরস্কের কাছে যেসব এস–৪০০ বিক্রি করেছে, সেগুলো মূল এস–৪০০ নয়, বরং এর রপ্তানিযোগ্য সংস্করণ (export version)। এমতাবস্থায় এস–৪০০ সিস্টেম আদৌ এফ–৩৫ বিমানের তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে কিনা, কিংবা করলেও তুর্কি এস–৪০০ অপারেটররা যে নিশ্চিতভাবে রাশিয়াকে এই তথ্য সরবরাহ করবে– এই বিষয়গুলো অস্পষ্ট।
তৃতীয়ত, গ্রিস, ন্যাটোর আরেকটি সদস্য রাষ্ট্র, রুশ–নির্মিত ‘এস–৩০০’ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু এজন্য গ্রিসের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনো প্রকার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি। ওদিকে রুশ–নির্মিত এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ব্যবহার না করার জন্য তুরস্ককে চাপ প্রদান করা হচ্ছে– একে তুর্কিরা মার্কিনিদের ‘দ্বিচারিতা’ হিসেবে বিবেচনা করে। যদিও গ্রিসের এস–৩০০ হস্তগত করার প্রেক্ষাপট বহুলাংশে ভিন্ন (মূলত সাইপ্রাস রাশিয়ার কাছ থেকে এস–৩০০ ক্ষেপণাস্ত্র ক্রয় করেছিল এবং পরবর্তীতে তুরস্কের সঙ্গে এই নিয়ে গুরুতর সঙ্কটের প্রেক্ষাপটে সেগুলোকে গ্রিসের কাছে হস্তান্তর করেছিল), কিন্তু তুর্কিরা দুটি ঘটনাকে সমজাতীয় হিসেবে বিবেচনা করে।
সর্বোপরি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তুরস্কের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের কারণ হিসেবে ‘তুরস্ক কর্তৃক রুশ অস্ত্র ক্রয়’কে চিহ্নিত করেছে। এটি বাহ্যিক কারণ, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের এই সিদ্ধান্তের অন্তর্নিহিত কারণ হচ্ছে তুরস্কের ক্রমশ দৃশ্যমান হতে থাকা ‘কৌশলগত সার্বভৌমত্ব’ (strategic sovereignty)। তাত্ত্বিকভাবে, বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রেরই সার্বভৌমত্ব রয়েছে, অর্থাৎ নিজস্ব ইচ্ছা অনুযায়ী চলার স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু কার্যত কোনো রাষ্ট্রই পূর্ণ সার্বভৌমত্ব চর্চা করতে পারে না, কারণ প্রতিটি রাষ্ট্রেরই কিছু বাধ্যবাধকতা থাকে। ‘কৌশলগত সার্বভৌমত্ব’ বলতে কোনো রাষ্ট্রের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাজনৈতিক, সামরিক ও পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে বুঝানো হয়ে থাকে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ন্যাটো জোটের প্রধান সদস্য, এবং ন্যাটো জোটের অন্যান্য সদস্যদের ‘কৌশলগত সার্বভৌমত্ব’ বহুলাংশে সীমিত, কারণ তাদের রাজনৈতিক, সামরিক ও পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ন্যাটো জোটের (প্রকৃতপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের) নির্দেশনা অনুসরণ করতে হয়। ন্যাটোভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর কৌশলগত সার্বভৌমত্ব সীমিত হওয়ার কারণেই রুশ–প্রস্তাবিত ‘সাউথ স্ট্রিম’ পাইপলাইন প্রকল্প থেকে বুলগেরিয়াকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে, এবং মার্কিন তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের (Liquified Natural Gas, ‘LNG’) মূল্য রুশ গ্যাসের চেয়ে অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও পোল্যান্ডকে মার্কিন এলএনজি ক্রয় করতে হচ্ছে।
ন্যাটো জোটের অংশ হিসেবে তুরস্কেরও কৌশলগত সার্বভৌমত্ব ছিল সীমিত, এবং এই পরিস্থিতি বজায় রাখাই যুক্তরাষ্ট্রের জন্য কাম্য। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তুরস্ক ক্রমশ স্বতন্ত্রভাবে রাজনৈতিক, সামরিক ও পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শুরু করেছে, এবং এর হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, তুরস্ক ক্রমশ একটি কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হচ্ছে, যেটি যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের অনেকের কাছে পছন্দনীয় নয়। সামরিক ক্ষেত্রে, তুরস্ক স্বতন্ত্রভাবে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে আরম্ভ করেছে (এবং রাশিয়ার কাছ থেকে এস–৪০০ ক্রয় করেছে)। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে, তুরস্ক ন্যাটো সদস্য গ্রিস ও ফ্রান্স এবং মার্কিন মিত্র সৌদি আরব, ইমারাত ও ইসরায়েলের সঙ্গে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে, রাশিয়া, ইরান ও চীনের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়া বৃদ্ধি করেছে, এবং নিজস্ব একটি প্রভাব বলয় সৃষ্টি করতে শুরু করেছে।

২০২০ সালে তুর্কি পররাষ্ট্রনীতির দিকে যদি লক্ষ্য করা যায়, তাহলে দেখা যাবে, বেশ কয়েকবার বিভিন্ন রণক্ষেত্রে তুরস্ক ও রাশিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছে। সেই হিসেবে এই রণক্ষেত্রগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র ও তুরস্কের কার্যক্রম সমন্বিত হওয়াই যৌক্তিক ছিল। লিবিয়ার ক্ষেত্রে এটি আংশিকভাবে ঘটেছেও। তুরস্ক লিবিয়ায় চলমান গৃহযুদ্ধে ত্রিপোলিভিত্তিক ‘জাতীয় ঐক্যের সরকার’–এর (Government of National Accord, ‘GNA’) পক্ষে সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপ করেছে এবং ফ্রান্স, রাশিয়া, মিসর, ইমারাত, সৌদি আরব ও গ্রিসের সমর্থিত ‘লিবিয়ান ন্যাশনাল আর্মি’র (Libyan National Army, ‘LNA’) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। রাশিয়া ব্যতীত এলএনএর বাকি সমর্থক রাষ্ট্রগুলোর প্রত্যেকটিই যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র, কিন্তু নিজস্ব ভূরাজনৈতিক হিসেব থেকে যুক্তরাষ্ট্র এই যুদ্ধে তুরস্ককে মৌন সমর্থন প্রদান করেছে।
কিন্তু অন্যান্য স্থানে তুরস্কের স্বার্থের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের অসামঞ্জস্য দেখা দিয়েছে। সিরিয়ায় তুরস্ক ও যুক্তরাষ্ট্র উভয়ই সিরীয় সরকারের বিরোধী, কিন্তু তুরস্ক যেখানে ‘সিরিয়ান ন্যাশনাল আর্মি’ ও অন্যান্য মিলিট্যান্ট গ্রুপকে সমর্থন দিচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র সেখানে কুর্দি–নিয়ন্ত্রিত ‘সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্সেস’কে সমর্থন দিচ্ছে। কুর্দি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের তুরস্ক ‘সন্ত্রাসবাদী’ হিসেবে বিবেচনা করে, এবং তাদের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন তুর্কি–মার্কিন সম্পর্কে তিক্ততার সৃষ্টি করেছে। তদুপরি, সিরিয়া নিয়ে একটি সমঝোতায় পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে তুরস্ক রাশিয়া ও ইরানের সঙ্গে একটি ত্রিপক্ষীয় মেকানিজম সৃষ্টি করেছে, এবং এর ফলে যুক্তরাষ্ট্র এই সমীকরণ থেকে বাদ পড়ে গেছে।
অনুরূপভাবে, সাম্প্রতিক নাগর্নো–কারাবাখ যুদ্ধে তুরস্ক আজারবাইজানকে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছে, এবং তুর্কি–আজারবাইজানি জোট আর্মেনিয়াকে পরাজিত করে আজারবাইজানের অভ্যন্তরে আর্মেনীয়দের দখলকৃত ভূমির অধিকাংশ পুনর্দখল করেছে। আর্মেনিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে রাশিয়ার মিত্র, কিন্তু ২০১৮ সালে আর্মেনিয়ায় সংঘটিত ‘রঙিন বিপ্লবে’র পর আর্মেনিয়া মার্কিনপন্থী/পশ্চিমাপন্থী নীতি গ্রহণ করেছিল এবং রুশ প্রভাব হ্রাস করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। তুরস্কের উদ্যোগে আরম্ভ হওয়া এই যুদ্ধের ফলে আর্মেনিয়া পুনরায় রুশ বলয়ের গভীরে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে, এবং আজারবাইজান তাদের ভূমিতে রুশ সৈন্য মোতায়েন করতে দিতে সম্মত হয়েছে। এই যুদ্ধের ফলে নাগর্নো–কারাবাখ সমস্যা কার্যত রুশ–তুর্কি দ্বিপাক্ষীয় বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে, এবং ফলশ্রুতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের সহ–সভাপতিত্বে এই সমস্যার সমাধানে নিয়োজিত ‘ওএসসিই মিনস্ক গ্রুপ’ এই সমীকরণ থেকে ছিটকে গেছে।

পূর্ব ভূমধ্যসাগরে তুরস্ক ন্যাটো সদস্য ফ্রান্স ও গ্রিস এবং গ্রিসের মিত্র সাইপ্রাসের সঙ্গে সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধে লিপ্ত হয়েছে। ন্যাটো সদস্যদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বের ফলে জোটটির টিকে থাকা নিয়ে কিছুটা সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে, যদিও এখনো ন্যাটোতে কোনো গুরুতর সঙ্কট দেখা দেয়নি। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব ভূমধ্যসাগরে উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য তুরস্ককে দায়ী করেছে।
অর্থাৎ, তুরস্ক ক্রমশ তার ‘কৌশলগত সার্বভৌমত্বে’র পাল্লা বৃদ্ধি করে চলেছে, যেটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পছন্দনীয় নয়। রুশ–মার্কিন ভূরাজনৈতিক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে তুরস্কের ভৌগোলিক অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (যেহেতু তুরস্ক–নিয়ন্ত্রিত বসফরাস ও দার্দানেলিস প্রণালীদ্বয় ভূমধ্যসাগরে রাশিয়ার প্রবেশদ্বার) এবং এজন্য যুক্তরাষ্ট্র কোনোভাবেই তুরস্কের ওপর নিয়ন্ত্রণ হাতছাড়া করতে ইচ্ছুক নয়। তাই তুরস্কের ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যুক্তরাষ্ট্র দেশটিকে একটি প্রচ্ছন্ন বার্তা প্রদান করেছে– তুরস্কের পূর্ণ কৌশলগত সার্বভৌমত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাম্য নয়।
কিন্তু কিছু কিছু বিশ্লেষকের ধারণা, তুরস্কের ওপর মার্কিন অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞায় যুক্তরাষ্ট্রের জন্য হিতে বিপরীত হতে পারে। একে তো এই নিষেধাজ্ঞায় তুরস্ক কর্তৃক এস–৪০০ পরিত্যাগ করার সম্ভাবনা কম, তার ওপর তুর্কি প্রতিরক্ষা খাতের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা তুরস্ককে যুক্তরাষ্ট্র বাদে অন্যান্য অস্ত্র রপ্তানিকারক রাষ্ট্রের দিকে ঠেলে দিতে পারে। তদুপরি, নিষেধাজ্ঞার ফলে তুর্কি মিলিটারি–ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ঠিকই, কিন্তু একই সঙ্গে প্রতিরক্ষা খাতে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য তুরস্কের প্রচেষ্টাও বৃদ্ধি পাবে, যা তুরস্কের কৌশলগত সার্বভৌমত্বকে আরো মজবুত করবে। এর ফলে সামগ্রিকভাবে লাভবান হবে রাশিয়া এবং ক্ষেত্রবিশেষে চীন।
অবশ্য তুরস্ক যে এখনই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন করে পূর্ণ কৌশলগত সার্বভৌমত্ব অর্জন করতে চায়– এমনও নয়। ১৯৫০–এর দশক থেকে ন্যাটো জোট তুরস্কের জন্য রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে আসছে, এবং এই নিরাপত্তা বেষ্টনীকে হারাতে তুরস্ক ইচ্ছুক নয়। কারণ তুরস্ক যদি ন্যাটোর সদস্য না থাকে, তাহলে রাশিয়া ও অন্যান্য রাষ্ট্র তুরস্কের স্বার্থের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে, এবং তাদেরকে একাকী মোকাবিলা করা তুরস্কের পক্ষে সম্ভব হবে না। আর তুরস্ক যদি ন্যাটোর সদস্য হিসেবে থাকতে চায়, সেক্ষেত্রে তাকে আংশিকভাবে হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে।
বর্তমান মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে তুর্কি রাষ্ট্রপতি রেজেপ তাইয়্যিপ এরদোয়ানের সুসম্পর্ক ছিল এবং এজন্য সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তুরস্ক যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে বেশ কিছু ছাড় পেয়েছে। বস্তুত মার্কিন কংগ্রেস তুরস্কের ওপর যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, সেটি তারা করেছে ট্রাম্পের ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়ে। এদিকে বিশ্লেষকরা ধারণা করছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সদ্য নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি জোসেফ বাইডেন তুরস্কের প্রতি তুলনামূলকভাবে কঠোর নীতি অবলম্বন করবেন। উল্লেখ্য, যেদিন মার্কিন ইলেক্টোরাল কলেজ আনুষ্ঠানিকভাবে বাইডেনকে ২০২০ সালের মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিজয়ী হিসেবে ঘোষণা করেছে, সেদিনই মার্কিন কংগ্রেস তুরস্কের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

সম্প্রতি তুরস্ক বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, এবং এগুলোকে ভবিষ্যৎ বাইডেন প্রশাসনের প্রতি ইঙ্গিত হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। যেমন: আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে সাম্প্রতিক নাগর্নো–কারাবাখ যুদ্ধে আজারবাইজানি বিজয় উপলক্ষে আয়োজিত প্যারেডে এরদোয়ান একটি কবিতা আবৃত্তি করেছেন, যেটিতে ঊনবিংশ শতাব্দীতে আজারবাইজান ও ইরানি আজারবাইজানের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা বলা হয়েছে। সাম্প্রতিক যুদ্ধে আজারবাইজানি সাফল্যে ইরানি আজারবাইজানিদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ দেখা গেছে, এবং এজন্য এরদোয়ানের এই কবিতা পাঠকে ইরানি আজারবাইজানিদের ইরান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আজারবাইজানে যোগদানের প্রতীকী আহ্বান হিসেবে ইরান বিবেচনা করেছে। তদুপরি, ইরানি ভিন্নমতাবলম্বী হাবিব চাবকে অপহরণের দায়ে তুরস্কে ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
অনুরূপভাবে, সিরিয়ায় কুর্দি–নিয়ন্ত্রিত আইন আল–ইসা শহরটিকে রুশরা সিরীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, অন্যদিকে, তুর্কিরা শহরটির ওপর গোলাবর্ষণ করছে। একই সময়ে তুরস্ক ও ইউক্রেনের মধ্যে সামরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ইউক্রেন তুরস্কের কাছ থেকে ‘বায়রাকতার টিবি২’ ড্রোন ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। ইউক্রেনীয় ও অন্যান্য প্রচারমাধ্যমে প্রচারণা চালানো হচ্ছে, আজারবাইজান যেভাবে তুর্কি ড্রোনের সহায়তায় নাগর্নো–কারাবাখ ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চল পুনর্দখল করেছে, ইউক্রেনও অনুরূপভাবে পূর্ব ইউক্রেনের হারানো অঞ্চল পুনর্দখল করবে।
অন্যদিকে, সম্প্রতি এরদোয়ান সৌদি আরবের সঙ্গে চলমান দ্বন্দ্বের মাত্রা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে সৌদি বাদশাহ সালমানের সঙ্গে ফোনে আলোচনা করেছেন এবং বাহরাইনের আমিরের নিকট ফোনে সেদেশের প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুতে শোকবার্তা প্রদান করেছেন। একই সময়ে তুরস্ক ইসরায়েলে একজন নতুন রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করেছে, যে পদটি কয়েক বছর যাবৎ খালি ছিল।
ধারণা করা হচ্ছে, আসন্ন বাইডেন প্রশাসন যাতে তুরস্কের প্রতি বেশি কঠোর নীতি অবলম্বন না করে, সেজন্য তুরস্ক ইরান ও রাশিয়ার ওপর চাপ বৃদ্ধি করছে এবং মার্কিন মিত্র সৌদি আরব, বাহরাইন ও ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এমতাবস্থায় তুরস্ক হয়তো নিষেধাজ্ঞার ভয়ে এস–৪০০ সিস্টেম পরিত্যাগ করবে না (যেহেতু এটি তুরস্কের জন্য ‘মর্যাদার বিষয়’ হয়ে দাঁড়িয়েছে), কিন্তু এটি স্পষ্ট যে, তাদের ‘কৌশলগত সার্বভৌমত্বে’র একটি নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে এবং এজন্য তুরস্কের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার ফলে তুর্কি–মার্কিন সম্পর্কের আংশিক অবনতি ঘটলেও তুরস্কের সহসা মার্কিন বলয় ত্যাগ করার এখনো কোনো সম্ভাবনা নেই।