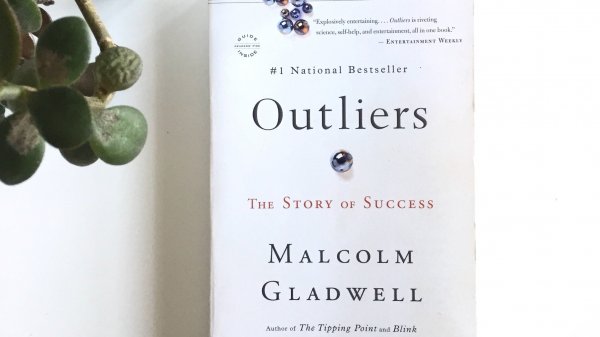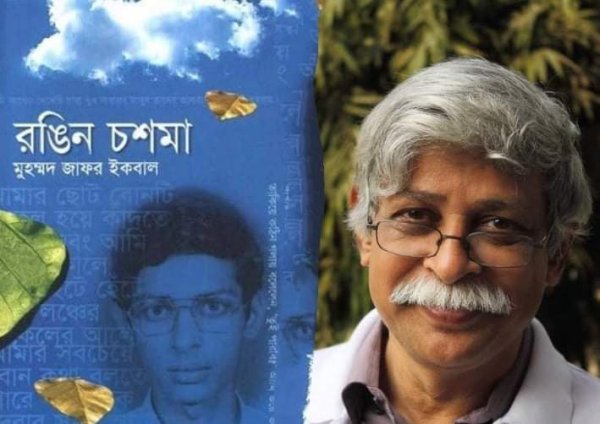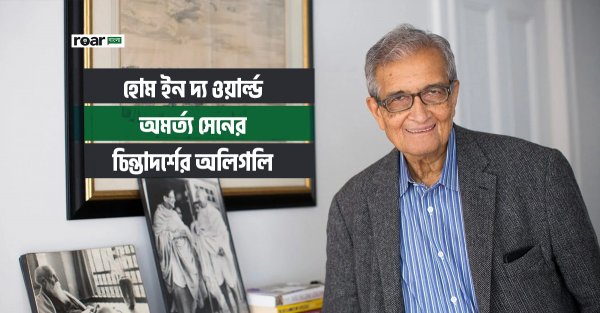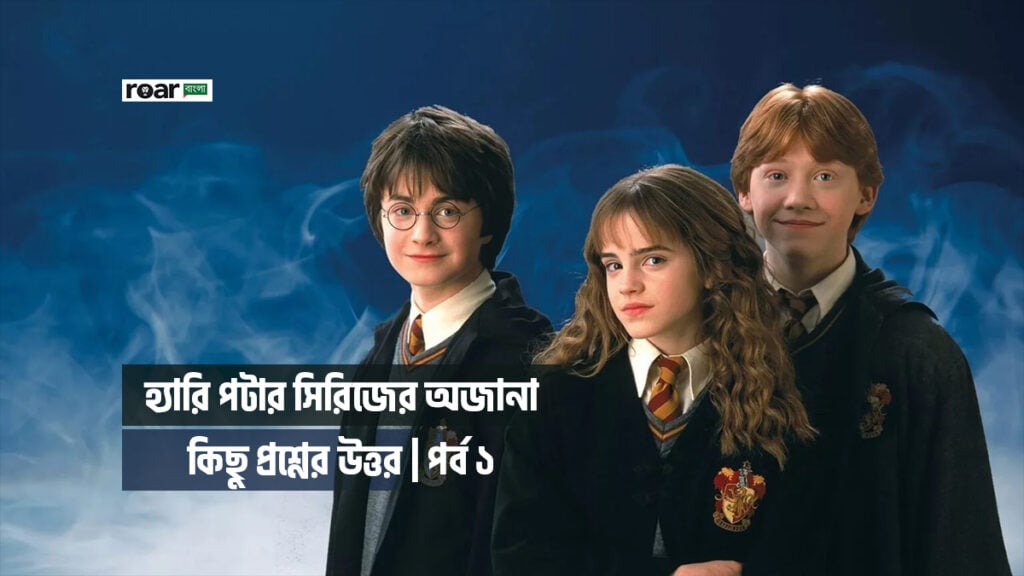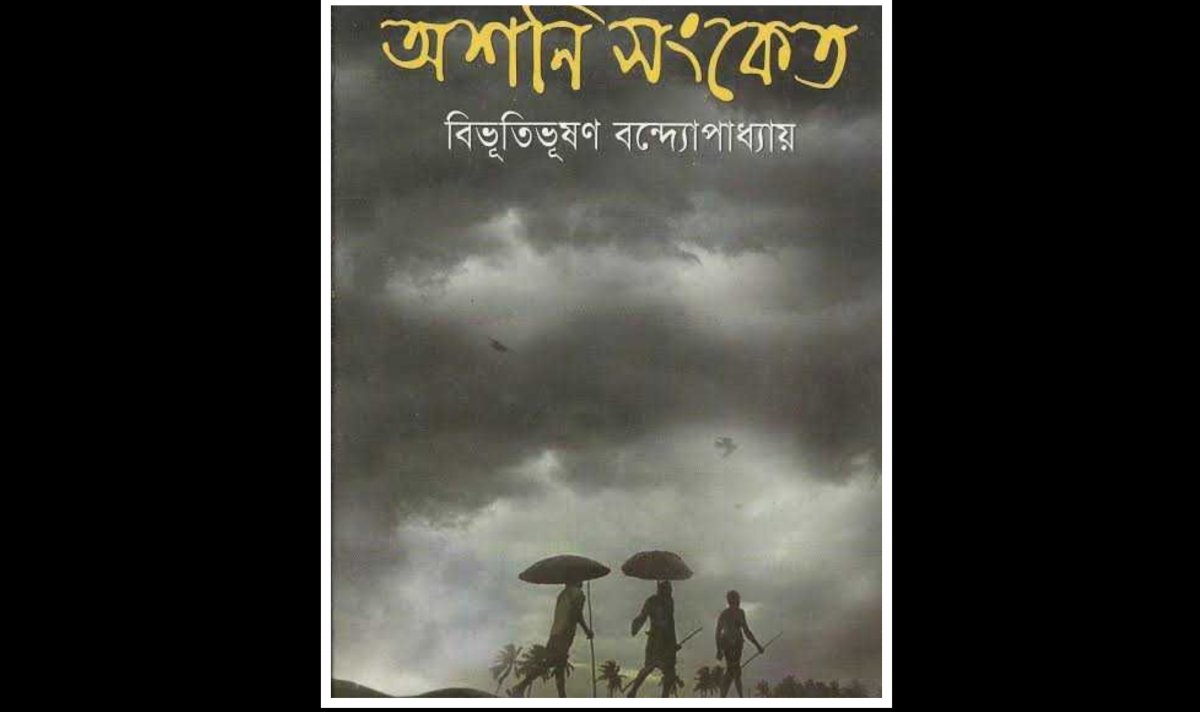
১৯৪৩ সাল। বাংলার ইতিহাসে কুখ্যাত, ১৭৫৭’র পরে সবচেয়ে বড় মন্বন্তরের কারণে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। জাপানি সেনারা দখল করে নিয়েছে ব্রহ্মদেশ মায়ানমার। সিঙ্গাপুরের মতো মায়ানমারেও ইংরেজ শক্তির পরাজয় সুনিশ্চিত। মায়ানমার হয়ে শত্রুসেনারা যদি ভারতবর্ষ আক্রমণ করে? প্রধানমন্ত্রী ডব্লিউ চার্চিল নিলেন এক ভয়ংকর পরিকল্পনা— স্কর্চড আর্থ (Scorched Earth); শত্রুকে ঘায়েল করতে হবে এমন সব জিনিসকে ধ্বংস করে, যা তাদের জন্য দরকারি, তাদের জন্য অপরিহার্য।
এরই অংশ হিসেবে ব্রিটিশ প্রশাসন নৌব্যবস্থা বন্ধ করে দিল। ভেঙে পড়ল কৃষি যোগাযোগ। সেনাসদস্যদের জন্য সকল জায়গা থেকে মজুদ করা হতে থাকল খাদ্যশস্য। উপরন্তু জাপানি সৈন্যরা যাতে কোনোভাবে চালের নাগাল না পায়, সেজন্য বাজেয়াপ্ত করা হলো গুদামগুলো। চাল আমদানি বন্ধ হয়ে গেলো বার্মা থেকে। খাদ্যদ্রব্যের দাম হু হু করে বাড়তে থাকলো বাজারে, গ্রামাঞ্চলে দেখা দিল নিদারুণ খাদ্যসংকট। সর্বোপরি, বাংলার ভাগ্যাকাশে দেখা দিলো দুর্ভিক্ষের ঘনঘটা। খাবারের হাহাকারে প্রাণ গেলো প্রায় পঞ্চাশ লাখ মানুষের; পথে প্রান্তরে লুটিয়ে পড়তে লাগল না খেতে পাওয়া হাড্ডিসার মানবদেহ। দুর্ভিক্ষের এই ভয়াল প্রেক্ষাপটে গ্রামজীবনের করুণ আখ্যান নিয়ে রচিত হয়েছে অমর কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘অশনি সংকেত’।

একথা বলাই বাহুল্য যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়(১৮৯৪-১৯৫০) বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে একজন। বাংলা সাহিত্যে ধূমকেতুর মতো তার আবির্ভাব যেমন আকস্মিক, তেমন বিস্ময়কর। তার কালোত্তীর্ণ সৃষ্টি ‘পথের পাঁচালী’ কিংবা ‘অপরাজিত’ চিরায়ত বাঙালি জীবনে উপন্যাসরূপে যেন যথার্থ মহাকাব্য। তিনি যখন ‘অশনি সংকেত’ রচনায় হাত দেন, তখন তার বয়স প্রায় পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই। তখন তিনি পথের পাঁচালী, অপরাজিত এবং আরণ্যকের প্রথিতযশা সাহিত্যিক। রেডিও বক্তৃতা উপলক্ষে সেসময় বিভূতিভূষণ এসেছিলেন কলকাতায়। ঘাটশিলায় থাকার কারণে তেতাল্লিশের মন্বন্তরের মর্মান্তিক রূপ তার জানা ছিল না, কলকাতায় তার মারাত্মক রূপ দেখে তিনি মর্মাহত হন বিশেষভাবে। আপন অভিজ্ঞতায় এই মর্ম বেদনা থেকেই জন্ম হয় ‘অশনি সংকেত’—এর।
উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ‘মাতৃভূমি’ পত্রিকায়, ১৩৫০ বঙ্গাব্দের মাঘ থেকে। ১৩৫৪-তে পত্রিকাটির অবলুপ্তির সাথে সাথে ‘অশনি সংকেত’-এরও প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। বিভূতিভূষণ উপন্যাসটির সম্পূর্ণ প্রকাশ দেখে যেতে পারেননি। অনেক সমালোচক অবশ্য এর সাদামাটা পরিসমাপ্তির জন্য উপন্যাসটিকে বিভূতিভূষণের ক্লাসিক উপন্যাসের স্বীকৃতি দিতে নারাজ। এই উপন্যাস অবলম্বনে চিত্রনাট্য তৈরি করে ১৯৭৩ সালে সত্যজিৎ রায় ঐ নামেই চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। চলচ্চিত্রটি বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ ছবির স্বীকৃতিসহ বেশ কয়েকটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করে।

উপন্যাসের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে একটি প্রান্তিক গ্রাম্য পরিবারকে ঘিরে। পরিবারের কর্তা গঙ্গাচরণ কুলীন ব্রাহ্মণ—পাড়াগাঁয়ের একমাত্র উচ্চবর্গীয় ব্রাহ্মণসন্তান। দুই সন্তান এবং স্ত্রী অনঙ্গকে নিয়ে তার বাস। সে দরিদ্র, তবে শিক্ষিত এবং একই সাথে চতুর। টোলে ছাত্র পড়িয়ে, কবিরাজি করে, যজমানের বাড়িতে পূজা করে তার আয়-রোজগার। গ্রামের সকলেই তাকে সমীহ করে চলে, যেকোনো দরকারে ব্রাহ্মণসেবা করে পুণ্য অর্জনে তারা সদা সচেষ্ট। সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা সেই অজপাড়াগাঁয় একসময় দেখা দিল দুর্যোগের করাল ছায়া। গ্রামবাসী জানল, যুদ্ধ শুরু হয়েছে। গোলাভরা ধান, নদীভরা মাছ, ক্ষেতভরা সবজি—গ্রামীণ প্রাচুর্যের ভেতর বেড়ে ওঠা গ্রামবাসী, দু’মুঠো ভাতের জন্য যে মানুষ অনাহারে মারা যেতে পারে—এ কথা যাদের কল্পনাতেও কখনো আসেনি, তারাই দেখল হু-হু করে বেড়ে যাচ্ছে চালের দাম।
এক মণ ধান চার টাকা থেকে লাফিয়ে হলো চব্বিশ টাকা, আবার পরশুই দাঁড়ালো চল্লিশ টাকায়। শূন্য হলো গুদামভরা পাহাড় সমান চালের সারি সারি বস্তা। যারা একদিন স্বপ্রণোদিত হয়ে মাছ, সবজি এনে ব্রাক্ষণকে সেবা দিত, তারাই দু’মুঠো চালের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরতো লাগল গ্রামের পর গ্রাম। গুদাম লুট, খুনোখুনি পর্যন্ত হতে লাগলো গ্রামে। গঙ্গাচরণের হাঁড়িতেও টান পড়লো— এবেলা কোনোমতে খাবার জোটে, তো ওবেলা আখা জ্বলে না। আধপেটা খেতে পাওয়াও যেন মহামূল্য বস্তু হয়ে ওঠে তাদের কাছে। উজাড় হতে লাগল গ্রামকে গ্রাম, আহারের তাড়নায় অভাবী গঙ্গাচরণের বাড়িতেই আশ্রয় নিতে লাগল ক্ষুধায় জীর্ণ-শীর্ণ পরিচিতজনেরা। পিতা-মাতার দুঃখ, আক্ষেপ আর দীর্ঘশ্বাস বাড়িয়ে এরই মধ্যে অনঙ্গের কোলে এলো তৃতীয় সন্তান।
গাঁয়ে দুর্ভিক্ষের দাবানলে যেদিন মতি নামের মেয়েটির চিতা প্রথম জ্বলে উঠল, সেদিন মানুষ বুঝতে পারল মূর্তিমান বিপদের সংকেত— দুর্ভিক্ষের দাবানলে ছাই হয়ে উড়ে যাওয়ার, লক্ষ মানুষের জন্য বিনাশের অশনি সংকেত। নিস্তেজ-নিস্তরঙ্গ ব্রাহ্মণ পরিবারকে রেখে জঠরজ্বালা নিবারণের নিমিত্তে অনিশ্চিতের পথে গ্রামবাসীর যাত্রার সংবাদেই শেষ হয় এ উপন্যাসের কাহিনী। দুর্ভিক্ষের দাবানলে এভাবে এক সহায়-সম্বলহীন দরিদ্র ব্রাক্ষ্মণ পরিবারের বেঁচে থাকার লড়াই উপস্থাপনের মাধ্যমে বিভূতিভূষণ পাঠকদের নিয়ে গেছেন সেই কঠোর সময়ে।

বিভূতিভূষণ দুর্ভিক্ষ নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বক্তব্য রেখেছেন। আক্ষেপ করে বলেছেন,
“এত বড় মন্বন্তর ঘটে গেল বাংলাদেশে, অথচ চিত্রে ও রঙ্গমঞ্চে আমরা তার কী ছবি পেলাম? আমরা পেলাম নায়িকার নাকে কান্না, প্যানপ্যানানি গান, মিষ্টি মিষ্টি কথায় নায়কের প্রেম নিবেদন আর মান্ধাতার আমলের যাত্রাপালার ট্রাডিশনে কতগুলো পৌরাণিক নাটক!”
স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য তার এই অন্তর্ভেদী আক্ষেপ এবং একইসাথে একটি সচেতন ও স্বদেশী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় ‘অশনি সংকেত’—এ। দুর্ভিক্ষের আগমনের আগের সময়টি, দুর্ভিক্ষ এবং তৎপরবর্তী সময়ের চিত্র সত্যিই চমৎকার ফুটিয়েছেন বিভূতিভূষণ। উপন্যাসটি শুরু হয়েছে জলাধারে অনঙ্গের সাথে জনৈক গ্রামীণ নারীর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে, যেখানে নারীটি দেবী আসনে বসিয়ে অত্যন্ত মর্যাদা দিয়ে কথা বলছে তার সাথে। টোলে পড়িয়ে, মাতব্বরদের সাথে ওঠাবসা করে গ্রামে ধীরে ধীরে গঙ্গাচরণের পসার বাড়ছে, সংসারে মোটামুটি সাচ্ছল্য আসছে— এমন অবস্থায় একদিন গঙ্গাচরণ শোনেন যুদ্ধের কথা। গ্রামান্তরে পুরোহিত দীনু ভট্টাচার্য সাহায্য চাইতে আসে তার কাছে, চালের দাম নাকি বাড়ছে ক্রমেই। প্রথমে বিশেষ গা না করলেও তার অবস্থা সঙ্গিন হয়, যখন একদিন সে বাজারে চাল লুটের মধ্যে গিয়ে পড়ে।
গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থ বিশ্বাস মশাইয়ের উপর আক্রমণ হয় একসময়, তিনি গ্রাম ছাড়েন। অভাবের দিনে গঙ্গাচরণ হারিয়ে ফেলেন তার শেষ আশ্রয়স্থলটুকুও। এভাবে শান্ত ভুজঙ্গের ন্যায় দুর্ভিক্ষের এগিয়ে আসা, ঘনিয়ে ধরা, তার শ্বাসরোধ করা চাপ এবং তার প্রাণান্তক ছোবল স্তরে স্তরে গঙ্গাচরণের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে বাঙ্ময় করে তুলেছেন বিভূতিভূষণ, তার মায়াময় বর্ণনায়। বিভূতিভূষণের চরিত্রচিত্রণের কুশলতার তারিফ না করে পারা যাবে না। এই ক্লেশ, এই সমস্যার মধ্যেও গৃহলক্ষ্মী অনঙ্গ চরিত্রে তিনি চিরায়ত বাঙালি রমণীর প্রতিমূর্তি তুলে ধরেছেন, যে কি না অতিথিপরায়ণ। অতিথিসৎকারে কোনো অভাব-অনটন যার জন্য বাধা নয়, নিজে না খেয়ে হলেও অতিথিকে সেবা করার ব্যপারে সে দ্ব্যর্থহীন—স্বয়ং শ্রীলক্ষ্মী। কিছুটা সুখ এবং একইসঙ্গে আক্ষেপের সুরে তাই আমরা গঙ্গাচরণকে স্ত্রীর বিষয়ে বলতে শুনি,
“ওর সঙ্গে মিছে তর্ক করে কোনো লাভ নেই। মুখের ভাত অপরকে ধরে দিতে ও চিরকাল অভ্যস্ত। অনঙ্গ মুখ ফুটে বলবে না কখোনো— কি খেয়েচে, না খেয়েচে। এমন স্ত্রী নিয়ে সংসার করা বড় মুশকিলের কাণ্ড!”

আগেই বলেছি, দুর্ভিক্ষের মর্মন্তুদ বিবরণই মূলত উপন্যাসটির মূল উপজীব্য। দুর্ভিক্ষ যে কতটা শক্তিশালী, কতটা অনভিপ্রেত, ক্ষুধাতাড়না— জীবনপথে তা কত বড় পটপরিবর্তনের সূচনা করতে পারে— এই উপন্যাসে অন্তর্বেদনা, সহমর্মিতায় অথচ কঠোর বাস্তব ও একইসঙ্গে মায়ামাখানো গ্রামবাংলার জীবনের রূপের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন বিভূতিভূষণ। সময়টা ছিল এমনি, যে অখণ্ড বাংলার মানুষের স্বপ্ন তখন অর্থ, অট্টালিকা আর প্রতিষ্ঠা নয়, শুধু দু’মুঠো চাল। একটু ভাতের ফেনের জন্যে উলঙ্গ-জীর্ণদেহী নারী-পুরুষ ভিক্ষা করে বেড়ায় বাড়ি-বাড়ি গিয়ে, ভেতো বাঙালি কীভাবে অভাবের তাড়নায় ভাত ছেড়ে কচু, মেটে আলু, জংলি শাক খেতে শুরু করে, সেটাও জোটাতে না পেরে যোগাড় করে গুগলি, শামুক, ঝিনুক খায়— তার হৃদয়গ্রাহী বিবরণ আমরা পাই এ লেখায়। উপন্যাসটি আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে, যখন আমরা দেখি, ভাতের জন্য কাপালীদের ছোট বউ নিজের শরীর বিকিয়ে দেয় পরপুরুষের কাছে।
এভাবেই উপন্যাসটিতে পাঠক দুর্ভিক্ষের জীবন্ত এবং সর্বগ্রাসী রাক্ষসরূপ দেখতে পাবেন, মনুষ্যত্বের অন্তঃস্থল থেকে— সংবেদনশীল ও মানবিক মানুষের হৃদয়ে যা হাহাকার জাগাতে বাধ্য। এই উপন্যাস পড়ার পর বোধকরি মুখের খাবার নষ্ট করা কঠিনই হয়ে পড়বে!
অনলাইনে বইটি সংগ্রহ করতে ক্লিক করতে পারেন নিচের লিঙ্কে:
১) অশনি সংকেত