
আমাদের অনুসন্ধিৎসু মনে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে বৈচিত্র্যময় সব প্রশ্ন খেলে যায় প্রতিনিয়ত। মনস্তাত্ত্বিকভাবেই আমরা সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে ভাবতে পছন্দ করি। স্রষ্টা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনার একটা প্রান্তে গিয়ে তাঁর অস্তিত্ব আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে এমন চিন্তাভাবনা ও অনুসন্ধান-প্রবণতার পেছনে আমাদের বয়স, সমাজ, রাষ্ট্র এবং অভিজ্ঞতা ইত্যাদির প্রভাবই কি শুধু দায়ী? নাকি সৃষ্টির অস্তিত্বের মাঝেই রয়েছে স্রষ্টাকে অনুসন্ধান করার মজ্জাগত স্বভাব? ঠিক এমন দ্বান্দ্বিক একটি চিত্রকে বিশ্লেষণ করে গড়ে উঠেছে পৃথিবীর প্রথম দর্শনভিত্তিক উপন্যাস ‘হাই ইবনে ইয়াকজান’। এর পটভূমি হলো ভারত মহাসাগরের জনমানবহীন একটি দ্বীপ। যে দ্বীপে পশুপাখির সাথে সখ্যতা নিয়ে বেড়ে উঠে একটি মানবশিশু। যার নাম হাই ইবনে ইয়াকজান বা ইয়াকজান তনয় হাই।

হাই ইবনে ইয়াকজানের প্রচ্ছদ; Source: goodreads.com
বইটির প্রভাব
বইটির কাহিনী বর্ণনার আগে বরং বইটির প্রভাব নিয়েই আলোচনা করি। ‘হাই ইবনে ইয়াকজান’ আজ থেকে ৯০০ বছর আগের অর্থাৎ ১২ শতকে লেখা একটি উপন্যাস। এটি বিশ্ব সাহিত্যের প্রথম দর্শনভিত্তিক উপন্যাস। ১২ শতকের উপন্যাস হলেও এই বইটি ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগে (১৬৫০-১৮০০) প্রভাবক হিসাবে কাজ করেছিলো। যেসব বই ইউরোপে বিজ্ঞান বিপ্লব এবং ইউরোপকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করার পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছিল সেসব বইয়ের মধ্যে এই বইটি অন্যতম। শুধুমাত্র যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে কিভাবে স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভব করা যায় তার দার্শনিক ও কাল্পনিক এ উপাখ্যানকে সেই সময়ের দার্শনিকেরা ‘ফিলোসফাস অটোডিডাকটাস’ নামে স্বতন্ত্র তত্ত্ব হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন।

ইবনে তোফায়েলের প্রতীকী ছবি; Source: alcala2016.org
ইবনে তোফায়েল ১১৬০ সালে মারাক্কেসে আরবি ভাষায় এই বইটি রচনা করেন। ১৪ শতকে মোসেস রাব্বি নারবোনেনসিস বইটি হিব্রু ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৪৯২ সালে ‘মেনিফেস্টো অফ রেনেসার’ রচয়িতা ইতালীয় দার্শনিক জিওভান্নি পিকো ডেল্লা মিরানডোলা (১৪৬৩-১৪৯৪) বইটির সর্বপ্রথম ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। পরে ১৬৫৩ সালে বিখ্যাত ব্রিটিশ প্রাচ্যবিশারদ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এডওয়ার্ড পোকোক জুনিয়র (১৬৪৮-১৭২৭) এবং আরবি ভাষায় একজন পণ্ডিত এই উপন্যাসটি সরাসরি আরবি থেকে ‘ফিলোসফাস অটোডিডাকটাস’ নামে ল্যাটিনে অনুবাদ করেন।
১৬৭১ সালে বইটি আরবি টেক্সটসহ অক্সফোর্ড থেকে প্রকাশিত হলে পুরো ইউরোপের বুদ্ধিজীবী মহলে হৈচৈ ফেলে দেয়। তখন যুক্তি ও বিজ্ঞান বিকাশের হাওয়া পুরোদমে বইছিল। দার্শনিক জন লক তার ‘এন এ্যাসে কনসার্নিং হিউম্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং’ (১৬৮৯) বইয়ে এই ধারণার কথা প্রকাশ করলে হাই ইবনে ইয়াকজানের তিনটি ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। জার্মান দার্শনিক লিবনিজ (১৬৪৬-১৭১৬) ও ডাচ-ইহুদি দার্শনিক স্পিনোজা (১৬৩২-১৬৭৭) উভয়ই এর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। স্পিনোজার উৎসাহে এর সফল ডাচ অনুবাদ (বাউমিস্টার, আম্সটার্ডাম ১৬৭২) এবং লিবনিজের কারণে দুটি জার্মান অনুবাদ সম্ভব হয়।
সাইমন ওকলের ইংরেজি অনুবাদ ‘দ্য ইমপ্রুভমেন্ট অব হিউম্যান রিজন: এগজিবিটেড ইন দ্য লাইফ অব হাঈ ইবন ইয়াকজান’ প্রকাশিত হওয়ার ১১ বছর পর ১৭১৯ সালে ডানিয়েল ডেফো এটি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস ‘রবিনসন ক্রুসো’ (১৭০৮) রচনা করেন। এখানেও একটি জনমানবহীন দ্বীপের বর্ণনা রয়েছে। এর সাথে হাই ইবনে ইয়াকজানের ধারাবাহিকের মিলের কথা লেখক এন্টনিও প্যাস্টর ‘দি আইডিয়া অফ রবিনসন ক্রুসো’ বইয়ে (১৯৩০) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এই ক্লাসিক উপন্যাসে হাই ইবনে ইয়াকজানের লেখক ইবনে তোফায়েলের পদচিহ্ন সহজেই শনাক্ত করা সম্ভব। উল্লেখ্য, বইটির প্রভাবের ক্ষুদ্রাংশ এখানে খুবই সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হলো। গভীরভাবে জানার জন্য রেফারেন্সের লিঙ্কগুলোতে প্রবেশ করতে হবে।
সারনির্যাস
নিরক্ষীয় অঞ্চলের কাছেই ভারত মহাসাগরের একটি দ্বীপে হাই ইবনে ইয়াকজানের বেড়ে ওঠা। সেই দ্বীপদেশে জন মানুষের কোনো চিহ্ন ছিলো না। চতুর্দিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বেষ্টনী আর বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর মাঝে সেই দ্বীপটিতে হাই ইবনে ইয়াকজান বড় হতে থাকেন। শিশু হাইকে প্রথমে একটি মা হরিণ দুগ্ধ পান করিয়ে লালন পালন করতে থাকে। হরিণটির কাছে মাতৃস্নেহে তিনি বড় হতে থাকেন। অন্যান্য প্রাণীদের সাথেও তার বেশ সখ্যতা গড়ে ওঠে। প্রাণীদের সাথে তিনি যোগাযোগব্যবস্থা গড়ে তোলেন। প্রাণীদেরকে তিনি বুঝতে পারতেন, আর তাকেও প্রাণীরা বুঝতো।

হরিণ মাতার সাথে ইয়াকজান; Source: elifsanat.com
একদিন তিনি একটি লাঠি খুঁজে পান। লাঠির কাজ কী তা তিনি জানতেন না। পরে তিনি এই লাঠির কাজ ও নিজের দুটি হাতের গুরুত্ব অনুধাবন করেন। লাঠি ও হাতের গুরুত্ব অনুধাবনের মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে শিকারীরূপে আবিষ্কার করেন। একদিন তার মা হরিণটি মারা যায়। মা হরিণের মৃত্যু নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনায় নিমগ্ন হন। মায়ের মৃত্যুর কারণ খুঁজতে থাকেন তিনি।
এভাবে মা হরিণটির মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তিনি প্রাণীর মৃত্যু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেন। মৃত্যুর কারণ খুঁজতে গিয়ে ধারালো প্রস্তর খন্ড দিয়ে মা হরিণটির দেহ ব্যবচ্ছেদ করতে থাকেন। দেহ ব্যবচ্ছেদ করতে গিয়ে তিনি এই ধারণায় উপনীত হন যে, আত্মা হচ্ছে প্রাণীর সমগ্র দৈহিক অঙ্গের চালিকাশক্তি এবং এমন এক অদৃশ্য শক্তি যা মৃত্যুর পর প্রাণীদেহ ত্যাগ করে চলে যায় অন্যত্র। দেহ ব্যবচ্ছেদের মধ্য দিয়ে তিনি জীববিজ্ঞানের জ্ঞান লাভ করেন। যখন মৃত হরিণীর দেহ ক্রমশ শুকাতে থাকে তখন তিনি দাঁড়কাক থেকে এ শিক্ষাও পেলেন যে, মৃতদেহকে মাটিতে পুঁতে রাখতে হয়।

প্রতীকী ছবি; Source: elifsanat.com
একসময় তিনি আবিষ্কার করলেন, শুকনো ডালের ঘর্ষণের ফলে মৃত গাছে আগুন জ্বলে ওঠে। তিনি এক খণ্ড আগুন নিজের বাসস্থানে এনে ঘর আলোকিত করার পন্থা আবিষ্কার করেন। আগুনের স্পর্শে তাপ অনুভবের কারণ ও এর মর্মভেদ নিয়ে ভাবতে থাকেন। এভাবে ইয়াকজান বড় হতে থাকেন এবং তার দক্ষতাও দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি প্রাণীদের চামড়া দিয়ে নিজের জুতা ও পোশাক বানাতে শেখেন। তাদের পশম ও শন ব্যবহার করতে শেখেন।

ইয়াকজানের প্রতীকী ছবি; Source: elifsanat.com
পালকযুক্ত প্রাণীর গৃহ নির্মাণ দেখে তিনি বুঝতে পারেন কিভাবে গৃহ নির্মাণ করতে হয়। শিকারের জন্য তিনি শিকারী পশুকে প্রশিক্ষণ দেন। পাখির ডিম ও পশুর শিং এর ব্যবহারিক গুরুত্ব ধীরে ধীরে বুঝতে পারেন। তারকা গণনাও আয়ত্ব করে ফেলেন ইয়াকজান। এভাবে বুদ্ধি বিবেচনা প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাকৃতিক নিয়মে একের পর এক নতুন নতুন বিষয় সম্পর্কে জানতে পারেন। হাই ইবনে ইয়াকজান যখন ৩০ বছর বয়সে উপনীত হন তখন একজন সাধক সেই দ্বীপে সাধনা করতে আসেন। তখন হাই ইবনে ইয়াকজান প্রথমবার নিজের মতো একজন মানুষের দেখা পান।
তার এই ৩০ বছরের জীবনের সমস্ত শিক্ষা তাকে জ্ঞানের এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যায়, যে জ্ঞান সাধারণত একজন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানী অর্জন করে থাকেন। তার এই জ্ঞান অর্জনের পেছনে কোনো মানুষের অবদান ছিলো না। সম্পূর্ণ জ্ঞানই ইয়াকজান প্রকৃতি থেকে শিখেছেন। প্রাণী, পরিবেশ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি নিয়ে তার ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ একপর্যায়ে তাকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত করে যে, এই সবকিছুর পেছনে রয়েছেন একজন মহান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব, যিনি মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন।

চিন্তিত ইয়াকজান; Source: elifsanat.com
ফিলোসফাস অটোডিডাকটাস
এই গল্পে রয়েছে গভীর দার্শনিক প্রভাব, যার নাম ফিলোসফাস অটোডিডাকটাস। দর্শনে এই টার্মটির সৃষ্টি হয়েছে ইবনে তোফায়েল রচিত হাই ইবনে ইয়াকজান বইটির প্রভাবেই। ফিলোসফাস অটোডিডাকটাস মানে হলো স্বশিক্ষায় দর্শনলাভ। অর্থাৎ একটি নিষ্পাপ মনের নিজ ক্ষমতায় ক্রমান্বয়ে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হওয়ার ধারণাকে বলে ফিলোসফাস অটোডিডাকটাস। গল্পের হাই ইবনে ইয়াকজানের নির্দিষ্ট ধর্ম ছিল না কোনো। সে না মুসলমান, না খ্রিস্টান, না ইহুদী। তার বর্ণ নিয়েও তার কোনো ধারণা ছিলো না। সে আমাদের মতো সমাজের বাইরের এক প্রাণীসমাজে পিতামাতা, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, মনুষ্য সমাজ এবং কোনো ধর্মীয় গুরুর সহায়তা ছাড়া নিজে নিজেই বড় হয়েছে।
অথচ দ্বীপের প্রাণী, পরিবেশ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও পরিস্থিতিগত ঘটনাবলীর গভীর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞানের এমন এক মাত্রায় উপনীত হয়েছে যা সাধারণত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীরা অর্জন করে থাকেন। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যময়তার মধ্যে সূক্ষ্ম আন্তঃসম্পর্ক তাকে সামগ্রিক ঐক্যের বা কেন্দ্রীভূত শক্তি নিয়ে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে। সবকিছুর মধ্যে জড় ও আধ্যাত্মিক ব্যাপার খুঁজে পায় সে। এবং এ সবকিছুর পেছনের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে সে একজন পরমাত্মার পবিত্র অস্তিত্ব অনুভব করে। এভাবে হাই ইবনে ইয়াকজান প্রকৃতি থেকে বিজ্ঞানে, বিজ্ঞান থেকে দর্শনে প্রবেশ করে এবং পরিণামে পরমাত্মার জ্ঞান ও মরমীবাদে নিজেকে উৎসর্গ করে তথাকথিত কোনো গুরু ছাড়াই।

সেই দ্বীপের কাল্পনিক ছবি; Source: felsefen.com
ফিলসফাস অটোডিডাকটাসের মূল বিষয় অবলম্বনে আরো যে কয়টি বিখ্যাত বই আছে সেগুলো হলো ব্রিটিশ দার্শনিক ও রসায়নবিদ রবার্ট বয়েলকের (১৬২৭-১৬৯১) ‘দি এসপায়ারিং নেচারালিস্ট’ রচনায় অনুপ্রাণিত করে যার পটভূমিও একটি দ্বীপ। পরবর্তীকালে সুইস দার্শনিক ও লেখক জাঁ-জ্যাকুইস রুশোর (১৭১২-১৭৭৮) ‘এমিল’ (১৭৬২), রুডিয়ার্ড কিপলিং (১৮৬৫-১৯৩৬) এর ‘জাঙ্গল বুক’ (১৮৯৪) এবং এডগার রাইস বারোজের (১৮৭৫-১৯৫০) ‘টারজান’ (১৯১২)।
ইবনে তোফায়েলের হাই ইবনে ইয়াকজান ১৭ ও ১৮ শতকে সমগ্র ইউরোপে বেস্টসেলার বইয়ে পরিণত হয়েছিলো। আজও ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই উপন্যাসের অনুবাদ, গবেষণা ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ইউরোপের প্রায় সবক’টি ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশে উর্দু ও বাংলায় এর অনুবাদ হয়েছে। বাংলায় অনুবাদ করেছেন কাজী আখতারুদ্দিন।
Feature image source: halimedabelajarmendengar.wordpress.com
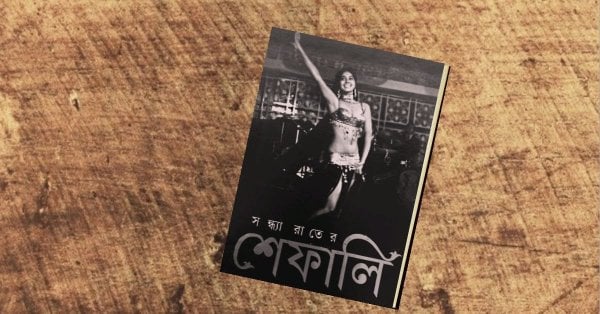
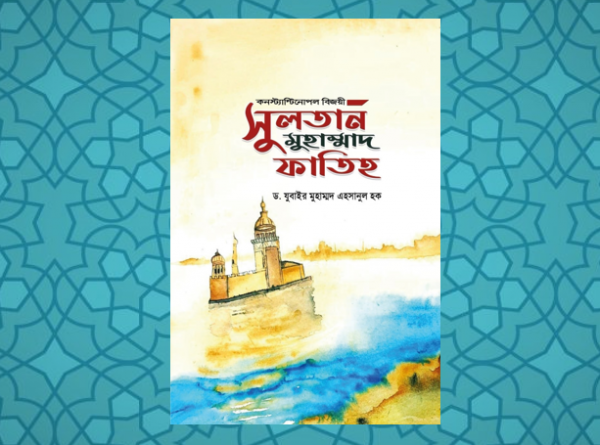
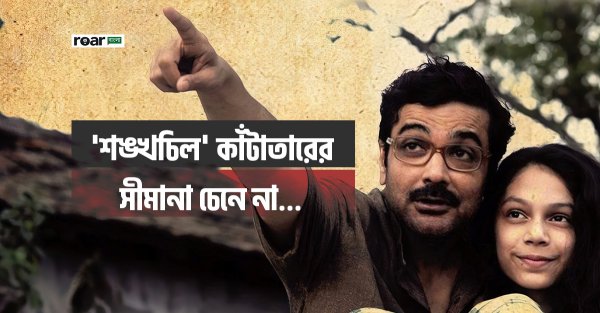
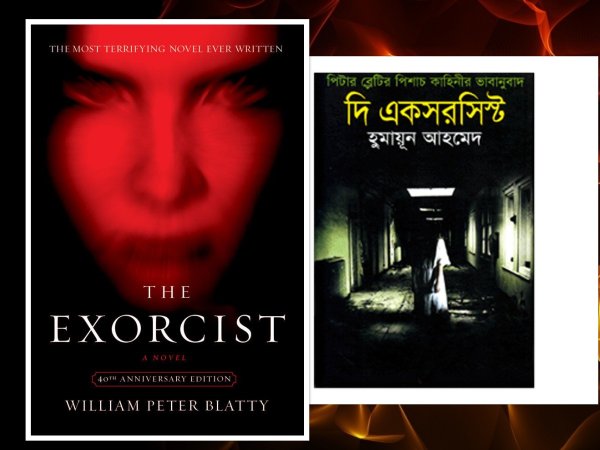



.png?w=600)