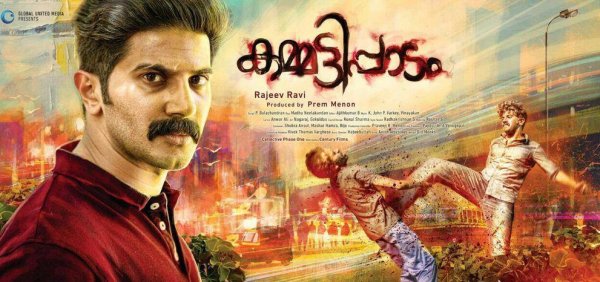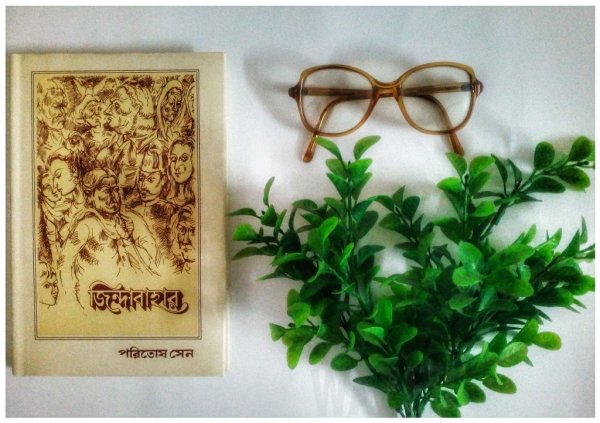প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতা, মিশরীয় সভ্যতা, সিন্ধু সভ্যতা; এই সব সভ্যতাই গড়ে উঠেছে নদীতীরে। কিন্তু এই নগরায়নের যুগে নদীতীরে যান্ত্রিক সভ্যতা গড়ে তুলতে গিয়ে নদীর অস্তিত্বকেই যে বিপন্ন করছি, সেই শোধ কি নদী কিংবা প্রকৃতি নেবে না? নিচ্ছে, এবং আরো নেওয়ার বাকি। ‘মাদার’ (২০১৭) সিনেমায় প্রকৃতির শোধ দর্শক দেখেছে। ‘ফার্স্ট রিফর্মড’ (২০১৮) সিনেমায় বিপর্যয় আর আক্ষেপও দেখেছে। তবে শীঘ্রই ৫০ বছর হয়ে আসতে চলা এই আলোচিতব্য সিনেমায়, প্রকৃতি আর মানুষের আদিম পশুবৃত্তির যে রূপ দর্শক দেখেছে, তা আজো স্মরণে রয়ে যায়। আজো সিনেমার সেই ‘মেইল সোডোমি’র বহুল আলোচিত দৃশ্যের বীভৎসতা চোখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য করে। ভয় পেতে বাধ্য করে।
সিনেমার প্রারম্ভিক দৃশ্য দিয়েই আরম্ভ করা যাক। পর্দায় নাম ভেসে আসতে আসতেই ব্যাকগ্রাউন্ডে শোনা যায় হাসি। তারপর ক্যামেরা সরাসরি চলে যায় নদীর নিবিড়তাকে ধরার উদ্দেশ্যে। ক্যামেরা শান্তভাবে এগিয়ে চলছে। ব্যাকগ্রাউন্ডে একজনের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। নদীর ভবিষ্যৎ নিয়ে সে উদ্বিগ্ন। কারণ, এই নদীতীরেই গড়ে তোলা হবে বেড়িবাঁধ। ইলেকট্রিক ড্যাম তৈরি করা হবে। তা নিয়েই ক্ষিপ্ত ওই কণ্ঠ। আমেরিকার দক্ষিণের এই বেঁচে থাকা শেষ নদীও এবার মরতে যাচ্ছে। বাকিরা তাকে উন্নয়ন দেখতে বলে। সে আরো ক্ষিপ্ত হয়। প্রতিশোধের চিত্রের আক্ষরিক আর রূপক দুই রূপই দেখতে পাওয়া যায় ‘ডেলিভারেন্স’ (১৯৭২) সিনেমায়।
নদীর দৃশ্য, বেড়িবাঁধ বানানোর কার্যক্রম, মাইন বিস্ফোরণের দৃশ্য; যেসব দৃশ্যের বক্তব্য হলো প্রকৃতির প্রতি মানুষের অবিচার, সেসবের দীর্ঘ মন্তাজ শেষে ক্যামেরা চলে যায় রাস্তা ধরে ছুটে চলা গাড়িগুলোর দিকে। ব্যাকগ্রাউন্ডে সিনেমার প্রধান চরিত্ররা তখনো কথা বলছে, কিন্তু কারো চেহারাই তখনো দেখা যায়নি। সেমি-ইম্প্রোভাইজড সংলাপে তাদের কথোপকথন চলছে। তারা চারজন। প্রত্যেকেই শহুরে। সপ্তাহান্তে এসেছে দক্ষিণের এই ক্যানোয়ি নদীতে কায়াকিং করতে। অবশ্য চারজনের মাঝে লুইসই আসলে এ ভ্রমণের আয়োজন করেছে। তার উপস্থিতিতে দলপতি বা নেতা গোছের ভাব এমনিতেই পাওয়া যায়। গাড়ি ছুটিয়ে এসে তেল ভরার বিরতি নিল তারা। ভাগ্যিস নিয়েছিল, তার কারণেই একটা ক্লাসিক দৃশ্যের সূচনা হলো।
ওইযে সিনেমার বিখ্যাত ‘ডুয়েলিং ব্যাঞ্জো’ কভারের দৃশ্য; এ দৃশ্যে প্রথমেই শহর আর গ্রামের মানুষদের একটা ‘কন্ট্রাস্ট’ চোখে পড়ে। গোটা সিনেমাতেই সেটা অভিঘাতী রূপে আছে অবশ্য। এ দৃশ্যে দেখা যায়, শহুরে অতিথিরা একটু বেশিই বিশৃঙ্খল করে তুলছে গ্রামের শান্ত ও নির্জন ভাবটাকে। গ্রামের লোকেদের নিয়ে তারা কৌতুক করছে, হাসছে। তারা যে অনাকাঙ্ক্ষিত অতিথি, গ্রামের লোকেদের নীরবতাতেই সেটা বুঝতে পারা যায়। তবে ক্ষণিকের জন্য গোটা বিষয়টিই স্মরণের আড়াল হয়ে থাকে চার বন্ধুর মাঝে একজনের গিটারের টুংটাং শব্দে। একটা সুর ধরার চেষ্টা করছে সে। এক সুরেই বুঝি সে শহর আর গ্রামকে বাঁধতে চায়।
এবং অনেকটা বেঁধেও ফেলে। তাইতো ব্যাঞ্জো হাতে গ্রাম্য এক অদ্ভুতুড়ে বালক ঠিক একই সুরটা ব্যাঞ্জোতে তুলছে। একদিকে গিটার, আরেকদিকে ব্যাঞ্জো। সুরের ধুয়া হয়ে উঠছে আরো মন মাতানো। সম্পাদনায় বিজোড় কাটগুলোকে মন্তাজের মতো সাজিয়ে সুরের ছন্দকে পুরোপুরি ছান্দসিক করে তোলা হয়েছে এ দৃশ্যে। একবার শহুরে যুবকের গিটার, আরেকবার গ্রাম্য কিশোরের ব্যাঞ্জো, বাকি তিন বন্ধুর হাসি হাসি মুখ; তাতে শহুরে গৌরব আর অহংকারও মিশে আছে। আরেকদিকে সুরের তালে তালে পা মেলানো বৃদ্ধ। সবকিছু যুগপৎভাবে ধরে সুরের ছন্দে নাচতে নাচতে এগিয়ে চলে দৃশ্যটি।

Image Source: Warner Bros.
দৃশ্যটির শেষভাগের এই সিক্যুয়েন্স আলাদাভাবে দেখা দরকার। দুই সুর যখন চূড়ান্ত স্কেলে পৌঁছাচ্ছে, তখনকার একটা শট দেখা যায়, লো অ্যাঙ্গেল থেকে। শহুরে যুবক ক্যামেরার দিকে পিঠ রেখে দাঁড়িয়ে বাজাচ্ছে। ওদিকে গ্রাম্য বালক মাচায় দুলুনিতে বসে বাজাচ্ছে, শান্ত কিন্তু দৃঢ়ভাব ধরে রেখে। নিখুঁত সিন ব্লকিংয়ের এই কম্পোজিশনে লো অ্যাঙ্গেল ধরায়, গ্রামের চরিত্রটিকে একটা সুপিরিয়র আকৃতি হয়ে উঠতে দেখা যায় শহুরে চরিত্রের কোণ থেকে। সেটা একদিক থেকে ধরা যেতে পারে বাজানোর নিপুণ দক্ষতা অনুযায়ী। কিন্তু আবার জিনিসটাকে একটা সূক্ষ্ম ফোরশ্যাডো’র রূপেও দেখতে পারা যায়। এই অঞ্চল তাদের। ভিটে তাদের। শহুরে চারজনের জায়গা এখানে নয়। এখানের শ্রেষ্ঠত্বটা গ্রামের মানুষদেরই। তাদের মনোভাব আর তেরছা দৃষ্টিতে সে বার্তা পরিষ্কার। খানিক বাদে সেটার আক্ষরিক রূপ দর্শক দেখতেও পায়।
এরপর চার বন্ধু যায় গ্রামের এক লোকের খোঁজে ক্যানোয়ি নদী যাওয়ার পথটা যে চিনিয়ে দিতে পারবে। সে দৃশ্যেও নিগূঢ় ভয়ের এক আবহ সৃষ্টি হয়। গ্রামের লোকটা নিষেধ করে, নদীর ওদিকে ঘেঁষতে। নদীর বিপদসংকুলতা নিয়ে সাবধান করে। খুব বুদ্ধিদীপ্ততার সাথে হরর সিনেমার ভয়ের পূর্বাভাসের কিংবা সাবধান বাণীর ট্রোপ’টা এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। শেষ অব্দি, অবশ্য ওই লোক রাজি হয়। ইঞ্জিনের গড়গড় শব্দ তুলে গাড়ি আবার ছুটতে থাকে। লুইস চরিত্রটি আপাদমস্তক অহমে পরিপূর্ণ। তথাকথিত পৌরুষবোধ তার মাঝে বাকি সবার চেয়ে বেশি। সবকিছুকেই তার কাছে মনে হয়, একটা খেলা। ঘোড়ার বেগে গাড়ি ছুটিয়ে, গাইডের অপেক্ষা না করে নিজেই এবড়োখেবড়ো রাস্তা ধরে এগিয়ে চলার বিষয়টাতেই আরো একবার তার চরিত্রের মনস্তত্ত্ব নিয়ে জানতে পারা যায়।
অবশেষে তারা পৌঁছায় সেই নদীতে। ওয়াইড শটে মোহাচ্ছন্ন সব ল্যান্ডস্কেপের দেখা মেলে। চার বন্ধুর একজন- ববি তো উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেই উঠল, এটা তার জীবনের ‘সেকেন্ড বেস্ট’ অভিজ্ঞতা। প্রকৃতির গভীরে গিয়ে একদম আদিম উত্তেজনাটাই তারা পায়। কায়াকিং করে নদীর পাশের একটা জঙ্গলেই তারা রাতটা থাকল। দর্শকের মনে হয়, গ্রাম আর শহরের মানুষের শ্রেণিগত দ্বন্দ্বের সেই অস্বস্তিদায়ক অবস্থাটা বোধকরি পার হয়ে গেছে। কিন্তু তেমনটা আসলে হয় না।
এই বন্ধুরা, কিংবা লুইসের কথাই যদি ধরা হয়, তারা এ নদীর রক্ষক কিন্তু নয়। তারাও এখানে কিছু না কিছু নিতে এসেছে। একটা বাণিজ্যিক সম্পর্ক এই নদীর সাথে তাদের আছে, যার আভাস প্রারম্ভিকে ব্যাকগ্রাউন্ডের কথার পর জঙ্গলে কাটানো রাতের আলাপনেও পাওয়া যায়। গ্রামের লোকেরা যে প্রকৃতি প্রেমিক, তা-ও নয়। কিন্তু তারা এ নদীকে সম্মান করে। ইলেকট্রিক বাঁধ নিয়ে তারা ক্ষিপ্ত। শুরু থেকে রাখা এই কন্ট্রাস্টের চরম রূপটাই পরদিন পাওয়া যায়।

Image Source: Warner Bros.
সকাল হতেই তাদের বোট আবার ছোটে। স্রোতের সাথে এগিয়ে চলতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলে ববি আর এড। পাহাড় দেখে বোটটা থামায় দু’জনে। তখনই তাদের সাক্ষাৎ হয় গ্রামের অদ্ভুতদর্শন দুই লোকের সাথে। অপরিচ্ছন্ন, নোংরা পোশাক পরিহিত দুই লোক। সাথে আছে অস্ত্র। চোখেমুখে মিশে আছে রুক্ষতা। দুই পাটিতে নেই সবক’টা দাঁতও। উত্তর আমেরিকার ভাষায়, এদের ডাকা হয় ‘হিলিবিলি’। এড আর ববি ভেবেছিল এদের থেকে নদীর গতিপথ জেনে নেবে। কিন্তু তারা যে চূড়ান্ত মাত্রায় ভুল ছিল, সেটা বুঝতে কিছুটা দেরিই করে ফেলে।
এটাই সিনেমার সবচেয়ে আলোচিত এবং বিখ্যাত সেই দৃশ্য। পরিচালক জন বুরম্যান, দুই হিলিবিলির উপস্থিতির মুহূর্ত থেকেই একটা চাপা উত্তেজনা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন গোটা ফ্রেমে। শুধু নৃশংসতার জন্যই এ দৃশ্য আলোচিত নয়, বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাণের মুন্সিয়ানার দিক থেকেও। পর্দার নৃশংসতা ওমন প্রবল ছোঁয়াচে হয়েছেই নির্মাণের দুর্দান্ত নৈপুণ্যের ফলে।
দুই হিলিবিলি কিছুটা সামনে এসে চকচকে দৃষ্টিতে এড আর ববির দিকে তাকিয়ে দন্তহীন পাটি বের করে হেসে কিছু একটা শলা-পরামর্শ করে। তাদের আলাপের সময় এড আর ববিকে ক্যামেরায় ফোকাস আউট করে দুই হিলিবিলির বাচনভঙ্গি আর হাসিকে ক্লোজে রাখা হয়। এরপর তারা যখন ওই দু’জনের দিকে তাকায়, তখন পরিচালক বুরম্যান সুকৌশলে ফোকাস সরিয়ে আনেন ববির উপর। সফটভাবে। এডের আড়ালে চলে যায় ববি। এ দিয়ে ববির অস্বস্তিটাও পর্দায় দৃশ্যমান হয়। দুই হিলিবিলির একজন ববির শরীরে অহেতুক খোঁচা মারে। অস্বস্তিটা আরো বাড়ে। হিলিবিলির কামনাটা তখন আরো নগ্নভাবে ক্যামেরার সামনে উপস্থাপিত হয়।
বুরম্যান এ দৃশ্যে সহসা কোনো কাট করেননি। দুই হিলিবিলির উপস্থিতির পর থেকে প্রায় তিন মিনিটের একটা লং টেক নিয়েছেন তিনি। কোনোরকম কাট না থাকায় আপনা-আপনিই দর্শকের মনস্তত্ত্বে একটা উত্তেজনা জায়গা করে নেয়। ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্সের ব্যবহার, উপরের উদাহরণের মতো সূক্ষ্ম ফোকাস শিফটিং করে পরিচালক সেই উত্তেজনাকে পরিস্থিতির হাতেই তুলে দিয়েছেন। ফলে কোনো ক্লোজআপ শট আর সংকীর্ণ জায়গা ছাড়াই, একটা দমবন্ধ অনুভূতি অনায়াসেই এ দৃশ্য তৈরি করেছে।
এড আর ববি চলে যেতে নিলে সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় দুই হিলিবিলি। ক্যামেরার সেটআপ তখন থাকে পেছনে। ওখান থেকে কোনো কাট ছাড়াই ক্যামেরা প্যান করে, তারপর আবার ট্র্যাকিং শটে এই চার চরিত্রকে অনুসরণ করে। যায় জঙ্গলের আরো গভীরে। এরপর শুরু হয় এড আর ববিকে হেনস্তা করা। এডকে বাঁধা হয় গাছের সাথে। ববিকে অস্ত্রের মুখে বাধ্য করা হয় পোশাক খুলতে।

Image Source: Warner Bros.
এরপর শুরু হয় এড আর ববিকে হেনস্তা করা। প্রাণ বাঁচাতে দৌড়ায় নিরস্ত্র ববি। কিন্তু বিফলে। সিনেমার অন্যতম জনপ্রিয় সংলাপ, “আই বেট ইউ ক্যান স্কুইল লাইক আ পিগ, বয়”– এর অবতারণা, দৃশ্যে তখনই হয়। হিংস্রতাকে আরো অবশ্যম্ভাবী করে তোলে এই সংলাপ। এডকে নীরবে সবকিছুর সাক্ষী হতে হয়। সিনেমার সম্পাদনার টেবিলে, দক্ষ সম্পাদনা এই দৃশ্যের ভয়াবহতাকে আরো অনুভূতিপ্রবণ করে তুলেছে। শিকারীর অভিব্যক্তির এক্সট্রিম ক্লোজআপ শট কাট করে আরেক হিলিবিলির দন্তহীন কপাটি দেখিয়ে তারপর আবার এডের অসহায় অবস্থাকে কেন্দ্রে এনে ভয়াবহতাকে মারাত্মক প্রভাব বিস্তারকারী হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন তিনি।
সিনেমার ব্যাকরণেও তিনি এনেছেন ভিন্নতা। সাধারণত এমন দৃশ্যগুলোতে শিকারের মুখের ক্লোজআপ কিংবা এক্সট্রিম ক্লোজআপ দেখা যায়, ওদিকে শিকারীর অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে ক্লোজ শট কিংবা মিডিয়াম শট ব্যবহার করা হয়, দর্শকের মাঝে ঘৃণা আর অসহায়ত্ব জাগাতে। বেশিরভাগ সময়ই ক্যামেরার সেটিং থাকে হ্যান্ডহেল্ড। কিন্তু এক্ষেত্রে জন বুরম্যান আগের সব ব্যাকরণ ভেঙে দিয়ে লং শটের ব্যবহার করেন। হিংস্রতাকে ধরেছেন একটু দূর থেকে। একটা পাতাবিহীন গাছকে রেখেছেন মাঝখানে।
তার ওপাশে নৃশংসতা। দক্ষ এই ব্লকিংয়ের পর ফোকাস’টা আসল শিকার কিংবা শিকারিতে নয়, বরং বন্ধু এডের উপর করেন। চোখের সামনে এমন জঘন্য দৃশ্যের সাক্ষী হওয়ার যন্ত্রণা কেমন, তা তুলে ধরতেই পরিচালক এই দৃষ্টিকোণ বেছে নিয়েছেন। এবং বলাই বাহুল্য, সেটা অমোঘ রূপ পেয়েছে। কোনোরূপ আবহসঙ্গীতের ব্যবহার নেই এখানে, গোটা সিনেমায়ও তেমন নেই। ‘র’ রাখার উদ্দেশ্যে। সে কারণে চোখ ফেরাতে চাইলেও, ফেরানো যায় না এই দৃশ্যে। অস্বস্তি আর অসহায়ত্ব নিয়েই তাকিয়ে থাকতে হয়। একটা ছোট্ট ট্রিভিয়া দেওয়া যাক, সিনেমা মুক্তির পর এই দৃশ্য দেখে অনেক পর্যটকই আমেরিকার দক্ষিণে যেতে ভয় পেতেন অনেক বছর ধরে।
কবি ও ঔপন্যাসিক জেমস ডিকির উপন্যাস হতে নির্মিত, মাইলফলক সৃষ্টি করা এ সিনেমা। পরবর্তী অনেক সিনেমাকে প্রভাবিত করার পাশাপাশি, নিউ ইয়র্ক টাইমসের শ্রেষ্ঠ ১০০০ সিনেমার তালিকায় আছে এটি। আমেরিকার ন্যাশনাল ফিল্ম রেজিস্ট্রি সংরক্ষণ করার জন্য নির্বাচিতও করেছে এ সিনেমাকে। গ্রেটনেসটা তুলে ধরতেই এই দুয়েক তথ্যের উল্লেখ। এবার একটু যেতে হয়, নির্মাণের আগের ঘটনায়। উপন্যাসিক জেমস ডিকি চেয়েছিলেন, সিনেমাটা পরিচালনা করবে স্যাম পেকিনপাহ্। তিনি একদা ম্যারিনে ছিলেন। তাই ডিকি ভাবলেন, সিনেমায় প্রকৃতির গুরুত্ব এবং হিংস্রতার ব্যাপারে তারা একাত্মতা পোষণ করবেন। পেকিনপাহ্ রাজি হলেও, হয়নি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ওয়ার্নার ব্রোস। তারা ডেকে আনলেন, ততদিনে ‘পয়েন্ট ব্ল্যাংক’ (১৯৬৭), ‘হেল ইন দ্য প্যাসিফিক’ (১৯৬৮)-এর মতো সিনেমা বানানো পরিচালক জন বুরম্যানকে। নাখোশ ছিলেন ডিকি।
চিত্রনাট্যের প্রথম খসড়া ততদিনে তৈরি হলো। কিন্তু দেখা গেল, ডিকি তার উপন্যাসের ছোটবড় সব ঘটনাদি রক্ষায় অনেক বেশি সচেতন। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা শুধু একটা দৃশ্য কীভাবে শুরু হবে, সে বর্ণনা দিয়ে গেছেন। তাতেই শেষ নয়। সাথে কোথায় ক্যামেরা বসানো হবে, কীভাবে দর্শককে ম্যান্যুপুলেট করতে হবে, সেসবও লিখেছেন। ওভাবে এগোলে আজকের এই ‘গ্রেট’ উপাধি পাওয়া হতো না। বুরম্যান এই খসড়া বাদ দিয়ে, ডিকিকে নিয়ে দ্বিতীয় খসড়া লিখতে বসেন। বুরম্যানের সিদ্ধান্ত ছিল, ‘দেখাও, কিন্তু খুব বেশি বলবে না’ পদ্ধতি। সে কারণেই তো ওমন বিখ্যাত সব দৃশ্যের সৃষ্টি হলো। নাহয় সেই প্রথম খসড়া অনুযায়ী, একটা অতি দীর্ঘ মঞ্চগোছের সিনেমা হতো ‘ডেলিভারেন্স’।

Image Source: Film at Lincoln Center
বলতে গেলে, ‘ডেলিভারেন্স’ ছিল প্রথম ইকো-থ্রিলার সিনেমা। এবং বৈষয়িক বিবেচনায়, একটি হরর সিনেমা। প্রকৃতি কখন কোন রূপ দেখায়, সেটার আশঙ্কাই একটা হরর। তার উপর নির্যাতন আর এর পরের প্রতিশোধের রক্তাক্ত ঘটনা তো রয়েছেই। এসবই তো জীবন্ত, ছুটে চলা হরর। ভিয়েতনাম যুদ্ধের একটা পরিপ্রেক্ষিত সূক্ষ্মভাবে, কিন্তু প্রভাব বিস্তারকারী এক প্রভাবক হয়ে সিনেমায় যোগ হয়ে যায়। দক্ষিণের গ্রামের সেই লোকেদের জীবনযাত্রায়, আচরণে যুদ্ধ পরবর্তী ট্রমা চোখে পড়ে। যুদ্ধ যে তাদের স্বাভাবিক আচরণ আর মানবিকতায় আঘাত হেনেছে, শারীরিক নির্যাতনের দৃশ্যে, প্রকৃতির প্রতিশোধের পাশাপাশি সে বক্তব্যও স্পষ্ট হয়ে উঠে।
মানুষ বনাম প্রকৃতির এই গল্পের সিনেমা সাংস্কৃতিকভাবেও সমৃদ্ধ। ইতিহাসবেত্তাদের নিকট আমেরিকার দক্ষিণভাগ নিয়ে গবেষণার নানা রাস্তা তৈরি করে দিয়েছে এই সিনেমা। দক্ষিণের মাচিসমো, পরিচিতি নিয়ে হতাশা ও দ্বন্দ্বের চিত্র থেকেই অনেক অনেক তত্ত্ব আর ব্যাখ্যার উপায় খুঁজে পাওয়া যাবে। এতসবের পাশাপাশি, হাইড্রো-ইলেকট্রিক বেড়িবাঁধের কারণে শীঘ্রই পাহাড়ি সংস্কৃতি আর সভ্যতার বিলীন হয়ে যাওয়া নিয়ে বিলাপের সুর আনা যায় সিনেমায়।
ডেলিভারেন্সে আগেকার নানা ন্যারেটিভ তো বুরম্যান ভেঙেছেনই, আরো একটা ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছেন সিনেমার দ্বিতীয় অঙ্কের পর মূল চরিত্রকে সরিয়ে দিয়ে। তিন অংকের ব্যাকরণ খুব স্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে এ সিনেমায়। প্রথম অঙ্কে, কেন্দ্রীয় চার চরিত্রের গঠন, তাদের সুপিরিয়রিটির চিত্র আর গ্রাম-শহরের দ্বন্দ্ব। দ্বিতীয় অঙ্কে, ক্যানোয়ি ভ্রমণ, যেখানে ওয়াইড লেন্সে উঠে আসে নদী আর প্রকৃতির শান্ত, মনোরম অবস্থা। চোখ আর মনকে সজীব করে দেয় এই অংশের ভিজ্যুয়াল। এই অঙ্কে আরো আছে ধর্ষণ ও একটি হত্যার বৃত্তান্ত। এরপর আসে শেষ অঙ্ক; মূল চরিত্র অর্থাৎ লুইস, আলফা মেইল, যে চরিত্রে বার্ট রেয়নল্ডসের অসাধারণ অভিনয় তাকে চরিত্রটার প্রোটোটাইপই করে তুলেছে।

Image Source: Warner Bros.
তো এই চরিত্রকে একটা দুর্ঘটনায় সরিয়ে দিয়ে ঘোড়ার লাগাম তুলে দেওয়া হয় এড চরিত্রের হাতে। অভিনয় করেছেন জন ভয়েট। এই সিদ্ধান্ত সিনেমার গতিপথ, ঠিক নদীর গতিপথের আদলে বাঁকানোর পাশাপাশি গোটা যাত্রাটা করে তুলেছে আরো অপ্রত্যাশিত, এবং বিজেতাই হয়েছে শেষ অব্দি। ড্রিউ চরিত্রটি ছিল নৈতিকতার মাপকাঠি হয়ে। ববি অপেক্ষাকৃত ভীতু, আঁতেল গোছের চরিত্র। তাই বোঝা যায়, এই নীরব থাকা; কিছুটা দ্বন্দ্বে ঝোলা; পরিস্থিতিতে বিস্মিত করার ক্ষমতা রাখা এডই কেন হাল ধরবে। জন বুরম্যানের পরিষ্কার দর্শনের কারণেই এত ভিন্নতা উপহার দিতে পেরেছে ডেলিভারেন্স; এবং হয়ে উঠেছে ‘ল্যান্ডমার্ক’ সিনেমা।
বুরম্যান বরাবরই কিছুটা খেয়ালী আর খ্যাপাটে গোছের এক প্রতিভা। আমেরিকান নিউ ওয়েবের সিনেমা, ইউরোপিয়ান আর্টহাউজ সিনেমা, ব্লকবাস্টার এপিক সিনেমা; সবই তিনি নির্মাণ করেছেন। এই সিনেমাটাই তো আমেরিকান নিউ ওয়েবের। আশির দশকে ব্রিটিশ সিনেমায় রেনেসাঁও এনেছেন। ভিন্ন জনরা, ভিন্ন ন্যারেটিভে কাজ করলেও নিজের একটা স্বাক্ষর ঠিকই রাখতেন। প্রকৃতি নিয়ে সূক্ষ্ম বক্তব্য, তা নিয়ে রোমান্টিকতা, স্টাইলিশ ভিজ্যুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ, বাস্তবসম্মত নির্মাণশৈলী; এসবেই তাকে খুঁজে পাওয়া যায়। এই সিনেমা সেক্ষেত্রে অবশ্যই এক সর্বোচ্চ অর্জন।

Image Source: Warner Bros.
প্রায় ৫০ বছর হয়ে এলেও আজো ‘ডেলিভারেন্স’ তার প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি। নদী ভরাট করে নদীসভ্যতার বিলীন করা, প্রকৃতিকে আরো বিরূপ করে তোলা, মানুষের পশুত্ব আরো নগ্ন আকারে বেরিয়ে আসছে তো আজকের সময়ে। বরং সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে আরো বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে এই সিনেমা। সেইসাথে নামের পাশে তার ‘গ্রেট’ স্ট্যাটাসটি দিনকে দিন আরো জ্বলজ্বলে হয়ে উঠছে।