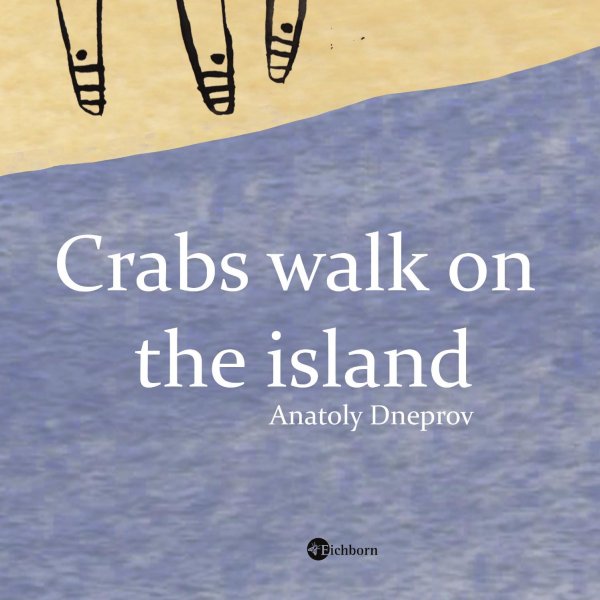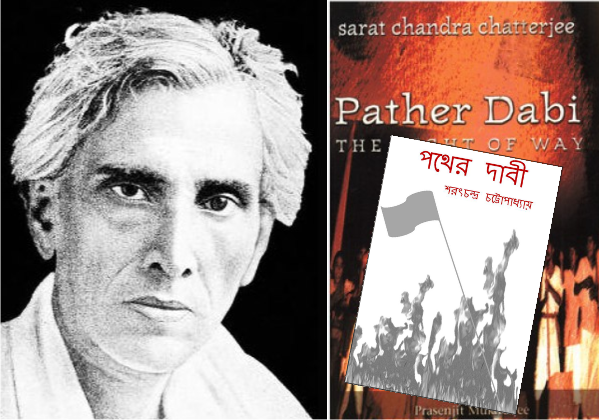ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২। উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের কালো জলরাশির বুক চিরে এগিয়ে যাচ্ছে একটি কনভয়। ৩৭টি বাণিজ্যিক জাহাজের সমন্বয়ে গঠিত এইচএক্স-২৫ নামের কনভয়টিকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে চারটি যুদ্ধজাহাজ। বহরটির গন্তব্য ইংল্যান্ডের লিভারপুল বন্দর। সৈন্যসামন্ত আর রসদে ভর্তি জাহাজগুলোর মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছে একটি কনসোলিডেটেড পিবিওয়াই ক্যাটালিনা বিমান। এয়ার এসকর্ট হিসেবে থাকা প্লেনটি পাক খেয়ে কনভয়ের সামনে অবস্থানকারী লিডিং ডেস্ট্রয়ারটির কাছাকাছি নেমে এল। এরপর সিগন্যাল লাইটের সাহায্যে মোর্স কোডে বার্তা পাঠাতে শুরু করল। ফ্লেচার ক্লাস ডেস্ট্রয়ার ‘গ্রেহাউন্ড’ও তার সিগন্যাল ল্যাম্প জ্বালিয়ে প্রত্যুত্তর পাঠাল। তারপর প্লেনটি বিশাল এক ইউটার্ন নিয়ে ফেরার পথ ধরল।
সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া চলচ্চিত্র গ্রেহাউন্ড-এর সূচনাদৃশ্য এটি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আটলান্টিক মহাসাগরের নৌযুদ্ধের ওপর ভিত্তি করে বানানো চলচ্চিত্রটিতে মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন টম হ্যাঙ্কস। মার্কিন নৌবাহিনীর একটি ডেস্ট্রয়ারের ক্যাপ্টেন চরিত্রে তাকে লড়তে হয়েছে এক দঙ্গল (উল্ফ প্যাক; কমপক্ষে আট থেকে ২০টির মতো ইউ-বোটের একত্রিত আক্রমণ) জার্মান ইউ-বোটের বিরুদ্ধে। বিশ্বযুদ্ধের সময় আটলান্টিক মহাসাগরের নৌপথ দখল নেওয়ার জন্য মিত্রশক্তি ও অক্ষশক্তি দু’দলই মরিয়া হয়ে ছিল। ব্রিটেনের অনেক প্রয়োজনীয় মালামালই তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা হতো, তাই দেশটির জন্য আটলান্টিক রুটের বিকল্প কিছু ছিল না। আবার ইউরোপিয়ান ফ্রন্টে মার্কিনীদের সেনা ও রসদ পাঠানোর জন্যও আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দেওয়া ছাড়াও আর কোনো কার্যকরী পথ খোলা ছিল না।
ওদিকে জার্মানির অপারেশন বারবারোসা‘র পর রাশিয়াকেও রসদ পরিবহনের জন্য আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর নির্ভর করতে হয়েছিল। যদি জার্মানি এ নৌরুটটি অকেজো করে দিতে পারত, তাহলে হয়তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল পুরোপুরি ভিন্ন হতো। তাই তো আটলান্টিকের বুকে ১৯৩৯-৪৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ছয় বছর নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছে মিত্র ও অক্ষশক্তি। ‘ব্যাটল অফ আটলান্টিক’ নামে খ্যাত এই নৌ-মহাযুদ্ধে মিত্রশক্তি হারিয়েছে প্রায় আশি হাজারের মতো নৌ-সেনা, বৈমানিক ও নাবিক। অন্যদিকে জার্মানির ইউ বোটের প্রায় ২৮-৩০ হাজার নাবিকের সলিল সমাধি ঘটেছে এ যুদ্ধে। আর অসংখ্য ডেস্ট্রয়ার, যুদ্ধজাহাজ, ইউ-বোট, বাণিজ্যপোত খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে আশ্রয় নিয়েছে আটলান্টিকের গভীরে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে সিনেমায় আনার হলিউড-প্রয়াসের সর্বশেষ কীর্তি হচ্ছে গ্রেহাউন্ড। অ্যারন স্নাইডারের পরিচালনায় প্রোটাগনিস্টের চরিত্রায়নের পাশাপাশি চিত্রনাট্যও লিখেছেন টম হ্যাঙ্কস। তবে মূল গল্প ইংরেজ ঔপন্যাসিক সি. এস. ফরেস্টার-এর ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত দ্য গুড শেফার্ড উপন্যাস অবলম্বনে সিনেমাটির চিত্রনাট্য তৈরি করা হয়েছে। ৫০ মিলিয়ন ডলার বাজেটের এ সিনেমায় আবারও ক্যাপ্টেন রূপে আবির্ভূত হয়েছেন টম হ্যাঙ্কস। প্রাইভেট রায়ানকে উদ্ধার করতে নিজের জীবন দিয়ে দেওয়া ক্যাপ্টেন জন এইচ. মিলার থেকে একদল ধূর্ত, শিকারী ইউ-বোটের টর্পেডো থেকে একটি গোটা কনভয়কে রক্ষা করার গুরুদায়িত্ব কাঁধে নেওয়া ক্যাপ্টেন আর্নেস্ট ক্রজ। বন্দুক-মেশিনগান ছেড়ে এবার ম্যাপ আর দূরবীন হাতে তুলে নিলেও ক্যাপ্টেন হিসেবে হ্যাঙ্কস যেন ঠিক আগের মতোই মানিয়ে গেছেন। হয়ে উঠেছেন যেকোনো মূল্যে নিজের অধীনস্থ মানুষগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রাণপণ প্রচেষ্টারত একজন সহানুভূতিশীল সেনাপতি। ক্যাপ্টেনের চরিত্র আরেকটু ঘেঁটে দেখার আগে আমরা বরং সিনেমার গল্পখানা নিয়ে একটু জেনে নিই।
১৯৪২ সালের শীতকালে আটলান্টিক পাড়ি দিচ্ছে ক্যাপ্টেন আর্নেস্টের কনভয়। জাহাজগুলোর গায়ে বরফের কুচো জমতে শুরু করেছে। একটু উজ্জ্বল উষ্ণ রোদ্দুর তো দূর অস্ত, মাথার ওপর জেঁকে বসে আছে কালো মেঘের ছায়া। দিনের বেলায়ও তাই আটলান্টিকের জল কুচকুচে কালো দেখাচ্ছে। সমুদ্রের বিশাল বিশাল ঢেউয়ের মাথায় বারবার আছড়ে পড়ছে জাহাজগুলো। তা-ও কলাম বজায় রেখেই এগোচ্ছে বহরটি, দু-একটা হয়তো একটু মাঝেমধ্যে বিচ্যুত হচ্ছে। বাণিজ্যপোতগুলোতে খাবার-রসদের পাশাপাশি রয়েছে অসংখ্য প্রাণ, যারা জানে না তারা আদৌ ইউরোপে পা দিতে পারবে কি না। কারণ, প্রতিটি জাহাজের কাপ্তান জানেন, যেকোনো সময় তার জাহাজটি আতশবাজির মতো বিস্ফোরিত হতে পারে। কে জানে, হয়তো তাদের চলার পথের ঠিক নিচেই কোনো ইউ-বোট তার টর্পেডো টিউবের দরজা খুলছে! হয়তো একটু পরই কিছুদূরের পানিতে চকচকে পিঠ দেখিয়ে প্রায় চুপিসারে কোনো টর্পেডো সবেগে ধেয়ে যাবে কোনো জাহাজকে বিষচুম্বন দেওয়ার জন্য। আটলান্টিকের এই মরণফাঁদ এড়ানোর জন্য এই বেসামরিক জাহাজগুলোর এখন একমাত্র ভরসা ক্যাপ্টেন আর্নেস্টের ইউএসএস কিলিং ডেস্ট্রয়ার (কলসাইন গ্রেহাউন্ড) ও তার সাথে আরও তিনটি ছোট-বড় যুদ্ধজাহাজ; ব্রিটিশ ডেস্ট্রয়ার হ্যারি, ডেস্ট্রয়ার ঈগল, ও কানাডিয়ান কর্ভেট ডিকি।

প্রথমেই বলা হয়েছিল একটি ক্যাটালিনা এসকর্ট প্লেনের কথা। আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দেওয়ার সময় কনভয়গুলোকে মার্কিন বন্দর থেকে সাগরের নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত পাহারা দিয়ে নিয়ে যেত এ ধরনের এসকর্ট প্লেনগুলো। একটি নির্দিষ্ট সীমানার পর প্লেনগুলোকে আবার ফিরে যেতে হতো, কারণ এগুলোর পক্ষে একটানা বেশি দিন সমুদ্রের ওপর অবস্থান করা সম্ভব ছিল না। তেমনিভাবে ইউরোপের কাছাকাছি পৌঁছালে পুনরায় সেখান থেকে আবার কনভয়গুলোকে এসকর্ট করা হতো। অর্থাৎ, অকূল দরিয়ার মাঝখানের এক দীর্ঘ দূরত্ব কোনো প্রকার এয়ার সাপোর্ট ছাড়াই পাড়ি দিতে হতো কনভয়গুলোকে। এই দীর্ঘ বিপদসংকুল অংশটি মিড আটলান্টিক গ্যাপ বা ব্ল্যাক পিট ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল। জার্মান ইউ-বোটগুলোও তাদের শিকারের জন্য এই ব্ল্যাক পিটে ওত পেতে থাকত।
ক্যাপ্টেন আর্নেস্টের সামনে এখন একটাই চ্যালেঞ্জ, মার্চেন্ট শিপগুলোকে যেকোনো মূল্যে ব্ল্যাক পিট পার করিয়ে দেওয়া। দীর্ঘ পাঁচ দিনের এ দূরত্বে তিনি কি পারবেন ইউ-বোটে গিজগিজ করতে থাকা ব্ল্যাক পিট নিরাপদে পার হতে? তদুপরি এটাই তার প্রথম সামুদ্রিক অভিযান, সদ্য পদোন্নতি পেয়ে গ্রেহাউন্ডের ক্যাপ্টেন হয়েছেন তিনি। দেশে ফিরে বিয়ে করারও কথা রয়েছে, নিজের বাগদত্তার সাথে তেমনটাই কথা হয়েছে। মাত্র নব্বই মিনিটের এ সিনেমাটি ক্যাপ্টেনের নেতৃত্ব, নৌযুদ্ধের কৌশল, আটলান্টিকের উচ্ছলতা এসবের ওপরই নির্ভর করে এগিয়েছে। ক্যাপ্টেন আর্নেস্টের সাথে আপনিও যদি দেড় ঘণ্টা আটলান্টিকের এ শ্বাসরুদ্ধকর অভিযানে শামিল হতে চান, তাহলে সময় করে দেখে নিতে পারেন সিনেমাটি।
আর্নেস্ট ক্রজ একজন ধর্মচারী মানুষ। তাকে দেখা যায় নিয়মিত বাইবেল পাঠ করতে, খাবার গ্রহণের আগে প্রার্থনা করতে। মিলিটারিসুলভ কড়া আচরণ তার ধাতে নেই। একদম আগাগোড়া নিপাট ভদ্রলোক তিনি। মিলিটারিতে কটুবাক্য, গালির ব্যবহার অহরহ থাকলেও তিনি তা ব্যবহার করেন না, অধঃস্তন কাউকে ধমক দিয়ে কর্তৃত্ব ফলান না। তার বোটে কেউ খারাপ শব্দ ব্যবহার করলে তিনি কিছুটা মনঃক্ষুণ্ণ হন। কিন্তু তাই বলে কাপ্তান হিসেবে তিনি যে অপ্রস্তুত, তা-ও নয়। বরং আর্নেস্ট একজন মেধাবী, সুচতুর, স্মার্ট কমান্ডার।
আর্নেস্টের চরিত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, তিনি একজন মানবতাবাদী। তার কাছে তার শত্রুরাও মানুষ, ক্রাউটস (মার্কিনদের দেওয়া জার্মানদের ব্যঙ্গাতক নাম) নয়। জার্মান সাবমেরিন ডুবিয়ে দেওয়ার পর তার অধঃস্তন নাবিক যখন পঞ্চাশটা ক্রাউটস কমলো বলে তাকে অভিনন্দন জানান, ক্যাপ্টেন আর্নেস্ট শুধু ভাবলেশহীন শীতল গলায় জবাব দেন, ‘হ্যাঁ, পঞ্চাশটা আত্মাও বটে।’
ডেস্ট্রয়ারের ক্যাপ্টেন হিসেবে জীবনের প্রথম ‘কিল’ পেয়েও আর্নেস্ট আত্মপ্রত্যয়, গরিমা, বা তৃপ্তিতে ভোগেন না। তাই বিজয়ের উদযাপনেও তিনি অংশ নেন না। ইউ-বোট ধ্বংস করার প্রমাণ নিয়ে যখন অপর ডেস্ট্রয়ারের ক্যাপ্টেন কৌতুক করেন, তাতেও অংশ নেন না আর্নেস্ট।
আর্নেস্ট: এসকর্টস, গ্রেহাউন্ড। ইউ-বোটের ধ্বংসাবশেষ আমরা দেখতে পেয়েছি।
ঈগল ক্যাপ্টেন: অভিনন্দন, ক্যাপ্টেন। মাছেদের কপালে আরও কিছু খাবার জুটল।
হ্যারি ক্যাপ্টেন: সব কৃতিত্ব আপনার, স্যার। কিন্তু নৌ দপ্তরের জন্য আমাদের একটা কিছু প্রমাণ দেখানোর দরকার হবে। এমনকি ক্যাপ্টেনের প্যান্ট হলেও চলবে।
আর্নেস্ট: (কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে) নিজ নিজ স্টেশনে ফিরে যান।
জয়ের আনন্দের বদলে তার ভেতরে বরং এক অবদমিত, অব্যক্ত চাপা কষ্ট তৈরি হয়। মানুষে মানুষে হানাহানির নিস্ফল এ লড়াইয়ে তিনি নিজেকে একজন অসহায় নিমিত্তরূপে আবিষ্কার করে আহতবোধ করেন। সব মিলিয়ে ক্যাপ্টেন আর্নেস্ট ক্রজ একজন স্থিতধী, সম্মাননীয় সামরিক কর্মকর্তা হিসেবে ক্রমশঃ দর্শকের সামনে আত্মপ্রকাশ করেন।

ক্যাপ্টেনের এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তার জাহাজের বাকি সবাইকেও স্পর্শ করে। সিনেমার শুরুতে আমরা দেখি জাহাজের দুজন তরুণ নাবিক নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাঁধিয়েছেন। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, ধীরে ধীরে নাবিকেরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। কিন্তু তারপর যেই না ব্ল্যাক পিটের বিভীষিকা শুরু হয়, তখন দেখা যায় পুরো জাহাজের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে এক ধরনের মোলায়েম পারস্পরিক বোঝাপড়া তৈরি হয়েছে। সবাইকে দেখা যায় পরামর্শের জন্য ক্যাপ্টেনের কাছে ছুটে আসতে, কেউ হয়তো অভিনন্দন জানাচ্ছেন, কেউ বা সিচুয়েশন রিপোর্ট দেখাতে আসছেন, আবার কেউ বা ক্যাপ্টেনের সামরিক হেলমেট যথাস্থানে রাখছেন পরম যত্নে। আবার ক্যাপ্টেন স্বয়ং গিয়ে জাহাজের ন্যাভিগেটরকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছেন যুদ্ধে নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য।
সামরিক কঠোর নির্দেশনা প্রদান বা মানার তেমন বালাই নেই এখানে, পুরো জাহাজটিই যেন একটি পরিবার। আর এই পুরো আত্মিক সংযোগের মধ্যে একটি চরিত্র খুব বেশি করে প্রকাশিত হতে থাকেন। তিনি হচ্ছেন জাহাজের রাঁধুনি জর্জ ক্লিভল্যান্ড। আমরা দেখি, প্রৌঢ় এই আফ্রিকান-আমেরিকানের ধ্যানজ্ঞান হলো ক্যাপ্টেন ঠিকমতো খাচ্ছেন কি না তা নিশ্চিত করা। তাই তাকে সবসময় দেখা যায় ক্যাপ্টেনের জন্য পরিপাটি করে খাবার সাজিয়ে আনতে। কিন্তু আর্নেস্ট সেই খাবার কখনো খেয়ে উঠতে পারেন না। কীভাবেই বা খাবেন, যখন তার শরণাপন্ন জাহাজগুলোতে থাকা প্রতিটি প্রাণ ক্ষণে ক্ষণে মরণের ভয়ে কেঁপে উঠছে!
গ্রেহাউন্ড-এর একটি সীমাবদ্ধতা হলো এর চরিত্রগুলোতে প্রাণের অভাব। সিনেমার শুরুতে আর্নেস্টের সাথে তার বাগদত্তার কথোপকথন দেখিয়ে আর্নেস্টের চরিত্রকে কিছুটা জীবনমুখী করার প্রচেষ্টা দেখা যায়। এমনকি সদাচারী আর্নেস্টের আচারনিষ্ঠতাও তার চরিত্রকে জীবন দানের (Characterization) উপাদান হিসেবে কাজ করে। কিন্তু পুরো সিনেমাটি স্রেফ একটি জাহাজের ওপর ভর করে এগিয়ে যায়, আর বেশিরভাগ অংশই আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণের ওপর টিকে থাকে। তাই আর্নেস্টের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলোও ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে যেতে শুরু করে। তার জায়গায় গ্রেহাউন্ডই বেশি প্রকট হয়ে ওঠে। কিন্তু সেদিক থেকে ক্লিভল্যান্ডের ছোট্ট, কম তাৎপর্যপূর্ণ চরিত্রটিই এ সিনেমায় সবচেয়ে বেশি প্রাণবন্ত, বেশি সমানুভূতিপূর্ণ।

জাহাজগুলো এগিয়ে যায়, পেছনে পেছনে ইউ-বোটও। একদম নেকড়ের মতো কনভয়টিকে অনুসরণ করে জার্মানরা। উলফ প্যাক নামটার সার্থকতা রক্ষায় মরিয়া তারা। মিত্রশক্তির জাহাজগুলোর রাডারে দেখা যায়, চারপাশ থেকে ধীরে ধীরে ঘিরে ধরছে হিটলারের সাবমেরিন বাহিনী। রাতের আঁধার হলেই আক্রমণ হানবে তারা। আর্নেস্ট জানেন, অন্ধকারে কিছুই দেখা যাবে না ডেস্ট্রয়ার থেকে। তিনি কি পারবেন এই নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে?
উত্তাল আটলান্টিকের পটভূমিতেই পুরো সিনেমা ধারণ করা হয়েছে। তাই পরিচালক ক্যামেরায় প্রয়োজনীয় ও পরিমিত ঝাঁকুনি রেখেছেন (Shaky camera)। মেঘাচ্ছন্ন দিনে কম সূর্যালোকের দরুন আলোর ব্যবহারও কম করা হয়েছে সিনেমায়। ফলে তৈরি হয়েছে অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি চমৎকার আবহ।

একটি দারুণ মন্তাজের কথা এখানে না বললেই নয়। রাতের বেলা যখন ইউ-বোটের টর্পেডোর আঘাতে একের পর এক জাহাজগুলো আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে ফুলঝুরির মতো ফেটে পড়ছিল, তখন ক্যামেরা হঠাৎ ওপরে উঠতে শুরু করে। ধীরে ধীরে বার্ডস আই ভিউ’তে এক্সট্রিম লং শটে বিশাল সমুদ্রের বুকে পুরো কনভয়টি প্রস্ফুটিত হয়। তারপর ক্যামেরা ধোঁয়াটে মেঘের রাশি ভেদ করে ওপরে উঠতে থাকে। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে কমলা আগুনের ঝলকানি আর ডিসট্রেস রকেটের সাদা আলোর গোলক উঁকি মারতে দেখা যায়। ক্যামেরা মেঘ ছাড়িয়ে আরও উর্ধ্বে আশ্রয় নিলে আমরা দেখি ওপরের আকাশ সবুজ অরোরায় ছেয়ে গেছে। দু’জায়গাতেই আলোর ঝলকানি; কিন্তু এক আলো চোখ কেড়ে নেয়, আরেকটা নেয় প্রাণ।
সিনেমার ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর (ব্লেক নিলি) বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। যুদ্ধের থ্রিল টিকিয়ে রাখতে মিউজিকগুলোর অবদান অনস্বীকার্য। আর ইউ-বোটকে ক্যামেরায় দেখানোর সময় ব্যাকগ্রাউন্ডে নেকড়ের ডাকের মতো তীব্র, করুণ, ভয়ানক সুরটি আরেকটি বড় প্রভাবক এ সিনেমার থ্রিলের।

ইউ-বোট নিয়ে আরও অনেক সিনেমা বানানো হয়েছে, যার মধ্যে জার্মান পরিচালক উলফগ্যাং পিটারসেনের দাস বুট (১৯৮১) সমালোচকদের ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছে। ‘দাস বুট’ আর ‘গ্রেহাউন্ড’-এর মধ্যে দুটো সাদৃশ্য রয়েছে। দুটো সিনেমাতেই একপক্ষের দৃষ্টিকোণ থেকে গল্প বর্ণনা করা হয়েছে। ‘দাস বুট’ আমরা দেখতে পাই ইউ-বোটের ক্যাপ্টেনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। আর ‘গ্রেহাউন্ড’ আগাগোড়া ক্যাপ্টেন আর্নেস্টের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখানো হয়েছে। দুটো সিনেমাতেই আমরা দেখি ক্যাপ্টেনরা আন্তরিকতার সাথে শত্রুর মোকাবেলা করছেন। ‘দাস বুট’-এ দেখা যায়, ক্যাপ্টেন লেফটেন্যান্ট হেইনরিখ লেম্যান-উইলেনব্রক মিত্রপক্ষের ডেস্ট্রয়ার ধ্বংস করছেন। কিন্তু সেই ডেস্ট্রয়ারের ভেতরে কী হচ্ছে, তার ক্যাপ্টেন কী পাল্টা পদক্ষেপ নিচ্ছেন, সেই জাহাজের নাবিকেরা কীরকম অনুভব করছেন, তা কিন্তু একবারের জন্যও দেখানো হয়নি। একই ব্যাপার ঘটেছে ‘গ্রেহাউন্ড’-এর ক্ষেত্রেও। জার্মান ইউ-বোটগুলোর কনিং টাওয়ারে ক্যামেরা কখনো প্রবেশের প্রয়োজন মনে করেনি। বরং বাইরে থেকে ধাবমান টর্পেডো দেখানো হয়েছে, কখনো বা কোনো ইউ-বোটের পানির নিচে টর্পেডো টিউবের দরজা খুলতে দেখা গেছে। কিন্তু গ্রেহাউন্ড-এ একটি অপ্রত্যাশিত ট্রুপ রয়েছে, যেখানে দেখা যায় ইউ-বোট থেকে জার্মান ক্যাপ্টেন রেডিওর মাধ্যমে আর্নেস্টের বহরকে হুমকি দিচ্ছে, পীড়ন (Bully) করছে। নিজেদেরকে ‘ক্ষুধার্ত গ্রে উলফ’ পরিচয় দিয়ে মিত্রশক্তির ডেস্ট্রয়ারগুলো একে একে ধ্বংস করার এই হুমকি আর্নেস্টের অবস্থানকে দর্শকদের কাছে আরও বিপদসঙ্কুল হিসেবে তুলে ধরেছে। দাস বুট বা ইউ-৫৭১ (২০০০) সিনেমায় আমরা দেখেছি, ইউ-বোটগুলো নীরবতাই পছন্দ করে। কারণ, একটু বেশি শব্দ হয়তো শত্রুদের রাডারে তাদের উপস্থিতির জানান দিয়ে দিতে পারে। তাই আশেপাশে শত্রু ডেস্ট্রয়ারের আনাগোনা টের পেলে ইউ-বোটের ভেতরে থাকা প্রতিটা প্রাণ তটস্থ হয়ে যায়। কিন্তু এ সিনেমায় তার বিপরীত চিত্র নিঃসন্দেহে বিতর্কযোগ্য।

গ্রেহাউন্ড-এর সাথে অন্য একাধিক সিনেমার কিঞ্চিৎ মিল ইচ্ছে করলেই দর্শক খুঁজে বের করতে পারেন। আগেই বলা হয়েছে, সেভিং প্রাইভেট রায়ান-এর ক্যাপ্টেন মিলারের সাথে গ্রেহাউন্ড-এর ক্যাপ্টেন ক্রজের বেশ মিল রয়েছে। এছাড়া দুটো সিনেমাতেই আরেকটি দারুণ সংযোগ খুঁজে পাওয়া যায়। দুটোতেই টম হ্যাঙ্কসের চরিত্রের জীবন-মরণের সাথে যুদ্ধবিমানের সম্পর্ক দেখা যায়। দুটোতেই আমরা দেখি প্রোটাগনিস্ট ত্রাতা হিসেবে উদ্ভূত হয়েছেন। আবার দাস বুট-এর সাথেও সিনেমাটির কেউ মিল খুঁজলে তাকে দোষ দেওয়া যাবে না। বলা যায়, টেকনিক্যালি ‘গ্রেহাউন্ড’কে বলা চলে ‘অ্যান্টি-দাস বুট’। প্রথমটাতে মিত্রশক্তির ডেস্ট্রয়ার জার্মানির সাবমেরিনের বিরুদ্ধে লড়ছে, পরেরটায় জার্মান সাবমেরিন মিত্রশক্তির ডেস্ট্রয়ারের ধ্বংস করার চেষ্টা করছে।
কিন্তু ‘দাস বুট’ বা ‘সেভিং প্রাইভেট রায়ান’-এর সিনেম্যাটিক শ্রেষ্ঠত্বের সাথে ‘গ্রেহাউন্ড’-এর তুলনা চলে না। ‘গ্রেহাউন্ড’ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শ্রেষ্ঠ সিনেমাগুলোর তালিকায় কখনোই নিজের নামটি তুলতে পারবে না। এ সিনেমার একমাত্র উপভোগ্য মুহূর্তগুলো হচ্ছে এর এঙ্গেজমেন্ট সিকোয়েন্সগুলো। ফ্রেন্ডলি ফায়ার, মিত্র জাহাজের সাথে প্রায় সংঘর্ষ, সমুদ্রের বুকে ইউ-বোট আর ডেস্ট্রয়ারের মুখোমুখি গোলাবর্ষণ ইত্যাদি দৃশ্যের টানটান উত্তেজনাপূর্ণ বাস্তবায়ন দর্শককে অবশ্যই বিনোদিত করবে। তবে পুরো সিনেমাই শুধু এরকম আক্রমণ, পাল্টা-আক্রমণ নিয়ে হওয়ায় অনেকের কাছে একে কনটেন্টের সাপেক্ষে দীর্ঘ বলে মনে হতে পারে।
টম হ্যাঙ্কসের অভিনয়শৈলী নিয়ে কথা বলা ধৃষ্টতা। কিন্তু ২০১৯ সালে আ বিউটিফুল ডে ইন দ্য নেইবারহুড চলচ্চিত্রে হ্যাঙ্কস নিজেকে যেরকম একজন সৌম্য-শান্ত-অমায়িক ভদ্রলোকের চরিত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন, সে তুলনায় ক্যাপ্টেন আর্নেস্টের চরিত্র যেন একটু সাধারণই বলা যায়। তবে এখানেও হ্যাঙ্কসের কাজকে হেলাফেলা করার কোনো অবকাশ নেই। পুরো সিনেমাই তার চরিত্রের ওপর এককভাবে নির্ভর করেছিল, ফলে স্টোরিটেলিংয়ের ভারসাম্য বজায় রাখতে মূল চরিত্র খুব শক্তিশালী হওয়ার দরকার ছিল, যেটা হ্যাঙ্কস তার নিজের মতো করেই দেখিয়েছেন।