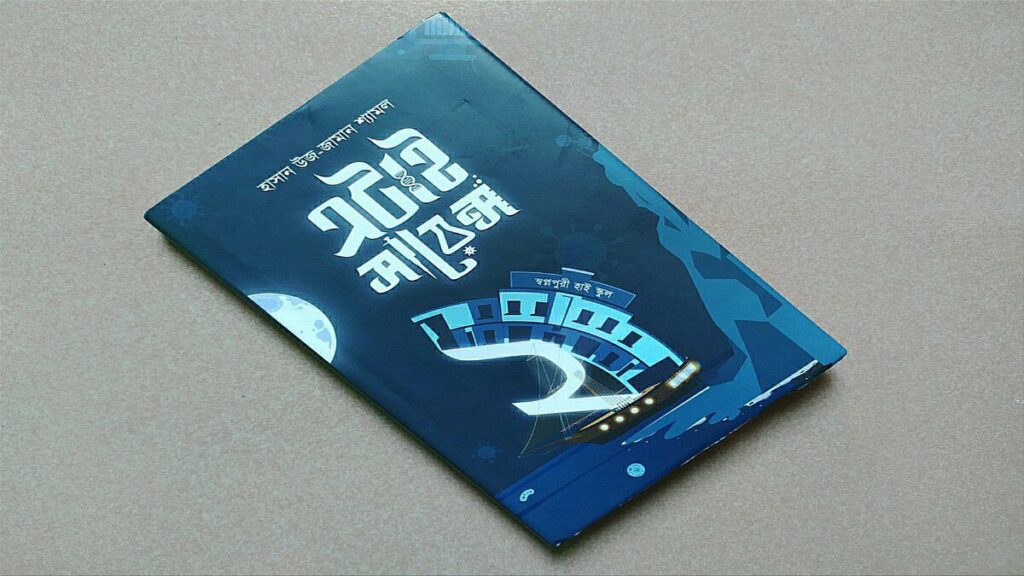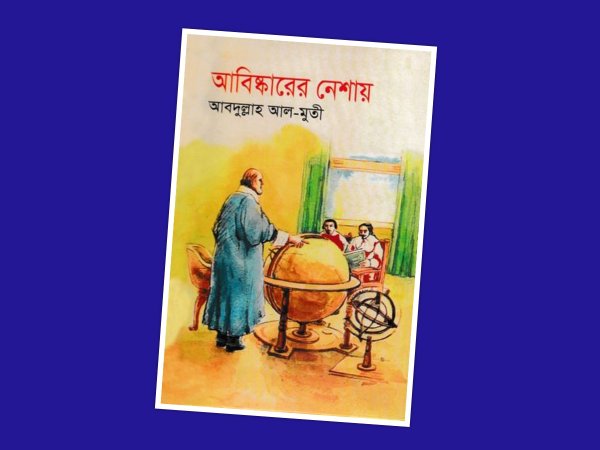লেখক মাত্রই স্রষ্টা; গল্প, উপন্যাস, কাব্য এসব তার সৃষ্টি। কখনো কখনো সৃষ্টির মহিমা ছাড়িয়ে যায় স্রষ্টাকে, স্রষ্টা পরিচিত হন তার নিজেরই সৃষ্টিকর্ম দিয়ে। প্রদোষে প্রাকৃতজন শওকত আলীর এমনই এক বিখ্যাত শিল্পকর্ম। যখনই কোথাও বাংলা সাহিত্যের এই অনবদ্য শিল্পীর নাম নেওয়া হয়েছে, সাথে তার এই শিল্পকর্মের নামও অন্তত একবার উচ্চারিত হয়েছে। শওকত আলীর পরিচয়ই হয়ে গিয়েছে ‘প্রদোষে প্রাকৃতজন খ্যাত লেখক’।
বাংলা একাডেমী পুরস্কার আর একুশে পদক পাওয়া এই লেখকের একেবারে প্রথম না হলেও, শুরুর দিককার (১৯৮৪) রচনা এই ঐতিহাসিক উপন্যাসটি। আর যে সময়ের ইতিহাস এই গ্রন্থ বর্ণনা করে তা দ্বাদশ শতাব্দীর বাংলা, যখন বাংলার শেষ রাজা লক্ষণ সেনের রাজত্বকাল প্রায় ক্ষীয়মাণ। তুর্কী মুসলমানরা বখতিয়ার খলজীর নেতৃত্বে একের পর এক নগর জয় করে ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছে তৎকালীন রাজধানী নদীয়ার দিকে।
উপন্যাসটি জাতে ঐতিহাসিক হলেও, ইতিহাস বর্ণনা এর মূল উদ্দেশ্য ছিল না। তৎকালীন সাধারণ নিচু শ্রেণির মানুষ তথা প্রাকৃতজনদের জীবনযাত্রা, জীবনদর্শন এবং তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া শত বছরের শোষণ ফুটিয়ে তোলাই ছিল এর অন্যতম উপজীব্য।

উপন্যাসের মূল চরিত্র কে তা সঠিক বলা যাবে না। কখনো মনে হবে মৃৎশিল্পী প্রাকৃতজন শ্যামাঙ্গ, আবার কখনো মনে হবে ক্ষেত্রকর বণিক বসন্তদাস। তার স্ত্রী মায়াবতী। স্বামী বাণিজ্য করতে গেছে বলে যার অবস্থান পিত্রালয়েই। এই মায়াবতীরই বাল্যবন্ধু লীলাবতী। এই লীলাবতী-ই যে প্রধান নারী চরিত্র তা নিয়ে অবশ্য সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তবুও অন্যান্য নারী চরিত্র, যেমন- মন্দিরদাসী ছায়াবতী কিংবা বিদ্রোহী কৃষ্ণা এদের কোনোভাবেই ছোট করে দেখার জো নেই।
ছোটবেলার ইতিহাস কিংবা সামাজিক বিজ্ঞান বই পড়ে আমাদের জানা এতটুকুই যে মাত্র আঠারো জন সৈন্য নিয়ে বখতিয়ার খলজী বিনা যুদ্ধে লক্ষণ সেনের রাজ প্রাসাদে ঢুকে বাংলা জয় করেন। কিন্তু বাংলা জয়ের উপাখ্যান কি এদ্দুরই? তখন সেখানকার জনগণের অবস্থা ছিল কেমন? এই জয়কে তারা কীভাবে নিয়েছিল? লক্ষণ সেনের আমলেই বা মানুষ কতটা ভালো ছিল?
গল্পের শুরু হয় একজন মৃৎশিল্পী শ্যামাঙ্গকে দিয়ে। মন্দিরের পুত্তলিকা বানিয়েই সে জীবিকা নির্বাহ করতো। তার রুচিবোধ ছিল অন্য প্রকৃতির। যে কারণে তথাকথিত স্টাইলে মূর্তি নির্মাণ না করে নিজস্ব ধরন এবং মননে বানাতো। কিন্তু কূলে সে নিচু জাতের হওয়ায় পূজা অর্চনার সর্বেসর্বা ব্রাহ্মণদের কাছে তার এই শিল্পকর্ম টেকে না। এমনকি তার গুরুদেব তাকে বলেন এইসব মূর্তি বিনষ্ট করতে।
“এ হয় না, প্রাসঙ্গিকতার ব্যাপারটি তুমি ছলনা ক্রমে আনছো, এ কেমন মুখাবয়ব, এ কেমন মুখভাব বলো? এ মানবিক লালিত্যে কি প্রয়োজন, শ্রীরামচন্দ্রের কি এই মুখাবয়ব হয় কখনো, জানকী আর যক্ষিণী মূর্তিতে যে কোন পার্থক্য নেই, এসব কাজ হবে না, বিনষ্ট করো।”
কিন্তু শিল্প মাত্রই শিল্পীর কাছে সন্তানতুল্য। তাই সে প্রতিবাদ করে। যার পরিণতিতে তাকে ছাড়তে হয় আশ্রম এবং তার গুরুদেবের সান্নিধ্য। সে বুঝতে পারে তার গুরুদেব অনেক বড় শিল্পী হলেও ব্রাহ্মণ তথা সমাজের উঁচু শ্রেণির কাছে তিনি বিক্রি হয়ে গেছেন। পথে পথে উদ্দেশ্যহীন ঘুরতে ঘুরতে সে পরিচিত হয় মায়াবতী আর লীলাবতীর সাথে। মায়াবতীর বাড়িতে আশ্রয়ও মেলে তার । মায়াবতীর মা তাকে সন্তানতুল্য করে আপন করে নেয়। কিন্তু তার নিরুদ্দেশ যাত্রা থেমে থাকেনা। সে আবারো ছুটে চলে।
মায়াবতীর স্বামী বসন্তদাস বাণিজ্যে গেছে, তাই মায়াবতী তার পিত্রালয়েই থাকেন। আর লীলাবতীর স্বামীর নাম অভিমন্যু। বিয়ের দিন রাতে সে লীলাবতীর মুখের ঘোমটা তুলে বলে, “আমার বিশ্বাস হয় না।” লীলাবতী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, “কী বিশ্বাস হয় না?” সে বলেছিল, “বিবাহে বিশ্বাস হয় না। নারীতে বিশ্বাস হয় না। তোমাকে বিশ্বাস হয় না।” সেদিন ই লীলাবতী বুঝেছিলো, এক বদ্ধ উন্মাদের সাথে তার বিয়ে হয়েছে। যে কারণে সেও পিতৃগৃহেই থাকতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

বসন্তদাস যাযাবর জীবন পছন্দ করে। পেশায় তার পিতা ক্ষেত্রকর বা চাষা। সেও হয়তো এই পেশা বেছে নিতে পারতো। কিন্তু ছোট থেকেই সে ছিল খানিকটা অন্যরকম। বাড়ি পালানোর স্বভাবটাই বড় হয়ে একদিন তাকে নিরুদ্দেশ যাত্রায় উৎসাহিত করে। টুকটাক বাণিজ্য করে করে সে ঘুরে বেড়ায়। আর লক্ষ্য করে সামন্তপতি এবং তার সৈন্যদের প্রভাব। বাণিজ্য করে লাভ যা হয়, তাও সামন্তপতিরা এসে কেড়ে নেয়। তবুও, সে কিছু টাকা হাতে নিয়ে ঘরে ফেরে। সংসার জীবন শুরু করে সে কিছুটা থিতু হলেও বেশিদিন তার সংসার ভালো লাগেনি। আবারো বাণিজ্যের কারণ দেখিয়ে সে চলে যায় বৈরাগ্যে।
পথে পথে সে ঘুরে বেড়ায়, নানান অভিজ্ঞতা হয়। যেখানেই যায়, সামন্তপতি, মহাসামন্তপতি এবং এদের অনুচরদের অত্যাচারে টেকা দায়। বিশেষ করে নিচু শ্রেণির মানুষদের উপরে অত্যাচার প্রায়শই মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। এর মধ্যে তার পরিচয় হয় কৃষ্ণা নামের এক সামন্তপতির পরিচারিকার সাথে, যে কিনা একজন বিদ্রোহী। এছাড়া পরিচয় হয় মিত্র নন্দীর সাথে। সেও একজন বিদ্রোহী। মিত্র নন্দীর তাকে বলে,
“নিজের জীবনের কথা কখনও ভেবেছেন? আপনার, আপনার পিতার, আপনার পিতামহের? মনে হয় না কি আপনি পুরুষানুক্রমে দাস? কায়স্থের দাস? আপনার কি ভগবান আছে? আপনি কি ভগবানের পূজা করতে পারেন? চণ্ডালদের কথা চিন্তা করুন, ডোম হড্ডিদের কথা চিন্তা করুন। নিম্ন-শূদ্রে কত বর্ণ ভেবে দেখেছেন? শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিভেদ, একে অপরের উপর লাঞ্ছনা করে, শোষণ করে, লুণ্ঠন করে। আপনি কি লুণ্ঠিত হননি, বলুন? সামন্তপতি যে আপনার সমস্ত কিছু অপহরণ করলো, তার প্রতিকার কোথায়?”
এছাড়াও কৃষ্ণার সাথে সাক্ষাৎ তার মনোজগতে এক আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে। লেখকের ভাষায়-
“ এবং ঐ শেষ সাক্ষাৎই তাকে যুক্ত করে দিয়েছে বৃহত্তর জগতের সঙ্গে। ঐ বিদায় যেন বিদায় নয়, বন্ধন। তারপর সে একাকী নয়। জগতের নানান প্রসঙ্গ এখন তার চিন্তা-ভাবনার বিষয় হয়ে যায়। তার বণিক জীবনের মৃত্যু ঘটেছে ফল্লুগ্রামে, বালিগ্রামে হয়েছে তার অন্ত্যেষ্টি এবং ঐ অন্ত্যেষ্টির পর আরম্ভ হয়েছে তার নতুন জীবন। সে জানে না, এই নতুন জীবনের কী নাম- কিন্তু সে একটি গভীর তাৎপর্য উপলব্ধি করে। এই উপলব্ধিটি মুক্তির। সীমারেখা থেকে মুক্তি, গণ্ডিরেখা থেকে মুক্তি, স্বার্থবুদ্ধি থেকে মুক্তি- এবং এইভাবে ঘৃণা থেকে, সংকোচ থেকে, হীনমন্যতা থেকে ক্রমাগত একের পর এক মুক্তি। ”
এরপর বসন্তদাস নিজেও একজন বিদ্রোহী হিসেবে মিত্রানন্দ এবং বৌদ্ধভিক্ষুদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে।
এর মধ্যে হয়ে গেলো এক অন্যরকম ঘটনা। পিপ্পলীহাট নামে এক জায়গায় স্থানীয় দুই ডোম নারীদের উপরে অত্যাচার করায় দুই সৈন্যকে মেরে ফেলে ডোমরা। তারই প্রতিক্রিয়া হিসেবে কিছুদিন পরে সৈন্যসহ সামন্ত নিজে এসে ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয় এবং এক নারীর যোনিদেশে লোহার রড ঢুকিয়ে হত্যা করে। এছাড়া শুলে চড়িয়ে হত্যা করে এক নিরপরাধ বৌদ্ধ ভিক্ষুকে। এই ঘটনার প্রভাব পড়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে। হত্যা, লুটতরাজ, ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়া ইত্যাদি অত্যাচারে নিচু শ্রেণির মানুষের জীবন জর্জরিত হয়ে ওঠে।
ওদিকে দেশে এসেছে যবন জাতি। লোকমুখে শোনা যায় তারা এক অদ্ভুত গোষ্ঠী। মনিব-ভৃত্য এক থালাতে বসে খায়। ভৃত্যের পেছনে মনিব উপাসনা করে। সাহসে তারা নির্ভীক, শক্তিতে তারা দুর্জয়। এই মুসলিম জাতি এসেছে তুর্কি থেকে। সামন্তপতিদের অত্যাচার থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য তাদের নাকি ডেকে এনেছে বৌদ্ধভিক্ষুরা। এই যবনজাতিরা একের পর এক নগর জয় করে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাচ্ছে রাজধানীর দিকে। কিন্তু সামন্তপতিরা ব্যস্ত নারী ভোগে এবং প্রজা নিপীড়নে।
অভিমন্যু যোগ দেয় সামন্তপতির বাহিনীতে এবং একত্রে আক্রমণ করে মায়াবতীদের গ্রাম। জ্বালিয়ে দেয়া হয় সব ঘরবাড়ি। শ্যামাঙ্গ এবং লীলাবতী পালিয়ে যায়। বসন্তদাস খুঁজে বেড়ায় মায়াবতীকে। লীলাবতী এবং শ্যামাঙ্গকে একলা পেয়ে কিছু সামন্ত সৈন্য তাদের আক্রমণ করে এবং লীলাবতীকে তুলে নিয়ে চলে যায়। যবন সৈন্যরা এই ঘটনা দেখায় তারা লীলাবতীকে উদ্ধার করে। এরপর থেকেই লীলাবতী থাকে যবন আশ্রমে।
যবন ধর্মের মহত্ত্বে লীলা মুগ্ধ হয়। সাথে সে বুঝতে পারে তার নিজের ধর্মমতে শ্যামাঙ্গের সাথে তার মিলন কখনোই সম্ভব নয়। কারণ সে বিবাহিত। কিন্তু সে লক্ষ্য করে যবন ধর্মে স্বামী-স্ত্রী অসুখী হলে ছেড়ে দিয়ে নতুন করে করে বিয়ে করতে পারে! সে শ্যামাঙ্গকে বলে,
“জানো, এদের ধর্ম একেবারেই অন্যরূপ। বিবাহ যদি সুখের না হয় তাহলে এরা দাম্পত্য বন্ধন ছিন্ন করতে পারে। এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়েই পুনর্বিবাহ করে।”
সে অতি সাধারণ বাঙালি নারী। তার পরিবার চাই, সন্তান চাই। তাই সে সিদ্ধান্ত নেয় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবার। কিন্তু শ্যামাঙ্গ নিজ ধর্ম ছাড়তে অস্বীকৃতি জানায়। তবু সে লীলাকে ছাড়তে পারে না। দোটানায় ভুগতে থাকে সে।
যবন সেনারা যত অগ্রসর হচ্ছে তত সামন্তপতিরা পালিয়ে যাচ্ছে, নয়তো নতি স্বীকার করে যোগ দিচ্ছে যবন বাহিনীতে। লক্ষণ সেন নারীসঙ্গে এতটাই অভিভূত ছিলেন যে তিনি যখন শুনলেন বখতিয়ার খলজী রাজধানীতে ঢুকে পড়েছে তিনি সাথে সাথেই নদী পথে পলায়ন করেন।

ওদিকে যবন সেনাদের সাথে যোগ দেয় অভিমন্যু। গ্রামের পর গ্রাম, নগরীর পর নগরী ধ্বংস করে সে এগুতে থাকে বিহারের দিকে। সেখানেই ছিল শ্যামাঙ্গ। বাকি সবাই নগর ছেড়ে পালালেও কয়েকজন বৌদ্ধভিক্ষুর সাথে সে রয়ে যায়। তাকে থেকে যাবার কারণ জিজ্ঞেস করা হলে সে বলে,
“সকলেই নগরী ত্যাগ করলে অতিথিদের অভ্যর্থনা কে করবে?”
এবং এটাই তার জন্যে কাল হয়ে দাঁড়ায়। যবন সেনার বর্শার আঘাতে মৃত্যুবরণ করে সে। অভিমন্যুর এসে দেখে শ্যামাঙ্গ মরে পড়ে আছে। শ্যামাঙ্গের সঙ্গে অভিমন্যুর এ দেখা যেন ছিল অবধারিত। লীলাবতীর প্রাক্তন স্বামী বনাম বর্তমান প্রেমিক। এভাবেই বাংলা জয় করে তুর্কী থেকে আগত মুসলিম সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী।
লেখক কাহিনী অসমাপ্ত রেখে গেছেন। লীলাবতীর কী হয়, মায়াবতী-ই বা কোথায়? কিংবা বসন্তদাস, এসব জানা যায়নি। তবে শ্যামাঙ্গের মৃত্যু নিয়ে লেখক নিজেই বলেছেন,
“তার মৃত্যু কি অনিবার্য ছিল? ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি রেখে আমাদের বলতে হয়, হ্যাঁ, অনিবার্যই ছিলো তার মৃত্যু। তার মতো মৃৎশিল্পীকে জীবিত থাকার অধিকার দেয়নি ঐ সময়ের সমাজ-ইতিহাস। কিন্তু সোমপুর মহাবিহারে প্রকীর্তিত শিল্পধারার উত্তরাধিকারী যে, তার নিঃশেষ মৃত্যু কি সম্ভব? আমাদের বিশ্বাস সম্ভব নয়। দৈহিক মৃত্যু হলেও প্রকৃত মৃত্যু তার হয়নি। তার সমস্ত জীবনোপলব্ধি বীজের মতো প্রোথিত ছিল অনন্ত জন্ম ধারাবাহী প্রাকৃতজনের নিত্য সংগ্রামী জীবন বৃত্তের মধ্যে।”
শাসক এর বদল হোক এটা বসন্তদাস ও চেয়েছিল। কিন্তু এরপর কী হবে? পরিবর্তে আসবেন কে? সে কি প্রজাবান্ধব হবেন? নাকি শতবর্ষের পুরানো শাসক ধারার পরিবর্তন-ই হবে শুধু, শোষণ আগের মতই চলবে? এইসব প্রশ্নের উত্তর ই খুঁজে গেছেন বসন্তদাস, যে প্রশ্নের উত্তর আমরা প্রায় ৮০০ বছর পরে এসেও খুঁজে চলেছি। তাই বলা যায়, ‘প্রদোষে প্রাকৃতজন’ উপন্যাসের চেতনা কালকে অতিক্রম করেছে। কালের নিরবচ্ছিন্ন ধারার এক খণ্ডে জন্মানো মানবজমিনে এখনো সেই একই প্রশ্ন হাজার বছর ধরে বিদ্যমান।
বইয়ের নাম: প্রদোষে প্রাকৃতজন || লেখক: শওকত আলী
প্রকাশক: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড || অনলাইন প্রাপ্তিস্থান: রকমারি.কম